
দুই নেতার জটিল সম্পর্কের সূক্ষ্ম ইতিহাস
ইতিহাসবিদ হিসেবে রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায়ের দক্ষতার অভ্রান্ত পরিচয় এই বই। আগেকার প্রধানত রাজনৈতিক ইতিহাস গবেষণার বিষয় থেকে সরে এসে এখন ‘হিস্টরি অব আইডিয়াজ’-এর প্রতি তাঁর আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে এই বইয়ে।
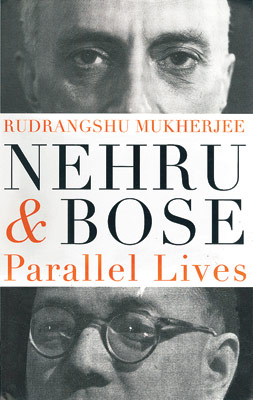
নেহরু অ্যান্ড বোস/ প্যারালাল লাইভস। রুদ্রাংশু মুখার্জি। পেঙ্গুইন ভাইকিং, ৫৯৯.০০
সুরঞ্জন দাস
ইতিহাসবিদ হিসেবে রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায়ের দক্ষতার অভ্রান্ত পরিচয় এই বই। আগেকার প্রধানত রাজনৈতিক ইতিহাস গবেষণার বিষয় থেকে সরে এসে এখন ‘হিস্টরি অব আইডিয়াজ’-এর প্রতি তাঁর আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে এই বইয়ে। বইটি একটি ইনটেলেকচুয়াল বায়োগ্রাফি, যাতে জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষচন্দ্র বসুর লেখা ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের রূপরেখাটি জানতে পারি। এঁরা দুই জনেই রাজনৈতিক জীবনে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তবু, তাঁদের বন্ধুত্বের মধ্যে নিহিত সম্ভাবনাটি শেষ পর্যন্ত অসম্পূর্ণই থেকে যায়। ১৯৩৯-এর এপ্রিলে সুভাষ দুঃখ করে বলেন, ‘ব্যক্তিগত ভাবে আমার নিজের, এবং বর্তমান সংকটের সময় আমাদের অবস্থানের সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা করেছেন পণ্ডিত নেহরু, আর কেউ না,’ (পৃ ২০৩)। আর, ১৯৪২-এর এপ্রিলে অক্ষশক্তির সাহায্য নিয়ে সুভাষ যখন ভারতকে স্বাধীন করতে চাইছেন, জওহরলাল বলেন, ‘একেবারে ভুল পথ, … আমাকে এর বিরোধিতা করতেই হবে,’ (পৃ ২৪৪)। ঘনিষ্ঠতার কিছু মুহূর্ত সত্ত্বেও তাঁদের দু’জনের জীবন ছিল ‘সমান্তরাল’। সাতটি অধ্যায়ে সময়ানুক্রমিক ভাবে ও বর্ণনাত্মক স্টাইলে বিন্যস্ত এই বই তাঁদের সেই সমান্তরাল জীবনের ছবি তুলে ধরে।
তাঁরা দুই জনেই এলিট-বৃত্তের মানুষ। দু’জনেই কেমব্রিজে পড়েছেন। দু’জনেই পেশাজীবন ছেড়েছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য। দু’ জনেই কংগ্রেসের বাম শিবিরের প্রতিনিধি ছিলেন। ইলাহাবাদ ও কলকাতায় দু’জনে দুটি মিউনিসিপ্যালিটি-র প্রধান হিসেবে কাজ করেছেন প্রায় একই সময়ে। গাঁধীর অসহযোগ আন্দোলন হঠাৎ স্থগিত হওয়ায় দু’জনেই হতাশ বোধ করেছিলেন। একই সময়ে তাঁরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ দুটি বই লিখেছিলেন। ১৯৩৫-এর জানুয়ারিতে সুভাষ ইউরোপে নির্বাসনে থাকাকালীন তাঁর দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল প্রকাশিত হয়। আর বন্দি দশায় জওহরলালের অ্যান অটোবায়োগ্রাফি লেখা শেষ হয় ১৯৩৫-এর ফেব্রুয়ারিতে। দুই জনেই তখন পারিবারিক শোকের মধ্যে: সুভাষ হারান পিতাকে, আর নেহরু, তাঁর স্ত্রী কমলাকে। সুভাষ কমলাকে প্রাগ-এ পৌঁছে দেন, সেখান থেকে লসান-এ জওহরলালের কাছে যান। লসান-এই কমলার মৃত্যু। প্রবাসী দুই বন্ধুর গভীর সংযোগের কথা আছে সংবেদনাময় অধ্যায় ‘টু উইমেন অ্যান্ড টু বুকস’-এ।
তবু যেন মানসিকতার দিক দিয়ে দু’জন অনেকটাই দূরবর্তী: তাঁদের দুটি বই আলোচনার মাধ্যমে খুলে দেখান রুদ্রাংশু। দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল অনেক ‘দৃঢ়, স্পষ্ট ভাবে রাজনৈতিক।’ তুলনায় অ্যান অটোবায়োগ্রাফি অনেক ‘অন্তর্মুখী, রাজনীতি বিষয়ে খানিক অনিশ্চিত।’ সুভাষের কাছে রাজনীতির স্থান সর্বদাই ব্যক্তিজীবনের উপর, তাই তিনি গোপনে-বিবাহিত স্ত্রী ও দুই মাসের শিশুকন্যাকে ছেড়ে দেশের ডাকে বেরিয়ে পড়তে পারেন। গাঁধীজির প্রতি সুভাষের মনোভাবেও আবেগ কম। গাঁধীর সঙ্গে প্রথম দেখায় তাঁর মনে হয়, ‘গাঁধীর দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা নেই।’ পরে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশের সঙ্গে গাঁধীর নৈকট্য, প্রত্যক্ষ আন্দোলনের বিরোধিতা, আলোচনা-অহিংসা-সমাজগঠন বিষয়ে গাঁধীর জেদ সুভাষকে বিরক্ত করে তোলে। জওহরলালেরও গাঁধীর সঙ্গে দ্বিমত ছিল। তিনিও প্রথমে তাঁকে ‘দূরবর্তী’, ‘অরাজনৈতিক’ বলে মনে করেছিলেন, ‘হিন্দ্ স্বরাজ’ বিষয়ে তাঁর সমালোচনা ছিল। তবু জওহরলাল আবেগগত ভাবে গাঁধীর উপর নির্ভর করতেন, যে নির্ভরতা তাঁর বাবা মতিলাল ও স্ত্রী কমলার মৃত্যুর পর বা়ড়তে থাকে। ‘বাপু’ ডাকটির মধ্যে এই ব্যক্তিগত আবেগের ছোঁওয়া। সুভাষ কিন্তু গাঁধীকে ‘মহাত্মাজী’ বলেই ডাকতেন। জওহরলাল মনে করতেন গাঁধীর মতো কেউ ভারতীয় সমাজের নাড়িটি বুঝতে পারে না। সুভাষ ভাবতেন, গাঁধীর ‘জাদুস্পর্শ’ নিয়ে বাড়াবাড়িটাকে চ্যালেঞ্জ জানানো দরকার।

একই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আলাদা ধরনের প্রতিক্রিয়া হত তাঁদের। গাঁধীর প্রচ্ছন্ন সমর্থনে কংগ্রেসের ‘ওল্ড গার্ড’ নেহরু ও সুভাষ, দুই কংগ্রেস প্রেসিডেন্টেরই বিরোধিতা করে। কিন্তু জওহরলাল পদত্যাগ করে বেরিয়ে আসেননি। তার একটা কারণ গাঁধীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক। তিনি এও মনে করেছিলেন যে, জাতীয়তাবাদের লড়াই এতে ব্যাহত হবে। এ দিকে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার মুখে পুনর্নির্বাচিত কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সুভাষ কিন্তু দল ছেড়ে বেরিয়ে এসে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা করেন, যাকে নেহরু একটা ‘নেতিবাচক পদক্ষেপ’ ছাড়া কিছু মনে করতেন না।
গাঁধীর ‘ছায়া’র জন্যই তাঁদের বন্ধুত্ব পূর্ণ ভাবে বিকশিত হতে পারেনি: রুদ্রাংশু বলেন। সুভাষ গাঁধীকে গুরু মানেননি, কিন্তু জওহরলালের কাছে গাঁধী ছিলেন ‘emotional anchor, a father figure.’ গাঁধীর বিরুদ্ধতা করার সময়ও নেহরু যেন ‘truant son’, অবাধ্য সন্তান। জওহরলালের দুর্বলতা সুভাষ বুঝতেন, তাই মন্তব্য করেন ‘জওহরলালের মাথা তাঁকে এক দিকে টানে, আর হৃদয় টানে গাঁধীর দিকে।’ (পৃ ২০৫)
রুদ্রাংশুর মতে, গাঁধীর সবচেয়ে খারাপ দিকটি উন্মোচিত হয় ত্রিপুরী কাণ্ডে, ‘সংকীর্ণ দলবাজির পাকে’ পড়েন তিনি। ঠিকই, এই সময়ে গাঁধীর দ্বিচারিতা অনস্বীকার্য। প্রেসিডেন্ট পুনর্নির্বাচনের বিষয়ে নেহরুর আবেদন গ্রাহ্য করেন গাঁধী। কিন্তু সুভাষের ক্ষেত্রে একই কাজ করতে তাঁর ছিল তীব্র অনীহা। সুভাষের বিষয়ে এতটা অনীহার কোনও কারণ ছিল কি? ত্রিশের দশকের মধ্যভাগেই সুভাষ গাঁধীর থেকে ভাবাদর্শগত ভাবে দূরে চলে যান, গাঁধীবাদী জাতীয়তাবাদের পর্বের সমাপ্তি ঘটিয়ে ‘ব্রিটিশ রাজ’-এর বিরুদ্ধে হিংসাত্মক আন্দোলনের কথাও ভাবেন। সুভাষের এই ‘ভিন্ নৌকায় সওয়ারি’ হওয়ার ইচ্ছেটা গাঁধীর অজানা ছিল না (পৃ ২৪৭)।
এই বই স্বভাবতই একটা প্রশ্ন তুলে দিয়ে যায়। গাঁধীর ‘ছায়া’ না থাকলেও কি তাঁদের জীবন এমন ‘সমান্তরাল’ হত? মনে হয় তাই। সুভাষ কংগ্রেস না ছাড়লেও দুই জনের রাজনৈতিক আদর্শ হয়তো ক্রমে আলাদা হয়ে যেত। জওহরলাল সারা জীবন ফ্যাসিজম ও নাৎসিজম-এর দৃঢ় সমালোচক ছিলেন, সুভাষ কিন্তু ফ্যাসিস্ট বা নাৎসি বা জাপানি বাহিনীর কোনও সমালোচনাই করেছেন বলে জানা নেই। মুসোলিনির মধ্যে ‘রাজনৈতিক উচ্চাশার প্রতিফলন’ দেখেছিলেন তিনি, হিটলারকে ‘পুরোনো ধাঁচের বিপ্লবী’ মনে করেছিলেন। ভবিষ্যৎ ভারতের জন্য ফ্যাসিজম ও কমিউনিজম-এর যে মিশ্র ভাবাদর্শের কথা ভাবতেন সুভাষ, জওহরলাল তার প্রবল বিরোধী ছিলেন। ‘বাইরের শক্তি’ দিয়ে ভারতকে স্বাধীন করার স্বপ্নও নেহরু কোনও কালে পছন্দ করেননি। জওহরলালের মনে হয়েছিল, ‘জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য এক ধরনের পথে’ তাঁরা বিশ্বাস রাখেন না। রুদ্রাংশুর ভাষায়, তাঁদের ‘জীবন কোনও সন্ধির সূত্র দিতে পারেনি।’
দুই নেতার এই সম্পর্কের মধ্যে একটা সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতাও পাওয়া সম্ভব। শেষ অধ্যায় ‘ফ্রেন্ডশিপ রিগেনড্’-এ পড়ি, আইএনএ-র প্রতি জওহরলাল কতটা সম্ভ্রম বোধ করতেন, এবং ‘জাপানি আগ্রাসনের পথটি দৃঢ় ভাবে আটকানোর জন্য’ নেতাজির প্রতিও শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর খবর আসায় নেহরু কেঁদেছিলেন। আইএনএ বন্দিদের হয়ে মামলা লড়তে নেহরু বিনা দ্বিধায় গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিলেন আইনজীবীর পোশাক। ১৯৪৬ সালের ২ জানুয়ারি সুভাষকে তিনি নিজের ‘ছোট ভাই’ বলে উল্লেখ করেন, দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে ‘সাহসী সৈনিক’ বলেন। জওহরলালের সঙ্গে একত্র উদ্যমে ইতিহাস রচনা করতে পারেননি বলে সুভাষ স্বভাবতই হতাশ বোধ করতেন, তবু সুভাষ জওহরলালকে তাঁর ‘রাজনৈতিক জীবনের বড় ভাই’ বলে স্বীকার করেছেন চিরকাল। ত্রিপুরীর ঘটনার পরেও তাঁর কাছে পরামর্শ চেয়েছেন। আইএনএ-র একটি বাহিনীর নাম রেখেছিলেন ‘জওহরলাল’। আজকের ভারতে রাজনৈতিক অসহনশীলতার দাপটে গণতন্ত্রের পরিবেশের যে করুণ হাল, তার প্রেক্ষিতে তাঁদের সম্পর্কের মধ্যে একটা বিকল্প মডেলের সন্ধান দেয় এই বই।
নেতাজি বিষয়ক সম্প্রতি প্রকাশিত ও এখনও-অপ্রকাশিত তথ্য থেকে সুভাষ-নেহরু সম্পর্ক বিষয়ে কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্ন উঠে আসতেও পারে। তবু আধুনিক ভারতের ইতিহাস-রচনায় এই বই একটি দুর্লভ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। দু’জন রাজনৈতিক নেতার সম্পর্ক, যেখানে রাজনৈতিক দূরত্বের ফাঁক দিয়ে ব্যক্তিগত মালিন্য কখনও প্রবেশ করেনি— সেই সম্পর্কের সূক্ষ্ম বুননের ভারসাম্যময় ইতিহাস কী ভাবে লিখতে হয়, এই বই তা দেখিয়ে দেয়।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য
Share this article
CLOSE- One number & One character
- Minimum 6 character
-
Forgot Password
Or
By continuing, you agree to our terms of use
and acknowledge our privacy policy







