
বাঙালি হয়ে ওঠার গোড়ার কথা
গোটা পালপর্ব ধরে চলেছে নানা সামাজিক সংশ্লেষ ও বিন্যাস, তৈরি হয়েছে নানা অন্বয় ও সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি।স্মৃতি তার চিরন্তনী খেলা পুরোদমে খেলতে শুরু করেছে... লিখছেন গৌতম ভদ্র
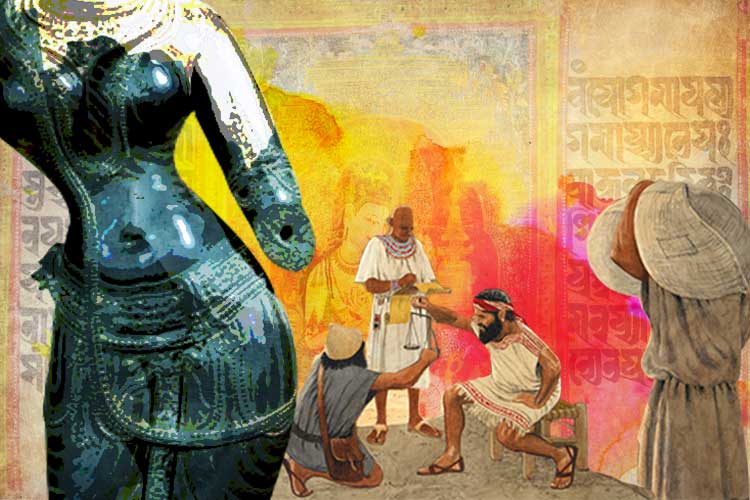
গোটা পালপর্ব ধরে চলেছে নানা সামাজিক সংশ্লেষ ও বিন্যাস।
গৌতম ভদ্র
আমার মতো বাঙালির বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে, স্মৃতি তার চিরন্তনী খেলা পুরোদমে খেলতে শুরু করেছে। ছোটবেলার পড়াশুনোটা মনে আসে, পিছুটান জাঁকিয়ে বসে, হালনাগাদ পড়া উত্তর আধুনিকতাবাদ থেকে ভার্চুয়াল মিডিয়া শোষিত উত্তর সত্যবাদের তত্ত্বগুলি বেবাক ভুলতে বসি। তাই আমাদের বাঙালিয়ানা ঠাহর করা বা বাঙালি হওয়ার মুহূর্তগুলি বা পর্বগুলি নিয়ে লিখতে বসে মনে পড়ছে স্কুলে অবশ্যপাঠ্য সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ‘আমরা’ কবিতাটি, পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকবে, গলা থাকলে আবৃত্তি করে স্কুলের অনুষ্ঠানে ছুটকো প্রাইজও পাওয়া যেতে পারে। কবিতাটিতে আমরা বাঙালি হয়ে জন্মাবার সব রকমের ঐতিহাসিক গৌরবের তুঙ্গশীর্ষগুলি ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে।
বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের কবিতা, কলকাতা আর ভারতের রাজধানী নেই, স্বদেশি আন্দোলন দীর্ণ। ঠিক এই সময়ে বাঙালিকে চাগিয়ে তুলতে একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা তো দরকার, ঘোর স্বাদেশিক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত চেষ্টার ত্রুটি করেননি, জনপ্রিয় কবিতাটির পাঠও সংস্করণভেদে মাঝে মাঝে বদল করেছিলেন। সিংহলী পুরাণ থেকে বাহুবলী বাঙালি নায়কের বি-দেশ (গ্লোবাল নয়) দখলদারির গল্পটা কীর্তি তালিকার শুরুর দিকেই রেখেছিলেন,
‘আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়, সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্য্যের পরিচয়’।
‘বাঙালীর সিংহল বিজয় একেবারে আর্কেটিপিক্যাল গল্প-তথ্য, স্বদেশি গানে, নাটকে, আত্মজ্ঞাপনের গর্বে, বার বার উল্লিখিত হয়েছে, যেমন,
‘একদা যাহার বিজয়সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়, একদা যাহার অর্ণবজ্যোত ভ্রমিল ভারতসাগর ময়’।
আরও পড়ুন: বিবেকানন্দের হিন্দুত্ব না বুঝিয়ে মানুষকে তাঁর কথা সরল ভাবেই বোঝানো যেত
আদতে সিংহলি পৌরাণিক গল্পটা অবশ্য খুব শ্রুতিসুখকর নয়। লালমাটি রাঢের অধীন সিংহবাহুর ছেলে পিতৃহন্তা বিজয়, ঘোর দুশ্চরিত্র ও অত্যাচারী, বাপে খেদানো ছেলে, সিংহলের যক্ষীকে শয্যাসঙ্গিনী করে ‘তাম্রপাণি’ দখল করেন, পিতার নামে ‘সিংহল’ রাজ্য বানান, পরে যক্ষীকে ত্যাগ করেন। যক্ষী অবশ্য গ্রিক নায়িকা মিডিয়া নয়, সে অসহায় অবস্থাতে নিহত হয়। গল্পটা গল্পই, তবে ওইটাই নাকি প্রাচীন আখ্যানে বাঙালি গৌরবের শুরুয়াত, দীনেশচন্দ্র সেন অন্তত তাই মনে করতেন। এই গল্পই নাকি ‘পৌরাণিক যুগের স্বপ্নকুহেলিকার উপরে’ বাঙালি হয়ে ওঠার ‘প্রচ্ছদপটে ইতিহাসের অরুণালোকে আসিয়া পড়িয়াছে’। নীহাররঞ্জন রায় সাবধানী ঐতিহাসিক, গল্পের মধ্যে স্মৃতির ক্ষীণ আভাস খোঁজেন। জৈন আচারাঙ্গ সূত্তে তীর্থঙ্কর মহাবীরের রাঢ়দেশে বিঘ্নিত ভ্রমণকাহিনি বা মহাভারতে পৌণ্ড্রক বাসুদেব বলে পুণ্ড্রদের কৃষ্ণবিরোধী এক রাজার গল্পের সঙ্গে এই কাহিনিটিকে মিলিয়ে তিনি আন্দাজ করেছিলেন যে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক থেকে পৌণ্ড্র, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কর্কট, সূক্ষ্ম প্রভৃতি কৌমরা এলাকায় নিজেদের ক্ষমতা সংহত করেছিল, আঞ্চলিক কিংবদন্তীর রাজারা কৌম অধিপতি ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ঐতিহ্য-বৃত্তের প্রান্তবাসী, তাদের ব্যবহার ও আচরণে সেই জীবন অভ্যাসই ধরা পড়ে। রাঢ়ে সিংহপুত্র বা সিংহবাহু বিজয়ের ডাকে কৌম রাজা, গত শতকে অনেকেই হুগলি জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার সিঙ্গুরকে সিংহপুর রাজধানী বলে চিহ্নিত করেছেন। বাঙালির আদিবীরপুরুষ দাপুটে সিংহবাহু বা তৎসন্তান বিজয়সিংহের নাম সাম্প্রতিককালে সিঙ্গুরের ভূমি আন্দোলন ও কারখানা হঠাও সংগ্রামে এক বারও শুনিনি। আত্মবিস্মৃত জাতি আর কাকে বলে!
আরও পড়ুন: গড়ে তুলি বাঙালির ‘জাতীয়’ বা ‘ন্যাশনাল’ ইতিহাস ও সংস্কারের উদ্যোগ
পৌণ্ড্র, বঙ্গ, রাঢ়, সূক্ষ্ম, ও একটু পরে সমতট (ভাটি) বরেন্দ্র প্রমুখ নানা এলাকায় নানা প্রত্নক্ষেত্র সমীক্ষা করে সভ্যতার নিদর্শন মিলেছে, পাণ্ডুরাজার ঢিবি, চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড় ইত্যাদি বেশ বোঝায় সমৃদ্ধ জনপদে বঙ্গভূমি সমৃদ্ধ ছিল, গুপ্তযুগে আর্যায়ত্রও এগিয়েছে, মহাসামন্তদের অধীনে রাজনৈতিক কেন্দ্রও জেঁকে বসেছে। সপ্তম শতকে নানা স্ব-স্বতন্ত্রপরায়ণ জনপদগুলি মিলে গৌড়ের নামের সূত্রে আবদ্ধ হল, শশাঙ্ক মুর্শিদাবাদের কর্ণ-সুবর্ণ থেকে উত্তর ভারতের মৌখরি রাজবংশ ও পুষ্যভূতি রাজবংশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হন এবং ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে থানেশ্বরের রাজ্যবর্ধন নিহত হন। শশাঙ্কই গৌড়েশ্বর, প্রতিপক্ষদের কাছে ‘গৌড়ভুজঙ্গ’ ধীরে ধীরে গৌড়সত্তার কাছে বাংলার অন্যান্য এলাকার সত্তা নিষ্প্রভ হতে থাকে। গৌড় মল্লার বেশি দিন শোনা যায়নি, যদিও গৌড়ী রীতি, আচরণ, নাগরিক, ব্যবহার, সংস্কৃত, সাহিত্যে জায়গা করে নিয়েছিল। উনিশ শতকে মাইকেলের মধুচক্র তো ‘গৌড়জন’ তথা সমগ্র বাংলাদেশের জন্য নিবেদিত ছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য টেক্কা দিল অবহেলিত বঙ্গ, বঙ্গাল, বেঙ্গলা, বাংলা তবে পশ্চিমের উপর পুবের প্রাধান্য আসতে আসতে পাঠান, মোগল ও ইংরেজ শাসন গড়িয়ে যায়। জবরদস্ত বিবরণটা অবশ্যই মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ আবুল ফজলের, একটি অনবদ্য দেশ বর্ণনা ‘প্রাচীন শাসকরা নিচু জমিতে পাহাড়ের পাদদেশে মাটি উঁচু করে ১০ ফুট ও ২০ ফুট চওড়া মাটির ঢিবি তৈরি করত, এগুলিকে বলা হত আল’। ঐতিহাসিক প্রবরের মতে, মূল ‘বঙ’-এর সঙ্গে শব্দান্ত আল প্রত্যয় হয়ে বঙ্গাল নামের জন্ম নেয়, আর তাই তো সুবে বাঙ্গালই যথার্থ নাম। গৌড়, গৌড়- বঙ্গ, বঙ্গদেশ, বঙ্গভূমি, শেষে একেবারে সত্যেন্দ্র বন্দনা, ‘সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ-ভঙ্গে, আমরা বাঙালী বাস করি সেই বাঞ্ছিতভূমি বঙ্গে’।
ওই বাঞ্ছিতভূমি বঙ্গের উপর প্রতিবেশীদের লোভের নাকি শেষ ছিলো না, তিব্বতি, কনৌজিয়া ও কাশ্মীরিরা গৌড়ে সপ্তম শতকের মাঝামাঝি থেকে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সুযোগ পেলেই হুজ্জুতি করত, আর বঙ্গভূমি জুড়ে ছোটখাটো, সামন্তনায়কদের খেয়োখেয়ির শেষ ছিল না। আর একটি মুহূর্ত, মাৎস্যন্যায়, ঘোর নৈরাজ্য বড় মাছরা ছোট মাছদের খেয়ে ফেলছে। তাম্রলিপিতে ঘটনাটা দাগানো আছে, সংকটমোচন করতে ‘প্রকৃতিপুজ্য’ গোপালদেবকে নির্বাচিত করল, বরেন্দ্রভূমির কোনও এক অজ্ঞাতকুলশীল মাতব্বর, পরবর্তী কালে এই পালদের ঠেলেঠুলে কায়স্থ বলা হয়েছে। বাঙালির দলাদলি ও খেয়োখেয়ির ইতিহাসে অনন্য ঘটনা, একমত হয়ে এক জনকে সর্ববাদীসম্মতরূপে নেতা মানা। ‘প্রকৃতিপুজ্য’ বলতে অবশ্য আমজনতা বোঝায়, এখানে এলাকা শাসক বা মাতব্বর মেনে নেওয়াই সঙ্গত। নেই নেই করে এই বংশটি প্রায় চারশত বছর ধরে বঙ্গভূমে রাজত্ব করেছে। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সরাসরি বলেছেন ‘শুদ্রশাসিত গৌরবময় যুগ’, বিতর্কিত বিশেষণ সন্দেহ নেই, তবে একেবারে ফেলনা নয়।
গোটা পালপর্ব ধরে চলেছে নানা সামাজিক সংশ্লেষ ও বিন্যাস, তৈরি হয়েছে নানা অন্বয় ও সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি। পালরাজারা ব্রাহ্মণ পোষক, ভূমিদানের অন্ত নেই অথচ বৌদ্ধবিহার, শাস্ত্রচর্চা মহাযানী-বজ্রযানী মূর্তিতে গৌড়-বঙ্গ ভরে গিয়েছিল, পোড়ামাটি স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের আলাদা রীতিই তৈরি হয়েছিল। ধর্মবিন্যাসে বামুনরা আগে ছিল কিন্তু ব্রাহ্মণতর জাতি আছে, করন-কায়স্থরা ‘রাজপাদোপজীবীনঃ’ বা আমলাতান্ত্রিক নানা কাজে লেগে পড়েছে, সৎ শূদ্র ও অসৎ শুদ্রদের থাক মিলিয়ে একেবারে ছত্রিশ জাতের নাম স্মৃতিগ্রন্থে তৈরি হচ্ছে, তাম্রলিপিতে এরা অনেকেই প্রতিবাসী, ক্ষেত্রকর বা কৃষক বা কুটুম্ব, সবশেষে মেদ, অন্ধ্র ও চণ্ডাল, একেবারে সমাজের অন্তেবাসী। শাসন আছে আবার ফসকা গেরোও আছে, নানা আদান-প্রদানে তো ধাপে ওঠানামা লেগেই আছে, নুলো পঞ্চাননের কুলজি গ্রন্থে সেই ঠেসটি শুনি, ‘বলাইত সাম্যবাদী, বিবাহ করিত ছত্রিশ জাতি। ভূমিপ হইলে হইতে চায় ক্ষত্র, রাজন্য বলিয়া বলায় যত্রতত্র’। জাতে ওঠার চাবিকাঠির মূল মন্ত্রটা ঠাহর করে দেওয়া আছে।
কৈবর্তরা ভাল ঠেলা দিয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পারেনি। অন্যপক্ষে একাধার থেকে সহজ সাধনায় জাতপাতকে নাকচ করা হচ্ছে, সমাজের বাইরে ডোম, চণ্ডাল, শবর ও কাপালিদের লোকায়ত জীবনের সহজ পন্থাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কায়া সাধনার চর্যাগীতিতে মুমুক্ষু নগ্ন শ্রমণ ও সন্ন্যাসীরাও তুচ্ছ উপমাময় ভাষা জোরদার, ‘নগ্ন হইলেই যদি মুক্তি হইত, তাহা হইলে কুকুর-শেয়ালেরও হইত, লোম উপড়ালেই যদি সিদ্ধি আসিত তাহা হইলে যুবতীর নিতম্বেরও সিদ্ধি লাভ হত’। পাল শাসনে বাঙালি যেন সাধারণ জীবনের কথা , মনের কথা বলার ভাষা পেয়েছিল। একাদশ শতকের শেষ ভাগে মালদহের জগদ্দল মহাবিহারে বিদ্যাকর বলে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ‘সুভাষিত রত্নকোষ’ বলে সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতাবলীর সংকলন করেছিলেন। মাঘ, কালিদাস বা ভবভূতির রচনার পাশাপাশি অখ্যাত বা স্বল্পখ্যাত পাল কবিদের লেখা গ্রামের কৃষিকাজ, পশুপাখি, গোদোহন থেকে দারিদ্র্য, বৃথা খাটুনি, হাভাতে বধূ, খিদের জ্বালা নিয়ে নানা চিত্র কবিতা বা ‘মুরাক্কা’ আছে, যেন এক কান্না হাসির দোলদুলানো পৌষফাগুনের পালার দেশজ পটচিত্র। মার্গ ও কৌমবনবাসী সংস্কৃতি জীবনের মাঝে দেশজ গ্রামভিত্তিক বাঙালি জীবনের রূপনির্মিতি পাল আমলেই হয়, তারই পরে রং দাগানো হয়েছে, কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের আগে পর্যন্ত খুব একটা পরিবর্তন হয়নি।

বাংলায় বাঙালি জীবন ত্রিমুখী বাঁকে পড়েছিল, হুসেন শাহির রাজত্বে বাঁকগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে
সেন রাজবংশের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির স্বল্পকাল পর্ব পুনরুত্থান ও বখতিয়ার খিলজির হামলার ক্ষণ উথালপাতালের সময়। তবে বড় চোট পেয়েছিল বৌদ্ধ কেন্দ্রগুলি, বৌদ্ধ সহজিয়ারা ছত্রখান হয়ে ঢুকে পড়েছিল নানা গ্রামের মান আশ্রিত লোকযানের, ধর্মঠাকুর, গ্রামদেবতা ও তন্ত্রের প্রলেপে গড়ে উঠেছিল নানা সম্প্রদায় ও গুহ্য সাধনার রকমফের। বাংলায় বাঙালি জীবন ত্রিমুখী বাঁকে পড়েছিল, হুসেন শাহির রাজত্বে বাঁকগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বর্ণিত তুর্কানা ও সুফিয়ানার দ্বৈত প্রক্রিয়ায় ইসলাম বাংলার নানা অঞ্চলে তার আস্তানা গাড়ল। পূর্ববঙ্গে ও দক্ষিণবঙ্গে জলাজঙ্গল কেটে গড়ে ওঠা নিম্নবর্গ ও কৌম সমাজে ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক পীররা নানা কৃষিকেন্দ্রিক কাজে বিন্দু হয়ে উঠলেন। ত্রিবেণীর দরাপ খান গাজিও বটে, আবার হিন্দু বামুনরা তাঁর নামে লেখা গঙ্গাস্তোত্র আওড়ান, পীর মুশকিল আসান বিংশ শতকের মাঝেও কলকাতার পাড়ায় মঙ্গল চামর বুলিয়ে যেতেন। ‘যোগকলন্দরে’ নাথ ও ফকির সাধনা মিলেমিশে যায়। মোহম্মদ আকবরের কবিতায় আল্লা রসুল, পুরাণ ও কোরান একটা আর একটার একই পর্যায়, রূপ নামের অন্তর মাত্র, যেমন,
‘হজরত আদম বন্দি জগতের বাপ/হিন্দু কুলে অনাদি নর প্রচার প্রতাপ।
মা হাওয়া চন্দুম জগৎ-জননী/হিন্দু কুলে কালী নাম প্রচারে মোহিনী।
হজরত রসুল বন্দি প্রভু নিজ সখা/ হিন্দু রূপে অবতারি চৈতন্য রূপে দেখা’

‘বাংলার হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই’
সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার শেষ নেই। দ্বিতীয়ত এই হুসেন শাহি বাংলাতেই ‘বাংলার হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই’ তাঁর জীবনলীলা শুরু করেন, বঙ্গীয় ভাবজগতে ভক্তির জোয়ার আনেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে নানা ধারা ছিল, হুসেন শাহীর আমলা কর্নাটকী রূপ সনাতন বৃন্দাবনে সংস্কৃত্যনুগ বৈধীভক্তি সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন, অন্যপক্ষে বাংলায় নিত্যানন্দ অবধুতের নেতৃত্বে রাধাপ্রেম ও কীর্তনে সারা বাংলায় প্রসারিত হয়, চৈতন্য-এর মধ্যে কৃষ্ণ যেন রাধা রূপে প্রেমে মাতোয়ারা, ভাগবতী বৃন্দাবন লীলা ও চৈতন্যের নবদ্বীপ লীলা যেন একটা আর একটার পরিপূরক। কীর্তন, পদাবলী চরিত জীবনী, নাটক ইত্যাদির মধ্যে নানা মানবিক ভাব ও আবেগ ভাষায় স্ফুটিত হয়। অকুণ্ঠ হৃদয়াবেগের উৎসরণী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দান, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি মৌলিক লক্ষণ। মধ্যযুগীয় কৃত্তিবাসী রামায়ণে রক্ষকুলের ভক্ত তরণীসেন ও বীরবাহুর তুলনা তুলসীদাসেও নেই, বাঙালি জীবনের ভক্তি প্রেমের প্রাবল্য এতটাই ছিল। বৃন্দাবনে গোস্বামীদের তত্ত্বসাধনা ও পুরীতে চৈতন্যের সাধক জীবনের শেষ পর্ব বাংলাকে ভারতের বৃহত্তর ভক্তি সাধনাক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। ষোড়শ শতকে গৌড়মন্ডলে বৃন্দাবন থেকে গোস্বামী শিষ্যরা ফিরে আসেন, নিত্যানন্দবাদীদের সঙ্গে সমঝোতা করেন। অবশ্যই বৈষ্ণব ভক্তদের জাতপাতের বিচার ছিল না কিন্তু সামাজিক অর্থে বৈষ্ণবরা স্মার্ত আচার মানতেন, ব্রাহ্মণরা সমাদৃত ছিল। কিন্তু জনকীর্তন ও ভক্ত সম্প্রদায়ের আবেষ্টনীতে মাহিষ্যদের মত কৃষিজীবী আর শঙ্খবণিক, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক-এর মতো উঠতি গোষ্ঠীরা গৃহস্থ হিসাবে তাদের মর্যাদার স্থান পেয়েছিল। নানা ‘ভূম’ গড়ে উঠছিল। সেগুলি ছোট ছোট জনবসতি, কৃষিকাজ ও গৃহস্থদের সামাজিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্র, এক জন অধীন বসতিতে নানা ধরনের বৃত্তির গোষ্ঠীকে মান্যতা দিয়ে ভারসাম্য রাখত। মুকুন্দরাম-এর কাব্য-আখ্যানের ব্যাধ কালকেতু এই রকম ভূমদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও দুষ্ট ভাড়ুদত্ত সব বানচাল করার চেষ্টা করে। এই ভূমদেশগুলির আরাধ্য কখনও চণ্ডী, কখনও বা কৃষ্ণ-রাধা, কখনও বা শিব বা বিষ্ণু। এই ভূমভিত্তিক দেশজ সংস্কৃতির মোজাইকে তৈরি হয়েছিল মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির রং-বেরঙ্গি নকশা, কখনও বা মল্লভূমে, কখনও বা চট্টগ্রামে। চৈতন্যদেব তো ওডিশা যাওয়ার পথে নিজে ‘ভিন্নপ্রায়’ জাতিদের মধ্যে প্রেমধর্ম বিতরণ করেন, ঝাড়খণ্ডী কীর্তন ও ঝুমুর কিন্তু বাংলারই সম্পদ। বৈষ্ণব মতে, রস এবং রসনা খুবই কাছাকাছি, বৈষ্ণব মহোৎসবে রসালো মালপোয়া, লুচি, ও নিরামিষ ব্যঞ্জনের সমাহার হত, চৈতন্যচরিতামৃত কবিরাজ কৃষ্ণদাস নানা খাদ্যরস আস্বাদনের উপমায় ভক্তিরসের বিবরণ দিয়েছেন। প্রাকৃতট গঙ্গাচরে মছলিখোর ভোজনরসিক বাঙালির খাদ্যসম্ভারকে তরকারি ও মিষ্টরসে সমৃদ্ধ করেছিল বৈষ্ণবরা বাঙালির রসিক হয়ে ওঠার এক বড় ধাপ।
বৈষ্ণবধর্মের তুলনামূলক খোলামেলা রূপের বিপরীতে মনে আসে যে এই চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকেই ‘বল্লালচরিত’-এর মতো কুলজি কাহিনি লেখা হয়, রঘুনন্দন স্মৃতিবিধান তৈরি করেন, কুলীন শীলের পরিবর্তে জাতপাতের দোষের কম-বেশি ধরে দেবীবর ঘটক উচ্চবর্গীয় সমাজের মেলবন্ধন করেন। তালিকায় দোষের রকমফের দেখলে পিলে চমকে ওঠে, ছুঁৎমার্গের যেন শেষ নেই। দোষকে ঘিরে জ্ঞাতি-গোত্র মিলিয়ে ‘সমাজ’ তৈরি হয়, মধ্যযুগীয় পুরাণে ‘সঙ্কর’ জাতির তালিকা দীর্ঘ হতে থাকে স্মার্ত নিগড়ের বিপরীতে; কৌলিন্য রক্ষা করার নানা সমীকরণের বিরুদ্ধে গল্পগুলির সামাজিক ইঙ্গিত স্পষ্ট, বজ্র আঁটুনি কিন্তু ফস্কা গেরো যবন ও ম্লেচ্ছ, নানা আর্যেতর জাতির প্রভাবে ও আনাগোনায় সমাজের মধ্যতর ও নিম্ন অংশ টলটলায়মান ছিল, বেগতিক বুঝলেই গোষ্ঠীরা নিজেদের আচার বা কৌলিক চ্যুতিকে ঘিরে একটা না একটা ‘সমাজ’ করত, মনমাফিক কুলজিও তৈরি করত।
ত্রিমুখী এই বাঁকের আশেপাশে কিছু কিছু গৌণ সাধনা বা ব্রাত্য পন্থিক জনরা থাকত, কৌম ও তন্ত্র বা লুপ্ত বৌদ্ধ সহজকায়-এর সঙ্গে তারা লগ্ন, নানা ছোট সম্প্রদায় বা ‘আউল-বাউল’দের নামে তারাও সমাজে অবস্থান করত। এরা সম্মাননীয় নয়, কিন্তু সহনীয় নানা ধরনের ভজন গোষ্ঠী, স্মার্ত নিন্দিত বর্ণাশ্রম বিরোধী।
ভক্তির প্রাবল্য ও যুক্তির জালে মধ্যযুগীয় বাংলার মনন দীর্ণ, নব্যন্যায় চর্চা ভারতীয় দর্শনে বাংলার অবদান, চৈতন্যের গৌরবতত্ত্ব পক্ষেই রঘুনাথ শিরোমণির যুক্তি বিজ্ঞান দার্শনিক তর্কের অভিনব ভাষা দিয়েছিল। এই মধ্যযুগের আবহেই লোকশ্রুতির রঘুনাথ মিথিলার পথে বাংলার অস্মিতাটুকু পলকের জন্য নাকি ঘোষণা করেন,
‘কাব্যেহপি কোমল ধিয়ো বয়মেব নান্যে, তর্কেহপি কর্কশধিয়ো বয়মেব নান্যে
তন্ত্রেহপি যন্ত্রিতধিয়ো নান্যে, কৃষ্ণেহপি সংযতধিয়ো বয়মেব নান্যে’।
‘আমরাই কাব্যে কোমলমতি, আর কেউ নয়, তর্কে আমরাই কর্কশবুদ্ধি আর কেউ নয়, তন্ত্রে আমাদেরই মতি যন্ত্রে আর কারুর নয়, কৃষ্ণে সংযত বুদ্ধি আমরাই আর কেউ নয়’। এই রকম টোকামারা কথা এর আগে কেউ উচ্চারণ করেনি।
গ্রাফিক: তিয়াসা দাস
-

সকাল ৯টা পর্যন্ত বাংলার তিন আসনে ভোটদানের হার ১৫.০৯ শতাংশ, দেশে সবচেয়ে বেশি এ রাজ্যেই
-

ইরানে প্রত্যাঘাত করল ইজ়রায়েল, ক্ষেপণাস্ত্র হানা ইসফাহানে, নিশানায় বিমানবন্দর, পরমাণুকেন্দ্র?
-

২০৪৩ বুথ, ১১২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী, বিক্ষিপ্ত অশান্তিকে সঙ্গী করেই ভোটে কোচবিহার
-

দক্ষিণের আট জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা, আরও বাড়তে পারে তাপমাত্রা, দহন থাকবে কত দিন?
Share this article
CLOSE- One number & One character
- Minimum 6 character
-
Forgot Password
Or
By continuing, you agree to our terms of use
and acknowledge our privacy policy









