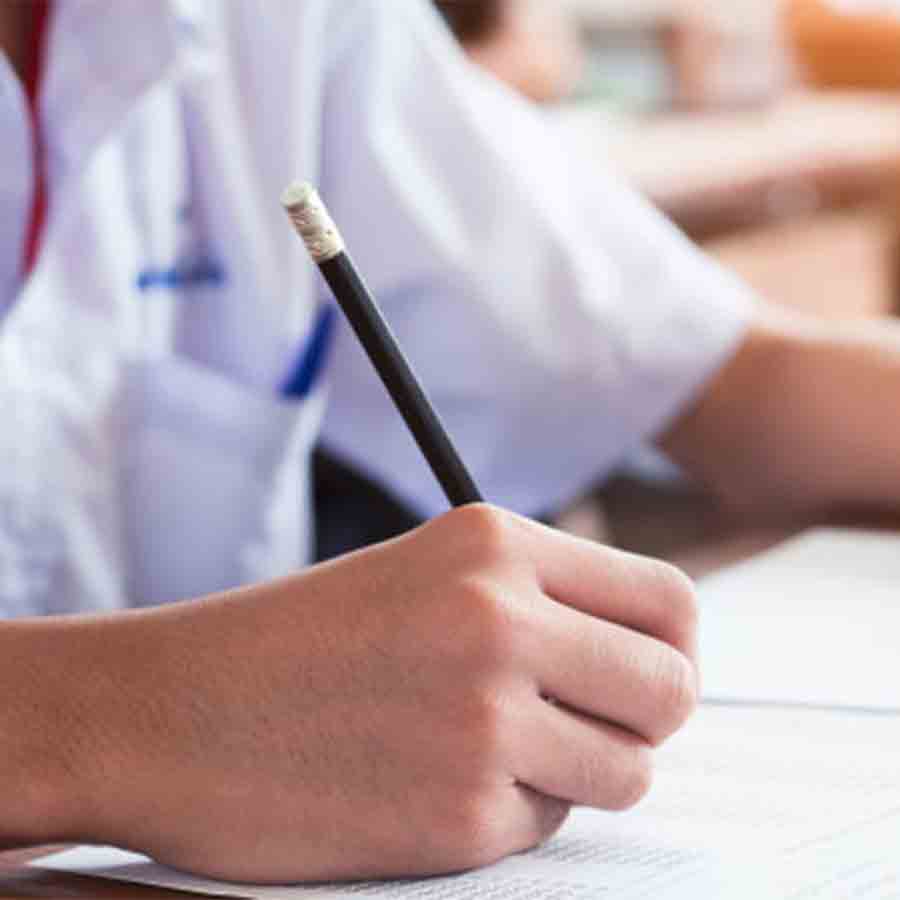চিনদেশের একটি প্রবাদপ্রতিম অভিশাপ হল— ‘তুমি এক আশ্চর্য সময়ের মধ্যে দিয়ে যাও’। আপাত ভাবে শুনলে এটি আশীর্বাদ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু কার্যত এটি ঠিক তার উলটো। এটি আসলে একটি বক্রোক্তি। যাকে উদ্দেশ্য করে এটি বলা হয়, তাকে এর দ্বারা এক শান্ত, নিস্তরঙ্গ জীবন থেকে বিচ্যুত হওয়ার অভিশাপই দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, তার জীবন ক্ষতবিক্ষত এবং দুর্যোগপূর্ণ হোক।
কেউ সাম্প্রতিক সময়ের সংবাদ শিরোনামগুলিকে লক্ষ করলে তাঁর মনে এমন প্রশ্ন জাগতেই পারে যে, আমরা কি সেই প্রাচীন চিনা অভিশাপে বর্ণিত ‘আশ্চর্য সময়’-এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি? এমন এক সময়, যখন সঙ্কটের পর সঙ্কট ক্রমাগত মাথাচাড়া দিচ্ছে। প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা অথবা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাগুলি যথাযথ ভাবে সেগুলির মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে প্রথমে সাইবেরিয়া বা উত্তর-পশ্চিম কানাডার উষ্ণতার তরঙ্গ এবং দাবানল (অন্যত্রও বটে)-কে ধরা যেতে পারে। সেই সঙ্গে ইওরোপের আধ ডজন দেশে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির কথাও মনে করা যেতে পারে। যে সব দেশের বাসিন্দারা এমন বন্যার খবর কেবল সংবাদমাধ্যম মারফত জেনে থাকতেন এবং যাঁদের ধারণা ছিল, এ সব কেবল বহুদূরের দেশে হয়ে থাকে, যাদের সম্পর্কে তাঁদের খুব স্পষ্ট ধারণা নেই।
এর পরে আমাদের সামনে চিকিৎসাবিজ্ঞান এক প্রায়-স্থায়ী সাবধানবাণী শুনিয়ে রেখেছে। সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম হুমকি দিচ্ছে, এক ‘অমর ভাইরাস’ তার প্রায় এক ডজন প্রজাতিকে নিয়ে ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে। যার বিপরীতে কোনও ‘হার্ড ইমিউনিটি’ বা সমষ্টিগত প্রতিরোধক্ষমতা তৈরি করা সে ভাবে সম্ভব নয়। ‘ফরেন অ্যাফেয়ার্স’ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধ জানাচ্ছে, ‘সার্স-কোভ-২ ভাইরাস মরবে তো না-ই, বরং তা আগামী বছরগুলিতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পিংপং বলের মতো এ দিক ও দিক দৌড়ে বেড়াবে।’ এ কথার সারবত্তা এই যে, যাকে একদা ‘স্বাভাবিক জীবন’ বলে মনে করা হত, সেই জীবনছন্দ খুব তাড়াতাড়ি ফিরবে বলে মনে হয় না। তৃতীয়ত, গণতন্ত্র এবং উদারপন্থার যুগ আপাত ভাবে মুক্ত সমাজগুলিতে ক্রমজায়মান ক্ষমতা, অস্বচ্ছতা এবং জাতীয় নিরাপত্তার অভাবে উবে যেতে বসেছে। স্বৈরতান্ত্রিক শাসকরা সর্বত্রই নতুন প্রযুক্তি মারফত নজরদারির সমাজ গড়ে তুলছেন। দানবাকার কর্পোরেট সংস্থাগুলির শুঁড় ক্রমেই সর্বত্র প্রবেশ করছে। যা আপাতত ততটা ভয়ঙ্কর বলে মনে না হলেও চিন্তার বিষয় হয়ে তো দাঁড়াচ্ছেই। কোনও সংশোধনমূলক পদক্ষেপ না ঘটলে সাহিত্যিক জর্জ অরওয়েলের বিভিন্ন রচনায় বর্ণিত ‘দুঃস্বপ্নের কাল’ নেমে আসা অসম্ভব নয়। চতুর্থত, যখন আঞ্চলিক স্তরে প্রভুত্বের উদ্দেশ্য নিয়ে চিনের বহুমুখী ক্ষমতার উত্থান শুরু হল, তখন তাকে আটকানোর জন্য আমেরিকার সংগ্রাম বিশ্বের ক্ষমতা-কাঠামোর মধ্যে এক পরিবর্তনকে দৃশ্যমান করে তুলল। তথাকথিত ‘মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ’-এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হল। এই ধরনের ক্ষমতাকেন্দ্রের বদল সাধারণত সামরিক সঙ্ঘাতের মাধ্যমেই দেখা যায়। নাৎসি জার্মানির উত্থানের পিছনে যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একটা বড় ভূমিকা ছিল। এ কথা সহজেই অনুমেয়। মনে রাখতে হবে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে জাপানের উত্থান ছিল এক দশকব্যাপী রুশ-জাপান যুদ্ধের অপ্রত্যাশিত ফল।


সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম হুমকি দিচ্ছে, এক ‘অমর ভাইরাস’ তার প্রায় এক ডজন প্রজাতিকে নিয়ে ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে। ছবি: রয়টার্স।
সাম্প্রতিক সংকটের পিছনে কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হল ক্রমবর্ধমান অসাম্য। যা ধনী-দরিদ্র-মধ্যবিত্ত নির্বিশেষে যাবতীয় দেশের সামাজিক ভবিষ্যৎ স্থিতাবস্থাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। এক আপাত অবহেলিত সচেতনতা কঠিন বাস্তব থেকে বেরিয়ে গিয়ে সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় এবং জাতিভিত্তিক বৈরিতার মধ্যে দিয়ে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে। যার জন্য দায়ী থাকবে তাদের অর্থনৈতিক স্বপ্নভঙ্গ। ইতিমধ্যে নীতিনির্ধারকরা রাজস্ব ও আর্থিক নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার সম্মুখীন হয়ে পড়তে পারেন।
এই সব ঘটনার পিছনে যে শক্তিগুলি ক্রিয়াশীল, সেগুলির শিকড় অত্যন্ত জটিল ভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক ক্রিয়াকর্মের দুর্বলতা, ইতিহাসঘটিত গণস্মৃতি, ক্ষমতা ও সম্পদের প্রতি আদিম লিপ্সা এবং প্রযুক্তির নিরন্তর কুচকাওয়াজ ইত্যাদির মধ্যে নিহিত। এই সব কিছুই এমন এক অনাগত সভ্যতার কথা বলে, যখন ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের উপরে মানবিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত। এক ধরনের বিশেষ মানব প্রজাতি নির্মিত এবং পৃথিবী বিবর্তনের কয়েকটি ধাপ পেরিয়ে গিয়েছে। প্রতিটি অগ্রগতিই এমন মায়া তৈরি করে যে, প্রতি মুহূর্তেই মনে হয়, ‘এই বুঝি আমরা সরাসরি স্বর্গে পৌঁছে যাচ্ছি’ (সাহিত্যিক চার্লস ডিকেন্সের ভাষায়)। ডিকেন্সকে অনুসরণ করে এ কথাও বলা যায় যে, আমরা সকলেই ‘ভিন্ন রাস্তায়’ সরাসরি স্বর্গে পৌঁছচ্ছি।


এক আপাত অবহেলিত সচেতনতা কঠিন বাস্তব থেকে বেরিয়ে গিয়ে সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় এবং জাতিভিত্তিক বৈরিতার মধ্যে দিয়ে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে। ছবি: রয়টার্স।
এই প্রবণতাগুলির মোকাবিলা কোনও নাগরিক কী ভাবে করবেন? পৃথিবী এই মুহূর্তে জলবায়ুগত পরিবর্তনের মারাত্মক বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তা থেকে সাবধান হওয়ার সময় চলে গিয়েছে। এ বার মাশুল গোনার পালা। সামাজিক অসাম্য এবং তা থেকে জন্মানো রাজনৈতিক বিপদগুলি নতুন সমাজ-শর্ত দাবি করে। যেখানে ধনীরা স্বল্পমেয়াদী স্বার্থরক্ষাকে দূরে সরিয়ে ভাবনাচিন্তা করবেন। এক ব্রিটিশ মন্ত্রীর কথা মনে পড়ছে, যিনি গত শতকের প্রথমার্ধে তাঁর জাতপাত ভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের জন্য যথাযথ কারণেই অপমানিত হয়েছিলেন। তাঁর নাম উইনস্টন চার্চিল। কিন্তু তাঁর কিছু অন্য দিকও ছিল।


পৃথিবী এই মুহূর্তে জলবায়ুগত পরিবর্তনের মারাত্মক বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে। ছবি: রয়টার্স।
সংস্কারক চার্চিল খনি শ্রমিকদের জন্য দৈনিক আট ঘণ্টার কাজের সময় বেঁধে দেওয়া, ন্যূনতম পারিশ্রমিকক নিশ্চিত করা, শ্রমিকদের আহারের জন্য অবকাশ নির্ধারণ করা, নিয়োগকেন্দ্র স্থাপন, বেকারদের জন্য রাষ্ট্রের তরফে ভর্তুকি-সহ বিমা প্রকল্প ইত্যাদি করেছিলেন। শোষক চরিত্রের মালিকপক্ষকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা অবশ্য তাঁর কাছ থেকে আশা করা যায় না। কিন্তু তিনি সম্পদের ভিত্তিতে করস্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। তার মানে এই নয় যে, চার্চিল একজন বাম মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। বরং বলা যায় চার্চিল ছিলেন স্বচ্ছতর ব্যবস্থার পক্ষে। তেমন স্বচ্ছতর ব্যবস্থা আবার প্রয়োজন, যা সঙ্কটাপন্ন গণতন্ত্র ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করবে। এমন ব্যবস্থা না থাকলে এই বিপন্নতার গভীরে পৌঁছে তা মেরামত সম্ভব নয়।