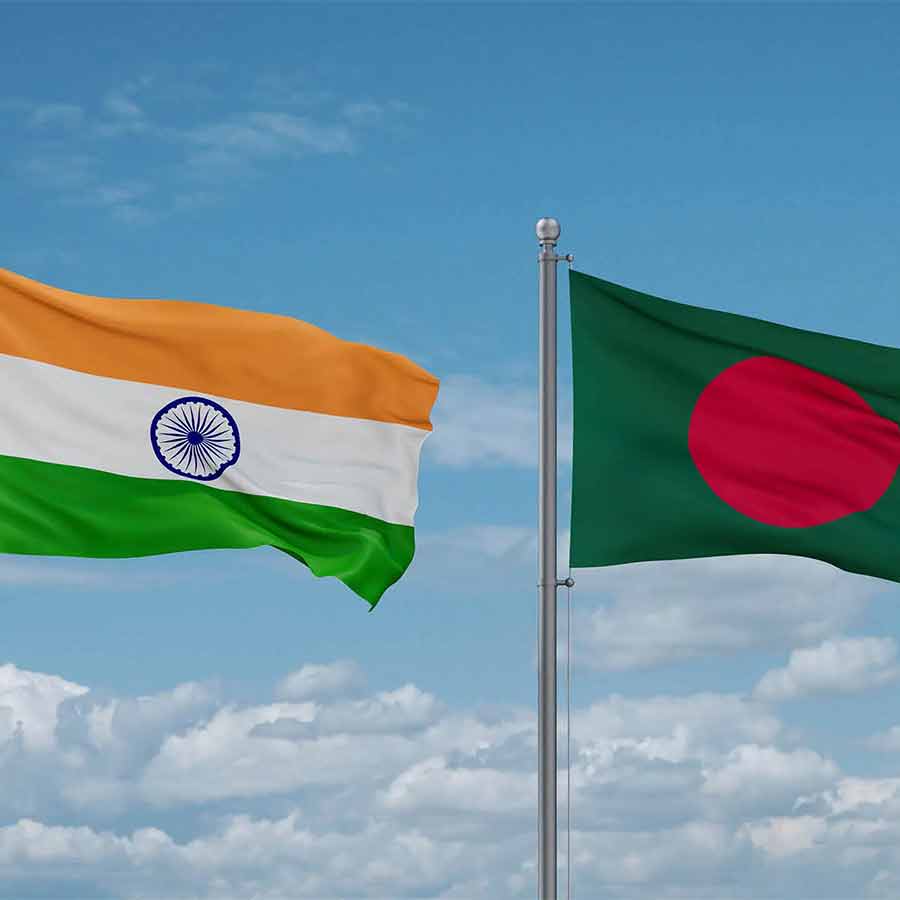সম্পাদক সমীপেষু: হাসির মহৌষধি
তথ্য বিশ্লেষণে মেশিন অবশ্যই সাহায্য করতে পারে, কিন্তু যন্ত্র মানুষের মতো উপাখ্যান সৃষ্টি করতে পারে না, ভুল স্বীকারের হাসিতে অংশগ্রহণ করতে পারে না, মানবিকতার আবেগ বুঝতে পারে না।

বিশ্বজিৎ রায়ের ‘সহাস্য জীবন্ত মানুষ’ (৩০-১১) পড়ে মনে হল, হাসির দায়িত্ব আজ শুধু বিনোদনের নয়, আত্মশুদ্ধিরও। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, শিবরাম— সবাই দেখিয়েছেন হাসি মানুষের অহং ভাঙে, সহজতা আনে, যুক্তিকে কোমল করে। রবীন্দ্রনাথ মানুষের দৃঢ়তার কেন্দ্রে দেখেছিলেন স্বচ্ছতা ও আত্মসমালোচনার শক্তি; বিবেকানন্দ বলতেন, যে হাসতে পারে, সে ভয় পায় না। এই সব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি জরুরি প্রশ্ন— আমরা কি এই হাসির ঐতিহ্যকে ধারণ করছি, না কি কেবল স্মৃতিচারণের মধ্যেই তা বাঁচিয়ে রাখছি? নীরদ সি চৌধুরীর পর্যবেক্ষণ তাই আজ খুব প্রাসঙ্গিক: নিজের অজ্ঞতা, ভুল ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে হাসতে পারাটাই প্রাজ্ঞতার প্রকৃত নিদর্শন। অথচ আজ এই জায়গাটিতেই আমরা দুর্বল। তথ্যের আধিক্য, উত্তেজনা ও মতদ্বন্দ্বের আবহে আত্মসমালোচনার নম্রতা হারিয়ে যাচ্ছে।
তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন বাস্তব— মানুষের চিন্তার জায়গায় যন্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রভাব। তথ্য বিশ্লেষণে মেশিন অবশ্যই সাহায্য করতে পারে, কিন্তু যন্ত্র মানুষের মতো উপাখ্যান সৃষ্টি করতে পারে না, ভুল স্বীকারের হাসিতে অংশগ্রহণ করতে পারে না, মানবিকতার আবেগ বুঝতে পারে না। মানবজীবনের সূক্ষ্মতা যন্ত্রের যুক্তির বাইরে। তাই মানুষ-যন্ত্রের সহাবস্থান হওয়া উচিত সহযোগিতার ভিত্তিতে, প্রতিস্থাপনের ভিত্তিতে নয়— এটিই লেখকের প্রবন্ধের অন্তর্নিহিত শিক্ষাও। এরই প্রেক্ষিতে বলতে হয়— হাসি সব সময় বই পড়ে আসে না। হাসির জন্য লাগে উদ্ভাবনী শক্তি, স্বপ্নদর্শিতা, সাহিত্যবোধের সূক্ষ্মতা। হাসির মধ্যেই ধরা পড়ে সাংস্কৃতিক মননের পরিচয়। মানুষকে মানুষ করে তোলে তার বেদনা, অভিজ্ঞতা ও স্বপ্ন— যার পরিণতিই হাসির জন্ম। হাসি বাঁচিয়ে রাখাই আজকের সমাজের সাংস্কৃতিক দায়— কারণ এই হাসিই মানুষের শেষ আশ্রয়, শেষ আলো।
অলোক কুমার মুখোপাধ্যায়সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগনা
পথহারা
বিশ্বজিৎ রায় তাঁর ‘সহাস্য জীবন্ত মানুষ’ প্রবন্ধে বর্তমান সমাজের ব্যক্তিচরিত্রের বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে পূর্বের আদর্শবাদী ঘরানার জীবনবোধকে তুলে ধরেছেন। যাঁরা নিজেদের স্বার্থ ভুলে গিয়ে হাসতেন এবং হাসাতেন। কিন্তু আজ বাঙালি নাকি অট্টহাসি দিতে ভুলে গিয়েছে। তা কিন্তু তারা ভোলেনি। তথ্যপ্রযুক্তির যুগে বিকল্প হাসিতে রূপান্তরিত হয়েছে মাত্র। অনাবিল ও নির্মল হাসির স্থলাভিষিক্ত হয়েছে নিরেট ট্রোল।
আসলে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় মানুষের দায়বদ্ধতার পরিবর্তে দায়ছাড়া ভাবই বেশি দেখা যায়। ফলে মানুষের সুকুমার প্রবৃত্তিগুলি হারিয়ে যাচ্ছে। প্রাণখোলা হাসি হাসতে গেলে সংবেদনশীল মন চাই। আর সংবেদনশীল মন গড়ার উপকরণ আমরা কোথায় পাব? কারণ হিংসা, দ্বেষ মানুষকে দিন দিন আরও অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে। তাই তো বলা হচ্ছে, হাসিটাও যেন বাণিজ্যিক হয়ে গিয়েছে। হাসির পিছনেও অভিসন্ধি বিদ্যমান।
আসলে বলিষ্ঠ জীবনবোধের অধিকারী হলে তবেই সঙ্কীর্ণতা স্পর্শ করতে পারে না। নির্ভেজাল ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবন ধাবিত হলে আত্মবিশ্বাস জন্মায় আর এই আত্মবিশ্বাসের আয়নায় প্রকৃত সত্যকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্মজীবনে ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর। কাজের পরিপ্রেক্ষিতে নানা শ্রেণির লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশার সুযোগ পেয়েছিলেন। আবার ইংরেজ কর্মচারীদের আচার ব্যবহার ও বিচারপদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁর কলমে সেই উপলব্ধি ধরা পড়েছে। অথচ আজ সমাজেরই কিছু মানুষ রাজনৈতিক মদতে পরিপুষ্ট হয়ে স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে সাম্প্রদায়িক বলছেন।
হিন্দু ধর্ম দর্শন বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীকে প্রভাবিত করেছিল ঠিকই, কিন্তু তার মধ্য দিয়েই ধরা পড়েছিল তাঁর অনন্য সমাজভাবনা। কপালকুণ্ডলায় নবকুমারের প্রথম স্ত্রী জীবন দিয়ে দেখিয়ে গিয়েছে, দাম্পত্য সম্পর্কের ঘাত, প্রতিঘাত থাকবে। কিন্তু তাকে সরিয়ে প্রেম মুগ্ধতার প্রথম ফুলটিকে বাঁচিয়ে রাখাটাই সুন্দর জীবনের শর্ত।
সে দিন অনন্ত সমুদ্রের জনহীন তীরে নবকুমারকে কপালকুণ্ডলা শুধিয়েছিল, পথিক তুমি কি পথ হারিয়েছ? সত্যিই নবকুমারের মতো পথ হারিয়েছি আমরা। তাই উদ্বিগ্ন মুখ থেকে হাসি গিয়েছে হারিয়ে।
নারায়ণ সাহা, কলকাতা-৮৪
আলোর পথে
“মহাকাশে দৈত্যাকার ‘রেডিয়ো কোয়াজ়ার’, আবিষ্কার চার বাঙালির” (২১-১১) প্রতিবেদন পড়ে মুগ্ধ হলাম। বিজ্ঞানী সব্যসাচী পাল ও তাঁর দলের এই যুগান্তকারী কাজ আমাদের গর্বিত করেছে। আমাদের চার পাশে যখন রাশিফল, গ্রহের অবস্থান আর তার শুভ-অশুভ প্রভাব নিয়ে পাতার পর পাতা ও সময় খরচ হয়, তখন এই ধরনের খাঁটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের খবর এক নতুন আশার আলো দেখায়। বিজ্ঞানীরা দূরবর্তী নক্ষত্রের আলো মেপে, তার রেডিয়ো তরঙ্গ বিশ্লেষণ করে নতুন তথ্য তুলে আনছেন; আর কেউ কেউ মানুষের আগামী কালের ভাগ্যরেখা মেপে চলেছেন কফির কাপে বা হাতরেখায়! এক জনের পর্যবেক্ষণ পরিমাপ ও গাণিতিক প্রমাণের উপর নির্ভর করে, আর অন্য জনের বহু পুরনো ভ্রান্ত ধারণা এবং লোকবিশ্বাসের উপর।
আসলে, সত্যিকারের বিজ্ঞানই পারে মানুষের অজ্ঞতা এবং অলীক বিশ্বাসকে দূর করতে। এই আবিষ্কার প্রমাণ করে যে, আকাশের দিকে তাকালে রাশিচক্র নয়, বরং খুঁজে পাওয়া যায় মহাজাগতিক বস্তুর বিজ্ঞানসম্মত তথ্য।
দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, কলকাতা-৪০
বেহাল উচ্চশিক্ষা
রাজ্যের বহু কলেজে চলতি শিক্ষাবর্ষে স্নাতকে ভর্তির চিত্র আবারও চিন্তা বাড়াচ্ছে। কোথাও গোটা বিভাগের ছাত্রসংখ্যা আঙুলে গোনা, কোথাও ভর্তি হার ৩০ শতাংশের নীচে। শহর থেকে মফস্সল— উচ্চশিক্ষার ভিত ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে।
সমস্যার মূলে রয়েছে ভর্তি-প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা ও জটিলতা। ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের অভিযোগ, বার বার ভর্তি-তারিখ বদল, দীর্ঘ কাউন্সেলিং ধাপ, এবং অপেক্ষা-তালিকার বিভ্রান্তি তাঁদের অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলেছে। এরই সুযোগে বহু পড়ুয়া আগেভাগে বিকল্প পথ— বেসরকারি কলেজ, আইটি ট্রেনিং, বৃত্তি বা প্রশিক্ষণমূলক কোর্সের দিকে চলে যাচ্ছে।বর্তমান শিক্ষাবাজারে যেখানে দক্ষতা-নির্ভর ও বাস্তবমুখী শিক্ষার চাহিদা বাড়ছে, সেখানে অনেক কলেজেই আধুনিক গবেষণাগার, ইন্ডাস্ট্রি-কানেক্ট, ইন্টার্নশিপ বা প্রজেক্ট-ভিত্তিক পড়াশোনার সুযোগ সীমিত। বহু প্রচলিত বিষয়েই ছাত্রসংখ্যা কমে যাওয়ার প্রবণতা স্পষ্ট। এমন প্রবণতার প্রভাব বহুস্তরীয়। ফাঁকা আসন মানে শুধু নিষ্ক্রিয় ক্লাসরুম নয়— বরং সরকারি অর্থব্যয়ের অপচয়, শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের ভারসাম্যে ভাঙন এবং গ্রামীণ এলাকা ও প্রথম-প্রজন্মের পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষায় পৌঁছনোর সুযোগ আরও কমে যাওয়া। দীর্ঘমেয়াদে এর অভিঘাত পড়ে শিক্ষার মানের উপর।
সমাধানের পথও অসম্ভব নয়। ভর্তি প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা, কলেজগুলিকে আরও স্বাধীনতা দিয়ে স্থানীয় স্তরে ভর্তি পরিচালনার সুযোগ দেওয়া, এবং পাঠ্যক্রমে দক্ষতা-নির্ভর উপাদান যুক্ত করা জরুরি। শিল্প-সহযোগিতা, স্টার্ট-আপ প্রকল্প বা রিসার্চ-অভিযোজন— এ সব বাড়ালে স্নাতক কোর্সগুলির প্রতি নতুন করে আগ্রহ তৈরি হতে পারে। উচ্চশিক্ষা যে কোনও রাজ্যের মানবসম্পদের ভিত্তি। তাই ক্রমবর্ধমান আসন-শূন্যতাকে শুধুমাত্র প্রশাসনিক ত্রুটি হিসাবে দেখা যাবে না— এটি কাঠামোগত পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তারও সঙ্কেত।
ওয়াসিকুজ্জামান, ডোমকল, মুর্শিদাবাদ