
বাঙালি জাতিকে স্বাবলম্বী হওয়ার পথ দেখালেন তিনি
বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে তিনিই খুঁজে বের করলেন রসায়ন শাস্ত্রে প্রাচীন ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। তিনি প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাঁর জন্মদিন পেরিয়ে এসে লিখছেন শুভ্রদেব বলবিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে তিনিই খুঁজে বের করলেন রসায়ন শাস্ত্রে প্রাচীন ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। তিনি প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাঁর জন্মদিন পেরিয়ে এসে লিখছেন শুভ্রদেব বল
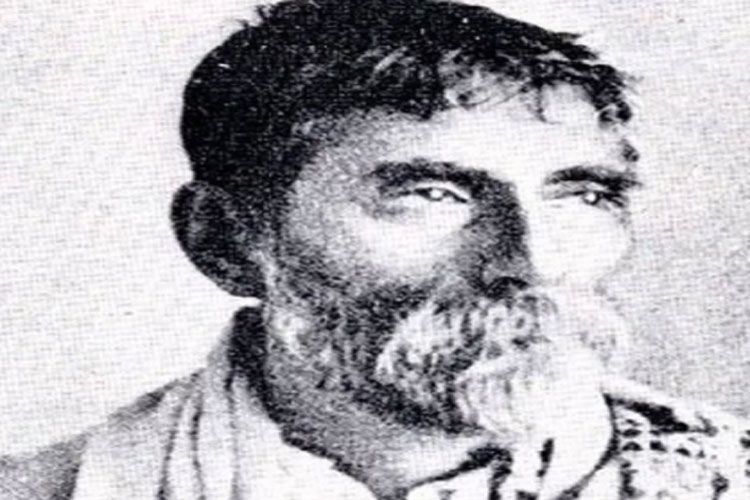
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।
রসায়নের ক্লাস। ছাত্রদের সামনে এক টুকরো হাড় হাতে নিয়ে বুনসেন বার্নারে পুড়িয়ে মুখে পুরে দিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ছাত্রদের শেখালেন, এটা ক্যালসিয়াম ফসফেট। এছাড়া আর কিছুই নয়। সেটা কোন প্রাণীর হাড় তা-ও আর চেনার উপায় রইল না।
রসায়ন দিয়ে শুধু রসায়ন শিক্ষাই নয়, ছাত্রদের মনে ধর্মান্ধতার মূল উপড়ে ফেলার মন্ত্রটিও প্রবেশ করিয়ে দিতেন তিনি। যত টুকু দরকার, তার বাইরে কতটুকুই বা পড়ার আগ্রহ আছে আমাদের বইবিমুখ আগামীর? অথচ, বই পড়ার আগ্রহ থেকেই জন্ম হয়েছিল এই বাঙালি মনীষীর। নিজের সফলতাকে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন সার্থকতার শিখরে।
১৮৬১, ২ অগস্ট অবিভক্ত বাংলাদেশের রাড়ুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন প্রফুল্লচন্দ্র। প্রপিতামহ মানিকলাল রায় ছিলেন নদিয়া (কৃষ্ণনগরের) ও যশোরের কালেক্টরের দেওয়ান। পিতামহ আনন্দলাল রায় ছিলেন যশোরের সেরেস্তাদার। পিতা হরিশচন্দ্র রায় ও মাতা ভুবনমোহিনী দেবী। বাবা মায়ের আদরের সেই ছোট্ট ফুলু পরবর্তীতে হয়ে ওঠেন ‘মাস্টার অফ নাইট্রাইটস’ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।
কেমন ছিল তাঁর এই জীবন পথ?
নিজ গ্রামে পিতার প্রতিষ্ঠিত স্কুলেই তাঁর শিক্ষার সূচনা। পিতা পুত্রের সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। বই পড়া অপেক্ষা পিতার সঙ্গে কথা বলে অনেক বিষয় বেশি করে শিখতেন। ১৮৪৬ সালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণনগর কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ, ক্যাপ্টেন ডি এল রিচার্ডসনের লেখা ‘ব্রিটিশ কবিগণের জীবনী’ বইটি তিনি পান তাঁর পিতার কাছ থেকে। এটাই ছিল তাঁর অমূল্য পৈতৃক সম্পদ।
১৮৭০ সালে সপরিবার চলে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন হেয়ার স্কুলে। রাত জেগে পড়াশোনা করার ফলে হজমের সমস্যা ও রক্ত আমাশয় হলে তিনি ফিরে আসেন নিজের গ্রামে। এই অসুস্থতাই ছিল তাঁর জীবনে ছদ্মবেশী-আশীর্বাদ। কারণ গ্রামে এসে তিনি অনেকখানি সময় কাটাতেন পিতার তৈরি লাইব্রেরিতে। বাঁধাধরা বইয়ের বাইরে, শেক্সপিয়ার, এমার্সন, কার্লাইল, ডিকেন্সের রচনা, নিউটন, গ্যালিলিও, ফ্রাঙ্কলিনের জীবনী, বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি ইচ্ছেখুশি বই পড়ার আনন্দে মেতে উঠলেন তিনি। স্যর উইলিয়াম জোন্সের প্রশ্নের উত্তরে জোন্সের মায়ের উক্তি ‘পড়িলেই সব জানিতে পারিবে’ কথাটি প্রফুল্লচন্দ্রের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে।
১৮৭৩ সালে ফিরে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন অ্যালবার্ট স্কুলে। এরপর এন্ট্রান্স পাশ করে ভর্তি হন মেট্রোপলিটনে। কারণ বিদ্যাসাগরের এই কলেজটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সেটি তাঁর ‘নিজের’ বলে মনে হত। ভারতে প্রথম এই প্রতিষ্ঠানটিই উচ্চশিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার মতো সুলভ করার সাহসী প্রচেষ্টা দেখায়। এফএ পড়ার সময় থেকেই প্রেসিডেন্সি কলেজে 'বাইরের ছাত্র' হিসেবে অধ্যাপকদের রসায়ন বিষয়ে বক্তৃতা শুনতেন। নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি রসায়নের প্রতি আকৃষ্ট হন। ইংরাজি সাহিত্যানুরাগী প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞানের আনুগত্য স্বীকার করে নেন। রসায়ন নিয়ে ভর্তি হন প্রেসিডেন্সিতে। এখানে তিনি বিখ্যাত প্রফেসর আলেকজান্ডার পেডলারের সান্নিধ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজ গৃহেই ছোট্ট গবেষণাগার গড়ে গবেষণা শুরু করেন। নিজের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটির গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পরীক্ষা দেন এবং উত্তীর্ণ হন। ১৮৮২ সালে ইংল্যান্ড যাত্রা করেন।
এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি থেকে ১৮৮৪ সালে বিএসসি ডিগ্রি পান। এখানে ইন্ডিয়ান বিফোর অ্যান্ড আফটার দ্য মিউটিনি’ বিষয়ে এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। সত্যের সাধক ছিলেন বলেই ভারতে ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক শাসনের কুপ্রভাব সাহসিকতার সঙ্গে তুলে ধরতে পেরেছিলেন তাঁর সেই লেখায়। তাঁর ব্রিটিশ বিরোধী প্রবন্ধটি পুরস্কৃত না হলেও প্রশংসিত হয়েছিল। এডিনবার্গ থেকেই ১৮৮৭ সালে ডিএসসি ডিগ্রির সঙ্গে সঙ্গে ‘হোপ প্রাইজ’ বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৮৮-তে তিনি ফিরে এলেন কলকাতায়। প্রেসিডেন্সিতে শুরু হয় তাঁর শিক্ষক জীবন। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নেটিভ হওয়ার কারণে অপেক্ষাকৃত কম মাইনে ও কম সম্মানের প্রভিন্সিয়াল অধ্যাপক হিসেবে সেখানে যোগদান করেন তিনি। তাঁর সুন্দর বাচনভঙ্গি ও রসবোধ দিয়ে বাংলা ভাষায় বক্তৃতার মাধ্যমে রসায়নের পাঠ ছাত্রদের কাছে সহজবোধ্য ও মনোগ্রাহী করে তুলতেন। বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের সফলতার জীবন কাহিনি গল্পের ছলে তুলে ধরতেন ছাত্রদের কাছে। অল্প সময়েই শিক্ষক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ, পঞ্চানন নিয়োগী, পুলিন বিহারী সরকার, গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী, এ কে ফজলুল হক, রসিক লাল দত্ত তাঁরই ছাত্র ছিলেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি চলতে থাকে তাঁর গবেষণা।
এক দিন হঠাৎই তিনি আবিষ্কার করলেন রসায়নের এক অতি বিষম বস্তু মারকিউরাস নাইট্রাইট। ইউরোপীয় বিজ্ঞানীগণ তাঁকে মাস্টার অব নাইট্রাইটস আখ্যায় ভূষিত করেন। পরনে ধুতি, কালো কোট, চুল অবিন্যস্ত, তাঁর এমন উদাসীন বেশভূষায় আবৃত ছিল এক দূরদর্শী কর্মচঞ্চল প্রাণ। তিনি বুঝেছিলেন, ‘‘একটা সমগ্র জাতি শুধুমাত্র কেরানী বা মসীজীবী’’ হয়ে টিকে থাকতে পারে না। বাঙালি জাতিকে স্বাবলম্বী হওয়ার পথ দেখালেন তিনি। ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিকল ওয়ার্কস। মূলধন বলতে ছিল, মাত্র আটশো টাকা আর পূর্ণ আত্মবিশ্বাস।
এ ছাড়াও ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস, বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস, ন্যাশনাল ট্যানারি ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠায় তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। এডিনবার্গে থাকাকালীন সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল সোসাইটির সদস্য রূপে বিভিন্ন রাসায়নিক কারখানা পরিদর্শন করে রাসায়নিক কারখানা তৈরির প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তিনি। বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে তিনিই খুঁজে বের করলেন রসায়ন শাস্ত্রে প্রাচীন ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। ধাতু সঙ্কর তৈরিতে ভারত যে পিছিয়ে ছিল না, চরক সংহিতা-সুশ্রুত সংহিতায় উল্লেখিত অস্ত্রোপচারের সূক্ষ্মাগ্র যন্ত্র যেমন স্ক্যালপোল বা ল্যানসেট তার প্রমাণ। ইস্পাত আবিস্কারের প্রথম কৃতিত্বও প্রাচীন ভারতের। প্রাচীন রসায়নে শুধু ইজিপ্ট, সিরিয়া, চিন বা আরব নয় প্রাচীন ভাতরবর্ষও যে কতটা এগিয়ে ছিল,তা তুলে ধরতেই তিনি লিখলেন ‘দ্য হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি’। এ বিষয়ে প্যারিসের বিখ্যাত বিজ্ঞানী মার্সিলিন বের্তেলোর সান্নিধ্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। এই কাজের জন্য সংস্কৃত ও পালি ভাষা শিখেছিলেন।
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। তিনি বলেন, ‘‘দেয়ার আর অকেশনস্ দ্যাট ডিমানডেড দ্যাট আই সুড লিভ দ্য টেস্ট টিউব টু অ্যাটেন্ড টু দ্য কল অফ দ্য কান্ট্রি। সায়েন্স ক্যান ওয়েট, স্বরাজ কান্ট।’’ তাঁর অর্জিত আয়ের প্রায় সবটুকুই দেশহিতার্থে দান করে গিয়েছেন। ত্যাগেই ছিল তাঁর তৃপ্তির আনন্দ। ১৯৪৪, ১৬ জুন। শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন অকৃতদার বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী। তাঁকে আমরা কতটা মনে রেখেছি? আমাদের অভ্যস্ত জীবনের চক্রবূহ্যে আত্মতৃপ্তি কোথায়? আত্মকেন্দ্রিক হতে হতে আমরা ক্রমশ আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ছি না তো?
শিল্প স্বনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিকল আজ বিলগ্নিকরণের পথে। ২০১৬ সালে এই সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র। জল গড়ায় কোর্টে। সংস্থার আধিকারিক মাইক্রোবায়োলজিস্ট ও কর্মীদের চেষ্টায় বিগত তিন অর্থবর্ষেই লাভের মুখ দেখেছে এই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা। গত অর্থবর্ষে এর মুনাফা হয় সর্বাধিক— প্রায় ২৫ কোটি টাকা। সংস্থার পানিহাটির ২৭ একর জমিতে রয়েছে ফিনাইল ও ন্যাপথলিন তৈরির কারখানা। এখানকার অতিরিক্ত ২৫ একর জমিও (যার বর্তমান বাজার মূল্য ৪০০ কোটি টাকা) বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। এছাড়াও মানিকতলার ১৪ একর জমিতে রয়েছে ওষুধ তৈরির কারখানা। কানপুরে ৩ একর ও মুম্বাইতে একটি বাড়ি সহ দেড় একর জমি রয়েছে।
এখানকার বহু পণ্য যেমন ফিনাইল, কালমেঘ, ক্যান্থারাইডিন অয়েল, ন্যাপথালিন, ইথুরিয়া অয়েনমেন্ট, অ্যাকুয়াটাইকোটিস সহ নানা ওষুধ অত্যন্ত জনপ্রিয়। সংস্থাটির সঙ্গে জুড়ে রয়েছে প্রায় চারশো কর্মীর পরিবার। সেই সঙ্গে জুড়ে আছে জাতীয়তাবাদী বাঙালির গৌরবগাঁথা।
স্বাভাবিক ভাবেই এমন ঐতিহাসিক এবং বর্তমানে লাভে চলা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেঙ্গল কেমিক্যালস বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্ত সবাইকেই বিস্মিত করেছে। কেন্দ্রের এই বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচিত হোক। আগামী দিনে ঋণমুক্ত হয়ে মিনিরত্ন (মহারত্ন, নবরত্ন, মিনিরত্ন ১, মিনিরত্ন ২) ক্যাটাগরির তকমা আদায় করে নিক বেঙ্গল কেমিক্যালস।
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রদর্শিত পথই হোক আমাদের লক্ষ্য। তাঁর জীবনালোকে দূরীভূত হোক আত্মবিস্মৃতির আঁধার।
নেতাজি বিদ্যামন্দির প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক
Share this article
CLOSE- One number & One character
- Minimum 6 character
-
Forgot Password
Or
By continuing, you agree to our terms of use
and acknowledge our privacy policy







