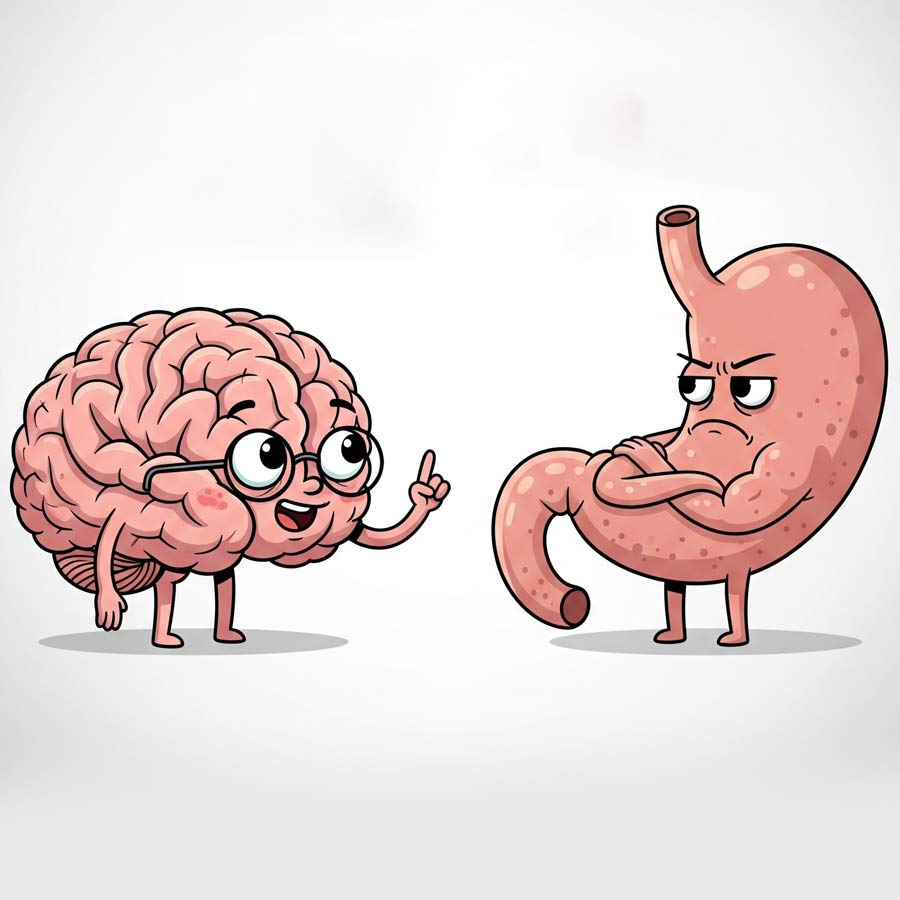যে সময়ের কথা এখানে বলতে বসেছি, সেই বিশ তিরিশের দশকে টিভির তো না-ই, বেতার যন্ত্রেরও এত রমরমা এই শহরে ছিল না। তালতলা পাড়ার যে গলিতে আমরা থাকতুম, তার মাত্র একটা বাড়ির ছাদে এরিয়েলের তার খাটানো ছিল, তাও সম্ভবত ইলেকট্রিক বিল বেড়ে যাওয়ার ভয়ে— সে বাড়ির কর্তারা তাঁদের বেতার যন্ত্রটিকে অবরে-সবরে চালাতেন। তবে অন্য সময়ে না-ই চলুক, মহালয়ার দিন রাত ফুরোবার আগেই যে সেটা গমগম করে উঠে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিত, এটা মনে পড়ে। তার অনেক আগেই অবশ্য পাড়ার বোষ্টুমিটির গানের পদ পালটে যেত। অন্য সময়ে সে ‘বিষ্ণুপ্রিয়া জাগো বলে নূপুর কেন বাজলি না রে’ গাইত বটে, কিন্তু ভাদ্র মাস শুরু হতেই তার গলায় ফুটত আগমনী গানের কলি। খঞ্জনী বাজিয়ে সে তখন গাইত, ‘যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী, উমা আমার ভারী কেঁদেছে’।
ছানাপোনা নিয়ে মা-দুর্গা এই সময়ে বাপের বাড়ি যান। আমার মায়ের জীবনে বাপের বাড়ি যাওয়ার সুযোগ বড় একটা ঘটত না বলেই হোক, সদর-দরজায় আগমনী গান শুরু হলেই তিনি বড় উতলা হয়ে উঠতেন। জ্বলন্ত উনুন থেকে হাঁড়ি কিংবা কড়াইটাকে নামিয়ে রেখে, হাত মুছতে মুছতে হেঁসেল থেকে একছুটে তিনি যে তখন সদর-দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেন, এটা ভুলিনি। গান শুনে বোষ্টুমির ঝুলিতে এক-কৌটো চালের সঙ্গে একটা সিকি কিংবা দুয়ানি ফেলে দিয়ে বলতেন, রোজ এসে গান শুনিয়ে যেয়ো। বাড়িতে এসে গান শুনিয়ে যারা চাল কিংবা পয়সা নিয়ে যেত, কেউ যে তাদের ভিখিরি বলবে, মা এটা পছন্দ করতেন না। বলতেন ওরা ভিখিরি হবে কেন, ওরা কাজ করে দু’পয়সা রোজগার করছে, গান শোনানো তো একটা মস্ত বড় কাজ, সবাই ও-কাজ পারে?
আগমনী গান একবার শুরু হলেই হল, দেখতে দেখতে পুজো এসে যেত। এখন তো গলিতে-গলিতে বারোয়ারি দুর্গাপুজো হয়, আমাদের ছেলেবেলার সেই কলকাতায় এত পুজোর রহট দেখিনি। চাঁদা আদায়ের এত দাপটও তখন ছিল না। তালতলা-পড়ার চৌহদ্দি তো নেহাত কম নয়, কিন্তু তার মধ্যে বারোয়ারি পুজো হত মাত্র একটিই। মাঠের মধ্যে পুজো, মায়ের হাত ধরে আমরা সেখানে আরতি দেখতে যেতুম। আমরা মানে ছোটপিসি, দিদি আর আমি। পুজোর মাঠের মস্ত আকর্ষণ ছিল স্বদেশি মেলা। তাতে যাঁরা স্টল সাজিয়ে বসতেন, একমাত্র স্বদেশি জিনিসপত্র ছাড়া অন্য কিছু তাঁরা বিক্রি করতেন না। বিক্রিবাটার সঙ্গে সঙ্গে চলত শিক্ষা বিতরণের কাজ। দেশলাই, সাবান কিংবা কাগজ কী ভাবে তৈরি করতে হয়, স্বদেশি মেলার কয়েকটা স্টলে সে-সব হাতে কলমে শেখানো হত। মেলায় ঢুকবার পথে, মুখে টিনের চোং লাগিয়ে গান্ধীটুপি-পরা একজন ভলান্টিয়ার তারস্বরে বলে যেতেন যে, আমরা যত দিন বিলিতি জিনিস কিনব, দেশ তত দিন স্বাধীন হবে না। ‘অতএব মা-বোনেরা প্রতিজ্ঞা করুন যে আজ থেকে শুধু স্বদেশি জিনিসই আপনারা কিনবেন।’ আজ যদি কেউ বাগবাজার কি সিমলে-পাড়ার সর্বজনীনে দাঁড়িয়ে এইরকমের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে বলেন, তা হলে মুক্ত অর্থনীতির প্রবক্তারা হয়তো ভির্মি যাবেন, তবে সে-কালের বারোয়ারিতে এই স্বদেশি মেলা যে একটা বাড়তি মাত্রা যোজনা করত, তাতে সন্দেহ নেই।
খুব ছেলেবেলায় কলকাতার পুজো অবশ্য খুব একটা দেখিনি। গাঁয়ের বাড়িতে ঠাকুর্দা-ঠাকুমার কাছে থাকতুম। সেখান থেকে মাঝেমধ্যে যে এই শহরে আসিনি তা নয়, তবে সেটা দু’-চার দিনের জন্য আসা, পাকাপাকি ভাবে কলকাতা আসি ১৯৩০ সালে। তার আগে যে স্মৃতি, তা গ্রামাঞ্চলের শরৎকালের। পূব বাংলার নাবাল অঞ্চল সম্পর্কে যাদের কোনও ধারণা আছে, তাঁরা জানেন যে, পুরো শরৎকাল জুড়ে সেখানকার মাঠঘাট সব জলের তলায় ডুবে থাকে। স্থলপথ বলে আর কিছু থাকে না, গ্রামগুলো হয়ে যায় বিচ্ছিন্ন এক-একটা দ্বীপের মতো। ফলে, পঞ্জিকায় যা-ই লিখুক না কেন, দোলায় কিংবা ঘোড়ায় নয়, যে-গ্রামে পুজো হচ্ছে, দেবীর আগমন ও বিদায়, এই দু’টো ব্যাপারই ফি-বছর সেখানে নৌকাযোগে ঘটে থাকে। তাঁর প্রতিমা অবশ্য বাইরে থেকে নৌকায় চেপে আসে না, সেটি ধীরে ধীরে তৈরি হয়ে ওঠে পুজো-মণ্ডপেই। গ্রামে কুমোর থাকলে ভাল, নয়তো তাঁকে অন্য কোনও গ্রাম কিংবা কাছাকাছি কোনও গঞ্জ থেকে আনিয়ে নিতে হয়।
আমাদের গ্রামে লক্ষ্মীপুজো, সরস্বতীপুজো, মনসাপুজো, কার্ত্তিকপুজো, শনি-সত্যনারায়ণের পুজো, এমনকি কালীপুজোও হত, কিন্তু দুর্গাপুজো হত না। কারণ আর কিছুই নয়, দুর্গাপুজো রীতিমত ব্যায়সাধ্য ব্যাপার, এবং আমাদের গ্রামে অত সঙ্গতিপন্ন পরিবার একটিও ছিল না। আমরা যারা ছেলেপুলের দল, এই নিয়ে তাদের দুঃখ ছিল অনেকখানি। সেই দুঃখ আরও বেড়েই যেত, রাত্তিরে ঠাকুমার পাশে শুয়ে যখন শুনতে পেতুম যে, দূরের কোনও গ্রাম থেকে মাঠজোড়া জলের ওপর দিয়ে ঢাকের শব্দ ভেসে আসছে। এই ঢাকের শব্দও আসলে এক ধরণের আগমনী বাজনা ছাড়া আর কিছু নয়।
যেমন পুজোর, তেমনি এই প্রস্তুতি-পর্বেরও একটা আনন্দ থাকে। দিনের বেলায় দেখতুম, কোমর-অব্দি জলে-ডোবা ধানগাছের উপর দিয়ে রৌদ্রছায়ার খেলা চলেছে, আকাশটা মাঝে মাঝে কালো হয়ে যাচ্ছে, আবার পরক্ষণেই হয়ে উঠছে অসহ্য রকমের নীল, জলের মধ্যে ফুটে আছে শয়ে-শয়ে সাদা আর লাল শাপলা, উঠোনের লাউ-কুমড়োর মাচার উপরে ডানা নেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছটফটে দুর্গা-টুনটুনি, বাতাসে উড়ছে দুটো-তিনটে দলছুট বোলতা, শিউলিগাছের তলাটা ফুলে ফুলে একেবারে সাদা হয়ে আছে, মনে হচ্ছে যেন ঘাসের উপরে ধবধবে সাদা রঙের একখানা চাদর বিছিয়ে রেখেছে কেউ। সেই সঙ্গে রাত্তিরে ভেসে আসত ওই ঢাকের শব্দ। কল্পনা করে নিতুম যে, কোথাও কোনও পুজো-মণ্ডপে এখন একমেটে-দুমেটের পর প্রতিমার গায়ে রং ধরানো হচ্ছে, সেখানে ভিড় জমেছে ছেলেমেয়েরা। যত ভাবতুম, মন ততই খারাপ হয়ে যেত। পুজোর এই যে প্রস্তুতি-পর্ব, খড়ের কাঠামোর ওপরে মাটি ধরানো, রং চড়ানো, তার আনন্দের ভাগ তো আমরা পাচ্ছি না।
তাই বলে যে পুজো দেখতুম না, তা নয়। লোকে পুজোর সময় মামাবাড়ি যায়, আমরা যেতুম বাবার মামারবাড়িতে। সে-গ্রাম আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় মাইল ছ’-সাত দূরে। সেখানে খুব মস্ত মাপের পুজো হত। কলকাতা থেকে বাবা, মা, কাকারা, ছোটপিসি আর দিদি আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে এসে পৌঁছতেন দেবীপক্ষের চতুর্থী কি পঞ্চমীর দিন। সদর-শহর পর্যন্ত রেলগাড়িতে এসে তারপর সেখান থেকে যে তিনমাল্লাই নৌকো করে তাঁরা আসতেন, দু’-একটা দিন সেটাকে আটকে রেখে তার পর সেই নৌকোতেই যাওয়া হত বাবার মামারবাড়ির গ্রামে। সেখানে পুজোর ক’টা দিন খুব হইচই করে কাটত। ভাসানের দিন প্রতিমাকে নৌকোয় তুলে বাড়ির পাশের খাল দিয়ে চসে যাওয়া হত বড় নদীতে। সেখানে বাজি ফাটানো হত, তুবড়ি জ্বালানো হত, তারপর আশেপাশের হরেক গ্রাম থেকে যে-সব নৌকো সেখানে এসে জমায়েত হত, তাদের বাইচ হত খুব জবরদস্ত রকমের। নৌকোতে নৌকোতে ধাক্কাধাক্কি লাঠালাঠি হত না তা নয়, মারদাঙ্গায় জখম হয়ে দু’-দশ জন জলে পড়ে যেত না তাও নয়, তবে সাঁতার কেটে তারা আবার উঠে পড়ত ঠিকই, কেউ কখনও প্রাণে মারা পড়েছে বলে শুনিনি।
যে সব গ্রামে পুজো নেই, সেখানকার লোকজনেরাও— পুজো না দেখুক— দশহরার দিন নৌকো করে বড় নদীতে চলে আসত বিসর্জন দেখবার জন্য। নদীর ধারে গঞ্জ। তার ঘাটে-ঘাটে সেদিন বিকেল থেকেই শয়ে-শয়ে নৌকো এসে ভিড় জমাত। ভাসানের পালা চুকে যাওয়ার পরে বাড়িতে ফিরে দেখতুম মা, ঠাকুমা, পিসিমা, কাকিমা, জ্যাঠাইমা’রা সব কাঁসার রেকাবিতে মিষ্টি সাজিয়ে বসে আছেন। প্রণাম, আলিঙ্গন ইত্যাদির পরে হাতে-হাতে সেই মিষ্টির রেকাবি ধরিয়ে দেওয়া হত। মিষ্টি মানে রসগোল্লা-সন্দেশ নয়, গ্রামে ও-সব পাওয়াও যেত না, সবই নারকোল ক্ষীর আর চিনি দিয়ে তৈরি। নারকোলের নাড়ু, নারকোলের তক্তি, নারকোলের চন্দ্রপুলি। পরদিন যাওয়া হত গ্রামের অন্য সব বাড়িতে। কোনও বাড়িতেই নারকোল-গাছের কিছু কমতি ছিল না। নোনা জমি বলে তাতে ফলনও হত প্রচুর।
নারকোলের শাঁসকে চিঁড়ের মতো করে কুটে নিয়ে যে মিষ্টি তৈরি করা হত, তার স্বাদ তো ছিল চমৎকার। তা ছাড়া তিলের নাড়ু আর মুড়ি-চিঁড়ে-খইচুরের মোয়া তো ছিলই। ফলে, রসগোল্লা-সন্দেশ নেই বলে যে অতিথি-আপ্যায়নের ব্যাপারে কোনও অসুবিধে হচ্ছে, গ্রামাঞ্চলে এমনটা কখনও ঘটতে দেখিনি।
দুর্গাপুজোর জের মিটতে-না-মিটতেই এসে যেত লক্ষ্মীপুজো। বাড়িতে-বাড়িতে, মাটির প্রতিমা নয়, পটের পুজো হত। তবে ফি বেস্পতিবার যেমন পাঁচালি পড়ে পুজোর কাজ চালানো হয়, কোজাগরী পুর্ণিমার লক্ষ্মীপুজোয় অত সংক্ষেপে সেটা হবার উপায় ছিল না। পুরুত এসে রীতিমতো ঘণ্টা নেড়ে মন্ত্র পড়ে পুজো করতেন। মেয়েরা উলু দিতেন, শাঁখ বাজাতেন। পূর্ববঙ্গের ছেলেপুলেরা তো পাঁচ বেলা ভাত খায়। কিন্তু সে দিন ঘটত ব্যতিক্রম। রাত্তিরের জন্য থাকত লুচি-পরোটা মোহনভোগের ব্যবস্থা।
তার পরে তো কলকাতায় চলে আসি। এসে চোখ একেবারে ছানাবড়া হবার জোগাড়। কেননা, এর আগে শুধু ঘরোয়া পুজোই দেখা হয়েছে, বারোয়ারি পুজো যে কী বস্তু, সে সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না। এত হইচই, হুল্লোড়, আলো, রোশনাই, বাজি-পটকা, এত ভিড় করে সবাই পুজো-প্যান্ডেলে ঠাকুর দেখতে আসছে, ভিড়ের মধ্যে কেউ কেউ হারিয়েও যাচ্ছে, টিনের চোঙে তাদের নাম ঘোষণা করা হচ্ছে— তালতলার বারোয়ারি পুজো দেখে একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। স্বদেশি মেলার কথা তো বলেছি, এখন মনে পড়ছে যে, পুজোর মাঠের একপাশে লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, মেয়েদের আত্মরক্ষার উপায় ইত্যাদিরও কয়েকটা প্রদর্শনী ছিল। বড়দের কথাবার্তা থেকে আন্দাজ করেছিলুম যে, শারীরিক কসরতের এই সব প্রদর্শনী নিয়ে পুলিশের তরফে আপত্তি উঠেছিল, তবে বারোয়ারি পুজো-কমিটির কর্তারা তাতে কান দেননি।
কালীপুজোর রাতে বাজিপটকার ধুম বাড়ত চতুর্গুণ। ছুঁচোবাজির উৎপাতে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করা ঘোর বিপজ্জনক হয়ে উঠত। যে-সব হাউই আর উড়নতুবড়ি ছোড়া হত, সাঁই সাঁই করে সেগুলো আকাশে উঠে যেত বটে, কিন্তু ভিতরের বারুদ পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার পরে কোনটার খোল যে কখন মাথায় এসে পড়বে, কোনও ঠিক-ঠিকানা ছিল না। যেমন কালীপুজোর রাতে, তেমন তার পরেও কয়েকটা দিন বেশি রাতে কলকাতার আকাশে দু-চারটে ফানুস ওড়ানো হত। বুকের মধ্যে আগুন নিয়ে হেলতে-দুলতে আকাশ পাড়ি দিচ্ছে ফানুস, দেখে যে কী ভাল লাগত, সে আর বলবার নয়।
কলকাতার পুজো অবশ্য কখনও আমার খুব ভাল লাগেনি। ভিতরে-ভিতরে কেমন যেন একটু অস্বস্তি হত। বাজনা-বাদ্যি, হইচই, আলোর জলুস, বাজি-পটকা, পুজোর আকর্ষণ তো এখানে কিছু কম নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কিংবা হয়তো সেই জন্যেই, সেই বয়সেও বড্ড হাঁফ ধরে যেত। আমি গ্রামের ছেলে, গ্রামের পুজোয় এত সব আকর্ষণ থাকে না। কিন্তু সব মিলিয়ে একটা শান্ত শ্রী থাকে, মনের মধ্যে তার একটা টান সর্বদা টের পেতুম। তা ছাড়া, মানুষের সাজ-বদলই এই সময়ে এখানে বড্ড বেশি চোখে পড়ে, আকাশের সাজ-বদলের ব্যাপারটা বলতে গেলে চোখের আড়ালেই থেকে যায়। মহালয়ার দিন থেকে শুরু হত পুজোর ছুটি, সঙ্গে সঙ্গে বইপত্তর গুছিয়ে নিয়ে পুব বাংলার সেই গ্রামের বাড়িতে ফেরবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতুম। জলে ডোবা আলপথ দিয়ে নৌকো চলছে, দুদিক থেকে নৌকোর উপরে এসে পড়ছে ধানের পাতা, আকাশটাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন মস্ত একটা নীলের গামলাকে কেউ মাথার উপরে উপুড় করে ধরে রেখেছে, সেই নীলের মধ্যে সাদা মেঘগুলোকে সাবানের ফেনা বলে মনে হচ্ছে, নারকোল গাছের মাথা থেকে ঝাঁপ খেয়ে ফের ডানা ছড়িয়ে বাতাস কেটে ঊর্ধ্বাকাশে উঠে গেল একটি শঙ্খচিল— চোখ বুজলেই শরৎকালের সেই দৃশ্যগুলো আজও স্পষ্ট দেখতে পাই।
না, কলকাতার পুজো নয়, এখানকার সুতো, ইস্কুরুপ, নাটবল্টু কি পেরেক দিয়ে বানানো অত্যাশ্চর্য প্রতিমা নয়, মফস্সলের পুজোই আমার পছন্দ। তার সবচেয়ে বড় কারণ নিশ্চয়ই এই যে, পুজোর সঙ্গে প্রকৃতিকেও সেখানে বোনাস হিসেবে পাওয়া যায়।
প্রথম প্রকাশ: ‘বারোয়ারি পুজোর সঙ্গে থাকত স্বদেশি মেলা’ শিরোনামে,
পুজো ক্রোড়পত্র, ১৯৯৫। সংক্ষেপিত।