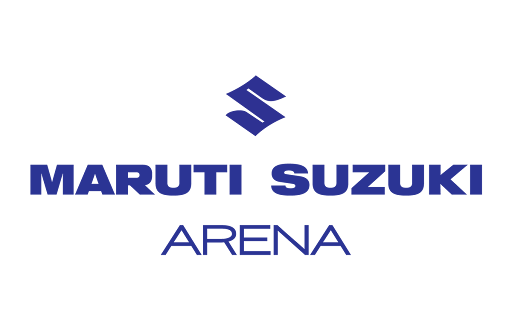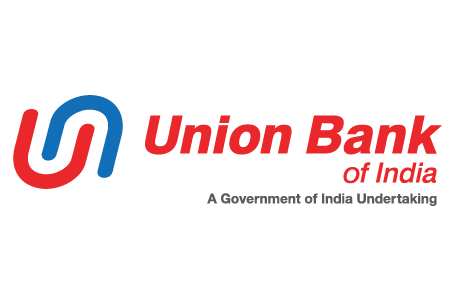গুপ্তিপাড়া স্টেশনের আগেই কালনা-কাটোয়ামুখী স্টেট হাইওয়ে ছেড়ে লেভেল-ক্রসিং পেরোলাম। দু-একজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে রথতলার মাঠের পাশে গুপ্তিপাড়ার গুপো সন্দেশের মুখচোরা দোকানগুলোর মায়া কাটিয়ে বৃন্দাবনচন্দ্র মঠের পাকারাস্তায় বাঁক নিতে হল। বৃন্দাবনচন্দ্রের মঠ গুপ্তিপাড়ার বিখ্যাত মন্দির, সবাই চেনে। বলা উচিত মন্দির সমূহ। তার টেরাকোটা বিষ্ণুপুরের থেকে নামে খাটো, দর্শনে আর চরিত্রে খাটো কিছু নয়। এছাড়া কিছু বিচিত্র দেওয়ালচিত্রও আছে, যারা কালের আর অপরিকল্পিত পুনরুদ্ধারের প্রকোপে ক্রমশ ফিকে, নয়তো বিকৃত হচ্ছে। গুপ্তিপাড়ার নামকরা জগন্নাথের রথও তার যাত্রা শুরু করে এই মন্দির থেকেই।
আমাদের গুপ্তিপাড়া আসার মুখ্য উদ্দেশ্য কিন্তু অন্তত এই যাত্রায় বৃন্দাবনচন্দ্র মঠ দেখা নয়। মঠের একটু আগেই রাস্তার উপরে বাঁদিকে অধুনানির্মিত ‘দেশকালী’ মন্দিরের মুখে যে আকাশজোড়া গাছতলা, তার শাখায় শাখায় গুচ্ছ-গুচ্ছ ফলখেকো বাদুড় বাদুড়ঝোলা হয়ে আগন্তুকদের মাথা গুনছে। গাছের গোড়ায় বালগোপালের ৫ ফুট উঁচু গোলিয়াথ মূর্তি কতকটা ভূমিস্পর্শমুদ্রায় ঠায় বসে; হাতের আঙুলগুলো ঝড়ে-জলে-বৃষ্টিতে গলে পড়ছে, তবু ভ্রুক্ষেপ নেই। এরই গা ঘেঁষে মেঠো গ্রাম্য রাস্তা ঢুকে গেছে উত্তরপানে। একটা গাড়ি কোনওক্রমে যেতে পারে, তাও কারও পাশ কাটাতে গেলে দু-ধারের ঝোপঝাড়গুলোকে তাদের ফুলপাতা খুইয়ে মূল্য চোকাতে হয়। এই রাস্তায় দুশো গজ মতো গিয়ে বাঁহাতে একটা খোলা মাঠ আর তারই একপাশে একটা ছোটখাটো পাকা মণ্ডপ। দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর পুজো হয়, বহুবছর ধরে, নিয়মিত। পাকা মণ্ডপ বেশি দিনের নয়, তবু তার স্থাপনাও নয় নয় করে ৭৯ বছর হল। প্রস্তর ফলকে লেখা আছে,‘শ্রীশ্রীবিন্ধ্যবাসিনী মাতার পূজামণ্ডপ/ শ্রীসতীশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের ব্যয়ে নির্ম্মিত / সন ১৩৪৬ সাল’ । আর তারই একটু তলায় অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের চতুষ্কোণ দ্বিতীয় ফলক– যেটা দেখবার জন্যে এই ৯০ কিলোমিটার পথ ঠেঙিয়ে কলকাতা থেকে এখানে আসা। তাতে লেখা - ‘বারোয়ারী সৃষ্টিস্থান / গুপ্তিপাড়া বারোয়ারী ঁবিন্ধ্যবাসিনী পূজা / প্রতিষ্ঠিত: সন ১১৬৮ সাল (আনুমানিক)’।
বারোয়ারি শব্দের একাধিক উৎস বাংলার মনীষীরা নির্দেশ করেছেন। যেমন বারোপকারিক থেকে (রাজশেখর বসু : চলন্তিকা), বারো + ওয়ারিস থেকে (রাধারমন রায়), বার+ওয়ারি থেকে (আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি) ইত্যাদি। কিন্তু যে উৎস সর্বজনের কাছে বেশি প্রচলিত বা প্রচারিত, তা হল ‘বারো’ যুক্ত ‘ইয়ার’ থেকে ‘বারোয়ারি’। বারোজন ইয়ার বা বন্ধু মিলেই নাকি এই ধরনের পুজোর প্রথম আয়োজন করেন। এর পিছনে গল্প একটা নিশ্চয় আছে।


বিন্ধ্যবাসিনী দেবীমূর্তি (ছবি: বিন্ধ্যবাসিনী পূজাকমিটির সৌজন্যে)
কী সেই কাহিনি? কথিত আছে, ১৭৫৮ সালের কোনও জগদ্ধাত্রী পুজোয় গুপ্তিপাড়ার এক ধনী গৃহস্থের বাড়িতে কয়েকজন মহিলা পুজো দেখতে গিয়ে ঢুকতে পারেননি তো বটেই, উপরন্তু দারোয়ানের কাছে অপমানিত হয়ে ফিরে আসেন। তাঁদের পরিবারের পুরুষরা কথাটা জানতে পেরে স্থির করেন যে তাঁরা নিজেরাই জগদ্ধাত্রী পুজো করবেন। ধনী পরিবারের মতো সঙ্গতি না থাকায় তাঁরা বারোজন বন্ধু মিলে চাঁদা তুলে এই জগদ্ধাত্রী পুজো করেন। জগতের যিনি তথাকথিত ধাত্রী তাঁর পুজোয় আশপাশের সবাই বিনা বাধায় অংশ নিলেন। পুজোয় শুধু তার আয়োজনকারী মূল পরিবারের অধিকারের পরিবর্তে সর্বসাধারণের সম-অধিকার স্বীকৃত হল। গুপ্তিপাড়ায় বারোজনের একত্রিত উদ্যোগে পূজিতা এই জগদ্ধাত্রী দেবীই ‘বিন্ধ্যবাসিনী’ নামে পরিচিতা। আর এই মণ্ডপ ঠিক সেখানেই, যেখানে নাকি ১৭৫৯ সালে প্রথম বারোয়ারি বা বারো-ইয়ারি আয়োজনে বিন্ধ্যবাসিনী পূজিতা হয়েছিলেন।


বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর পূজামণ্ডপের ফলকে বাংলার প্রথম বারোয়ারির উল্লেখ
সাধারণ মানুষের অবারিত অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত হওয়ায় বারোয়ারি পুজোর এই পদ্ধতি আর সংজ্ঞা সহজেই সবার হৃদয় স্পর্শ করল। কিছু বছরের মধ্যেই বাংলার এখানে সেখানে বারোয়ারি পুজোর প্রচলন হল। বিশেষভাবে দশভুজা দুর্গা সার্বজনিক দেবী হিসেবে রাজবাড়ি-জমিদারবাড়ির দালানকোঠা ছেড়ে ছেলেমেয়েকে নিয়ে পথে নামলেন। ১৯১০ সালে কলকাতার ভবানীপুরে সনাতন ধর্মোৎসাহিনী সভাপ্রথম বারোয়ারি দুর্গাপুজোর আয়োজন করলেন। এখন শুধু কলকাতা শহরেই বারোয়ারি দুর্গাপুজোর সংখ্যা তিন হাজার ছাড়িয়েছে।


গুপ্তিপাড়ায় অনুষ্ঠিত বাংলার প্রথম বারোয়ারি পুজোর সাল নিয়ে কিছু মতান্তর আছে। মণ্ডপের ফলক অনুসারে ১১৬৮ (ইংরেজি ১৭৬১), আবার হুগলি ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে লেখা আছে ১১৬৬ (ইংরেজি ১৭৫৯)। ‘পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি’ বইতে বিনয় ঘোষ ১৭৫৯ সালের সপক্ষেই আরও কিছু তথ্য দিয়েছেন। ১৭৫৮ সালে যদি ওই মহিলারা অপমানিত হয়ে থাকেন তা হলে প্রথম পুজোর বছর ১৭৫৯ হওয়ারই বেশি সম্ভাবনা। আবার শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত ‘ফ্রেন্ডস অব ইন্ডিয়া’ পত্রিকার ১৮২০ সালের মে সংখ্যায় প্রকাশিত তথ্য অনুসারে এই পুজো শুরু হয় ১৭৯০ সালে। প্রতি বছর জগদ্ধাত্রী পুজোর সময়ে গুপ্তিপাড়ায় বিন্ধ্যবাসিনীদেবীর বারোয়ারি পুজো আজও অব্যাহত। বিন্ধ্যবাসিনী পুজো কমিটির হিসেবে, ২০১৮ সালে পুজোর ২৫৮ বছর পূর্ণ হবে।