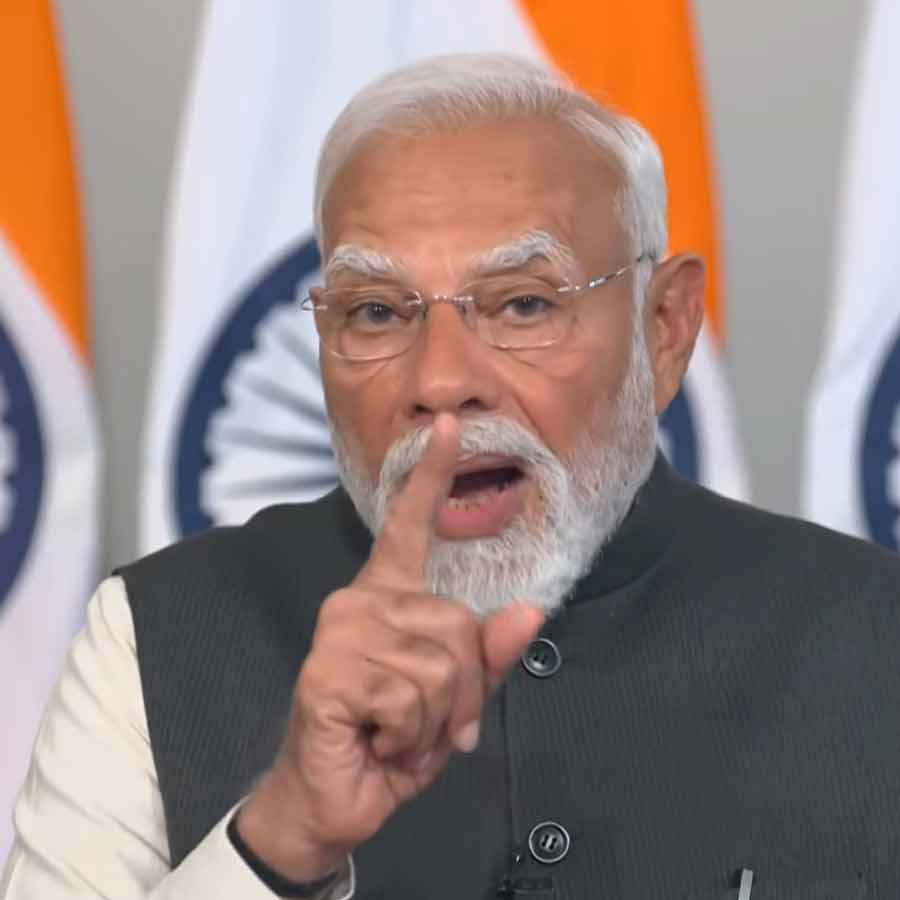কয়েক দিন আগে সন্ধ্যাবেলায় দাঁড়িয়েছিলাম অযোধ্যায় সরযূর ধারে। বড় নদী নয়, মাঝারি সাইজের স্রোতস্বিনী। নদীর ধারে বাঁধানো ঘাট, স্নান থেকে শ্রাদ্ধশান্তি সবই চলে। জায়গাটার নাম ‘রাম কি পেড়ি’। রামচন্দ্রের সঙ্গে এই ঘাটের কোনও সম্পর্ক নেই। আগে ছোট ঘাট ছিল, বন্যায় ডুবে যেত। বাবরি মসজিদ কাণ্ডের ঢের আগে, আশির দশকে এই ঘাট উঁচু করে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়। তারই নাম ‘রাম কি পেড়ি’। গত দীপাবলিতে এই ঘাটেই এক লক্ষ সত্তর হাজারের বেশি প্রদীপ জ্বালানো হয়েছিল। হরিদ্বারের গঙ্গায় কখনও এত বিপুলসংখ্যক প্রদীপ ভাসেনি।
ঘাটে আসার পথে নির্মীয়মাণ এক বিনোদন পার্ক। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের অনুপ্রেরণায় তৈরি হচ্ছে ১০০ মিটার উঁচু বিশাল এক রামের মূর্তি। খড়ম পায়ে, ধনু হাতে দাঁড়িয়ে আছেন দুর্বাদলশ্যাম। রামচন্দ্র খড়ম পায়ে দিতেন কি না জানি না, কিন্তু অত বিশাল মূর্তি দেখলে গা ছমছম করে। তুলসীদাসের বালকাণ্ড মনে পড়ে। কৌশল্যা এসে দেখলেন, দোলনায় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিশাল এক পুরুষ। ভয়ার্ত মা প্রার্থনা করলেন, ‘প্রভু, তুমি আবার আমার কোলের ছেলে হয়ে যাও।’ বাৎসল্যমধুর ভক্তিবাদ। হায় ভক্তি, তোমার দিন গিয়াছে! সবই এখন অতিকায়। এখানে একশো মিটার উঁচু রাম, গুজরাতে দেড়শো মিটার উঁচু বল্লভভাই পটেল। উচ্চতার অনেক অসুবিধা আছে। দুষ্টু লোকে বলতেই পারে, রামচন্দ্র এই ভারতে উচ্চতায় পটেলের থেকেও পিছিয়ে।
সন্ধ্যা সাতটায় এই সরযূঘাটে আরতি শুরু হয়। মাইকে গান, নদীর সামনে দাঁড়িয়ে পাঁচ জন পুরোহিত ভারী ভারী পিতলের প্রদীপ নিয়ে সরযূ বন্দনায় রত। হরিদ্বারের হর-কি-পৌড়ী বা বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটের স্টাইলে। শুনলাম, এই সরযূ আরতিটি নতুন অবদান। যোগী আদিত্যনাথের পরিকল্পনাতেই এর সৃষ্টি। কিন্তু প্রদীপের ওজন যতই বেশি হোক, উপনদী সরযূ কি গঙ্গার মাহাত্ম্য পাবে! গঙ্গা শুধু মর্তধামে বয় না, স্বর্গে অলকানন্দা ও পাতালে ভোগবতী নামে বয়ে যায়। শঙ্করাচার্য সাধে তাকে ‘ত্রিভুবনতারিণীতরলতরঙ্গে’ বলেননি। এই গঙ্গা ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে থাকেন, শিব তাঁকে জটায় ধারণ করেন। আবার বাচস্পতি মিশ্র তাঁর ‘তীর্থচিন্তামণি’তে লিখছেন, এই নদী বিষ্ণুস্রোতস্বরূপী! ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের সম্মিলিত মিথের আলোকছটা সরযূতে কোথায়!
একটু আগে গিয়েছিলাম সরযূর ধারে এক শিবমন্দিরে। নাগেশ্বরনাথ! জনশ্রুতি, রামচন্দ্রের ছেলে কুশ সরযূতে স্নানে নেমেছিলেন। পরের এপিসোড মহাভারতের অর্জুন-উলুপীর গল্পের মতো। এক নাগকন্যা কুশের প্রেমে বিহ্বল হয়ে তাকে টেনে নদীর অতলে নিয়ে যান। শিবের ভক্ত ছিলেন তিনি, কুশ তাঁর জন্য এই শিবলিঙ্গ স্থাপন করে দেন।
প্রাচীন শিলালিপিতে অযোধ্যার প্রথম উল্লেখ কবে? কনৌজের গঢ়বাল বংশীয় রাজা চন্দ্রদেব শৈব। একাদশ শতাব্দীতে তাঁর এক শিলালিপি জানাচ্ছে, আশ্বিন মাসের অমাবস্যায় সরযূতে স্নান সেরে তিনি সূর্যদেব, শিব ও বাসুদেবের আরাধনা করেছেন। তার পর পিতৃপুরুষকে পিণ্ড অর্পণ করেছেন। শ্রীরামচন্দ্র কখনও এই জনপদে এক এবং একমাত্র আরাধ্য ছিলেন না। সাচ্চা হিন্দু জানেন, প্রকৃত নগরে এক এবং একমাত্র কোনও আরাধ্য থাকেন না, সেখানে অনেক দেবতারই সহাবস্থান।
সেটা আরও বোঝা গেল বারাণসীতে এসে। এখানে বিশ্বনাথ মন্দির আছে, রয়েছে দুর্গামন্দির, সূর্য উপাসনার লোলার্ক কুণ্ড। রাজঘাটের কাছে বিষ্ণু আরাধনার আদিকেশব ও বিন্দুমাধব মন্দির। এই বৈচিত্র অযোধ্যার নেই। সেখানে শুধুই রাম-সীতার কনকমহল, দশরথমহল ইত্যাদি। আদিনাথ, অজিতনাথ প্রমুখ পাঁচ জৈন তীর্থঙ্কর যে অযোধ্যায় জন্মেছিলেন, তা আজ শুধুই স্মৃতি। আদিনাথ বা ঋষভদেবের মন্দিরটি তা-ও আছে, কিন্তু বৌদ্ধ দার্শনিক অসঙ্গ ও বসুবন্ধু যে এই জনপদেই থাকতেন, অযোধ্যা ভুলে গিয়েছে। এখানেই বহুত্ববাদের সংস্কৃতি শিরোধার্য-করা মহানগরী ও এক দেবতাকে নিয়ে উন্মাদনায়-মেতে-ওঠা এক মফস্সলের তফাত। বারাণসী জাতকের রাজা ব্রহ্মদত্তের আমল থেকে বাণিজ্যশহর। মুঘল আমলেও তাভার্নিয়ে, র্যালফ ফিচ, স্যর টমাস রো-র মতো বিদেশিরা গঙ্গাতীরে এই বারাণসীতে এসেছেন এবং মুগ্ধ হয়েছেন। অযোধ্যা নিয়ে বিদেশিদের প্রথম সাক্ষ্য জাহাঙ্গিরের আমলে উইলিয়াম ফিঞ্চের। অযোধ্যায় আসার পর স্থানীয়রা তাঁকে কিছু টিলায় ধ্বংসস্তূপ দেখিয়েছেন। ওখানেই ছিল রামচন্দ্রের দুর্গ। সরযূর ও পারে দুই মাইল গিয়ে এক গুহা থেকে ব্রাহ্মণেরা নিয়ে এসেছেন কিছু কালো চাল। রামচন্দ্রের শেষকৃত্য এই গুহাতেই করা হয়েছিল, তাই চালগুলি আজও কালো। রামের জন্মস্থান তখন অযোধ্যা চিনত না, কাল্পনিক শেষকৃত্যের স্থান চিনত। ধর্ম কোনও অজর, অক্ষয় পুঁথি নয়, জনসংস্কৃতিতে বারংবার তার বয়ান বদলে যায়।
দুই শহরের সঙ্গে জড়িয়ে অনন্য এক কবির স্মৃতি। তুলসীদাস। মুঘল সম্রাট আকবরের আমলে অযোধ্যা থেকে বারাণসীতে এসে তিনি ‘রামচরিতমানস’ রচনা করেন। কবির নামে বারাণসীতে আছে তুলসীঘাট, অযোধ্যায় ‘তুলসী স্মারক ভবন’ নামে ১৯৬৯ সালে তৈরি এক পাঠাগার। স্মারকে কী আসে যায়! কিশোরী জনকনন্দিনী ভোরবেলায় মিথিলার মন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছিলেন, বিশ্বামিত্রের সঙ্গে আসা তরুণ কিশোরটিকে দেখে তিনি মুগ্ধ। এই পূর্বরাগ বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসে নেই, তুলসীদাসে আছে। তুলসীদাস ভক্তির কথা বলেন, প্রেমের কথাও বাদ দেন না।
মুঘল জমানার শেষ দিকে, দুই শহরের সঙ্গেই জড়িয়ে গেলেন বিধবা এক নারী। ইনদওরের অহল্যাবাই হোলকার। অযোধ্যায় বেশ কয়েকটি রামমন্দির, সরযূঘাট থেকে বারাণসীর বিশ্বনাথ মন্দির, দশাশ্বমেধ, মণিকর্ণিকা ঘাট তিনিই বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। আজকের মনুবাদীরা ধর্মীয় ঐতিহ্য জানলে বুঝতে পারতেন, গঙ্গা ও সরযূতীরের দুই ধর্মক্ষেত্রেই কবি ও নারীর উত্তরাধিকার।
দুই ধর্মনগরের বৃত্তান্তেই রয়ে গিয়েছে নতুন ভারতের দুই শূন্যস্থান। শেখপুরা, মদনপুরায় বেনারসি শাড়ির কারিগরদের মুসলিম মহল্লা, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রাস্তায় যানজটের মধ্যেও নীরব এক শূন্যস্থান পীড়া দেয়। রাজার পৃষ্ঠপোষণায় মেধার শূন্যস্থান! হিন্দু তীর্থযাত্রীরা তখন জিজিয়া কর ও নানা অত্যাচারের সম্মুখীন। বারাণসীর বিখ্যাত পণ্ডিত কবীন্দ্রাচার্য শাহজাহানকে গিয়ে বললেন, জিজিয়া করটা তুলে দিন। মুঘল সম্রাট তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা শুনেছিলেন। জিজিয়া তো তুলেই দিলেন, উল্টে কবীন্দ্রাচার্য হয়ে গেলেন শাহজাদা দারাশিকোর শিক্ষক। সম্মানিত হলেন ‘গঙ্গালহরী’র কবি জগন্নাথ পণ্ডিতরাজাও। মুঘল বাদশাহরা বিধর্মীদের সম্মান দিতে কসুর করেননি।
এই ঐতিহ্যটাই গুঁড়িয়ে গিয়েছে। অযোধ্যায় দূর থেকে লোহার রেলিং, র্যাফ ও পুলিশ-অধ্যুষিত এক চত্বর দেখালেন রিকশাওয়ালা, ‘এখানেই ছিল বাবরি মসজিদ।’ বুকটা কেমন যেন ছাঁৎ করে উঠল।
স্বস্তি মিলল অযোধ্যার অদূরে ফৈজাবাদে। এখানেই অওধের প্রথম নবাব সুজাউদ্দৌল্লার সমাধি— গুলাববাড়ি (ছবিতে)। সামনে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের নোটিস বোর্ড জানিয়ে দিচ্ছে এই সমাধিস্থলের বৈশিষ্ট্য। মূল গম্বুজটি কেবল গোলাকার নয়, ভাল ভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, গম্বুজের ভিত্তিরেখাটি অন্য রকম। উল্টানো পদ্মফুলের মতো। কে বলে, পদ্ম শুধুই হিন্দুত্ববাদী দলের প্রতিভূ!
এই সুজাউদ্দৌল্লার বংশধর, লখনউয়ের নবাব গাজিউদ্দিন খানের আমলেই তৈরি হল অওধের রাজচিহ্ন। দু’দিকে দু’টি মাছ— মাহি মারাতিব। অধুনা পশ্চিমবঙ্গের সরকারি চিহ্ন যেমন ‘ব’, উত্তরপ্রদেশের সরকারি চিহ্ন রামের ধনুক আর অওধের নবাবদের ওই দুই মাছ। যোগী আদিত্যনাথের রাজ্য নিরামিষ-ঐতিহ্যের প্রতিভূ নয়।
মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়, ইতিহাস বিকৃত করা যায়, কিন্তু সমন্বয়ের ঐতিহ্যে আঁচড়ও কাটা যায় না।