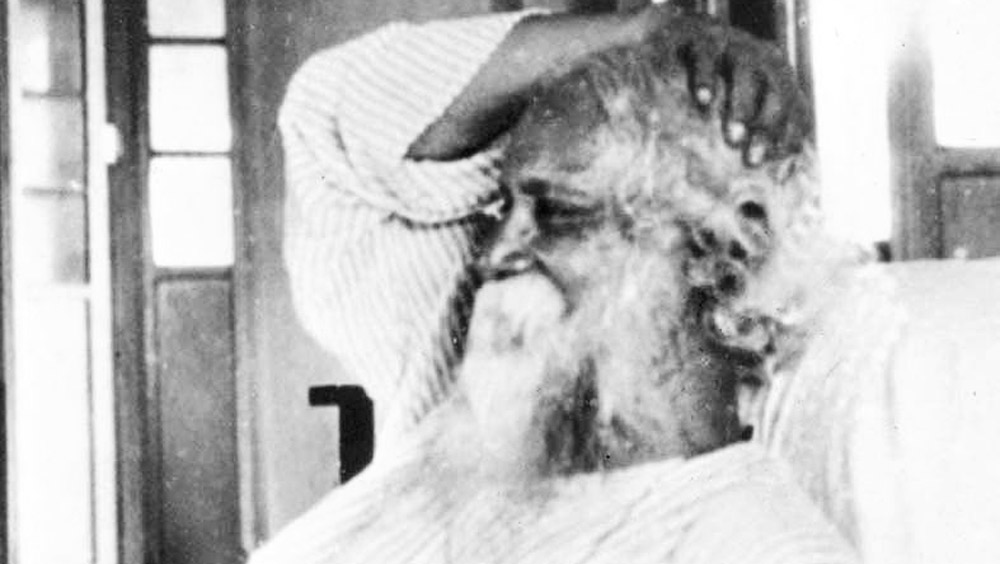দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে আলোচনায় ১৯৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, “আমি যখন গান বাঁধি তখনই সব চেয়ে আনন্দ পাই। মন বলে— প্রবন্ধ লিখি, বক্তৃতা দিই, কর্তব্য করি, এ সবই এর কাছে তুচ্ছ।” সব সৃষ্টির মধ্যে তাঁর এই গানই যে বেঁচে থাকবে, এমন এক দৃঢ় প্রত্যয়ও তিনি ব্যক্ত করেছিলেন রানী চন্দকে। বুঝতে অসুবিধে হয় না নিজের তৈরি গান তাঁর কত প্রিয় ছিল। কিন্তু জনারণ্যে কী ভাবে বেঁচে আছে এই অতুলন সৃষ্টি? সংযোজিত দশ বছর শেষে ২০০১-এ স্বত্ব উঠে যাওয়ার পর রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনে কিছু বিপজ্জনক প্রবণতা লক্ষিত হচ্ছে। মুখ্যত সুর, তাল বিকৃত করে গাওয়া হচ্ছে। এ-হেন বিকৃতি কি আগে ঘটেনি? ১৯৪০-এ প্রফুল্ল মহলানবিশের উদ্যোগে গঠিত রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিষ্ঠান ‘গীতালি’-র উদ্বোধনী ভাষণে রবীন্দ্রনাথ সখেদে বলেছিলেন, “এখন এমন হয় যে, আমার গান শুনে নিজের গান কিনা বুঝতে পারি না। মনে হয় কথাটা যেন আমার, সুরটা যেন নয়। নিজে রচনা করলুম, পরের মুখে নষ্ট হচ্ছে, এ যেন অসহ্য।” কিন্তু এই বিকৃতিগুলি তখন গায়কদের ততটা ইচ্ছাকৃত ছিল না, কারণ তখন শান্তিনিকেতনের বাইরের মানুষের ঠিক তালিমের তেমন সুযোগ ছিল না, অনেক গানের স্বরলিপি পাওয়াও সমস্যা ছিল। কিন্তু এ কালে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিকৃতির মূলে নিছক চমক সৃষ্টি করে গায়ক-গায়িকাদের সহজে যশোলাভ আকাঙ্ক্ষা।
বিকৃতির ধরনগুলি দেখা যেতে পারে। কয়েক বছর আগে দ্য বং কানেকশন ছবিতে ‘পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে’ তাল বদলে (দাদরা থেকে কাহারবা) ও কুৎসিত ভোকাল রিফ্রেন ‘উল্লাল্লা উল্লাল্লা’ সহযোগে ব্যবহৃত হয়। আজকের ইউটিউবে দ্বৈতকণ্ঠের গানটির ভিউ ৩৯ লক্ষ, লাইক ৩৩কে। পাশে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ঠিক ভাবে গাওয়া এ গানের ভিউ ১৯কে, লাইক খুবই কম, ২০২। এলার চার অধ্যায় ছবিতে ব্যবহৃত কীর্তনাঙ্গ আখরযুক্ত ‘মাঝে মাঝে তব দেখা পাই’ জনপ্রিয় হওয়ার পর এ গান গাইতে নানাজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বেশির ভাগই দেখা গেল মাঝখান থেকে গান শুরু করছেন, অতিরিক্ত অলঙ্করণ যোগ করছেন, কেউ গান শুরু করছেন ‘আহা মাঝে মাঝে’ বলে, যে শব্দটি আখরযুক্ত, আখরহীন কোনও পাঠেই নেই। রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলতে হয়: “পরের গানের উন্নতিসাধনে প্রতিভার অপব্যয় না করে নিজের গানের রচনায় মন দিলে তাঁরা ধন্য হতে পারেন।” জনৈক গায়িকার মাঝখান থেকে শুরু করা ‘মাঝে মাঝে তব’ গানের ভিউ ও লাইক দেখলে চমকে উঠতে হবে, যথাক্রমে ২.৫ কোটি, ১.৯ লক্ষ! পাশেই ঋতু গুহের গাওয়া এ গানের ভিউ ৬৬কে, লাইক মাত্র ৬৬৯! বেডরুম ছবিতে বহুশ্রুত ‘মায়াবনবিহারিণী হরিণী’-র স্থায়ীতে অদ্ভুত ভাবে কোমল রেখাব লাগিয়ে দেওয়া হল, যা স্বরলিপিতে নেই। ইউটিউবে এ গানের ভিউ ১০ লক্ষ, লাইক ১৩কে। অথচ, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের ঠিক সুরে গাওয়া এ গানের ভিউ ১.৪ লক্ষ, লাইক ৭৭৭। তাও এই পরিসংখ্যান দু’-তিন বছর আগের।
এই হিসাব থেকে স্পষ্ট, কেন অনেকে গান বিকৃত করে গাইছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে দু’-একটি ব্যতিক্রম (‘বড় বিস্ময় লাগে’, ‘শুভ্র প্রভাতে পূর্ব গগনে’) ছাড়া তানালঙ্কার প্রয়োগ করেননি, সুরবিহারও (ইম্প্রোভাইজ়েশন) বিশেষ অপছন্দ করতেন। মুখ্যত উচ্চাঙ্গসঙ্গীতকে নির্ভর করে স্বকীয় ভাবে মৌলিক গান তৈরি করে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের শৃঙ্খল ভাঙতে চেয়েছিলেন। অথচ, আজকাল নামী-অনামী গাইয়েরা রাগসঙ্গীতের ধরনে শুরুতে আলাপ করছেন, তানকর্তবে ভরিয়ে তুলছেন গান। এক জনের ‘দুই হাতে কালের মন্দিরা’ গানশেষে প্রায় এক মিনিট তানকর্তব, ভানুসিংহের পদাবলী-র ‘গহন কুসুমকুঞ্জমাঝে’-র শেষে তারানা। গলার কায়দা দেখিয়ে চমক সৃষ্টি করে শ্রোতা আকর্ষণই লক্ষ্য। অধিকাংশই অদীক্ষিত শ্রোতা, তাতেই মুগ্ধ। আসলে গায়ক ও শ্রোতা উভয়েরই তৈরি হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের কথা স্মর্তব্য, “শুনিবারও প্রতিভা থাকা চাই, কেবল শুনাইবার নয়।”
গায়কদের দায়িত্ব অনেক বেশি, কিন্তু অধিকাংশই তা নিয়ে সচেতন নন। বিকৃত গান-পরিবেশনের পিছনে সহজে যশোলিপ্সার সঙ্গে আছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতভাবনা সম্পর্কে অজ্ঞানতাও। রবীন্দ্রনাথের অতি মূল্যবান গ্রন্থ সংগীত-চিন্তা বিষয়ে শিক্ষক বা ছাত্র ক’জন ওয়াকিবহাল, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, কয়েকটি সঙ্গীত-শিক্ষায়তনে গান শেখানোর পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে ‘থিয়োরি’ পড়ানোর ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সিংহভাগ পড়ুয়া তা কোনও ক্রমে পরীক্ষার খাতায় উগরে দেওয়ার জন্য মুখস্থ করে, হৃদয়ে আত্মস্থ করে ক’জন? ব্যক্তিগত ভাবে কারও কাছে গান শেখা মানে ৪০-৪৫ মিনিটের মধ্যে একটা গান তোলা। ক’জন শিক্ষক রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে ছাত্রদের অবহিত করেন? অতীতে সরকারি স্তরে রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিক্ষকদের জন্য একটা শিক্ষাক্রমের উদ্যোগ করা হয়েছিল যে, কী ভাবে তাঁরা শেখাবেন। দুঃখের বিষয়, তা স্থায়িত্ব পায়নি। গান শেখার ক্ষেত্রে আর একটি ব্যাপার ইদানীং লক্ষণীয়: অনেকেই শিখতে চান নামী লোকের কাছে, শিখছেনও। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, নামী মানুষটি মাসে এক দিন শেখাতে আসছেন, বাকি দিন শেখাচ্ছেন তাঁর কোনও ছাত্র বা ছাত্রী! সুচিত্রা মিত্র, সুবিনয় রায়, মায়া সেনরা কোনও দিন তা করেননি।
আর একটি মারাত্মক প্রবণতা, বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই শ্রমসাধ্য দীর্ঘ তালিমের বদলে মঞ্চে বা টিভিতে গাইতে ব্যগ্র। টাকা খরচ করে বা প্রতিপত্তির জোরে সাধারণ স্তরের বহু গায়ক গাইছেন, ইউটিউবে গান আপলোড করছেন। গানে যন্ত্রানুষঙ্গ মাত্রা-ছাড়ানো, গানের মেজাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন।
রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগৎ এখন এমন কিছু অসুখে আক্রান্ত। পঁচিশে বৈশাখ, বাইশে শ্রাবণ আর বছরভর নানা অনুষ্ঠানের আয়োজনেই কি আমাদের সব দায়িত্ব শেষ? গানের বিকৃতি ও অন্য সমস্যাগুলি বিষয়ে সচেতন ও সতর্ক হওয়ার কোনও দায় নেই?