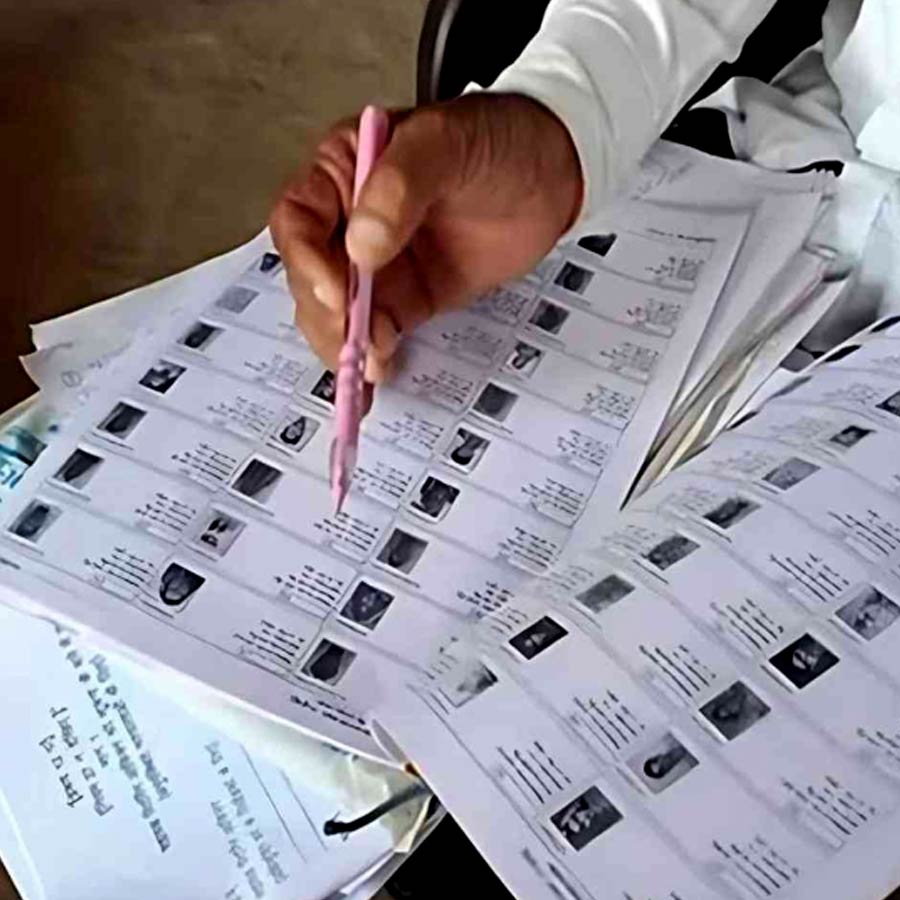‘‘কাকে বেশি ভালবাস তুমি? বাবাকে? না মাকে?’’
এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর বিশ্বের কোনও শিশু বা প্রাপ্তবয়স্ক আজও দিতে পারেনি। কারণ দু’চারটে হাতে গোনা সম্পর্ক আমাদের এতটাই আচ্ছন্ন করে রাখে যে, তাদের এক, দুই, তিন, চার নম্বরে সাজানোর অমর্যাদাটা একটা অবাস্তব চেষ্টা। অথচ বাবার রাগ গিয়ে পড়ে মায়ের উপর, আর মায়ের একরোখামির সব দায় বাবার ঘাড়ে। রাগব, ঝগড়া করব, রাতবিরেতে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতেও পারি— এমনকী মধ্যরাতে নির্লজ্জের মতো ফিরেও আসতে পারি। তবু তারা এক-দুই বা বেশি-কম বাবা-মা হতেই পারেন না। সারাজীবন মুখ দেখব না। তবু ওই মুখ দু’টো আমার সম্পত্তি। সৃষ্টি ও স্রষ্টার এই অনন্ত খেলা পিতা-মাতা ও সন্তানেরই নয় শুধু, মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যেও যেন চলতেই থাকে। সেই প্রাগৈতিহাসিক সম্পর্কের বন্ধনটা ধরেই নতুন করে প্রায় খেলার ছলে টান মারলেন পরিচালক সুজিত সরকার। শনিবার নাইট শোতে হাইল্যান্ডে পার্কের মধ্যরাতের ভরা প্রেক্ষাগৃহে সপরিবারে ‘পিকু’ দেখলাম!
গল্পটা বলে দিই? পিকু মেয়ে, বাবা ভাস্কর ব্যানার্জি—দু’জন দিল্লি প্রবাসী বাঙালি। ‘পিকু’র মা নেই। একটি কাজের লোক। সারাক্ষণ থাকে। বাবার অর্থাৎ ভাস্করবাবুর জ্বালায় ঠিকে মেয়েটি চলে গিয়েছে। কৃপণ বলে গাড়ি গ্যারেজে থাকে— কেবল অফিসের অ্যাকাউন্টে ভাড়ার গাড়ি চড়ে পিকু। মেয়ে নায়িকা, বাবা নায়ক। আর এই ছবির খলনায়ক বাঙালির জীবনের রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতোই চিরকালীন ও চিরনবীন। এমন খলনায়ক ভারতীয় সিনেমায় মানুষ আগে কখনও দেখেনি। অথচ সবার জীবনেই পিছন ছাড়ে না সে। তার ভালনাম পায়খানা। ডাকনাম হাগু!!! ‘ব্যানার্জিবাড়ি’র সমস্যা নিয়ে গল্প হলেও এ যেন বাঙালি ঐতিহ্যের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বললাম না, পিছন ছাড়ে না আমাদের। তাই বৈঠকখানার মতোই পায়খানার ঘরটিও বাড়ির চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ জয়েন্ট হিসেবে রয়েই গেল।


এ নিয়ে লজ্জাসঙ্কোচের কিছু নেই। কারণ ‘গু’ একটি সংস্কৃত শব্দ। যার অর্থ অন্ধকার বা আবর্জনা। তার থেকেই জন্ম ‘গুরু’ শব্দটির। ‘রু’ অর্থাৎ আলো। মানে দাঁড়াল অন্ধকার থেকে যিনি আলোর পথ দেখান তিনি গুরু! এ ছবির গুরু পরিচালক সুজিত সরকার। সুজিত স্পষ্ট জানেন গোপাল ভাঁড়ের নৌকায় পটি পাওয়ার গল্প শুনে যে বাঙালি বড় হয়, বাঙালির যে কোনও পারিবারিক আড্ডায় শেষ বেলায় পটি-প্রসঙ্গ উত্থাপন হবেই, যে বাঙালির বেগ ও আবেগ দুয়ে মিলে রবীন্দ্রসঙ্গীতও মানে বদলে ল্যাট্রিন সং হয়ে ওঠে। চমকাবেন না। ছোটবেলা থেকেই একাধিক এমন গান পটির প্রসঙ্গে অব্যর্থ ভাবে মিলে যেতে দেখেছি। যেমন, ‘তোমার হল শুরু, আমার হল সারা!’ বা ‘এসেছিলে তবু আসো নাই, জানায়ে গেলে!’ মনে পড়ছে নিশ্চয়ই? এমনকী আমরা চর্যাপদের জ্ঞানীদের নামগুলোকেও মাফ করিনি— যেমন ভুসুকপাদ, লোমপাদ— এ রকম অজস্র নাম কেবলমাত্র পাদ-দেশে এসে বাঙালির খোরাক হয়েছে! সুজিত একেবারে সেই প্রাচীন ভীমরুলের চাকে ঢিল মারলেন। ফুটো হয়ে অঝোরে সম্পর্কের মধুও ঝরল, ভীমরুলের ঝাঁকও হল্লা করে উড়ে বেড়ালো হাসি আর করতালিতে!
‘পিকু’-র পরিচালক সুজিত সরকার।
ছবি: সুব্রত কুমার মণ্ডল।


যখন পৃথিবীতে সন্তানরা বাক্সপ্যাঁটরা গোছাচ্ছেন এ দিক ও দিক জীবিকার সন্ধানে, ঠিক তখন অসহায় নিঃসঙ্গ এক বাবার হৃদয়ে হাত রাখল আজকের এক ভারতীয় সিনেমা, ‘পিকু’। বাবার ওষ্ঠকাঠিন্য ও কোষ্ঠকাঠিন্য— দু’য়ের চাপে ব্যক্তিজীবন বিপর্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও উজ্জ্বল সুন্দরী পিকু সেই ছোটবেলার ধরা হাতটা আজ জীর্ণ হয়ে গেলেও ছাড়ল না। এই সুজিতই ‘ভিকি ডোনর’য়ের স্রষ্টা। স্পার্ম ডোনর নিয়ে ঠাট্টা করতে করতে কখন যেন সুজিত বুকপকেটের পিছনে ছুরি চালিয়ে দেন! এ বারও তাই হল। কন্সটিপেশন, পায়খানা, হাগুর শতনাম ও শতরূপ শ্রবণ করতে করতে জীবনের ‘সার’ বস্তুর ঠিকানা খুঁজে পেল দর্শক। ‘ওল্ড এজ’ আজ নাকি সামাজিক সমস্যা! বাংলা নয়, সারা বিশ্বের! প্রবাসী সন্তানের আসার অপেক্ষায় মৃত বাপ-মাকেও দু’-চারদিন অপেক্ষা করতে হয় পিসহাভেনে! আমাদেরই চারপাশে বাড়ছে বৃদ্ধাশ্রম। এমন সময়ে যথার্থ একটা ছবি বানালেন টিম সুজিত। উত্তর কলকাতা নিয়ে প্রযোজক সুজিত ক’দিন আগেই ‘ওপেন টি বায়োস্কোপ’য়ে বাজিমাত করে গেছেন। তখন সত্যি বুঝিনি ওটা ছিল ওঁর ‘পিকু’র উত্তর কলকাতা ও বাঙালিয়ানার হোমওয়ার্ক। হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের পর হিন্দি সিনেমার অন্দরমহলে বাংলার হাস্যরসের নতুন দূত সুজিত সরকার।
অভিনয় নিয়ে কিছু না লেখাই ভাল। সুপারস্টারদের বড় মাপের অভিনেতা হতে দেখার সুযোগ যখন ঘটে, তখন তার তৃপ্তিই আলাদা। দিনের পর দিন ‘বাবুমশাই’ যে উচ্চতায় নিজেকে নিয়ে যাচ্ছেন, তা এই ছবি না দেখলে বোঝা যায় না। তবে আমার বিশ্বাস, বাংলা উচ্চারণ আরও একটু ভাল করতে পারেন উনি। কেন করলেন না জানি না! ইরফানের স্বাদ আমি কলকাতায় বসে ঋত্বিককে দিয়ে মেটাই। অমন আধুনিক ও বড় মাপের অভিনেতা একটু এক রকম হলেও এত স্বাভাবিক ও বুদ্ধিদীপ্ত, কিছু বলার থাকে না। যিশু বেশ ভাল কাজ করল এ ছবিতে। ‘বরফি’র অতৃপ্তি এ ছবিতে একটু মিটল। রঘুবীর যাদব আমার ছোটবেলার হিরো। আজও তাই। ওকে যেন কত চিনি, জানি, ভালবাসি, দয়া হয়, কান্না পায়! মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় একদমই মৌসুমী এ ছবিতে। উজ্জ্বল উপস্থিতি তাঁর।
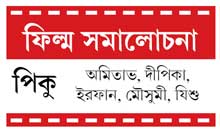

আলাদা প্যারাগ্রাফ দীপিকার জন্য বরাদ্দ করলাম। রাগ, দুঃখ, অভিমান, প্রেম, হতাশা, নিঃসঙ্গতা, একজন সুন্দরীর বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয়ে এমন দম আটকানো অভিজ্ঞতা হয়! উফ! এ ছবি দেখলেই বুঝবেন। আমার মন কেড়ে নিল ‘পিকু’র ছোট ছোট ইমোশন। যেগুলো ব্যাডমিন্টন শাটলের মতো ওর আর ইরফানের মধ্যে অথবা বাবা-মেয়ের মধ্যে অনায়াসে যাতায়াত করছিল। অনুপমের গানের সঙ্গে দীপিকা, ইরফান আর পিছনের সিটে অমিতাভ বচ্চনকে দেখে অদ্ভুত গর্ব হল! কলকাতার গানকে ড্রাইভারের সিটে বসানোর জন্য ধন্যবাদ।
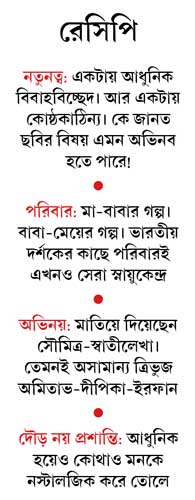

সমালোচনা করার মতো বিন্দুমাত্র ইচ্ছে থাকে না এই ছবি দেখে বের হওয়ার পর। একটা ভাল লাগার পাশাপাশি নিজের ছোটবেলা-প্রয়াত বাবার কথা, সবই ঘুরপাক খায়। বাবা-মায়েদের বয়স হচ্ছে সবারই। সন্তানের জন্য অপেক্ষা করাটাই যেন তাঁদের শেষ কর্মজীবন! তখন ঘুম ভাঙায় ‘পিকু’। ডাকে। ধাক্কা দেয়। সঙ্গ দিতে বলে। এখানেই ছবির শুরু, এখানেই এই ছবির শেষ।
কহানির গ্রাফ আঁকলে কখনওই এ ছবির কোনও চূড়া নেই। পর্বত হয়ে ওঠে না এই ছবি। বরং মালভূমির মতো বিশাল একটা টেবিলটপ উপত্যকার প্রশান্তি দেয়। তাই দিন গড়ায়, সমস্যা আর জীবন একই থাকে প্রথম থেকে শেষ বিন্দুতে! এই জাতীয় ছবিকে দশে নম্বর দেওয়ার ইচ্ছে থাকে না। তাই মার্জনা চেয়ে ওই খোপটা উহ্য রাখলাম। বাবা-মায়ের মতোই ভাললাগা-মন্দলাগা মিশেই আপন একটা ছবি হয়েই রইবে ‘পিকু’।
এই বিষয়-নির্মাণে ‘ভিকি ডোনর’য়ের উচ্চতাকে ছাপিয়ে যেতে পারতেন পরিচালক। হাসি-ঠাট্টা, গ্যাস-পটির উপলক্ষে ছবির শেষ বেলায় আরও একটা ধাপ উত্তরণের অতৃপ্তি আমার মনে জমে রইল। তবু বারবার আমার বাবাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমি ‘পিকু’র কাছে চিরঋণী হয়ে রইলাম। একটা গিটার আর ক্রেমাফিনের শিশি ছিল বাবার চিরসখা। গানবাজনা, হই-হুল্লোড়ের মধ্যেও দেখেছি ল্যাক্সেটিভের শিশি একদিনও হাতছাড়া না করতে। বাবা থাকতে ‘পিকু’ যদি দেখতাম... আরও কয়েক দিন দু’জন দু’জনকে আর একটু বেশি পেতাম। ইস! মনের মধ্যে এই একটু মিউকাস জমে রইল!