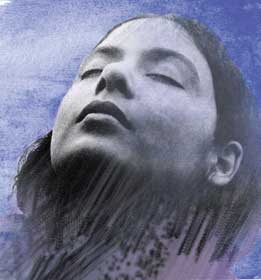আবার মাইয়া?”
সে জানলও না ওই মুহূর্ত থেকেই শুরু হয়ে গেল তার যুদ্ধ।
নিজের মা। হতাশা, নিরাশা ক্ষোভে তার সদ্য নাড়িকাটা আট-নম্বর মেয়ে-সন্তানকে পা দিয়ে ঠেলে দিয়েছিল। এগারো ভাইবোনের সবচেয়ে ছোট, মেয়ে হয়ে জন্মানোর ঘোর অপরাধে অপরাধী সেই মেয়ে আঁতুড়ঘরের আগুনের মালসার ওপর পড়তে পড়তেও বেঁচে গেল। ধরে নিল তার মেজদি।
জিতে গেল সে। সদ্য পৃথিবীতে আসা, জন্মেই লাথি খেয়ে আগুনে পুড়ে মরতে মরতেও বেঁচে গেল অনাকাঙ্ক্ষিত মেয়েটি। টিকে থাকার প্রথম সংগ্রাম। প্রথম লড়াই। প্রথম যুদ্ধ। তখন কে জানত, এ যুদ্ধ চলবে জীবনভর।
লড়াই করতে করতেই আশিটা বছর পেরিয়ে আসা সেই মেয়ে সুপ্রিয়াদেবী। আমার ‘বেণু আন্টি’।
আমাদের পরিবারের সঙ্গে একটু একটু করে ক্রমশ ওদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং নিবিড় ভালবাসার সম্পর্ক সেই ষাটের দশক থেকে। ওদের বলতে বেণু আন্টি আর উত্তমকাকুর কথা বলছি।
আমি তখন খুবই ছোট। আমার বাপের বাড়ি প্রতাপাদিত্য রোডে। যে বাড়িতে যাতায়াত ছিল গানের জগতের সমস্ত কৃতী শিল্পীর। সে লতা মঙ্গেশকর-আশা ভোঁসলে-মহম্মদ রফি থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়-মান্না দে-কিশোরকুমার হয়ে ভি বালসারা। এঁদের বাড়িতে নিয়ে আসার মূল মানুষটি ছিলেন হেমন্তকাকু। তবে সূত্র আমার বাবা, সাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।
ওই সময় বাবার সঙ্গে আমি বেণু আন্টির ময়রা স্ট্রিটের বাড়িতে প্রায়ই যেতাম। উত্তমকাকু আমাদের বাড়িতে আসতে চাইত খুব। বাবা বাধা দিত। বলত, “তুমি এলে এত লোক ভিড় করবে যে বাড়ি ভেঙে পড়বে।” কিন্তু বাবারই জনপ্রিয় বই নিয়ে ‘কাল তুমি আলেয়া’ করার জন্য উত্তমকাকু টানা প্রায় একটা বছর বাবার অনুমতির অপেক্ষায় ছিল। তাতেও বাবা রাজি না হওয়ায় একবার পয়লা বৈশাখের সকালে সটান হাজির হয়েছিল বেণু আন্টিকে নিয়ে। সেই ছিল ওদের প্রথম আমাদের বাড়িতে আসা।

বেণু আন্টি এবং উত্তম কাকু দুজনেই আশুতোষ-সাহিত্য অনুরাগী। বিশেষ করে বেণু আন্টিই তার সেই ছোটবেলা থেকেই গোগ্রাসে বই পড়ার অভ্যাসে উত্তমকাকুকে বাবার বই বেছে বেছে পড়ে শোনাত। যেগুলোতে পরের পর সিনেমায় অভিনয় করে গেছে উত্তমকাকু। ওই সময় থেকে বেণু আন্টিকে আর সুপ্রিয়া দেবীকে আমি নিজের চোখে এবং আমার বাবার চোখে দেখেছি, জেনেছি, বুঝেছি।
এখানে সব চেয়ে আগে যে কথাটা বলতে চাই তা হল, আমার বেণু আন্টি বা সকলের সুপ্রিয়াদেবী কারও ‘ঘর’ ভাঙেনি। ব্যাপারটা আমার যেমন নিজের চোখে দেখা, তেমন বাবার কাছেও শোনা।
আমি তখন খুবই ছোট যখন ষাটের দশকে উত্তমকাকু তার ভবানীপুরের বাড়ি ছেড়ে বেণু আন্টির ময়রা স্ট্রিটের বাড়িতে বরাবরের মতো চলে এল। সে এক উত্তাল সময়। কাগজে-কাগজে, ফিল্ম ম্যাগাজিনে এ জন্যে সুপ্রিয়াদেবীকে কাঠগড়ায় তুলে যা-তা লেখা হচ্ছে। তাকেই দায়ী করে গসিপে গসিপে ভরে উঠছে কলকাতা। বহু ছবি থেকে ইচ্ছে করে বাদ দেওয়া হচ্ছে। ঘরে, ঘরে, চায়ের টেবিলে, মদের আসরে এই নিয়ে রসালো আলোচনা, গল্প, কেচ্ছা। আমার বাবা তখনই বলত, “বেণু কারও ঘর ভাঙেনি। উত্তমই ভাঙা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ওর কাছে গেছে।”
বাবাকে হুবহু ‘কোট’ করলাম। আজও কানে বাজে বাবার সেই গমগমে গম্ভীর গলার স্পষ্ট কথাগুলো। আজ এত দিন বাদে এই কথা শুনে কারও অপ্রিয়ভাজন হলে কিচ্ছু করার নেই। কথাটা যে একশো ভাগ সত্যি, সে হলফ করে বলতে লাগে না।
অনেকেই জানে, কিন্তু স্বীকার করে না, যে বেণু আন্টির কাছে চলে আসার আগেও উত্তমকুমার বেশ কয়েক বার নিজের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।
সুপ্রিয়াদেবী নয়! আশ্রয় চেয়েছিলেন অন্তত দু’জন সহশিল্পীর কাছে। কোথাও জায়গা হয়নি। অথচ সেটা তাঁদের পক্ষে অনেক সহজ ছিল।
একা, বিশাল ফ্ল্যাট নিয়ে থাকা ডিভোর্সি যুবতী নারী, যার একমাত্র বাচ্চা মেয়ে বাইরের বোর্ডিং স্কুলে, তার পক্ষে এক কথায় উত্তমকুমারের মতো বিবাহিত পুরুষকে কোনও কিছুর পরোয়া না করে— না সমাজ, না বাইরের দুনিয়া, না নিজের আত্মীয়স্বজন বা কাজের জগৎ— এক কথায় এক ছাদের নিচে থাকতে দেওয়া, অথবা একসঙ্গে নিয়ে থাকা, দুর্মর বুকের পাটা আর নিখাদ টান ছাড়া অসম্ভব।
যা সেই সময়ে বুঝেছিল আমার বাবা এবং বুঝেছিল বলেই হতে পেরেছিল ‘বেণুর দাদা’। উত্তমকুমারেরও।
সেই সময়ে বেণু আন্টিকে দেখেছি একফালি ছোট্ট চিলতে স্লিভলেস ব্লাউজে, খোলা চওড়া পিঠ, সুঠাম হিপ্, সরু কোমরের লুব্ধ বাঁকের কার্ভেচারে। শিফন শাড়ির স্বচ্ছতায় নিটোল বুকের দুরন্ত বিভাজিকায়। কম ঝড় ওঠেনি। কম সমালোচনা হয়নি। কিন্তু বেণু আন্টি না, সুপ্রিয়াদেবী নির্বিকার। মনে হয়, ইচ্ছে করেই জেনে বুঝে অমন সাজত বেণু আন্টি। একটা না-বলা বিদ্রোহ ছিল ভেতরে ভেতরে। ছিল নীরব উপেক্ষা, নিঃশব্দে তাচ্ছিল্যের হেলাফেলা। ওই সব নিম্ন মানের চরিত্রগুলোর প্রতি। যেন কিছু না বলেই ওই শরীর ওই মন বলে দিত, “দূরে থাকো। আমার থেকে সরে থাকো।”
সব জেনে বুঝে নিরন্তর নিন্দে, সমালোচনা আর কেচ্ছার বোঝা মাথায় নিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো চলা— এও লড়াই বইকী! অবিশ্রান্ত সংগ্রাম।
বাবা বলত, “যারা বেণুকে নিয়ে এত চর্চা করে, তাদের মধ্যে যারা পুরুষ, তারা ওকে পেতে চায়। ফিজিক্যালি কামনা করে। আর মেয়েরা ওর মতো ফিগার চায়, ওর মতো সাজতে চায়, কিন্তু পারে না। তাই হিংসে করে। আর সেই জন্যই সহ্য করতে পারে না।”
কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। কিন্তু এমন ভালবাসলেও অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র ছিল না বাবা। তাই ‘লাল পাথর’ বা ‘সন্ন্যাসী রাজা’ দেখে যেমন অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছে, তার বেণুর সাজ-সৌন্দর্য মেকআপের, তেমনই নিজের বই ‘কাল তুমি আলেয়া’ বা ‘সাবরমতী’ দেখে সমালোচনা করতেও ছাড়েনি।
এখান থেকেই ফিরে যাব বেণু আন্টির জীবনের গোড়ার পর্বে।
বর্মা। ১৯৩৩। ৮ জানুয়ারি। বাংলার ২৪ পৌষ। হাড় হিম করা নিশুতি পৌষালি রাতে কাঁটায় কাঁটায় ১২টায় সারাটা জীবন ধরে কঠিন সংগ্রামের ভবিতব্য এবং ক্ষমতা নিয়ে দুনিয়ায় এল নামকরা অ্যাডভোকেট গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আর কিরণবালাদেবীর আট মেয়ে তিন ছেলের সবচেয়ে ছোট, এগারোতম কন্যা-সন্তান বেণু। ‘সুপ্রিয়া’ নামকরণ বাড়ি থেকে হয়নি। হয়েছে অনেক পরে। বড় অদ্ভুতভাবে, সে গল্পে না হয় পরে আসছি।

ময়রা স্ট্রিটের বাড়িতে লক্ষ্মী পুজোয়
বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে বিশাল ভরভরতি সংসার। নামজাদা অ্যাডভোকেট বাবার দু’হাতে রোজগার। কাকা ডা. সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তখনকার মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের ক্যাবিনেট মিনিস্টার। বড় জামাইবাবু সাহিত্যিক বনফুল— নিটোল সম্ভ্রান্ত পরিবার।
ভালই ছিল বড় বাড়ির ছোট মেয়ে। কিন্তু ক’দিন? জন্মই যে যুদ্ধ, নিরন্তর লড়াই আর সঙ্কুল সংগ্রামের তিলক কপালে নিয়ে!
কপালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাইরের পৃথিবীতে তখন যুদ্ধের দামামা। বর্মার বিশাল প্রাসাদের মতো বাড়ি, বাবার অত বড় প্র্যাকটিস, সব ছেড়েছুড়ে সেই বাঁচার তাড়নায়, টিকে থাকার তাগিদে, কখনও নৌকায়, তারপর পায়ে হেঁটে দু’মাস ধরে হাঁটাপথে পথ চলে কলকাতায় পালিয়ে আসা। ... বয়স তখন কত? দশ কী এগারো!
বেণু আন্টির মুখেই শুনেছি সেই অবিশ্বাস্য প্রাণশক্তি নিয়ে তখন থেকে যুঝে যাওয়ার কথা। ইরাবতী নদীর জল তখন বিষিয়ে গেছে। মুখে দেওয়ার উপায় নেই। তেষ্টায় ছাতি থেকে নাভি পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ। সমানে চোখের সামনে মানুষ মরছে। কাপড়ে ঝুলিয়ে চারদিকে ধরে মৃতদেহ নিয়ে জলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। যারা পারছে, তারা এগিয়ে চলেছে জীবনের দিকে। মুমুর্ষু স্বামীকে ফেলে শিশু কোলে স্ত্রী। এরকম অজস্র, অগুনতি দৃশ্য। এমনই এক মহিলার কাছে তার দুটি বাচ্চার জন্য আগলে রাখা জল থেকে এক বিন্দু চেয়েছিল তৃষ্ণায় মরে যাওয়া বেণু। দশ-এগারো বছরের মেয়েকে শুনতে হয়েছিল কঠিন, নির্দয় বাস্তবের তীব্র তিরস্কার— “না ওরা ছোট, এই জল ওদের। তুমি বড়...,” তেষ্টায় মরতে মরতে দশ বছরের মেয়ে জানল, সে ‘বড়’ অর্থাৎ ওই জল ছাড়াই তাকে বাঁচার জন্য লড়াই করতে হবে। করেও ছিল এবং মরতে মরতেই বেঁচে গেল।
বেণু আন্টি এই ঘটনা বলতে বলতে বলেছিল, “জলের তেষ্টা যে কী তেষ্টা, কল্পনাও করতে পারবি না। কতকাল আগের কথা! এখনও আমার সেই তেষ্টা যায়নি। আজও আমি সেই তেষ্টার বিভীষিকায় আঁতকে উঠি।”
সত্যিই আশি পেরনো সুপ্রিয়াদেবীর চোখেমুখে আট-দশ বছরের বেণুর সেই জলের আর্তি আমি স্পষ্ট দেখেছি।
কলকাতায় এসে ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ি। কিন্তু থিতু হওয়া জীবন যে জন্ম থেকেই কপালে নেই!
আর্থিক টানাপড়েনে কলকাতার পাট উঠিয়ে দেশভাগের পূর্ব পাকিস্তান, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ। ’৪৭-এর মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ, মৃত্যুর মিছিল। আবার কলকাতা।
বড় দিদিদের বিয়ে দিতে গিয়ে বাবার হাত শূন্য। সেই রকম এক সময়ে চন্দ্রাবতীদেবীর সান্নিধ্য, আর সিনেমায় আসা। চন্দ্রাবতী দেবীর একই পাড়ায় পাশের বাড়িতে উঠেছিল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার।
চোদ্দো-পনেরোর শ্যামলা কিশোরী বেণু জানলায় বসা গাঢ় নীল ব্লাউজে ফেটে পড়া রঙের চন্দ্রাবতী দেবীকে মুগ্ধ চোখে দেখতে দেখতে একদিন হঠাৎই নিজেরও অজান্তে দৌড়ে গিয়ে তাঁর বাড়ি ঢুকে পড়েছিল। — “কে রে কে রে!”— করে চন্দ্রাবতীদেবী তাকে ধরেছিলেন। কী করবে? কী বলবে?
নার্ভাস হয়ে ঝকঝকে দাঁতে কেবল অপ্রতিভ হেসেছিল বেণু। তখন কাছে এগিয়ে এসে হাত ধরে যাচাই করা চোখে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে চন্দ্রাবতী দেবী বলেছিলেন, “আবার হাসো তো!” ... আবার নিরুপায় একমুখ হাসি। এর পর চন্দ্রাবতী দেবী পরিচালক নীরেন লাহিড়ীকে ফোনে জানিয়েছিলেন, “তুমি যেমন চেয়েছ, সেরকম ঝকঝকে সুন্দর দাঁতের, কাটাকাটা নাক-চোখ-মুখের ছিপছিপে লম্বা মেয়ে পেয়েছি।”
এর পরই বেণু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়াছবির দুনিয়ায় পা রাখা। সে ছবির নাম ‘নাগপাশ’। অসিতবরণ নায়ক, কিন্তু মুক্তি পেল না সেই ছবি।
যত সহজে ঘটনাপ্রবাহ বলা গেল, তত সহজে কিন্তু হয়নি! সিনেমায় নামতেও কম যুদ্ধ করতে হয়নি বনেদি, সম্ভ্রান্ত বাড়ির সঙ্গে!
চন্দ্রাবতী দেবী নিজে নীরেন লাহিড়ীকে সঙ্গে নিয়ে বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতে গিয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলায় হয়তো কিছুটা কাজ হয়েছিল।
বাধা দিয়েছিলেন বড় জামাইবাবু সাহিত্যিক বনফুল। চোদ্দো-পনেরো বছরের মেয়ে তখন কোমর বেঁধে তাঁর বাড়ি গিয়ে বলে এসেছিল, “আপনি আপনার বই সিনেমা হওয়ার জন্য দিতে পারেন, আর আমি সিনেমা করলেই যত দোষ?”
এর পর বেশ কিছু কাল এক থমকানো গুমরে থাকা সময়। বেণু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিন আর কাটতে চায় না। ছোট থেকে শুধু ছুটে ছুটে একবার এখানে, তো আরেকবার ওখানে তাড়া খেয়ে বেড়াতে বেড়াতে কোথাওই নিয়মমাফিক লেখাপড়ার জন্য স্থায়ী নোঙর ফেলা হয়নি সবথেকে ছোট মেয়েটির। কিন্তু পড়ত সে।
গল্পের বই পড়ার আগ্রাসী খিদে ছিল তার বরাবরই। বই পড়া, সংসারে মায়ের হাতে হাতে কাজ করা, এর মধ্যেই এল দ্বিতীয় ছবির ডাক— ‘বসু পরিবার’। এমপি প্রোডাকশনসের ব্যানারে। এখানেই ‘সুপ্রিয়া’-তে রূপান্তরিত হল বেণু বন্দ্যোপাধ্যায়। এও এক গল্প।
তখন ফার্ন রোডের বাড়ি থেকে এমপি প্রোডাকশন্সের বাস বেণু বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুলে স্টুডিয়ো যাওয়ার পথে আর্টিস্ট বা প্রোডাকশন হাউসের লোকজনদের ওঠাতে ওঠাতে পূর্ণ সিনেমার সামনে মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা উত্তমকুমারকে তুলে নিত।
এই ছবিতে উত্তমকুমার বেণু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় ভাই, ভাইবোন! একেই বোধ হয় বলে ভাগ্যের নির্মল কৌতুক, স্বচ্ছ হিউমার। যাক সে তো পরের কথা।
পাহাড়ি সান্যাল ছিলেন এই ছবিতে। তিনিও বাসযাত্রী। বরানগরে এম পি প্রোডাকশনস-এর স্টুডিয়োতে যাওয়ার লম্বা পথে হঠাৎই একদিন আজন্ম একটি মাত্র এলেবেলে নামের বেণু শুনল পাহাড়ি সান্যালের দরাজ গলার হাঁক— “সুপ্রিয়া! সুপ্রিয়া!”
কে সুপ্রিয়া? কাকে ডাকছেন উনি? হা হা হেসে বিখ্যাত প্রবীণ অভিনেতা বলেছিলেন, “তুই-ই তো সুপ্রিয়া! তোর নামই সুপ্রিয়া।”
সেই থেকে বেণু বারাবরের জন্য ‘সুপ্রিয়া’। শৈল্পিক খেয়ালে কী অপূর্ব রূপান্তর!
এর পর থেকে নায়িকার রোল। এখন স্মৃতি প্রায়ই বিশ্বাসঘাতকতা করে। নায়িকা হিসেবে প্রথম সিনেমার নাম জিজ্ঞেস করায় একটু ভেবে বলল, “বোধ হয় ‘শুন বরনারী’।”
আর নায়ক? এ বার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড পজেজিভ উত্তরে “আর কে? তোর কাকু ছাড়া?”
আমার কাকু অর্থাৎ উত্তমকুমার। চলছে পর পর ছবি করা। বলতে গেলে সেই টাকাতেই বিয়ে হয়ে গেল ঠিক উপরের বোন ছোড়দির।
এ বার শুরু হল সব চেয়ে ছোট মেয়ের জন্য পাত্রের খোঁজ। যার নেট রেজাল্ট অসম্ভব অদ্ভুত! এবং একমাত্র আমার বেণু আন্টির পক্ষেই বোধ হয় এটা সম্ভব।
বেণু প্রায়ই শ্যুটিং শেষে বাড়ি ফিরে দেখত তার দুর্দান্ত সুপুরুষ বাবা সর্বক্ষণের সঙ্গী শ্বেতপাথরের মাথাওয়ালা শৌখিন লাঠি হাতে ঘেমেনেয়ে টকটকে লাল হয়ে বিমর্ষ মুখে মাকে বলছেন, “পাঁচ হাজার ছ’হাজার টাকা পণ হাঁকছে সব। কী যে করি, কোথায় পাই...!”
আগের মেয়ের বিয়েতে ঢেলে খরচ হয়ে গিয়েছে। অসাধারণ রূপবান, ব্যক্তিত্বময় বাবার এই অসহায়তা সহ্য হচ্ছিল না সব চেয়ে ছোট মেয়েটির। তখনই ঘটল সেই অভাবনীয় ঘটনা। যার অনুঘটক বেণু তথা সুপ্রিয়া নিজে।

পার্কসার্কাসে প্রায়ই যেত আরেক দিদির বাড়ি। সেখানে অফিস ক্লাবের থিয়েটারের মহড়া চলত। একদিন বাবাকে ফের ওই অবস্থায় দেখে ‘ধুত্তেরি’ বলে ট্রামে চেপে সোজা পার্কসার্কাসে দিদির বাড়ি। সাহেবের মতো ফর্সা, লম্বা অতি সুদর্শন এক যুবাপুরুষ বাইরের ঘরে বসা। সে’ও একদৃষ্টিতে দেখছিল ছিপছিপে শ্যামাঙ্গী সুদর্শনাকে। বেণু শুনতে পেল দিদিকে জিজ্ঞেস করছে, “মেয়েটি কে?”
তার বোন শুনে ফের রসিকতা করে বলেছিল, “‘আমার সঙ্গে বিয়ে দেবে?” নিছকই মজা। কিন্তু! দিদির কাছ থেকে ছেলেটির অফিস, কনট্যাক্ট নম্বর ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য জোগাড় করে চুপচাপ চলে এল বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির টাকার জন্য বিয়ে না-হওয়া ছোট মেয়ে।
কন্যাদায়গ্রস্ত অসহায় বাবার এগারো নম্বর কনিষ্ঠ কন্যাসন্তানটি আগুপিছু কিচ্ছু না ভেবে গড়িয়াহাটের ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়ের দোকান থেকে সোজা ফোন করল কনট্যাক্ট নম্বরে।
ও প্রান্তে ছেলেটির গলা পেতেই প্রথম বোমাটা ফাটাল, “আপনি আমাকে বিয়ে করবেন?” ওদিক থেকে হতভম্ব প্রশ্ন, “কে? আপনি কে!”
এদিক থেকে স্থির স্বরে, “আমি দীপ্তিদির বোন। পার্কসার্কাসে যার বাড়িতে আপনি আমাকে দেখে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। আমি রাজি। আপনি করবেন আমায় বিয়ে?”
ওদিক থেকে প্রচণ্ড থতমত গলায়, “আমি...আমি একটু ভেবে দেখি...তা ছাড়া আমার মা রয়েছেন। তাঁরও মত নিতে হবে।”
বেণু তথা সুপ্রিয়া বললেন, “ভাবুন। মায়ের মত নিন। আমি পরে আবার ফোন করব।”
ফোন রেখে বাড়ি। কাউকে একটি কথাও জানাল না। এই সুদর্শন ছেলেটিই বিশ্বনাথ চৌধুরী। বেণু বন্দ্যোপাধ্যায় বা সুপ্রিয়ার প্রথম স্বামী। সে নয়, আঠারো বছরের মেয়েই বিয়ে করে ছাড়ল তাকে, বাবাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিতে। একেবারে রেজিস্ট্রি করেই বাড়ি এসে ঢুকল।
তখন রাস্তায় সন্ধের আলো জ্বলে গেছে। সময় পেরিয়ে গেছে বাড়ি ফেরার। রাশভারী বাবা রেগে টকটকে লাল হয়ে হাতের লাঠি উঁচিয়ে, “কোথায় ছিলে এত ক্ষণ?”
ছোট মেয়ে অকম্পিত গলায়, “লাঠি নামান। আপনি আমায় মারতে পারেন না। আমি বিবাহিত মেয়ে। রেজিস্ট্রি করে এসেছি।”
ঘটনার আকস্মিকতায়, ধাক্কায় সবাই প্রথমে বজ্রাহত। পরে মেনে নেওয়া, হিন্দুমতে বিয়ে, সবই করা হল।
বিয়ের পর থার্ডক্লাস ট্রেনে চেপে, তারপর রিকশা করে শ্বশুরবাড়ি বদ্যিবাটিতেও হাসিমুখেই গিয়েছিল বড় বাড়ির ছোট মেয়ে সুপ্রিয়া চৌধুরী। কিন্তু এই অদ্ভুত বিয়ের কাহিনি বলতে বলতে আমার বেণু আন্টি বারবারই বলেছে, “জানিস, যখনই রেজিস্ট্রি অফিসে বসে সই করলাম সুপ্রিয়া ‘চৌধুরী’, সেই মুহূর্তে মন ডেকে উঠেছিল,— ভুল, ভুল, বিরাট বড় ভুল করলাম। এর খেসারতও দিতে হবে আমাকেই।”
হয়েছিলও তাই। আমার বেণু আন্টি অর্থাৎ সুপ্রিয়া দেবীর বরাবরই সুন্দর পুরুষ-ভাগ্য। কী বাবা, কী প্রথম স্বামী, কী প্রেমিক বা দ্বিতীয় স্বামী। কিন্তু সেইসঙ্গে আজীবন যুদ্ধ করার খেসারত।
প্রথম বিয়েতে সুপ্রিয়া চৌধুরী তার স্বামীর কাছ থেকে একটিই ইতিবাচক জিনিস পেয়েছিল— সন্তান— ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে, সোমা। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও টেকেনি এ বিয়ে।
অথচ অতি সাধারণ শ্বশুরবাড়ি, শাশুড়ি, দেওরের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হয়নি কোনও দিন। আজও বেণু আন্টি নির্দ্বিধায় প্রথম শাশুড়ি সম্পর্কে বলে, “মা।” বলে, “মা আমায় খুব ভালবাসত।”
দেওর সম্বন্ধেও একই সস্নেহ ভালবাসা মাখা কথা। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে বিবাহিত জীবন নিয়ে মানসিক এবং দৈহিক নির্যাতনে জর্জরিত।
তখন যথেষ্ট নাম, যথেষ্ট রোজগার, একমাত্র মেয়েকে নামকরা বোর্ডিং স্কুলে রেখে পড়ানো। কিন্তু এতটুকু স্বস্তি নেই, শান্তি নেই নিজের ঘরে। যার ফলে মাঝেমাঝেই হিন্দুস্তান পার্কের বাড়ি থেকে ‘স্পেনসর্স’ হোটেলে পালিয়ে গিয়ে একা থাকা।
সেই দিনে সেই সময়ে এটা কম কথা নয়। কম সাহসের কাজ নয়। উত্তমকুমারের সঙ্গে তখন সম্পর্ক শুধুই সহকর্মীর, সহজ বন্ধুত্বের। যাক, প্রথম বিয়ে তো ভাঙল।
বিশ্বনাথ চৌধুরী চলে গেলেন দিল্লি। ফের বিয়েও করলেন ডিভোর্স না করেই এবং করলেনও প্রথম স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেই, “আমি কি বিয়ে করতে পারি?”
সুপ্রিয়া, তখনও চৌধুরী, সেই মুহূর্তে তার বুকের মধ্যে কিছু— কোনও কিছু হয়েছিল কি হয়নি, কেউ জানে না।
স্বামীকে এক কথায় ছাড় দিয়েছিল। বলেছিল “নিশ্চয়ই।” পরে ফর্মাল ডিভোর্স। ময়রা স্ট্রিট-এ বিশাল ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে, সব দিক থেকে নিজের সামর্থ্যে নিজের সঙ্গে একা থাকা শুরু হল সুপ্রিয়া ‘দেবী’র।
আবারও বলছি, তখনকার সেই দিনে, ষাটের দশকের গোড়ায়, পূর্ণ যুবতী, দুরন্ত শরীরী আকর্ষণের কৃষ্ণাসুন্দরীর এইভাবে একা থাকা বিরাট সাহস আর প্রচণ্ড সংগ্রামী ক্ষমতা ছাড়া অসম্ভব।
এর পর জীবনের দ্বিতীয় ভাগ। যেখানে প্রবেশ উত্তমকুমারের।
আমার বাবা বারবারই বলত, “বেণু হচ্ছে সোফিয়া লোরেন অব দি ইস্ট। ও রকম ফিগার, হাইট, অ্যাপিল ইন্ডাস্ট্রিতে আর আছে? সেই সঙ্গে অভিনয়।”
এই অবধি বলে প্রায়ই চুপ করে যেত। কারণ, বাবা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত, সুপ্রিয়াদেবীর অসামান্য অভিনয় প্রতিভা বা ক্ষমতার ষোলো কলা পূর্ণ হয়নি, হতে পারেনি। তাতে যে ‘গ্রহণ’ লেগেছে, ‘ছায়া’ পড়েছে, তার নাম ‘উত্তমকুমার’!
হ্যাঁ, আপামর উত্তম-ভক্ত পাঠক শক্ড হবেন জেনেও বলছি এই কথা। নিজে উত্তমকুমারের অসামান্য আকর্ষণ আর অভিনয়ে চরম মুগ্ধ মোহাবিষ্ট হয়েও বলছি একই কথা। বেণু আন্টি নয়, অভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবী এমনই বিলীন হয়ে কাটিয়ে দিল সারাটা জীবন, নিজের পূর্ণ বিকাশের শ্রেষ্ঠ সময়টা ‘উত্তম-প্রেমে’, যে তার ‘আমি’ বলে আর কিছু রইল না। যে ‘আমি’র মধ্যে আরও অনেক অনেক সম্ভাবনা ছিল, বিস্ময়কর প্রতিভা ছিল, দুর্দান্ত ন্যাচারাল অ্যাক্টিং-এর ক্ষমতা ছিল। ক্লাসিক্যাল নৃত্যকলা ছিল, মুম্বই থেকে তখনকার টপ হিরোদের সঙ্গে কাস্ট হওয়ার ডাক ছিল। কিন্তু হল না।
সব কিছু থাকা সত্ত্বেও উত্তমকুমারের প্রখর দীপ্তির ‘রিফ্লেক্টেড গ্লোরি’তে আচ্ছন্ন, ‘চাঁদের আলো’ হয়ে থাকাই বেছে নিল অসামান্য ক্ষমতার অভিনেত্রী সুপ্রিয়াদেবী। যার জ্বলজ্বলে প্রমাণ ‘মেঘে ঢাকা তারা’।
বহু কাল আগে শক্তিপদ রাজগুরুর গল্প ‘চেনা মুখ’ পড়তে পড়তে পাশে ঘুমন্ত স্বামী বিশ্বনাথ চৌধুরীকে জাগিয়ে তুলে সুপ্রিয়া চৌধুরী অনুনয় করেছিলেন, “যদি কেউ কোনও দিন এই বইটা নিয়ে ছবি করে আর আমাকে ‘নীতা’ করতে দেয়, তাহলে তুমি টাকা-পয়সা নিয়ে একটা কথাও বোলো না”— অদ্ভুতভাবে পরদিনই বিকেলে তাদের হিন্দুস্তান রোডের বাড়ির সামনে অস্থির ভাবে পায়চারি করতে করতে তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ঋত্বিক ঘটক।
সুপ্রিয়া চৌধুরী তখনও শ্যুটিং থেকে বাড়ি ফেরেননি। তাঁকে দেখামাত্র বাঙাল ভাষায় বিচিত্র সম্বোধনে ঋত্বিক ঘটক বলে উঠেছিলেন, “অ্যাই ছেমড়ি, একটা ছবি করতাসি ‘চেনা মুখ’ গল্প নিয়া। তর লিগা একটা পার্ট আসে— ‘নীতা’। সব কাম প্যাক-আপ কইরা দশ দিনের লিগা শিলং চল...” নিজের চোখকানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না সুপ্রিয়া। পরেরটা তো ইতিহাস। সবাই জানে। এখনও, এই আশি বছর পার করেও, সুপ্রিয়াদেবী মানেই ‘মেঘে ঢাকা তারা’।
সুপ্রিয়াদেবীর অভিনয় মানেই “দাদা আমি বাঁচতে চাই...” সন্দেহ নেই, শ্রেষ্ঠ অভিনয়। সমস্ত সত্তা নিংড়ানো সেই হাহাকারে গায়ে কাঁটা দেয় আজও। কথা নয়, ডায়লগ নয়, ওই হাহাকারই সুপ্রিয়াদেবী।
মেকআপহীন ওই চেহারা, গোটা ছবি জুড়ে মারাত্মক সব টুকরো টুকরো শট, অদ্ভুত নীরব অথচ প্রচণ্ড বাঙ্ময় অসাধারণ অভিব্যক্তিগুলোই সুপ্রিয়াদেবী। কিন্তু তার পরেও নিজের জীবনে সত্যিই ‘মেঘে ঢাকা তারা’ হয়েই কেন রয়ে গেল সে? কেন মেঘের ঘেরাটোপ ভেঙে নিজের প্রখর রৌদ্রতেজে দীপ্যমান হল না? কোথাও তো কোনও খামতি ছিল না।
মনে পড়ে ‘সন্ন্যাসী রাজা’-তে বৈধব্যবেশে তার অসামান্য দৃষ্টিপাত। সন্ন্যাসীর বেশে উত্তমকুমারকে অপরিসীম প্রেমে দেখতে দেখতে কী কোমল উষ্ণতায় বলে ওঠা, “এই সন্ন্যাসী আমার স্বামী।”
পরক্ষণেই অভিনয়ের একেবারে বিপরীত মেরুর তুঙ্গে ঝলসে উঠে ক্ষিপ্ত বাঘিনির গর্জন, “ওই ওই ডাক্তার! ও আমার স্বামীকে মেরেছে। আমাকে দিনের পর দিন...” কিংবা ‘লাল পাথর’-এ গাঁয়ের অশিক্ষিত বিধবা-বৌ থেকে রবিঠাকুরের ‘চোখের বালি’ পড়া রাজেন্দ্রাণীতে উত্তরণ!
জমিদারের রোলে উত্তমকুমারের সপাট চাবুক মুখে আছড়ে পড়ার পর পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া সেই গনগনে ভীষণ, নিঃশব্দ অঙ্গার চাউনি! অথবা ‘কাল তুমি আলেয়া’-র সেই বিখ্যাত রেপ সিন।
যেখানে দৃশ্য জুড়ে উত্তমকুমারের ব্যাক আর তার শার্ট মুঠো করে ধরা সুপ্রিয়াদেবীর হাত। এক হাতের শটে প্রথমে প্রবল বাধা দেওয়া থেকে আস্তে আস্তে টোটাল সারেন্ডার। শুধুমাত্র হাতের মুঠির অব্যর্থ সঞ্চালনে। প্রথমে শুধু “না, না, না,” ক্রমশ সেটাই অদ্ভুত শীৎকার। ভাবা যায় অভিনয়ের এই রেঞ্জ?
এর পরেও, এত কিছু সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আমার বেণু আন্টি তথা সুপ্রিয়া দেবী আক্ষরিক ভাবেই মেঘে ঢাকা তারা হয়ে থেকে গেল তার গোটা জীবনটায়। স্বেচ্ছায়, আত্মপীড়নে, নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে, নিজের সঙ্গে নিজে যুঝতে যুঝতে।
মানিয়ে নেওয়া আর মেনে নেওয়ার অবিরাম লড়াই। নিঃশর্ত সমর্পণের নিরন্তর সংগ্রাম। আইনি স্বীকৃতি না পেয়েও উত্তমকুমারের সামাজিক স্ত্রী হওয়ার প্রতিটি কর্তব্য নিখুঁতভাবে পালনের যুদ্ধ।
সব চেয়ে আশ্চর্যের যা, সেটা হল আঠেরো বছর ধরে সব চাহিদা পূরণ করে নিজেকে বিসর্জন দিয়ে ঘর করার পর ১৯৮০ সালের ২৪ জুলাই উত্তমকুমারের মরদেহ নিয়ে খেয়োখেয়ি না করে নিঃশব্দে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার নিদারুণ যুদ্ধ।
ময়রা স্ট্রিট নয়, উত্তমকুমারের ভবানীপুরের বাড়ি নয়, স্টুডিয়োতে গিয়ে উত্তমকুমারকে শেষ দেখা দেখার অকল্পনীয় যুদ্ধ। ভাবা যায় কী করে এটা করতে পারল বেণু আন্টি!
সব শেষে বলি, জীবনের সঙ্গে লড়াই কিন্তু থামেনি আমার বেণু আন্টি বা সুপ্রিয়াদেবীর। কখনও বাড়িঘর, কখনও সাংসারিক ঝঞ্ঝাট, কখনও অশক্ত শরীর, কখনও মস্তিষ্কের ধোঁয়াশা। তবু চলছে দাঁতে দাঁত চিপে তার বাঁচার লড়াই। আমি বাঁচতে চাই। এ চাওয়া ‘নীতা’র চাওয়া নয়। এতে কোনও হাহাকার নেই। কোনও অসহায়তা নেই।
আছে শুধু জেদ। যোদ্ধার জেদ। তাই আশি বছর পার করা ‘মেঘে ঢাকা তারা’ আজ পুরোপুরি মুক্ত। স্বকীয় দীপ্তিতে জ্বলজ্বলে দ্যুতিময়।