আমি কোনও মানুষকে প্রথম মারা যেতে দেখি সিনেমার পর্দায়।
তাঁদের বেশির ভাগই বৃদ্ধ বাবা-ঠাকুর্দা, দু’একজন অবশ্য নায়ক।
দেখতে দেখতে মনে হত মরে যাওয়ার পদ্ধতি একটাই। অসুস্থ মানুষটি শ্বাসরুদ্ধ হবেন, মাথা তুলতে চেষ্টা করবেন, মুখ হাঁ করে বাতাস নিতে চাইবেন আর তারপরে বালিশে মাথাটা পড়ে মুখ একপাশে স্থির হবে।
আর যারা দেখবেন, তারা ‘বাবা গো’, ‘দাদাগো’, ‘ওগো’ ইত্যাদি শব্দ চিৎকার করে মৃতের শরীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন।
অতএব ধরে নিয়েছিলাম, মানুষ মরবার মুহূর্তে খুব কষ্ট পায়, ভয়টয় পায় না। কারণ ভয় পেতে গেলে যে মানসিক অবস্থার দরকার তা তখন থাকে না। কিন্তু যিনি চলে গেলেন তিনি কতখানি ভয় পেয়ে গেলেন তা বোঝার আগে আমি ভয় পেতে শুরু করলাম।
কোনও মৃতদেহ বহন করে শ্মশানযাত্রীরা যাচ্ছেন দেখে লোকে কপালে আঙুল ছোঁয়াত, না বুঝে আমিও ছোঁয়াতে লাগলাম।
ওটা কিন্তু মানুষকে যতটা না শ্রদ্ধা জানাতে, তার চেয়ে বেশি করা, এই চিন্তা থেকে যে, আমার যেন এই অবস্থা না হয়। এসব বাল্যকাল-কৈশোরের ভাবনা যখন মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করার কোনও দরকার পড়ে না।
আমার পরিচিত কাউকে মারা যেতে না দেখে কলেজে পড়তে কলকাতায় এলাম।
হাতিবাগানের এক সিনেমা হলে পাহাড়ি সান্যাল মশাইকে সেই আগের মতো মারা যেতে দেখে হস্টেলে ফিরছি, হঠাৎ কানে এল এক প্রৌঢ়া কেঁদে বলছেন, “আমি যাব না, হাসপাতালে যাব না, হাসপাতালে গেলে আমি ঠিক মরে যাব, আমার খুব ভয় করছে।”
ওঁর কথায় কান না দিয়ে আত্মীয়রা ওঁকে ট্যাক্সিতে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গেল। কৌতূহলী হয়ে তখনও দরজায় দাঁড়ানো এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, “ওঁর কী হয়েছে?”
ভদ্রলোক বলেছিলেন, “ন্যাবা। বাড়িতে কিছুতেই সারছে না।”
সেদিন জেনেছিলাম, ন্যাবা হল জন্ডিস। সে সময় জন্ডিস হলে খাওয়াদাওয়ার কড়াকড়ি করলে সেরে যেত। কেউ মরার কথা ভাবত না।
ওই প্রৌঢ়াও ভাবেননি। কিন্তু তিনি হাসপাতালে গেলে মরার কথা ভেবেছেন।
হাসপাতাল ভীতি অনেকেরই ছিল। এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ছিল দেবকুমারদা। পঁচিশ বছরেই নাকি মরা পোড়ানোয় সেঞ্চুরি করেছেন। বলেছেন, “আমি স্ট্যাটিসটিক দিচ্ছি, যা বোঝার বুঝে নে। আমি মেডিক্যাল কলেজ থেকে বাইশটা, নীলরতন থেকে পনেরোটা, পিজি থেকে বারোটা, মাড়োয়ারি হাসপাতাল থেকে তিনটি, বিআরসিং থেকে দশটা ডেডবডি নিয়ে শ্মশানে গিয়েছি। দশ বছরে একশটা।”
গোনাগুনি করে একজন জিজ্ঞাসা করল, “বাকি আটত্রিশটা?”
দেবকুমারদা বলল, “একটাই তো বাকি আছে। আর জি কর।”
হ্যাঁ, তখন আর জি করের খুব সুনাম ছিল না। এখনকার মতো চিকিৎসা তখন হয়তো হত না। যন্ত্রপাতিরও হয়তো অভাব ছিল। এখন যেমন স্বচ্ছন্দে চিকিৎসার জন্য লোক ওই হাসপাতালে যায়, তখন যেতে ভয় পেত। ওই প্রৌঢ়াও পেয়েছিলেন।

পৃথিবীতে মানুষের থাকার সময় নির্দিষ্ট নয়। হাতে গোনা কয়েক জন একশ বছর দিব্যি কাটিয়ে দেন। বেশির ভাগই চলে যান ষাট থেকে আশির মধ্যে। লক্ষ করেছি, আশি পার করে দেন যাঁরা, তাঁদের সংখ্যা বেশি নয় এবং নব্বই পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারেন।
কিন্তু ষাট পার করে যাঁরা বিভিন্ন অসুস্থতায় আক্রান্ত হন, তাঁরাই হাসপাতালে না গিয়েও মৃত্যুভয় পেতে শুরু করেন।
এই পৃথিবীতে আমি এত কাল আছি, মেট্রো সিনেমার পাশের গলিতে গিয়ে তড়কা খেয়েছি কত, মরে গেলে তা খেতে পারব না। অথচ হাজার হাজার লোক খেয়ে যাবে। এই রাস্তায় কত হেঁটেছি, আর হাঁটতে পারব না। কেন আমি আরও অনেক বছর না হোক, বছর দশেক বাঁচব না? এই প্রশ্ন থেকেই কি ভয়ের জন্ম?
রক্ত পরীক্ষা করে যে রিপোর্ট এল তাতে জানা গেল সুগার বেশ বেশি। ডাক্তার বললেন, “চিনি আলু একেবারে বন্ধ, রোজ সকালে দুই কিলোমিটার হাঁটুন।”
যাঁর সকাল হত সাড়ে আটটায়, তিনি ভোর পাঁচটায় কেড্স পরে দেশবন্ধু পার্কে ছুটছেন জীবন বাড়াবার আশায়! সেটা অবশ্যই মৃত্যুভয়ে।
তাঁকে যদি বলা হয়, “ভোর বেলা হাঁটছেন? এখন তো গাছ কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়ছে, ফুসফুসের বারোটা বেজে যাবে। হাঁটতে হলে বিকেলে হাঁটুন।’ সঙ্গে সঙ্গে সময়টা পাল্টে ফেলে বিকেলে হাঁটা শুরু করবেন। বাঁচতে হবে, যে করেই হোক।
ছোট হয়ে আসছে জীবন। কেউ কেউ টের পান, অনেকেই পান না। যাঁরা পান না, তাঁরা ভাল থাকেন। সাতাত্তর বছর বয়সে ফোন করে জিজ্ঞাসা করেন, “সমরেশ, সামনের বছর কেদার বদ্রী যাব, তুমি কি যেতে চাও?” অনেকে আরও বেশি সময়ের কথা ভাবেন।
যাঁরা টের পান, তাঁদের বেশির ভাগই অসুখী। শরীরের চামড়ায় ভাঁজ পড়ছে। সাদা চুলে রং বুলিয়েও ম্যানেজ করা যাচ্ছে না। হাঁটুতে ব্যথা, যা পূর্ণিমা-অমাবস্যায় মারাত্মক, সুগার বেড়েছে, হাঁটলে মাথা ঘোরে। এসবই মনে করিয়ে দেয় সময় বেশি নেই।
আর এই কথাটা একবার মাথায় ঢুকলে মানুষ কি খেঁকুড়ে হয়ে যায়? সবাই ভাল ভাবে বেঁচে থাকবে আর আমাকে চলে যেতে হবে, এটা ভাবলেই কি মন ক্ষিপ্ত হয়?
মনে ভয় জাগে। মৃত্যুভয়।
একটা কালো ছায়া ছুটে এসে আমাকে তুলে নিয়ে মহা অনন্তে মিশে যাবে। কোথাও আমার চিহ্ন থাকবে না। আশ্চর্য! রবীন্দ্রনাথ কী করে লিখলেন “মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে!” ওই ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি যদি নিপুণ শিল্পের মর্যাদা পায় তাহলে আমরা, সাধারণ মানুষরা তার প্রশংসা করতে পারি না কেন? আদৌ কি শিল্প বলে ভাবতে পারি? কিন্তু কথাগুলো রবীন্দ্রনাথের, যিনি সারা জীবন একের পরে এক মৃত্যু দর্শন করেছেন।
কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচেতনা নিয়ে ভাবতে গেলেই গোলমালে পড়তে হয়। এই শ্যামসমান বলে উল্লসিত হচ্ছেন, আবার মরতে চান না বলে ঘোষণা করছেন। দ্বিতীয়টা সাধারণ মানুষের মনের কথা। প্রথমটাকে কেউ মানতে পারছে না।
কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, ‘হে ছলনাময়ী, তুমি তোমার আপন হাতে দৃষ্টির পথ বিচিত্র ছলনা দিয়ে কণ্টকাকীর্ণ করে রেখেছ—’ তখন স্তম্ভিত হতে হয়।
এই ছলনাময়ী কে? সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেব লিখেছেন, তিনি পরমব্রহ্ম হতে পারেন না, কারণ তাঁর লিঙ্গ নেই। কিন্তু এ স্থলে শব্দটি পরিষ্কার স্ত্রী লিঙ্গে আছে।
মৃত্যু যদি ছলনাময়ী হয় তাহলে তিনি নিশ্চয়ই তাকে ভয় পাননি। মৃত্যু এসেছে ধীরে ধীরে। তৃষ্ণার জলপাত্র নিয়েছে সে, ছলনায় হেসে হেসে বিশ্বাস ভেঙেছে, হঠাৎ তীরের কাছে এসে তরী ডুবিয়েছে। তাহলে মৃত্যু কি রবীন্দ্রনাথের কাছে কোনও এক নারীর মতো ছিল? এইখানেই তাঁর বোধের সঙ্গে আমাদের ফারাক।
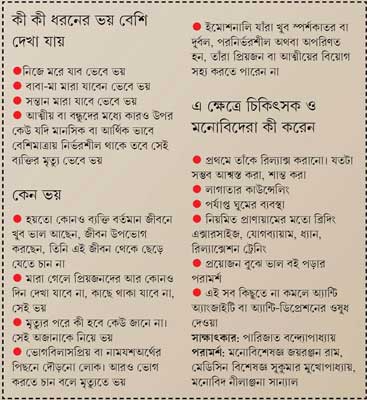
কনিষ্ঠ পুত্র শচীন্দ্রনাথ মুঙ্গেরে বন্ধু ভোলার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে কলেরায় আক্রান্ত হন। খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ সেখানে পৌঁছান। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় উন্নতি না হওয়াতে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় হোমিওপ্যাথি শুরু হয়।
যেদিন অসুখ বৃদ্ধি পায় সেই রাতে শমীন্দ্রনাথের পাশে রাত জেগেছিলেন ভূমেন্দ্রনাথ। তাঁর কথা অনুযায়ী, ‘রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরেই জাগিয়া বসিয়া রহিলেন। রাত্রি প্রভাত না হইতেই সব শেষ হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরেই আছেন। এ ঘটনা তাঁহাকে শুনাইতে যাইবার সাহস হইল না। তখন তিনি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অবস্থিত। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, এই সময়ের যাহা কিছু কৃত্য আমি করিয়া দিলাম। এখন অবশেষে যাহা কর্তব্য আপনি করুন। ব্রাহ্মণের মতোই শমীর শেষকৃত্য যেন হয়, আর আমার কিছু বলিবার নাই। পরে, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে মীরা দেবীকে সান্ত্বনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লিখেছিলেন (৭ অগস্ট, ১৯৩২) সেখানে শমীর মৃত্যুর কথা ছিল। — ‘যে রাত্রে শমী গিয়েছিল সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক, আমার শোক যেন তাকে একটুও পেছনে না টানে। শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে কম পড়েনি— সমস্তর মধ্যে সব রয়ে গেছে, আমিও তারই মধ্যে।’
এই অবধি হয়তো মেনে নেওয়া যায়। কয়েকশ সাধারণ মানুষের মধ্যে একজনকে পাওয়া যাবে যিনি নিজেকে সামলে রাখবেন। কিন্তু তারপর?
অমিতাভ চৌধুরী জানাচ্ছেন, শ্মশান থেকে স্টেশন এসে যখন রবীন্দ্রনাথ কলকাতার ট্রেন ধরছেন তখন পৃথিবী জ্যোৎস্নায় ভাসছে। পুত্রশোকে দীর্ণ রবীন্দ্রনাথ ট্রেনের জানলা দিয়ে সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবতে পারলেন, আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে। এই গান যখন কেউ হাসিমুখে দুলে দুলে গেয়ে খুশি হন তখন বিস্ময়ে ভাবি, এরা কারা?
রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে ভয় পাননি। মৃত্যুকে অতিক্রম করেছেন। এমনকী তাঁর মৃত্যুর কিছু দিন আগে যখন বোঝা গিয়েছিল অস্ত্রোপচার ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা নেই, তখন কবি জিজ্ঞাসা করেছেন, “আমাকে বুঝিয়ে বলো তো ব্যাপারটা কী রকম? আমার কত দূর লাগবে? আগে থেকেই আমি সব বুঝে রাখতে চাই।” এই মনের জোর মৃত্যুভয়ে ভীত মানুষের থাকে না।
এই আমি সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত কোনও শ্মশান বা নার্সিংহোমে রাত্রিবাস করিনি। রুটিন পরীক্ষায় জেনেছি হার্ট খুব ভাল, রক্তে চিনি পরিমিত। ক্লোরেস্টেরলের বাড়াবাড়ি নেই। সকাল থেকে লিখে দুপুরে বেরিয়ে রাতে বাড়ি ফিরি গত তিরিশ বছর ধরে।
পঞ্চাশ বছর ধরে সিগারেট খাচ্ছি যা এখন আমাকে সবার সমালোচনার মুখে ফেলে দিয়েছে। ক’দিন সেই সিগারেট বিশ্বাসঘাতকতা করল। কাশি-সর্দি ছাড়াও শ্বাসে টান ধরতেই ডাক্তারের শরণাপন্ন হলাম। তিনি পরীক্ষা করে নার্সিংহোমের আই সি ইউতে চালান করে দিলেন।
প্রথম রাতে আমি সজ্ঞানে ছিলাম। একটা হলঘরে জনা আটেক মানুষ খাটে শুয়ে আছে। তাঁদের তিন জন যন্ত্রণায় কাতরে যাচ্ছে সমানে। আমি শুনছি। আমার নার্ভে লাগছে। এত কষ্ট পাচ্ছেন ওঁরা, এটা কি মৃত্যুযন্ত্রণা? নার্সদের বললাম, ওদের ব্যথা কমাবার ওষুধ দিন। ওঁরা বললেন, দেওয়া হয়েছে।
তাহলে ব্যথা কমছে না কেন? আমার নাকে মুখে নল। কিন্তু পাশের বিছানার মানুষটি মাঝরাত থেকে সমানে ‘সিস্টার’ ‘সিস্টার’ ডেকে যাচ্ছেন। মুখের নল খুলতেই সিস্টারকে জিজ্ঞাসা করলাম, “ওঁর ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না কেন? কত কষ্ট করে ডাকছেন?”
সিস্টার বললেন, “উনি মোবাইল ফোন চাইছেন। এখানে এটা নিষিদ্ধ। তাছাড়া যাঁকে ফোন করতে চাইছেন তাঁকে উনি পাবেন না।” ভোরবেলায় মোবাইল ফোন চাওয়া মানুষটিকে সরিয়ে নেওয়া হল। নার্স বললেন, “আর মোবাইলের দরকার হবে না। এখন সামনাসামনি কথা বলছেন।”
“কার সঙ্গে?” আমি অবাক।
“ভগবান।” নার্স নিস্পৃহ।
মৃত্যুর আগে কি ভদ্রলোক ফোন করে ভগবানকে কিছু জানাতে চাইছিলেন? দ্বিতীয় দিনে আমার চেতনা ঝাপসা হল। মনে হচ্ছিল আমি তলিয়ে যাচ্ছি গভীর জলে। দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একটু বাতাসের জন্য। একেই কি মৃত্যুযন্ত্রণা বলে?
হঠাৎ ওই অবস্থায় কী রকম মজা লাগা শুরু হল। হতেই আমাকে রসাতল থেকে তুলে মহাশূন্যে নিয়ে যাওয়া হল। একটা সাদা বাড়ি। কোনও দরজা জানলা নেই। শূন্যে ভাসছে। বলা হল, সঙ্গে যা আছে দিয়ে দাও। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে শূন্যে ভাসালাম। তারপর সেই বাড়িতে ঢুকতে না পেরে ফিরে এলাম। ফিরতেই নার্সের গলা শুনলাম, “সেন্স আসছে, সেন্স আসছে।”
চোখ মেললাম যখন তখন পাশের তিনটি বেডের মানুষ বদলে গেছে। হয়তো বাড়ি ফিরে গেছেন। হয়তো—! কিন্তু নার্সিংহোমে আমি মৃত্যুভয় পাইনি। ফিরে এসে, বেঁচে কী করে থাকব তার জন্যে, এত উপদেশ শুনছি যে তিলতিল করে একটা শিরশিরানি জন্ম নিচ্ছে।
অবিলম্বে এর বিনাশ দরকার।









