অমিয় দেবের অনুবাদে বিমলকৃষ্ণ মতিলালের ‘ধর্ম ও যৌক্তিকতা’ প্রবন্ধটিতে আছে: “ধর্ম এক যৌক্তিক অন্বেষণ, অন্ধ বিশ্বাসের বিষয় নয়।” বিবিধ বিষয়ের প্রবন্ধে ঋদ্ধ সংখ্যাটি, জলসাঘর ছবির সূত্রে সত্যজিৎ ও সামন্ততন্ত্র বিষয়ে এক পুরনো বিতর্কের পুনর্বিচার সৌমিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের; সলিল চৌধুরীর শিল্পীমনের দ্বান্দ্বিকতা অবলম্বনে গানের ভুবন কী ভাবে এগিয়ে চলে ইতিহাসের কথকতায়, লিখেছেন প্রিয়দর্শী চক্রবর্তী। হিগস বোসন কণার আবিষ্কার নিয়ে মানস মাইতির আলোচনা, দ্রাবিড় জাতির অগস্ত্যায়নের রূপরেখা, জিন্না ও সুরাবর্দির নব মূল্যায়ন, মননশীল নানা রচনা। ক্রোড়পত্রে ঔপনিবেশিক বাংলায় শিক্ষা-সংস্কৃতিচর্চার খোঁজ।
অনুষ্টুপ, গ্রীষ্ম ২০২৩ সম্পা: অনিল আচার্য ৫০০.০০


‘বন্দে মাতরম্’ সঙ্গীতটি নির্দিষ্ট করে কবে ও কোথায় রচনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়? লেখকের সঙ্গে কেমন ছিল ইংরেজ শাসকের সম্পর্ক? ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে কী মনোভাব ছিল পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নের— এমন নানা বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে সংখ্যাটি। এ সবই রয়েছে ‘একালের নিরীক্ষা’ শীর্ষক অংশে। সে সঙ্গে দু’টি বই সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে ‘গ্রন্থ-সমালোচনা’ অংশে।
বঙ্গদর্শন ২১ সম্পা: রতনকুমার নন্দী ৩৫০.০০
শিশিরকুমার দাশ লিখেছিলেন, “ইতিহাস শুধু সঙ্গ ছাড়ে না।” দু’টি প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা, অধ্যাপনা, গ্রিক ভাষায় দক্ষতা— এ সবে শিশিরকুমারের সামগ্রিক পরিচয় মেলে না। কারণ, অজস্র গবেষণাগ্রন্থের সঙ্গেই রয়েছে তাঁর মৌলিক সাহিত্যসম্ভার। তাঁর স্মৃতিচারণের পাশাপাশি প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা, অনুবাদ সাহিত্য, ছোটগল্প, সাহিত্যতত্ত্ব, শিশুসাহিত্য, ইংরেজিতে লেখালিখি, ভাষাবিজ্ঞান-সহ নানা বিচিত্র ক্ষেত্রে বিচরণের বিষয়গুলি দেখতে চায় সংখ্যাটি। রয়েছে ডায়েরি, পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র, বইয়ের প্রচ্ছদের ঝলক।
গহন, শিশিরকুমার দাশ সংখ্যা সম্পা: মোস্তাক আহমেদ ৭৫০.০০
একাধারে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হিসাবে বিশিষ্ট মানুষটির শতবর্ষ উপলক্ষে সংখ্যাটি সংগ্রহযোগ্য। শিবনারায়ণ রায়ের গৌরকিশোর-মূল্যায়ন, আবদুর রউফের গৌরকিশোরের বাঙালি মুসলমানচর্চা, অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক ভারতে তাঁর প্রাসঙ্গিকতার উপর প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য। ‘ব্রজদা’, ‘রূপদর্শী’ রচনাগুলি নিয়েও কয়েকটি উপভোগ্য প্রবন্ধ রয়েছে। আর আছে গৌরকিশোরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রের পুনর্মুদ্রণ। “আপনার শুভবুদ্ধি জাগ্রত হোক”— তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে লেখা খোলা চিঠির শেষ বাক্যই বলে দেয়, গৌরকিশোরের মতো মানুষ আজ কত বিরল। তবে পুনর্মুদ্রিত লেখার সঙ্গে তারিখ/সময় উল্লেখ না থাকাটা সুসম্পাদনার নিদর্শন নয়।
তবু একলব্য, বিভাস চক্রবর্তী বিশেষ সংখ্যা (প্রথম খণ্ড) সম্পা: দেবারতি মল্লিক, দীপঙ্কর মল্লিক ১৭৫.০০
এই সময়ের বাংলা থিয়েটারের অন্যতম অগ্রগণ্য অভিভাবক, তাঁকে নিয়ে অনুরাগীজনের লেখায় মুগ্ধতা ধরা পড়বে বেশি, স্বাভাবিক। তবে তারই মধ্যে ফুটে উঠেছে নাট্যকার, অভিনেতা, নির্দেশক, টিভি-প্রযোজক এবং অন্য আরও পরিচয়ে ভাস্বর বিভাস চক্রবর্তীর দীর্ঘ চিন্তনজীবনের দ্রষ্টব্য মাইলফলক। ১৮টি ছোট-বড় লেখার অধিকাংশই হৃদ্য আবেগময়, শিল্পীর জীবনের বহু তথ্যের সন্নিবেশও প্রাপ্তি। দু’-তিনটি লেখায় ফুটে উঠেছে তাঁর কিছু নাট্যকৃতির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ। আগামী খণ্ডগুলিতে তাঁর কাজ ও ভাবনার সম-আলোচনা থাকবে, আশা করা যায়।
তবু একলব্য, বিভাস চক্রবর্তী বিশেষ সংখ্যা (প্রথম খণ্ড) সম্পা: দেবারতি মল্লিক, দীপঙ্কর মল্লিক ১৭৫.০০
পিতামহ যখন তারাশঙ্কর, তখন সে স্মৃতিকথাও হবে ওই নামের মতোই অত্যুচ্চ তারে বাঁধা— মনে হতে পারে। কিন্তু পৌত্র সৌম্যশঙ্কর (পত্রিকার সম্পাদকও তিনি) তুলে ধরেন এক অন্য তারাশঙ্করকে: বিষণ্ণ আক্ষেপে যিনি বলেন, “বৃহৎ সংসারের ভার বহন করতে গিয়ে অনেক অপাঠ্য-কুপাঠ্য রচনা করে গেলাম।” তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য এ পত্রিকায় নানা লেখার মালা: রতন ভট্টাচার্য ও ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতি, ছোটগল্প, কবিতা, নাটক-শ্রুতিনাটকও। অক্ষয়চন্দ্র সরকার থেকে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, ধর্মমঙ্গলের কবি থেকে কালীঘাট পট, লোককথার মহাকাব্য, টুসু-ভাদুগান— প্রবন্ধগুলি বিচিত্রগামী।
জিজ্ঞাসা, শতবর্ষে গৌরকিশোর ঘোষ সংখ্যা সম্পা: সন্দীপ পাল ১৫০.০০
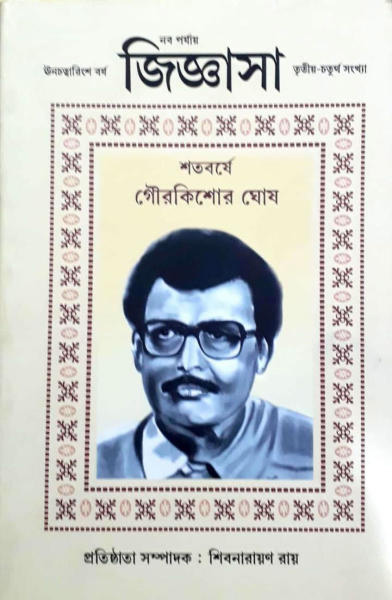

বৈদিক রুদ্রে চেনা শিব অনুপস্থিত, তিনি ব্যাপ্ত ও বিচিত্র পুরাণে। এ থেকেই তাঁর জনগ্রাহ্যতা, শাস্ত্র থেকে লোকজীবনে ছড়িয়ে পড়া। সম্পাদকীয়তে এই সূত্রে একটি শব্দবন্ধ লক্ষণীয়, ‘মহাদেব পরিক্রমা’। বেদ, পুরাণ থেকে লোকসংস্কৃতিতে শিবপ্রসঙ্গ নানা দিক থেকে আলোচিত নিবন্ধগুলিতে। রুদ্র, শিব, ভৈরব রূপে মহাদেবের বিশ্লেষণ যদি এই পরিক্রমার একটি দিক, অন্য ক্ষেত্রটি ছড়িয়ে বাংলার লোকায়তে: কিংবদন্তি, গাজন বোলান ঝুমুর গানে, ছড়ায় পুঁথিতে, পটচিত্র ও মন্দির-অলঙ্করণে। আছে পুরুলিয়া-বিষ্ণুপুর, রাঢ়ের শৈবক্ষেত্র, শিব-উপাসনা নিয়ে এষণাও।
কারুকথা এইসময় নভেম্বর’২২-এপ্রিল’২৩ সম্পা: সুদর্শন সেনশর্মা ৩০০.০০
লা ফঁতেন-এর নীতিগর্ভ কাব্যের প্রথম সঞ্চয়নগ্রন্থ প্রকাশ পায় ১৬৬৮-তে। এই নীতি-উপদেশমূলক কবিতাগুলি পড়ে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর কাব্যরচনায় কী ভাবে তা কাজে লাগিয়েছিলেন, তা নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী। এই দুর্লভ রচনাটির সঙ্গে আছে কবিতা বিষয়ক আরও দু’টি লেখা, পবিত্র সরকার ও সুতপা ভট্টাচার্যের। ১৯৪৫-৪৭’এর মধ্যে শান্তিনিকেতনে লেখা অসমিয়া কবি নবকান্ত বরুয়ার দু’টি কবিতার অনুবাদ রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের; রবীন্দ্রগানে অন্য সুরের প্রভাব ও প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানে প্রকৃতি ও গণিত নিয়ে আরও দু’টি প্রবন্ধ।
এবং জলঘড়ি, ক্রোড়পত্র: অন্তরঙ্গে মিহির সেনগুপ্ত সংখ্যা-সম্পাদক: অর্দ্ধেন্দুশেখর গোস্বামী স্বাগতা দাশ মুখোপাধ্যায় ২০০.০০
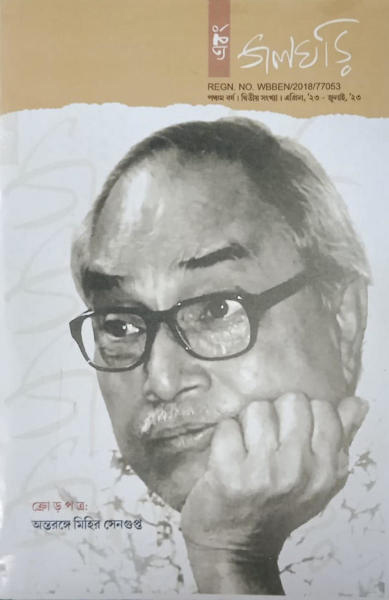

সুকান্ত চৌধুরীর প্রবন্ধ ‘বৈদ্যুতিন সংস্কৃতিচর্চার সন্ধানে’র পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ক্রোড়পত্র ‘অন্তরঙ্গে মিহির সেনগুপ্ত’। তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও শিবনারায়ণ রায়ের রচনা পুনর্মুদ্রিত ক্রোড়পত্রে। মিহিরবাবুর জীবনপঞ্জি, কালানুক্রমিক রচনাপঞ্জি, চিঠিপত্র, সর্বশেষ সভা-সম্ভাষণ, তাঁর পাণ্ডুলিপি থেকে প্রকাশিত রচনাদি— প্রতিটি রচনাই বিভিন্ন সময়পর্বের ইতিহাসের স্পর্শক। তাঁকে নিয়ে বিশ্বজিৎ রায় সুমনা রহমান চৌধুরী ও গোপা দত্ত ভৌমিকের আলোচনা। সহধর্মিণী সন্ধ্যা রায় সেনগুপ্তের ‘মিহির, তোমার সঙ্গে’ পূর্ববঙ্গে তাঁদের বিবাহ-পূর্ব আখ্যান, ১৯৫৯-৭১, যেখানে লীন হয়ে আছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও জন্মের কথা।
অতঃপর, ক্রোড়পত্র শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পা: সাইদুর রহমান ৪৫০.০০


সুশীলা বুড়ির আত্মকথা ‘যাযাবরী’-তে ফুটে ওঠে তুমুল স্রোতে ভেসে যাওয়া খড়কুটোর মতো মেয়েজীবন, কখনও ফুটপাত কখনও কুলি ক্যাম্প, কখনও বস্তির ঘরে ঠাঁই। মৌপিয়া মুখোপাধ্যায়ের কলমে ধরা পড়েন তাঁর মা, গান শেখাতে বাড়ির বাইরে বেরোনোর অধিকারটুকু বজায় রাখতে মেনে নিতেন যাবতীয় ঠিক-ভুল অভিযোগ। সুনীতা মেদ্যার ‘যতটুকু মনে পড়ে’ স্মৃতিকথায় চোখে পড়ে, ভরন্ত সংসারেও কী ভাবে চোরাগোপ্তা বঞ্চনা আর ক্ষোভ থেকেই যায়।
এবং মুশায়েরা, ইউলিসিস বিশেষ সংখ্যা সম্পা: কুন্তল চট্টোপাধ্যায় ৬০০.০০
“আকাশ পিতাকে এই পৃথিবীর ওপরে— মাথায়—/ জন্ম দিয়েছি আইমিই... আমার উৎস কোথায়?— সে তো সমুদ্রে”— ঋগ্বেদের দেবীসূক্তের অনুবাদ করেছেন মৌ দাশগুপ্ত। চন্দ্রা মুখোপাধ্যায় লিখেছেন গ্রামীণ মেয়েজীবনে গানের ব্যবহার নিয়ে। মোহনার কাছাকাছি অঞ্চলে নদীর পাড়ের মাটি থেকে কী ভাবে ধাপে ধাপে তৈরি হত লবণ, তার আকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন সুশীলকুমার বর্মণ। শুক্তি রায়ের পেরু ভ্রমণের অভিজ্ঞতা পড়তে ভাল লাগে।
কবিতীর্থ, জঁ-লুক গোদার সম্পা: অমলকুমার মণ্ডল ৪০০.০০
বোধশব্দ পত্রিকা ও প্রকাশনার উপহার নতুন একটি পত্রিকা, যেখানে চর্চা হবে হরফ ও টাইপোগ্রাফি নিয়ে! হরফচর্চা তাই সার্থকনামা। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকা, সূচিপত্রহীন, প্রথম পাতায় ছোট্ট ঘোষণা ও অবিলম্বে লেখা শুরু— কমিক বইয়ের বাংলা ফন্ট নিয়ে আবু জার মোঃ আককাস, সুকুমার রায়ের মুদ্রণচর্চা নিয়ে দীপঙ্কর সেন, কলকাতার হরফ ঢালাইখানা নিয়ে কলম ধরেছেন সম্পাদক নিজে। ব্রিটিশ টাইপোগ্রাফার রুয়ারি ম্যাকলিন-এর ট্রু টু টাইপ বইয়ের উত্তরভাষ অংশটি সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়ের বাংলা অনুবাদে, রাজীব চক্রবর্তী আলোচনা করেছেন নন-ল্যাটিন লিপি নিয়ে ফিয়োনা রস ও গ্রাহাম শ’-এর একটি বইয়ের।
এবং আমরা, প্রতিনায়ক সংখ্যা মুখ্য সম্পা: দেবলীনা রায়চৌধুরী বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০০.০০
স্রেফ কবিয়াল পরিচয়ে বিজয় সরকারকে ধরা যাবে না। কবিগানের প্রচলধারা ছাপিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন অভিনব, গানে এনেছেন পরিশীলন ও নান্দনিকতা, বহতা সময়কে তুলে ধরেছেন গানে। তবু তাঁকে নিয়ে বিদ্যায়তনিক পরিসরে চর্চা কম। সেই প্রয়াসই এ পত্রিকায়: দুই বাংলার গবেষক-লেখকদের সাক্ষাৎকার, প্রবন্ধ, মুক্তগদ্য কবিতার মধ্য দিয়ে। জ্যোতিভূষণ চাকী নিখিল সরকার মুনতাসীর মামুন শুভেন্দু মাইতি সাইমন জাকারিয়া শক্তিনাথ ঝা প্রমুখের ভাবনা মন ছোঁয়। মুদ্রিত হয়েছে বিজয় সরকারের গদ্য গান কবিগান, জীবনপঞ্জিও।
পড়শি, বিজয় সরকার সংখ্যা সম্পা: মৃদুল হক, সঞ্চিতা দত্ত ৫০০.০০
‘সাহিত্যিক শিবনাথ শাস্ত্রীকে বোঝা, তাঁর সাহিত্য ও সামাজিক কার্যাবলী ও সংস্কৃতিচর্চা’র নানা দিক তুলে ধরার সার্থক চেষ্টা মূল ক্রোড়পত্রটিতে। নানা নিবন্ধে ফুটে উঠেছে তাঁর জীবন; আত্মচরিত, উপন্যাস ও শিশুসাহিত্য, রামতনু লাহিড়ী ও শিবনাথ শাস্ত্রীর মূল্যায়ন, উনিশ শতকীয় প্রেক্ষাপটে তাঁর দ্বান্দ্বিক অবস্থান। আছে বেশ কিছু প্রবন্ধ: অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর অভয়ামঙ্গল কাব্য-মর্শিয়া সাহিত্য থেকে বিভূতিভূষণ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বেগম রোকেয়া তারাশঙ্কর জসীম উদ্দীন হয়ে দেবেশ রায় গোলাম মুরশিদের সাহিত্যকৃতির বীক্ষণ।
রাবণ, মে ২০২৩ সম্পা: সোমাইয়া আখতার ১৫০.০০


“প্রতিনায়ক নায়কের সমকক্ষ— শক্তিশালী, অনুভূতিপ্রবণ, প্রাণশক্তিতে ভরপুর... পরিস্থিতির স্বার্থে নায়কোচিত সাফল্য ও সম্মান পাননি।” এমন চরিত্রদের নিয়েই লেখালিখি এই পত্রিকা-সংখ্যায়। মহাভারতে কর্ণ ভীষ্ম দ্রৌপদী কুন্তী শিখণ্ডী শকুনি, রামায়ণে রাবণ মেঘনাদ কৈকেয়ী; পাশাপাশি ইন্দ্রের প্রতিনায়ক, ইন্দ্র ও জ়িউস প্রতিতুলনা, মহিষাসুর, হিরণ্যকশিপু, গ্রিক আখ্যানের হেরা ও মেদেয়া, সোফোক্লিসের নাটকের ক্রেয়ন, ইহুদি লোককথার লিলিথ— নির্বাচনগুলি সুভাবিত। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের পুরাণ, সংস্কৃত কাব্য ও নাট্যশাস্ত্রে প্রতিনায়কের তত্ত্ব ও রূপ ফুটে উঠেছে নিবন্ধে।
ভূমধ্যসাগর, বৈশাখ ১৪৩০ সম্পা: জয়া মিত্র ১৫০.০০
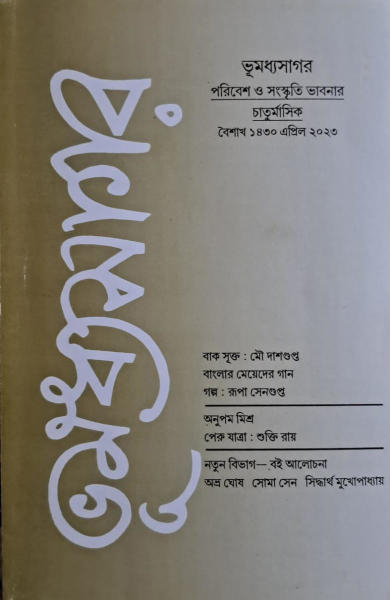

১৯২২ বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এক অলৌকিক বছর, ‘অ্যানাস মিরাবিলিস’— ইউলিসিস ও দি ওয়েস্ট ল্যান্ড প্রকাশের বছর। জেমস জয়েসের ছকভাঙা উপন্যাসের শতবর্ষ উদ্যাপন এ সংখ্যায়। জয়েস ও ডাবলিনের আন্তঃসম্পর্ক, ইউলিসিস-এর পুনঃপুনঃ পাঠের অভিজ্ঞতা, উপন্যাসের ‘টেকনিক’, পৌরাণিক থেকে আধুনিকতাবাদে যাত্রা, ক্রোনোটোপ-এর ধারণা। এলিয়ট ও জয়েস, দেরিদা ও ইউলিসিস, আইজ়েনস্টাইন ও জয়েস, জীবনানন্দের মাল্যবান ও জয়েসের ইউলিসিস, ইউলিসিস ও বাংলা উপন্যাসের মূল্যায়ন জয়েসের পাঠককে নতুন করে ভাবাবে। আছে মূল উপন্যাসের দু’টি নির্বাচিত অংশের বঙ্গানুবাদ-প্রয়াস, নোরা বার্নাকলকে লেখা জয়েসের চিঠিও, অনুবাদে।
হরফচর্চা, অগস্ট ২০২৩ সম্পা: সুস্নাত চৌধুরী ৬৫.০০
“সিনেমা লিখেই তিনি তাঁর দর্শনের কথা বলতে চেয়েছেন, সেটা তাঁর রাজনীতিও।... যাই তাঁর কাছে মনুষ্যত্ব বিরোধী ক্ষমতা তার-ই তিনি সবসময় বিরোধিতা করে গিয়েছেন তাঁর সিনেমায়।” জঁ-লুক গোদারকে ঘিরে বিশেষ আলোকপাত এই সংখ্যায়, সম্পাদকীয়তে তারই নান্দীমুখ। একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে অনুবাদ: গোদারের ১৯৭০-এ লেখা সিনেমা বিষয়ক ইস্তাহারের, গোদারের কবিতা, গদ্য ও চিঠির, চারটি অতি জরুরি সাক্ষাৎকারের। গোদারের উইকেন্ড ও নারীই হল নারী ছবি দু’টির চিত্রনাট্যও বাংলা অনুবাদে পড়তে পারবেন আগ্রহী পাঠক। ‘মূল্যায়ন’ অংশেও একগুচ্ছ প্রবন্ধ, গোদারের বহুবর্ণ মননবিশ্বকে তুলে ধরে।
ইতিহ, বিশেষ শিব সংখ্যা ১৪৩০ সম্পা: নবারুণ মল্লিক ৩২০.০০
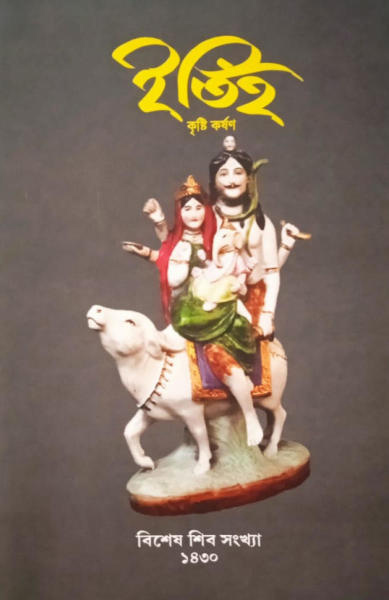

“সামনে থেকে যেন হিমালয় পাহাড় অদৃশ্য হয়ে গেল।” স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। বিবেকানন্দের-জীবনের অন্তিম অধ্যায় নিয়ে প্রবন্ধ এই পত্রিকা-সংখ্যায়; পাশাপাশি রামমোহন, মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, গিরিশ ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বাঘা যতীন, দেশবন্ধু, গগনেন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ, ভগিনী নিবেদিতা, নজরুল, জীবনানন্দ-সহ বাংলার বরণীয় মানুষদের জীবনের শেষ পর্ব বিভিন্ন লেখকের কলমে উঠে এসেছে এই বিশেষ সংখ্যায়। ‘শেষের প্রহর’ শীর্ষকটি তাই সার্থকনামা। আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে বিশেষ রচনাটিও মনোযোগ আকর্ষণ করে।
কোরক, শেষের প্রহর সম্পা: তাপস ভৌমিক ২০০.০০
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)









