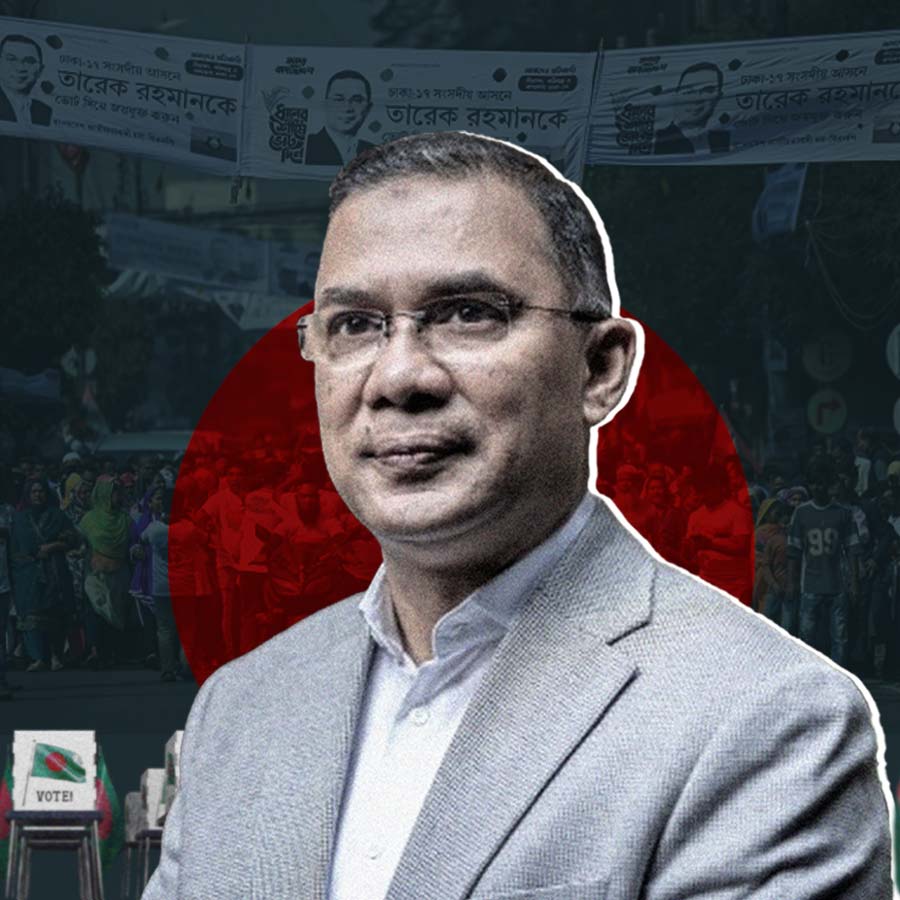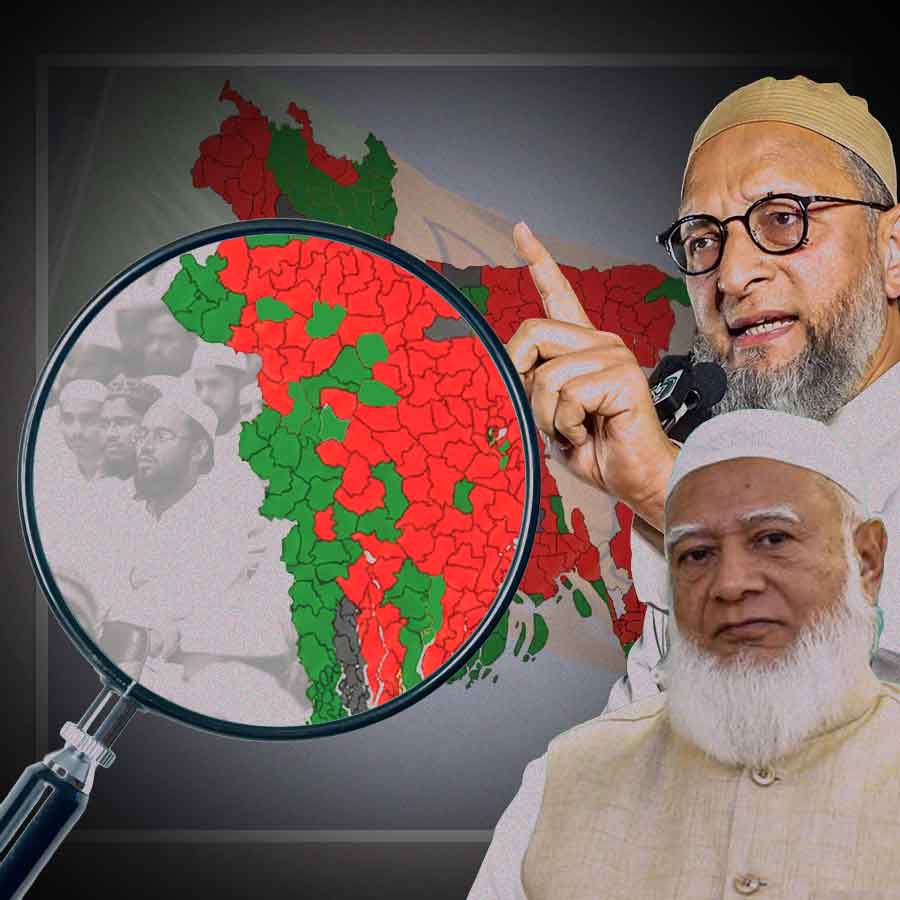“‘দোষী দু’পক্ষই’, যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে চিন্তায় রাষ্ট্রপুঞ্জ” (২৬-৩) শীর্ষক প্রতিবেদনটিতে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের যুদ্ধের এক মর্মান্তিক ছবি তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষত যুদ্ধবন্দিদের অবস্থা শোচনীয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রুশ যুদ্ধবন্দি অথবা ইউক্রেনের যুদ্ধবন্দিদের কারও আঙুল কেটে নেওয়া হয়েছে, কারও হাতটাই নেই, কারও ভেঙে দেওয়া হয়েছে পাঁজর, কাউকে গুলি করে মেরে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ ক্ষোভ প্রকাশ করেছে, রাশিয়া ও ইউক্রেন দু’পক্ষই এই ধরনের নৃশংসতার দোষে দোষী। এই তথ্যগুলি পড়ে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। এই একবিংশ শতাব্দীতে, যে সময়ে মানব-মস্তিষ্ক রোবটের মস্তিষ্কের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে, সেই সময়ে বিশ্বের দু’টি দেশ বিশেষ কোনও কারণ ছাড়াই, কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে অন্যায় ভাবে বিগত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের ইচ্ছেমতো পরস্পরের বসতবাড়ি, সম্পত্তি, একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ধ্বংস করে দিচ্ছে। বাদ পড়ছে না হাসপাতাল। স্কুল-কলেজ চলাকালীন শিক্ষার্থী-সহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উড়িয়ে দিচ্ছে। শত শত শিক্ষার্থী মারা পড়ছে।
অথচ, রাষ্ট্রপুঞ্জের কর্ম তৎপরতার বহর দেখে মনে হচ্ছে যেন, কিছুই হয়নি। মানবাধিকার রক্ষার জন্য ভারপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি যেন হাত-পা গুটিয়ে বসে খেলা দেখছে! অথচ, চেষ্টা করলে তাদের শীর্ষ ব্যক্তিরা কি এমন অমানবিক মারণযুদ্ধ অল্প দিনের মধ্যেই থামিয়ে দিতে পারত না? সেই সকল সংস্থার কর্মীদের কাছে আবেদন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এমন প্রাণঘাতী যুদ্ধ বন্ধ করা হোক।
চৈতন্য দাশ, ধুবুলিয়া, নদিয়া
মুক্তির স্মৃতি
সেমন্তী ঘোষের যুক্তিপূর্ণ কিন্তু সাবলীল আবেগে লেখা ‘আর এক অন্য মুক্তি’ (২৫-৩) প্রবন্ধটি পড়ে আপ্লুত হয়ে গেলাম। এ ইতিহাস আমাদের জীবন সেচে নেওয়া। তাই স্কুলের মাঝারি ক্লাসে পড়া বয়সে যা দেখেছি, যা শুনেছি, সেটুকু শুধু জানাতে চাই।
একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা শহিদ দিবসের আবেগ নিয়ে বাংলা ভাষার অধিকার আদায়, ও বাঙালি জাতির স্বীকৃতির জন্য ২৫ মার্চ, ১৯৭১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন মুক্তিযোদ্ধারা, প্রবল প্রতাপশালী পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যাঁর যা অস্ত্র ছিল, তাই নিয়েই তাঁরা রুখে দাঁড়ান। এই অসম যুদ্ধে সম্বল ছিল বাঙালির প্রবল সাহস ও দেশের জন্য আত্মবলিদানের শপথ। প্রবন্ধকার ১৩ এপ্রিল, ১৯৭১ আনন্দবাজার পত্রিকা-য় সন্তোষ কুমার ঘোষের লেখা উদ্ধৃত করেছেন— “ভুল, ভুল, একেবারে ভুল, সাত কোটি বাঙালিরে জননী মানুষও করেছেন,”— যা একদম সত্যি ছিল।
আমরা তখনও পূর্ব পাকিস্তানে। বাবা আমাদের নিয়ে তাঁর সাত পুরুষের ভিটেবাড়ি আঁকড়ে পড়ে আছেন। তাঁর মুক্তিযোদ্ধা ছাত্ররা আশ্বাস দিয়েছেন যে, তাঁরা প্রাণ দিয়ে আমাদের বাড়ি রক্ষা করবেন। বস্তুত, যুদ্ধ চলাকালীন মুক্তিযোদ্ধারা ব্যারিকেড করে কপোতাক্ষ নদ দিয়েই তিন দিক ঘেরা খুলনার দক্ষিণ অঞ্চলের আমাদের কয়েকটি গ্রামকে ঘিরে রেখেছিলেন। ৭ মার্চ আমরা ঢাকা বেতারে মুজিবুর রহমানের সেই ঐতিহাসিক ভাষণে শুনেছিলাম, “এ লড়াই স্বাধীনতার লড়াই... ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।” যুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানি সেনারা ঢাকা বেতার দখল করে নেয়। আমরা রেডিয়োতে কলকাতা ‘ক’-এ শুনতাম দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেগকম্পিত কণ্ঠে সংবাদ পাঠ, প্রণবেশ সেনের লেখা সংবাদ পরিক্রমা, আর উপেন তরফদারের সংবাদ বিচিত্রা। রেডিয়োর নব ঘুরিয়ে খুঁজে খুঁজে ধরা হত ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র’। এখানে যুদ্ধের খবর, কোথায় মুক্তিযোদ্ধারা জয়লাভ করেছেন, সে খবর দিয়ে মনোবল বৃদ্ধি করা হত। আর ছিল সেই সব বিখ্যাত গান, যেগুলি তুমুল জনপ্রিয় হয়েছিল। শুধু মুক্তিযোদ্ধারা নন, পূর্ব বাংলার সমস্ত মানুষ মনে জোর পেতেন এই সব গানে।
পরে এপার বাংলায় এসে জেনেছিলাম গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখায় গানগুলি গেয়েছিলেন অংশুমান রায় এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ট্রান্সমিটার ছিল কলকাতাতেই। ওখানে তখন প্রচার হয়েছিল, মুক্তিযোদ্ধাদের বেতার কেন্দ্র যশোর বর্ডারের কাছে, সেখান থেকে এগুলি প্রচার করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সিদ্ধান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশকে সাহায্য করার আগে মুক্তিবাহিনী তখন পিছু হটছে, গেরিলা সংগ্রামও নরঘাতক পাকিস্তানি সেনাদের রুখতে পারছে না। বিশ্বাসঘাতক রাজাকারদের সাহায্যে পাকিস্তানের খানসেনারা বাংলার কোণে কোণে গিয়ে বাঙালি নিধন যজ্ঞে মেতেছে। আমাদের ঘিরে থাকা মুক্তিযোদ্ধারাও অসম যুদ্ধে মারা যেতে লাগলেন। উপায় না থাকায় বিশ্বস্ত মাঝির সাহায্যে সারা রাত নৌকা চালিয়ে, শুধু প্রাণটুকু বাঁচিয়ে আমরা প্রায় সর্বহারার মতোই এপার বাংলার হাসনাবাদের ঘাটে উঠলাম। বিরাটিতে আত্মীয়ের বাড়িতে থাকাকালীন দেখেছি, প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু আত্মীয়স্বজনের ভিড়। কিন্তু তাতে কারও কোনও বিরক্তি নেই। যেন তাঁরা জানতেন, বাংলাদেশ ঠিক জিতে যাবে। হয়তো ডালটা আর একটু পাতলা হত, তরকারি একটু কম পড়ত, কিন্তু সবাই এক সঙ্গে বসে একই খাবার খাওয়া হত। একটা বাঙালি সত্তার আবেগ কাজ করত। শিল্পী-সাহিত্যিকদের মিছিলে হাঁটা সম্পর্কে ততটা অবগত ছিলাম না, কিন্তু কী করে যেন অন্নদাশঙ্কর রায়ের ‘দিকে দিকে আজ রক্ত গঙ্গা/ অশ্রুগঙ্গা বহমান.../ জয় মুজিবুর রহমান’ কবিতাটা শুনেছিলাম। আর শুনেছিলাম ঋত্বিক ঘটক, সলিল চৌধুরী, শচীন দেববর্মন এবং আরও সব গুণিজন পথে নেমে অর্থ সংগ্রহ করছেন, এখানে হাসপাতালে থাকা আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা, এবং বর্ডারে সংগ্রামরত তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য। তাঁদের আহ্বানে বম্বে থেকে দিলীপ কুমার, রাজেশ খন্নারাও এসে অনুষ্ঠান করছেন অর্থ সংগ্রহের জন্য। এর পর পরই আমরা দেখতাম, যশোর রোড দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ি যেত বাংলাদেশকে সাহায্যের জন্য।
ওই আত্মীয়দের পরামর্শে বাবা আগেই এখানে কম দামে অনেকটা নিচু জমি কিনে রেখেছিলেন। এ বার ছোট পুকুর কেটে ওই মাটি দিয়ে বাকি জায়গা উঁচু করে মায়ের গয়না বিক্রি করে আমাদের ছোট একতলা বাড়ি হল। আমরা স্কুলে ভর্তি হলাম। সপ্তাহে এক দিন লবণহ্রদ ক্যাম্পে গিয়ে, আসার সময় হাসনাবাদে যে বর্ডার স্লিপ দিয়েছিল, তা দেখিয়ে প্রচুর চাল, ডাল, তেল, চিনি, গুঁড়ো দুধ নিয়ে আসা হত। সে সময়ে এমন একটা আবেগ কাজ করত, যাঁরা সে সব দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন, অঢেল দেওয়ার মধ্যেই যেন তাঁদের সার্থকতা ছিল। সে সময় ক্যাম্পে থাকা এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম অধ্যাপকের সঙ্গে বাবার পরিচয় হয়েছিল। এ দেশে তাঁদের পরিচিত কেউ ছিলেন না, প্রাণ বাঁচাতে তাই ক্যাম্পে থাকা ছাড়া তাঁদের আর কোনও উপায় ছিল না।
তখন বাংলাদেশের জন্য পশ্চিমবঙ্গবাসীর বাঙালিয়ানার এমন একটা আবেগ ছিল যে ‘জয়’ ছাড়া তাঁরা আর কিছু ভাবতে পারতেন না। তবে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ভারতীয় সেনানায়ক ফিল্ড মার্শাল মানেকশ, জেনারেল অরোরা এঁদের কাছে পাকিস্তানি বাহিনীর পতন, ও তার নিদর্শন হিসেবে জেনারেল নিয়াজ়ির ব্যাজ ছিঁড়ে নেওয়া— এই সব খবর আমরা রেডিয়োতে শুনেছিলাম, কাগজে ছবিও দেখেছিলাম। এখানে প্রবন্ধকার দেশভাগের কলঙ্কে ‘পাতকী’ হওয়ার কথা লিখেছেন। কয়েক বছর পরে জরুরি অবস্থার সময় আমরা কিছুটা সমালোচনা করলে মা বলতেন, “তিনি আমাদের অন্নদাত্রী ছিলেন, অকৃতজ্ঞ হয়ে পাতকী হতে পারব না।”
শিখা সেনগুপ্ত, কলকাতা-৫১
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)