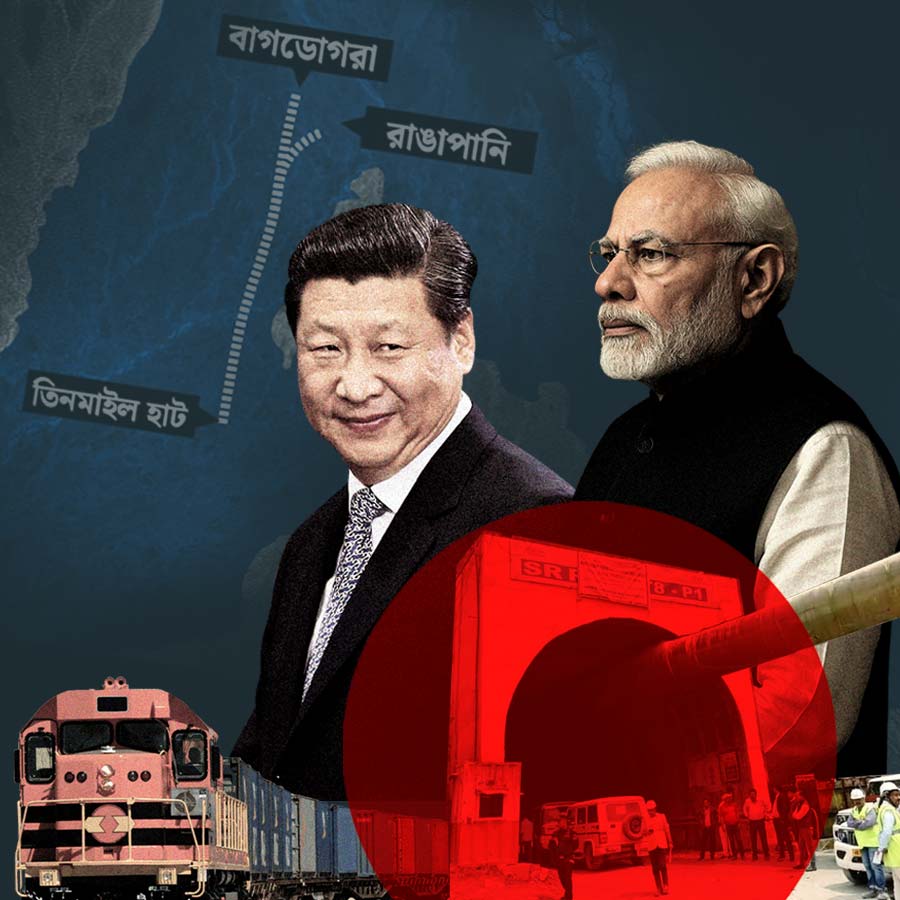আগামী ২০২৪ সালে লোকসভার নির্বাচন। এ দিকে বিরোধী নেতারা এখনও জোট বাঁধতে পারছেন না। জ্বালানির তেল, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য, জীবনদায়ী ওষুধের মূল্য প্রতি দিন ঊর্ধ্বগামী। একের পর এক সরকারি সংস্থা বিক্রি হচ্ছে, ব্যাঙ্কের জমা টাকার উপর সুদের হার কমানো হচ্ছে, চাকরি নেই, শিল্পে বিনিয়োগ নেই। তবুও দেশের একটা সম্প্রদায়ের মানুষ মোদীজিকেই চান, কারণ একক বিরোধী নেতার অভাব। বিরোধীদের মধ্যেও কোনও বোঝাপড়া নেই। কেউ চান কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে বিরোধী জোট করতে, কেউ চান কংগ্রেসকে নিয়েই জোট করতে। আর কংগ্রেস চাইছে, প্রধানমন্ত্রী হতেই হবে গান্ধী পরিবারের কাউকে।
সারা দেশে কংগ্রেসের ভোট ১৯ শতাংশের আশপাশে। তাই যারা কংগ্রেসকে বাদ রেখে বিরোধী জোট করে দেশের শাসনব্যবস্থার দখল নেবে ভাবছে, তারা ভারতের রাজনীতিতে পরিপক্ব নয়। তবে কংগ্রেসের একার পক্ষে দিল্লি দখল সম্ভব নয়। যে দল থেকে ভারতের তাবড় তাবড় নেতা জন্মেছেন, আজ সেই কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রস্তুতির ভার একটা অরাজনৈতিক সংগঠনের হাতে দিতে হচ্ছে! প্রশান্ত কিশোর নাকি কংগ্রেসকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনবেন!
এ বছর গুজরাত ও হিমাচলে বিধানসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনের পরে আগামী মে, ২০২৩-এর মধ্যে মেঘালয়, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড ও কর্নাটকে বিধানসভা নির্বাচন। এই ছ’টা রাজ্যে যদি বিজেপি ভাল ফল করে, তবে ২০২৪ সালে বিজেপির দিল্লি দখল প্রায় নিশ্চিত হবে। ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছিল, কংগ্রেস প্রধান বিরোধী দলের যোগ্যতাও প্রায় হারাতে বসেছিল মাত্র ৪৪টা আসনে জিতে। এর পর ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ৫২টা আসনেই আটকে যায়। তার পর থেকে বিজেপি অনেক জনবিরোধী কাজ করেছে, কিন্তু তাদের জনপ্রিয়তা নির্বাচনী অঙ্কের হিসাবে কমেনি। কংগ্রেসকে ঘুরে দাঁড়াতে গেলে চাই যোগ্য নেতৃত্ব, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মতো নতুন মুখ। দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে বেশির ভাগ মানুষ চাইছেন পরিবর্তন আসুক। কিন্তু বিরোধী নেতারা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ নিয়ে বেশি ভাবছেন। তাই শক্তিশালী বিরোধী জোটের সম্ভাবনা এই মুহূর্তে সামান্য।
পার্থময় চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা-৮৪
প্রাচীন পুঁথি
মৌ দাশগুপ্তের ‘গৌড়ের মেয়েরা’ (রবিবাসরীয়, ২৪-৪) লেখাটি আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি। একটি প্রাচীন পুঁথি অবলম্বনে এটি লিখিত। তবে উল্লিখিত পুঁথি ‘সেকশুভোদয়া’ আদৌ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে লেখা কি না, সে-বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যে মতভেদ আছে, সে কথা বলতে কসুর করেননি প্রবন্ধকারও। আমরা এ বিষয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুকুমার সেনের মত নেব, না কি দীনেশচন্দ্র সেনের মত, মীমাংসা করা সহজ নয়। তবে বর্তমানে যে পাঠটি আমাদের সামনে রয়েছে, তা যদি এতই বিকৃত হয়ে থাকে যে তার ভাষাকে আর লক্ষ্মণসেনের সভাকবি হলায়ুধ মিশ্রের লেখা বলে চেনা না যায়, তা হলে এর ভিত্তিতে সামাজিক কাহিনি যদিও বা লেখা যায়, ইতিহাস নির্মাণ যুক্তিসঙ্গত হবে না। এর রচনাকাল সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। বর্ণিত আখ্যানে লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় মুসলমান সাধুপুরুষ শেখ জালালউদ্দিন তাব্রিজির আগমনের কথা আছে, কেবল সেই কারণে বখতিয়ার খিলজির আগেই বাংলায় মুসলমান প্রবেশ ঘটেছিল বলে মেনে নেওয়া কঠিন। তার জন্য দৃঢ় সাক্ষ্য-প্রমাণ দরকার। জাহিরুল হাসান তাঁর বাংলায় মুসলমানের আটশো বছর বইতে বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠীকে স্থাপন করতে চেয়েছেন বখতিয়ার খিলজি-পরবর্তী সময়ে, অর্থাৎ ১২০৪ সাল থেকে। তাঁর বাংলায় মুসলমানের ইতিহাস বইটিতে সবিস্তার আলোচনা আছে এই প্রসঙ্গে। হলায়ুধ মিশ্রের ‘সেকশুভোদয়া’-র সুকুমার সেন-কৃত অনুবাদে (এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০২) ‘শ্রীমৎ সাহ জালালস্য’-র আশ্রমে আগমনের বছর বলা হয়েছে যাবনিক সন ৬০৮ এবং বিদায়ের কাল যাবনিক সন ৬১০। যাবনিক সন মানে হিজরি। ৬০৮ হিজরি খ্রিস্টীয় ১২১১/১২ সালের সমতুল। তখন কিন্তু লক্ষ্মণসেন বেঁচে নেই। সুতরাং, ১২১১ সালে শেখ জালালের সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়া অসম্ভব। ইতিহাসবিদ সুখময় মুখোপাধ্যায়ও ‘সেকশুভোদয়া’-কে জাল বই বলেছেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি প্রসিদ্ধ সুফি সাধক খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকির উক্তি সংগ্রহের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, শেখ জালালউদ্দিন তাব্রিজি ইলতুতমিসের রাজত্বকালে (১২১০-৩৬) দিল্লিতে আসেন, তার পরে বাংলায়। সুতরাং, সেকশুভোদয়া-র কাহিনিকে ঐতিহাসিক দলিল মনে করা চলে না।
বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, কলকাতা-১৪
শব্দদানব
ছেলেবেলায় ‘ডিজে’ শব্দটির সঙ্গে পরিচিত ছিলাম না। কয়েক বছর যাবৎ বুক-কাঁপানো, বাড়ি-কাঁপানো বাদ্যি বড় বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছে। যে কোনও পুজো বা অনুষ্ঠানে পাড়ায় ব্যবহার করা হয় এই দানবীয় বাদ্যযন্ত্রটি। তিরিশ-চল্লিশটা মাইক, দশ-পনেরোটা বড় বড় বক্স এক সঙ্গে বাজিয়ে যে শব্দ নিঃসৃত হয়, তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। বারোয়ারি পূজার দিন যখন এক দল গঙ্গায় জল আনতে যায়, তখন তাদের নিয়ে আসার জন্য ওই ভয়ানক বাদ্যযন্ত্রগুলোর সঙ্গে এক ঝাঁক তরুণ-তরুণী নাচতে নাচতে যায়। শব্দতাণ্ডবের ভয়ে সাধারণ মানুষ পূজাপ্রাঙ্গণে যেতে ভয় পান। প্রতিবাদ করলে জোটে দুর্ব্যবহার ও আক্রমণ। তাই প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, ডিজে বক্স বাদ দেওয়া হোক।
মঞ্জুশ্রী মণ্ডল, তারকেশ্বর, হুগলি
বৃক্ষনিধন
জয়া মিত্রের ‘রক্ষা করো এই গ্রহের প্রাণ’ (৫-৫) প্রবন্ধটি পড়ে আত্মপীড়নে ভুগছি। সত্যিই অবিশ্বাস্য গতিতে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বৃক্ষসংসার। উত্তর ২৪ পরগনার ইছাপুরে ‘নর্থল্যান্ড’ নামে ৭৫ বছরেরও বেশি পুরনো একটি এস্টেট থেকে প্রায় সহস্রাধিক দামি দামি বৃক্ষ কেটে নেওয়া হয়েছে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের জন্য। এর চার পাশে রয়েছে নর্থ ব্যারাকপুর পুরসভার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। একটা প্রাণচঞ্চল এস্টেটের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এখন শুধুই সৌর প্যানেল। যেন সৌর প্যানেলের শ্মশানভূমি। হায় পরিবেশ সচেতনতা!
বাবুলাল দাস, ইছাপুর, উত্তর ২৪ পরগনা
অবহেলিত
‘খাওয়া না-খাওয়ার পালা’ (২৯-৪) প্রবন্ধ প্রসঙ্গে বলি, গ্রামীণ জনপদে দীর্ঘকাল কর্মসূত্রে থাকায় দেখেছি যে, কন্যাসন্তানের প্রতি অবহেলার বীজ বপন হয় নামকরণেই। দুখি, খেঁদি, করুণা, ইতি প্রভৃতি নামে বাঁধা পড়ে অনাদরের স্বাক্ষর। এরাই বড় হয়ে দেখে বাড়িতে অসম সাহচর্য। সুস্বাদু, পুষ্টিকর ও লোভনীয় সব খাবারেই থাকে ভাই বা দাদার জোরালো অধিকার। মাছের মুড়ো থেকে ফলটুকু বা দুধটুকুও ফি দিন নির্দিষ্ট থাকে বাড়ির পুরুষ সদস্যদের জন্য। মা, ঠাকুমারা সাংসারিক কুনাট্যের কুশীলব হয়ে নীরবে এই ধারা বজায় রেখে যান। অপুষ্টির শিকার হয় মেয়েরা। অধোগতির এই সমাজে নারীকল্যাণ নিমিত্ত সরকারি বিবিধ উন্নয়ন প্রকল্প এদের জীবনে অধরাই থেকে যায়।
সুপ্রতিম প্রামাণিক, আমোদপুর, বীরভূম