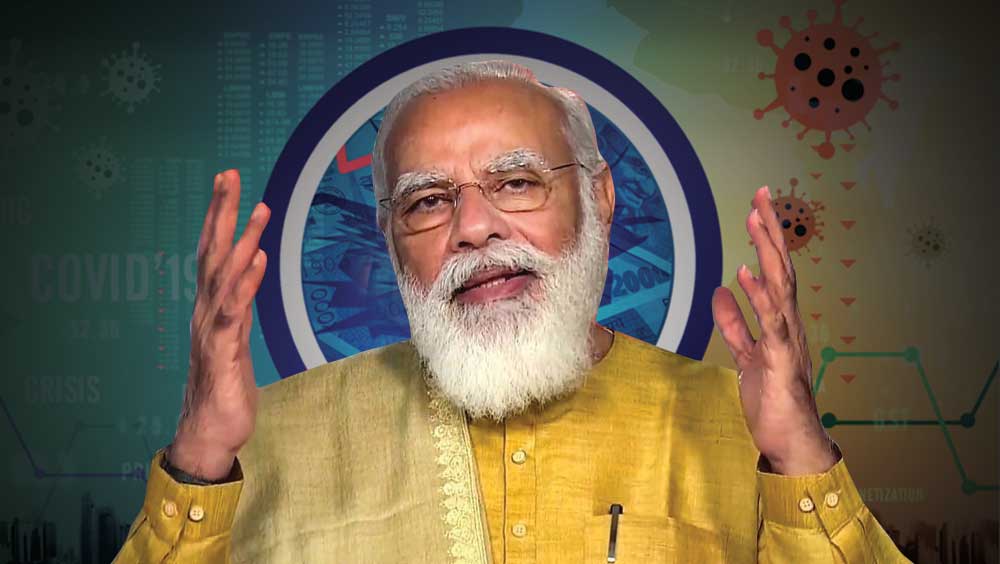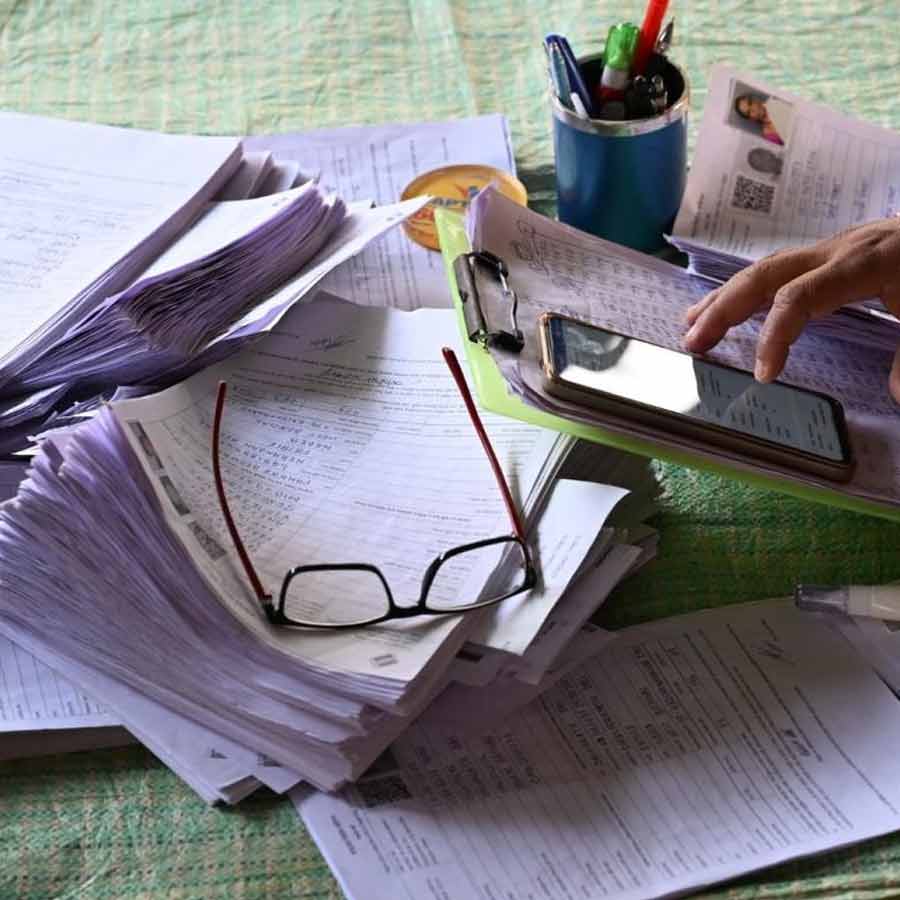হলিউডি ছবি ‘ওয়াল স্ট্রিট’-এর এক জায়গায় হাল হোলব্রুক চার্লি শিনকে বলেছিলেন, “টাকার আসল ব্যাপারটা কী জানো? টাকা তোমাকে দিয়ে সেই কাজগুলো করিয়ে নেয়, যা তুমি নিজে থেকে করতে চাও না।”
১৯৮৭ সালের সেই ছবিটি ছিল উচ্চতর অর্থনীতির খেলা ও তাকে ঘিরে আবর্তিত লোভের বিরুদ্ধে এক নৈতিক প্রতিবাদ। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ছবিটিকে বাস্তবের ওয়াল স্ট্রিটের চাকরির বিজ্ঞাপন বলে মনে হতে পারে! নৈতিকতা এবং অর্থনীতি নিয়ে এই পর্যন্তই। কিন্তু আন্তর্জাতিক স্তরে সাংবাদিকদের সম্মিলিত উদ্যোগ ‘প্যান্ডোরার বাক্স’ থেকে সেই তালিকাকেই বার করে আনে, যেখানে পরতে পরতে রয়েছে কর থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য গোপন আশ্রয়স্থলের হদিশ এবং দায়বদ্ধতা এড়িয়ে যাওয়ার প্রশ্ন। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমরা কী পেলাম? যা পাওয়া গেল, তাকে ‘ভণ্ডামি’ ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না।
আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন কংগ্রেসের উদ্দেশে প্রদত্ত এক ভাষণে সুইৎজারল্যান্ড, কেম্যান আইল্যান্ড প্রভৃতি করফাঁকির বিখ্যাত আশ্রয়স্থলগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ডেলাওয়্যার এবং সাউথ ডাকোটার মতো আমেরিকান স্টেটগুলির কথা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। যেগুলি কর সংক্রান্ত লুকোচুরি আর করফাঁকির স্বর্গরাজ্য। কার্যত এই সব জায়গাকে আজ ‘নয়া সুইৎজারল্যান্ড’ বলে ডাকা হচ্ছে। কারণ, আসল সুইৎজারল্যান্ড অনৈতিক ভাবে অর্থের গচ্ছিতকরণ বন্ধ করে দিয়েছে। সত্যিই আমেরিকা তার ‘ফরেন অ্যাকাউন্ট ট্যাক্স কমপ্ল্যায়েন্স অ্যাক্ট’ কাজে লাগিয়ে আমেরিকান নাগরিকদের অন্য দেশে আর্থিক সম্পত্তি বিস্তারে বাদ সেধেছে। কিন্তু এর বিপরীতে ওয়াশিংটন তুনামূলক সম্মতিজ্ঞাপনে রাজি হয়নি।
বারমুডা এবং ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডের মতো ব্রিটেনের অধীন সাগরপারের অঞ্চলগুলি কর ফাঁকির ওস্তাদদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ আশ্রয়স্থল। এর ফলস্বরূপ দেখা যায়, বিশ্বের মধ্যে কর আদায়ে ব্যর্থ দেশগুলির তালিকায় ব্রিটেন প্রায় শীর্ষস্থানে। কিন্তু এই ‘প্যান্ডোরার বাক্স’ থেকে বেরিয়ে আসা তালিকা নিয়ে যখন সে দেশের কনজারভেটিভ এবং লেবার দল পরস্পরের বিরুদ্ধে চাপানউতরে মাতে, তখন এই করফাঁকির স্বর্গগুলির বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ বা নতুন আইন প্রণয়নের বিষয়টি কিন্তু অনুচ্চারিতই থেকে যায়। এবং দেখা যায় যে, রাশিয়ার কোনও বিতর্কিত ব্যবসায়ী ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে এক নয়া সমীকরণ বার করতে পার্লামেন্টের কনজারভেটিভ সদস্যদের প্রতি দশ জনের এক জনকে টাকা খাইয়ে বসে আছেন।


ভারত এদের দু’একটি বিষয় শেখাতে পারে। ভারত ‘মরিশাস ট্যাক্স হোল’ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হয়েছে, যদিও এটি রাজনৈতিক দলগুলির পিছনে বেআইনি বিদেশি বিনিয়োগকে ন্যায্য বলে অনুমোদন দেয়। ইলেক্টোরাল বন্ড ব্যবস্থা আর্থিক বিষয়ে স্বীকারোক্তির ব্যাপারটি থেকে এক ধাপ সরে আসার জায়গা তৈরি করে দেয়। এবং রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচন উপলক্ষে কী পরিমাণ টাকা খরচ করছে, তার কোনও ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ সম্ভব হয় না।
করফাঁকি দেওয়ার পোতাশ্রয়গুলিতে মানুষ টাকা রাখে বিভিন্ন কারণে। যার মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত কারণ, অপরাধ, কর বাঁচানো বা এড়িয়ে যাওয়া, ট্রাস্টের মাধ্যমে এস্টেট বা স্থাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগের সুবিধা এবং এ সব ছাড়াও রয়েছে স্বৈরতান্ত্রিক দেশগুলিতে সরকার বদলের সময়ে নিরাপত্তার আশ্বাস। এই সব কারণের বেশ কয়েকটি অনৈতিক হলেও বেআইনি নয়। আবার কখনও কখনও এই সব করফাঁকির মুলুকের সুলুক-সন্ধানের দরকারও পড়ে না। মনে রাখতে হবে, অ্যামাজন-এর জেফ বেজোস এবং টেসলা-র এলোন মাস্ক বেশ কিছু বছর কোনও করই দেননি বা দিলেও খুব সামান্য পরিমাণে দিয়েছেন। কিন্তু পরে সংশোধনী প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। যে সব সংস্থা কর ফাঁকির মুলুকে আশ্রয় নিচ্ছে বা আয়ারল্যান্ডের মতো কম কর দিতে হয়, এমন রাষ্ট্রকে ব্যবহার করতে চাইছে, তাদের মনে রাখতে হবে, আন্তর্জাতিক স্তরে কর্পোরেট সংস্থার লভ্যাংশের উপর ১৫ শতাংশ কর ধার্য করা হয়েছে (যদিও প্রস্তাব ছিল ২১ শতাংশের)।


এ সব রাঘববোয়ালদের তালিকায় ভারতীয়দের অবস্থান কোথায়? খতিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এ দেশের বেশির ভাগ ব্যবসায়ীই নেহাতই ‘তুশ্চু’ এই সব তিমিঙ্গিলদের কাছে (তালিকার শীর্ষে অবস্থানকারীরা হয় বেশির ভাগই নিরপরাধ নয়তো এতটাই ঘাঘু যে, তাঁদের হদিশ করাই যায়নি)। এঁদের কারবার কয়েকশো কোটি টাকার সামান্য পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কেউ কেউ আবার বলেন, তাঁরা করপ্রদান বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে অবগত রাখেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই অনাবাসী এবং আইন ভঙ্গ করেন না। কিন্তু এঁদের মধ্যেই এমন এক জোড়া ব্যবসায়ী রয়েছেন, যাঁরা নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করেছেন এবং করফাঁকির মুলুকে স্থাবর সম্পত্তির মালিক হিসেবে তাঁদের দেখা গিয়েছে। লক্ষণীয়, সাম্প্রতিক কালে বেশ কয়েক হাজার নব্য-ধনী ভারতীয় ‘অনাবাসী’ তকমা নিজেদের গায়ে সেঁটেছেন এবং দুবাইয়ের মতো করফাঁকির আশ্রয়স্থলে তাঁদের সম্পদের বেশ বড়সড় অংশ নিয়ে থানা গেড়েছেন। এই পরিযানের কারণ হিসেবে তাঁরা যা দেখিয়েছেন, তার মধ্যে শিক্ষা থেকে উন্নততর পরিবেশে স্বাস্থ্য বা চিকিৎসার মতো পরিষেবার বিষয় রয়েছে।
যদি এক বার কেউ নৈতিকতার বাঁধন থেকে নিজেকে বার করে আনতে পারে, তা হলে তা কি ক্ষুদ্রতর অর্থনীতির সাপেক্ষে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দেখা দেয়? করফাঁকির মুলুকে মোট কত টাকা গচ্ছিত হয়েছে, সেই পরিমাণটি জানতে পারলে অনেকেরই চোখ চড়কগাছে উঠবে। এক আনুমানিক হিসেব অনুযায়ী অঙ্কটি ৫ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি থেকে ৩২ লক্ষ কোটি আমেরিকান ডলারের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডারের কয়েক বছর আগেকার এক হিসেব বলছে, ফাঁকি দেওয়া করের পরিমাণ সেই সময়ে ছিল ৫০ হাজার থেকে ৭০ হাজার কোটি আমেরিকান ডলার। নিঃসন্দেহে এই পরিমাণটি বিপুল, বিশ্বের মোট গৃহজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর ১ শতাংশের কাছাকাছি। যদি আমেরিকা আর ব্রিটেন তাদের ঢিলেঢালা ভাবটি ত্যাগ করে, তা হলে এই পরিমাণটি খানিক কমবে। তাদের কর-সাম্রাজ্যই এতে সব থেকে বেশি উপকৃত হবে। কিন্তু এই খেলা একান্ত ভাবেই ধনীদের। আর ধনী রাষ্ট্রের সরকারগুলি হল এই খেলার সব থেকে বড় খেলোয়াড়। ভাইমার আমলের জার্মানির পটভূমিকায় নির্মিত ১৯৭২ সালের ‘ক্যাবারে’ ছবিতে লিজা মিনেলি ও জোয়েল গ্রে-র গাওয়া একটি গান মনে পড়তে পারে এই প্রসঙ্গে, যেখানে বলা হয়েছিল— ‘মানি মেকস দ্য ওয়ার্ল্ড গো রাউন্ড... দ্যাট ক্লিঙ্কিং ক্ল্যাঙ্কিং সাউন্ড’ (সরলার্থ— ‘টাকাতেই ঘোরে দুনিয়া বনবন... যার শব্দ ঠনঠন ঝনঝন’)।