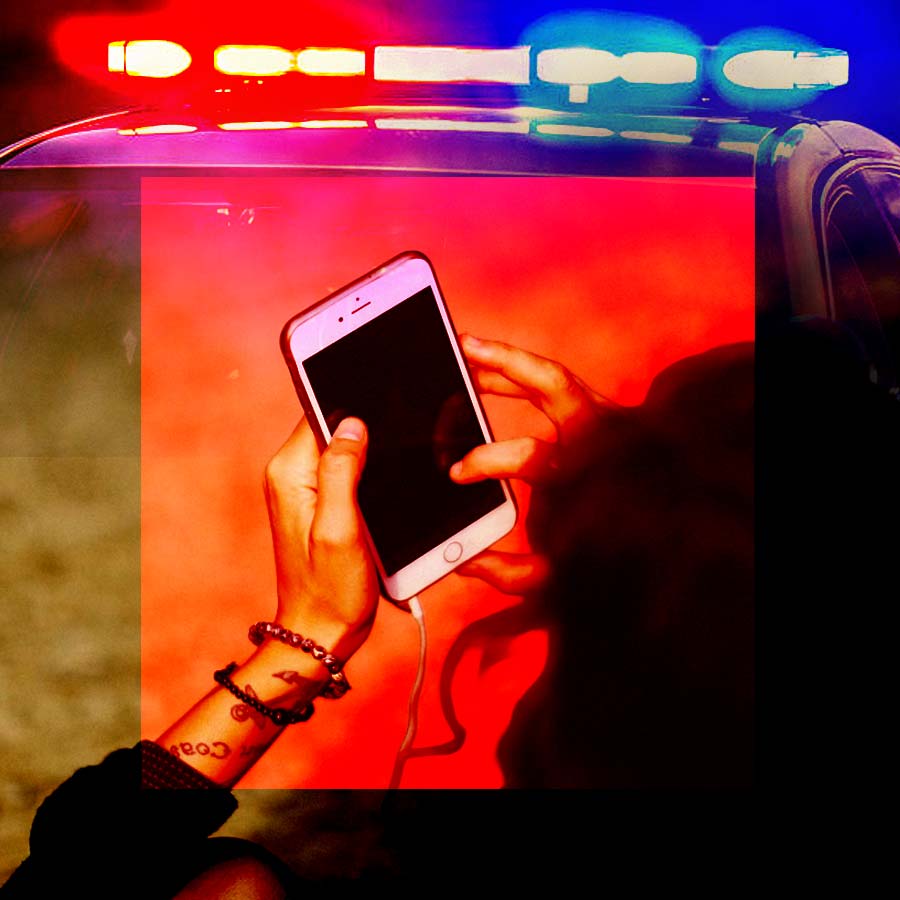দিনটা ছিল ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই। বাংলার ইতিহাসে বড় রকম পালাবদলের দিন। রাজমহলের যুদ্ধে মুঘল সম্রাট আকবরের সেনাপতি খান জাহানের হাতে পরাজিত হলেন বাংলার শেষ স্বাধীন আফগান সুলতান দাউদ খান কররানি। ভাবা যায়, হোসেন শাহি স্বর্ণযুগ শেষ হয়েছে মাত্র কয়েক দশক আগেই! চৈতন্যদেবের অন্তর্ধান ১৫৩৩ সালে, সুলতান হোসেন শাহ মারা যান ১৫১৯-এ। হোসেন শাহি বংশের শেষ সুলতান গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহ আফগান শের শাহের হাতে পরাজিত হন ১৫৩৮-এ।
দাউদ কররানির মৃত্যুদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় সুলতানি আমলের চূড়ান্ত অবসান হল ঠিকই, কিন্তু পুরোপুরি মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে লেগেছিল আরও তিন দশকেরও বেশি। বিদ্রোহী আফগানরা তো নানা জায়গায় ছিলই, আর কেন্দ্রীয় শাসনের অবসানে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে তখন বারো-ভুঁঞাদের অখণ্ড প্রতাপ। দফায় দফায় তাদের বাগে আনতেই কেটে গিয়েছিল অনেকটা সময়, শেষে মুঘল সুবাদার ইসলাম খান চিশতি ১৬১২-য় সারা বাংলা মুঘল অধিকারে আনেন। ধারাবাহিক অরাজকতার পর দেশে শান্তি ফিরল।
কিন্তু ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ শুধু এই বিপুল রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাঙালির সংস্কৃতিতেও ঘটে গেল বড় রকম পরিবর্তন। এর আগে ত্রয়োদশ শতকের সূচনায় মহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের ফলে ইসলামি শাসন প্রবর্তিত হয়। বাংলায় ইসলামি শাসনের প্রথম ১২৫ বছরে সুলতানরা কখনও দিল্লির অধীন, কখনও বা স্বাধীনতার পতাকা তুললেও ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই স্বাধীনতা বজায় থেকেছে টানা দুশো বছর। দিল্লির অধীনতা অস্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে এই সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় ধীরে ধীরে গড়ে উঠল বাঙালির নিজস্ব সত্তা। ইলিয়াস শাহি আমলেই হিন্দুরা প্রথম উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হন। ব্রাহ্মণ্য-পৃষ্ঠপোষিত সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব খর্ব হয়, ফার্সি হয়ে ওঠে রাজদরবারের ভাষা। আর সেই সুযোগে উঠে আসে সর্বসাধারণের ভাষা বাংলা। সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা দিকে এই বাঙালিত্বের বিচিত্রমুখী প্রকাশ ঘটেছে।
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তো সুপরিচিত। বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ থেকে শুরু করে কৃত্তিবাসের ‘রামায়ণ’, মালাধর বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’, বিজয়গুপ্তের ‘মনসামঙ্গল’, বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের ‘মনসাবিজয়’, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর মহাভারত, সবই স্বাধীন সুলতানদের সময়ের ফসল। কোথাও প্রত্যক্ষ পোষকতা, কোথাও বা সাহিত্য রচনার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া। কিন্তু বিশেষ করে চোখে পড়ার মতো বিকাশ ঘটেছে বাঙালির স্থাপত্যে, যা তুলনায় কম আলোচিত। এখানে রাজকীয় হস্তক্ষেপ ছিল একেবারে সরাসরি। তুরস্ক থেকে তো নয়ই, সুলতানরা দিল্লি-কেন্দ্রিক উত্তর-ভারতীয় স্থাপত্যশৈলীও আমদানি করলেন না, মন দিলেন নিজস্ব শৈলী নির্মাণে। বাংলার একেবারে নিজস্ব শৈলী, যা ভারতের আর কোথাওই পুনরাবৃত্ত হয়নি।
আর সেই শৈলীর সন্ধানে তাঁরা তাকালেন ঘরের দিকেই। বাংলার আবহমানের বাঁশ-খড়-কাদামাটির চালাঘরই তাদের আকর্ষণ করল। রাজমহল পাহাড় ছাড়া বাংলায় কোথাও পাথর নেই, তাই বাংলার স্থাপত্যে পাথরের ব্যবহার নিতান্তই কম। পোড়ানো ইটই ভরসা। তাই স্থাপত্যের আকারও আদিনা মসজিদের মতো ব্যতিক্রম ছাড়া, সাধারণ ভাবে ছোট এবং অনাড়ম্বর। ইসলাম এখানে নিজের দম্ভ দেখাতে চায়নি, মাটির কাছাকাছিই থাকতে চেয়েছে।
তবে বাংলার কিছু নিজস্ব উপকরণ ছিল। ইসলামি রীতির খিলান ও গম্বুজের সঙ্গে মিলে গেল বাংলার কুটিরের বাঁকানো চাল। পাল-সেন যুগের শিখর-মন্দিরের সঙ্গে এর কোনও মিল রইল না। কুটিরে খড়ের চালের যে বাঁক, তা বাঁশের মতো উপাদানের প্রয়োজনে। ইটের স্থাপত্যে তার দরকার ছিল না। কেউ কেউ বলেন, সুলতানি আমলের স্থাপত্যে বাঁকানো চালের ব্যবহার হয়েছে সহজে বর্ষার জল নিকাশের উদ্দেশ্যে।
আবার নিছক ভাল লাগা থেকেও তা হতে পারে। কারণ যা-ই হোক না কেন, এর ফল যে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল তা আমরা একটু পরেই দেখব। মালদহ জেলার পাণ্ডুয়ায় পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় তৈরি একলাখি সমাধিভবনে বাঁকানো চালের ব্যবহার প্রথম নজরে পড়ে, এর থেকে পুরনো কোনও ইসলামি স্থাপত্যে বাঁকানো চালের নজির নেই। পরে পুরো সুলতানি আমল জুড়ে বিভিন্ন ধরনের স্থাপত্যে এই রীতিই অনুসরণ করা হয়েছে।
বাংলার ইসলামি স্থাপত্যে পোড়ামাটির অলঙ্করণের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। পাণ্ডুয়া, গৌড় কিংবা অন্যান্য জায়গায় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে মসজিদ, সমাধি ও বিভিন্ন স্থাপত্য নির্মাণ করতে গিয়ে সুলতানরা বাংলার পরম্পরাগত পোড়ামাটির অলঙ্করণকে অন্য মাত্রায় তুলে নিয়ে গেলেন— এও এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। ভারতের আর কোথাও ইসলামি স্থাপত্যে টেরাকোটা অলঙ্করণ নজরে পড়ে না। বাংলার স্থাপত্যে টেরাকোটা অলঙ্করণের খুব পুরনো একটা ঐতিহ্য ছিল যা বাংলাদেশের পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারের পোড়ামাটির ফলকে দেখা যায়। তবে এ সব ফলক আকারে যেমন বড়, তেমনই মানুষ বা জীবজন্তুর রূপায়ণেও প্রাণোচ্ছল। তবে এই রকম টেরাকোটা অলঙ্করণের ধারা সম্ভবত বাংলায় ইসলাম আসার আগেই হারিয়ে গিয়েছিল। তাই সুলতানদের প্রয়োজনে তৈরি হল এক নতুন শিল্পী গোষ্ঠী, যে শিল্পীরা প্রাক্-ইসলামি যুগের মন্দির-নির্মাণ শৈলী থেকে অনেকটাই সরে এসে খিলান আর গম্বুজ দিয়ে ছাদ তৈরি শিখলেন, শিখলেন সূক্ষ্ম টেরাকোটা অলঙ্করণের রীতিনীতি। সে অলঙ্করণে প্রাণিজগতের কোনও রূপায়ণ নেই, শুধুই উদ্ভিজ্জ আর জ্যামিতিক নকশা।
মুঘল আমলের আগে পর্যন্ত এই স্থপতিরা মসজিদ বা সমাধি তৈরিতে একাগ্র মনে এই ভাবেই কাজ করে গিয়েছেন। তবে একেবারে গোড়ার দিকে (যেমন ১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দে পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ তৈরির সময়) যে হেতু স্থানীয় হিন্দু শিল্পীরাই ইসলামি স্থাপত্য নির্মাণের দায়িত্ব পেয়েছিলেন, তাই তাঁরা অন্তত অলঙ্করণের ক্ষেত্রে পরম্পরাগত অভিজ্ঞতার চিহ্ন রেখে গিয়েছেন। তারাপদ সাঁতরা দেখিয়েছেন, হিন্দু ভাস্কর্যে রূপায়িত ‘শিকলে ঝোলানো ঘণ্টা’র প্রতিকৃতি থেকে অনুপ্রাণিত শিল্পীরা দড়িতে ঝোলানো প্রদীপদানি বা প্রস্ফুটিত পদ্মের নকশা খোদাই করেছেন। আদিনা মসজিদের মিহরাবের উপরের অংশে টেরাকোটা অলঙ্করণে এমন নিদর্শন অনেক।
ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলার মন্দির নির্মাণে প্রায় এক অন্ধকার সময়। প্রান্তিক অঞ্চলে কিছু মন্দির হয়তো তৈরি হয়েছিল, পুরুলিয়া জেলার তেলকুপি তার সব থেকে বড় নিদর্শন— যদিও পাঞ্চেত জলাধার তৈরির ফলে তার প্রায় সবই এখন বিলুপ্ত। এগুলি অবশ্য পাথরের মন্দির। এই পর্বে পোড়ামাটির অলঙ্করণ-সহ ইটের মন্দিরের সংখ্যা নগণ্য— তার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বোধহয় উত্তরবঙ্গে রায়গঞ্জের কাছে বিন্দোলের ভৈরবী মন্দির। পাণ্ডুয়ার একলাখি সমাধিভবনের টেরাকোটা সজ্জার সঙ্গে এর মিল খুবই লক্ষণীয়। তার উপর এর চূড়া আবার গম্বুজাকৃতি। অনুমান করা যায়, মন্দির নির্মাণের এই পর্বে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল, বিন্দোল তারই অন্যতম উদাহরণ। তবে সাম্প্রতিক আমূল সংস্কারের পর তার খোলনলচে প্রায় বদলে গিয়েছে।
ষোড়শ শতকের বাংলায় শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে আস্তে আস্তে ফিরে এল সুস্থিতি। ভূস্বামীরা মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করায় নিজ নিজ অধিকারসীমায় অনেকটা স্বশাসনের অধিকার পেলেন। সীমান্তবর্তী বিষ্ণুপুর পেল বিপুল ক্ষমতা ও সম্মান। অন্য দিকে, চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম ইতিমধ্যেই প্রসারিত হয়েছে বাংলার নানা প্রান্তে। বৈষ্ণব ভাবান্দোলন এবং ক্ষমতাবান ভূস্বামীদের অক্লান্ত পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার স্থাপত্যে শুরু হল এক নবজাগরণ। সতেরো থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত নবপর্যায়ের এই মন্দির নির্মাণের ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল। কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলে নয়, তা ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বাংলাতেই।
কিন্তু এই নবজাগরণের স্থপতি কারা? মাঝের কয়েকশো বছরে তো মন্দির গড়ার স্থপতিরা প্রায় হারিয়েই গিয়েছিলেন। সে সময়ে তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন মসজিদ কি সমাধি বানাতে। আর মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলার স্থাপত্য দেখা দিল সম্পূর্ণ অন্য চেহারায়। এখন তো আর বাংলা স্বাধীন নয়, সর্বভারতীয় মুঘল সাম্রাজ্যের একটি সুবা মাত্র। তার স্থাপত্যেও তাই প্রভাব পড়ল সর্বভারতীয় মুঘল স্থাপত্যিক চরিত্রের। মসজিদ বা সমাধিতে আর সুলতানি আমলের মতো বাঁকানো চাল রইল না, কার্নিশ হয়ে গেল সোজা। রইল না বহিরঙ্গে সূক্ষ্ম পোড়ামাটির কাজ, এল সাদাসাপটা চুনবালি বা পঙ্খের কাজ। ফলত বেকার হয়ে গেলেন বাঁকানো চাল তৈরির দক্ষ কারিগররা, কিংবা পোড়ামাটির কাজের ওস্তাদ শিল্পীরা।
এ দিকে নতুন করে মন্দির তৈরির প্রণোদনা উপস্থিত, কিন্তু কারিগর বা শিল্পী কোথায়? এত দিন যাঁরা ইসলামি স্থাপত্য তৈরি করছিলেন, আস্তে আস্তে নিশ্চয়ই তাঁরাই ঝুঁকলেন এই দিকে। অথবা বলা যায়, তাঁদেরই ডাক পড়ল নতুন কাজে। এক দিন তাঁরা শিখে নিয়েছিলেন খিলান আর গম্বুজ তৈরি, সঙ্গে টেরাকোটা অলঙ্করণের কারিকুরি। ছাদের কার্নিশ কী করে বাঁকাতে হয়, বুঝে নিয়েছিলেন তাও। এ বার আবার সবই কাজে লাগল। সেই খিলান আর গম্বুজ দিয়েই মন্দির তৈরি হল, চালে রইল যথেষ্ট বাঁক, কিন্তু বাইরে থেকে মসজিদের মতো দেখতে হলে তো চলবে না। তাই চূড়ার গম্বুজ ঢাকা পড়ল নানা ভাবে— কোথাও চারচালা বা আটচালায়। বাংলার স্থাপত্যে তৈরি হল নিজস্ব চরিত্র। চাহিদা এতটাই ছিল যে বাংলার নানা অঞ্চলে তৈরি হল স্থপতিদের ঘাঁটি, প্রয়োজন মতো তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মন্দির তৈরি করতেন। স্থপতিদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর তৈরি মন্দিরে স্বাভাবিক ভাবেই নজরে পড়ে শৈলীর বিভিন্নতা, তবে এই বৈচিত্রের পিছনে পৃষ্ঠপোষকদের নানা রকম চাহিদার ভূমিকাও কম নয়।


সংমিশ্রণ: গৌড়ের ‘কদম রসুল’ (১৫৩১)। পরে নির্মিত বহু মন্দিরের সামনে আছে এই বাঁকানো চালের বৈশিষ্ট্য
যেমন বাংলার সুলতানদের চালাঘর ভাল লাগার ফলে তৈরি হয়েছিল এক অদ্বিতীয় আঞ্চলিক শৈলী, তেমনই মুঘলদেরও ভাল লেগেছিল বাংলার বাঁকানো চালের কুটির। অবশ্য বাংলার আঞ্চলিক মুঘল স্থাপত্যে তার সরাসরি কোনও প্রভাব পড়েনি ঠিকই, কিন্তু এ বারে তা ছড়িয়ে গিয়েছিল রাজ্যের বাইরে। জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শাহজাহান যখন বাংলায় আসেন, তখনই পূর্ববঙ্গে তাঁর নজরে পড়ে বাংলা চালের বৈশিষ্ট্য। সমসাময়িক মির্জা নাথান তাঁর ‘বাহারিস্তান-ই-ঘায়েবি’ বইয়ে স্পষ্ট করেই সে কথা লিখে গিয়েছেন। শাহজাহান দিল্লি ফিরে বাংলার কথা ভুলে যাননি, তিনি সিংহাসনে বসার পর মুঘল স্থাপত্যে জায়গা করে নিল ‘বঙ্গালি ছত্রী’ বা ‘বাংলাদার চাল’। সেখান থেকে মুঘল দরবারের অভিজাতদের সূত্রে উত্তর ভারত জুড়ে এই শৈলী ছড়িয়ে পড়ে, রাজপুত রাজারাও তাঁদের স্থাপত্যে এর ব্যাপক ব্যবহার করেছেন। বাংলায় সরাসরি মসজিদে না হলেও মসজিদের প্রবেশপথে দোচালা স্থাপত্যের ব্যবহার দেখা যায়। এমনকি মসজিদ বা সমাধি-সংলগ্ন কক্ষ হিসেবেও মুঘল আমলে দোচালা তৈরি হয়েছে।
এই পরিবর্তন এক দিনে হয়নি। সুলতানি আমলের শেষ দিকে, ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে সুলতান নুসরৎ শাহের তৈরি গৌড়ের ‘কদম রসুল’ স্থাপত্যটি এ প্রসঙ্গে বিবেচনা করা যেতে পারে। ইটের তৈরি বাঁকানো চালের এই স্থাপত্যের পুবমুখী প্রবেশপথটি তিনটি খিলানযুক্ত।
এই তিনটি খিলানের ভার যে দু’টি থামের উপর রয়েছে, সেগুলি আটকোনা আকৃতির।
কদম রসুলের সামনের দেওয়ালে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে ফুল-লতা-পাতার অলঙ্করণ। শুধু মাথার গম্বুজ বাদ দিলে পরবর্তী কালের বাংলার মন্দিরের সঙ্গে এই কদম রসুলের বহিরঙ্গের সাদৃশ্য অভাবনীয়। অথচ ১৫৩১-এর কাছাকাছি সময়ে তৈরি এমন কোনও মন্দিরের নজির আমাদের জানা নেই। বরং সতেরো-আঠেরো শতকে বাংলার নবপর্যায়ের মন্দির নির্মাণের গৌরবময় পর্বে বহু মন্দিরের সামনের অংশই একেবারে এই রকম দেখতে। শুধু ফুল-লতা-পাতার অলঙ্করণের বদলে সেই সব মন্দিরে রয়েছে রামায়ণ মহাভারত পুরাণের নানা কাহিনির রূপায়ণ, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় যাকে বলেছেন ‘চিত্রিত কথকতা’। এটা নিশ্চয়ই নিছক সমাপতন নয়।
সতেরো শতকেই বাংলার স্থপতিরা তাই সুলতানি আমলে অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তাঁদের পরম্পরাগত শিল্পকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত মন্দিরগুচ্ছের অনবদ্য স্থাপত্য-ভাস্কর্য তার প্রমাণ। বিষ্ণুপুর ও অন্যত্র যে সব বিখ্যাত মন্দির রয়েছে, তার বাইরে চালা ও রত্নরীতির যে অজস্র মন্দির বাংলার গ্রামে গ্রামান্তরে তৈরি হয়েছিল, তা আজও বাংলার নিজস্ব স্থাপত্য-চরিত্রের সাক্ষ্য বহন করে। অন্তরঙ্গে সেই খিলান-গম্বুজের ধারাবাহিক ব্যবহার, বহিরঙ্গে আটকোনা থাম আর টেরাকোটা অলঙ্করণে অটুট রইল সুলতানি আমলের উত্তরাধিকার।