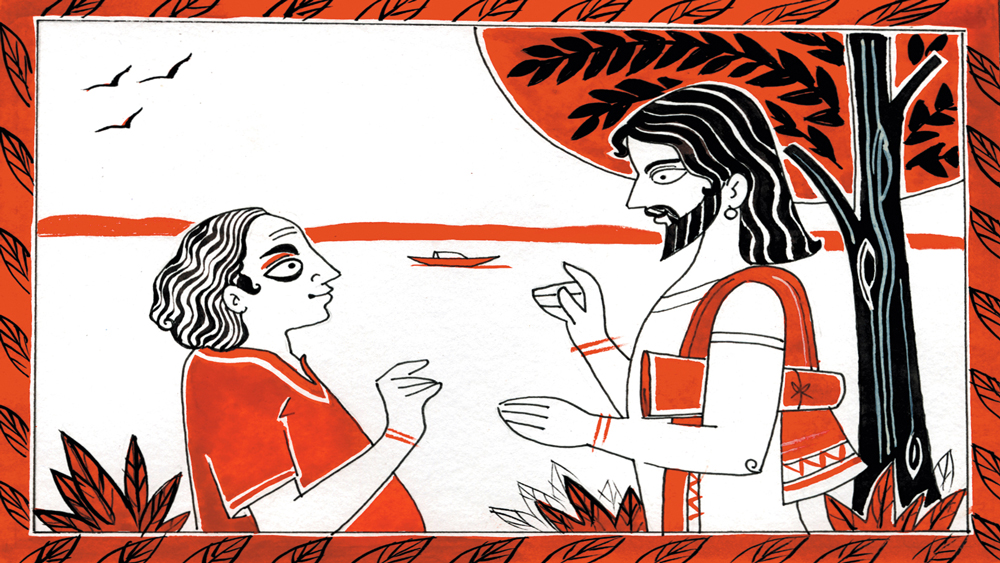গঙ্গার ঘাটে নামতেই জয়গোপাল দেখতে পেলেন, নদীর পাড়ের নরম কাদায় অনেকগুলো পায়ের ছাপ। কিছু দাগ হালকা। কিছু বেশ গভীর। বোঝা যায়, যিনি গঙ্গামাটিতে নেমেছিলেন, তাঁর বপুটি বিশাল। আবার এমনও হতে পারে, তিনি কাউকে কোলে করে নিয়ে গিয়েছেন!
জয়গোপালের মুখে স্মিত হাসি এল। তিনিও কিশোরী স্ত্রীকে এমন করেই গঙ্গার পাড়ে বয়ে নিয়ে যেতেন নৌকা পর্যন্ত। গলা পর্যন্ত ঘোমটা ঢাকা সেই কিশোরীর প্রতি তখন যে অপত্যস্নেহে মন পরিপূর্ণ থাকত, তাতে কী ভাবে যেন মিশে যেত পত্নীপ্রেম। ঘোমটার আড়ালে অধরের যে কোণটুকু দেখা যেত, তাতে যে লেগে থাকত কৌতুকের হাসির একটি চিহ্ন।
নৌকাঘাটের এই জনসমাগমে কত যে চিহ্ন ছড়িয়ে থাকে! তিনি পদচিহ্নগুলো থেকে অবশ্য খুঁজছিলেন মাঝিদের পদচিহ্ন। দেখতে পেলেন কয়েকটি তেমন পায়ের ছাপ চলে গিয়েছে ঘাট বরাবর এক পাশে অনেক দূর অব্দি। জয়গোপাল মাঝিদের সঙ্গে কথা বলে ওই কাদা পেরিয়েই ফিরলেন ঘাটে। গঙ্গাপ্রণাম করে নেমেছিলেন, গঙ্গাপ্রণাম করেই উঠলেন। ঘটিতে ভরা জলে পা ধুতে ধুতে দেখলেন, তর্কবাগীশ এক দৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন তাঁর দিকে। জয়গোপাল তখন ভাবছিলেন, এই যে সন্ধান প্রক্রিয়া, এই যে বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটি শৃঙ্খলার খোঁজ, এইটিই বারবার তাঁকে করতে হয়েছে। তিনি যে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, মিশনের পণ্ডিত। নদিয়ার বজ্রাপুরে আদি বাড়ি। তিনি জানেন, পরম্পরার মধ্যে লুকিয়ে থাকে স্বাতন্ত্র্য। সেই স্বাতন্ত্র্যের খোঁজ করতে হয় তাঁকেই।
তর্কবাগীশ এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন, ‘‘তর্কালঙ্কার বাড়ি যাবে?’’
জয়গোপাল জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘আজ কী বার বলো তো!’’ তর্কবাগীশের উত্তর, ‘‘আজ একাদশী। ত্রয়োদশীতে যাত্রা করলে ভাল। তবে দিনে দিনে যেও। কৃষ্ণপক্ষের আঁধারে একটু উপরের দিকে খুব সুবিধের নয়।’’ তর্কবাগীশ হেসে এগিয়েও এলেন। তার পরে পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘‘তুমি তিথি দিয়ে হিসেব করবে, না বার দিয়ে, সে তো তোমায় স্থির করতে হবে ভায়া! ইংরাজিতে ইহা ১৮২৯ সন। শুক্রবার। তুমি সাবেক টোলের ছাত্র। তুমি একাদশী ধরে এগোলে এক রকম হিসেব পাবে, শুক্রবার ধরে এগোলে আর এক রকম।’’
জয়গোপাল এই হাসিখুশি পণ্ডিতটিকে খুবই পছন্দ করেন। তাঁকে রাগানোর জন্য বললেন, ‘‘আচ্ছা, তর্কবাগীশ, টোলও সর্বদা এক কথা বলে কি? এই যে পতিতপাবনী ভাগীরথীর জল মাথায় ঠেকালাম, সেই ভগীরথ সম্পর্কে তুমি কী জানো?’’
তর্কবাগীশ খুবই অবাক হয়ে বললেন, ‘‘ভগীরথের গল্প বলছ?’’ জয়গোপাল পাল্টা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘ভগীরথের জন্মবৃত্তান্ত জানো?’’ অবাক তর্কবাগীশ বললেন, ‘‘সে তো মনে রাখার মতো কিছু নয় তর্কালঙ্কার। সগরের বংশে দিলীপের পুত্র ছিলেন ভগীরথ।’’ জয়গোপাল এ বার বললেন, ‘‘কিন্তু দিলীপ যে অপুত্রক ছিলেন ভায়া!’’
তর্কবাগীশ হাঁ করে চেয়ে বললেন, ‘‘সে কী কথা!’’ জয়গোপাল গা মুছতে মুছতে বললেন, ‘‘কৃত্তিবাস লিখেছেন, ভগীরথের জন্ম হয়েছে তাঁর দুই মায়ের রতিতে। তবে বলো!’’
স্তব্ধবাক তর্কবাগীশ কোনও মতে উচ্চারণ করলেন, ‘‘এ তুমি কী বলছ তর্কালঙ্কার!’’
তাঁকে দেখে এ বার জয়গোপাল হাসি মুখে পঙ্ক্তিগুলো আউড়ে গেলেন—‘অপুত্রক রাজা, দুঃখ ভাবেন অন্তরে। দুই নারী থুয়ে গেল অযোধ্যা-নগরে।।... মরিয়া দিলীপ রাজা গেল ব্রহ্মলোক।। ...স্বর্গেতে চিন্তিত ব্রহ্মা আর পুরন্দর।। কেমনে বাড়িবে বংশ নির্ম্মূল হইলে।। ভাবিয়া সকল দেব যুক্তি করি মনে। অযোধ্যাতে পাঠাইল প্রভু ত্রিলোচনে।। দিলীপ কামিনী দুই আছিলেন বাসে। বৃষ আরোহণে শিব গেলেন সকাশে।। দোঁহাকার প্রতি কহিলেন ত্রিপুরারি। মম বরে পুতবতী হবে এক নারী।। দুই নারী কহে শুনি শিবের বচন। বিধবা আমরা কিসে হইবে নন্দন।। শঙ্কর বলেন দুই জনে কর রতি। মম বরে একের হইবে সুসন্ততি।। এই বর দিয়া গেল দেব ত্রিপুরারি। স্নান করি গেল দুই দিলীপের নারী।। সম্প্রীতিতে আছিলেন সে দুই যুবতী। কতদিনে একজন হৈল ঋতুমতী।। দোঁহেতে জানিল যদি দোঁহার সন্দর্ভ। দোঁহে কেলি করিতে একের হৈল গর্ভে।।’
শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে গেল তর্কবাগীশের। তর্কবাগীশ বসে পড়লেন গঙ্গার ঘাটে। তার পরে বললেন, ‘‘বাল্মীকিতে এ কথা নেই!’’
জয়গোপাল বললেন, ‘‘না। এ সব কৃত্তিবাসের কল্পনা।’’ তর্কবাগীশ বললেন, ‘‘কৃত্তিবাসের রামায়ণ সম্পাদনা! বড় শক্ত কাজে হাত দিয়েছ হে তর্কালঙ্কার।’’
জয়গোপাল বললেন, ‘‘কথা হল কী জানো, এই যে লক্ষ্মণরেখার কাহিনি, রামের দুর্গাপুজো, হনুমানের সঙ্গে কালনেমির শয়তানি, ভগীরথের জন্মবৃত্তান্তের মতো এমন অনেক কথা বাল্মীকি থেকে দূরে গিয়ে কেন লিখলেন কৃত্তিবাস?’’ তর্কবাগীশ বললেন, ‘‘তোমার উৎকণ্ঠার কথা বুঝতে পারছি। তুমি জানতে চাইছ, কোন পথে কৃত্তিবাস ভাবতে চেয়েছিলেন!’’ জয়গোপাল খানিক চুপ করে থেকে বললেন, ‘‘সেই তো সব থেকে বড় কথা। সেই নদিয়া থেকে গৌড়ে গিয়ে এক কবি লিখলেন রামকথা, তাঁর নিজের মতো করে। এমন আরও হয়েছে। সেক্ষেত্রে কাহিনি বদলেছে। কৃত্তিবাস কিন্তু একই কাহিনিতে বুনে দিয়েছেন নিজের কথা! কৃত্তিবাস নতুন কোনও কথা বলতে চেয়েছিলেন, তাঁর নিজস্ব শৃঙ্খলায়?’’ উৎকণ্ঠার প্রসার হল তর্কবাগীশের মনেও। তিনি বললেন, ‘‘তোমার কোনও কাজে লাগলে বলতে দ্বিধা কোরো না।’’ জয়গোপাল বললেন, ‘‘তা হলে বলো, শৃঙ্খলা বলতে তুমি কী বোঝ?’’ তর্কবাগীশ সামান্য হেসে বললেন, ‘‘তুমি যা শিক্ষা দিয়েছ, রূপ ও বর্ণ নানা হতে পারে, কিন্তু তাঁর সিদ্ধি ও সাধ্য এক হলে তাকে একই বলে মেনে নিতে হবে। কিন্তু ভিন্ন রূপেরও প্রয়োজন রয়েছে।’’ বোঝাই যাচ্ছে, জয়গোপালেরই দেবী চণ্ডীর উপর বইটির কথা বলছেন তর্কবাগীশ।
মাত্র কিছু দিন আগেই সংস্কৃত কলেজে জয়গোপালের সঙ্গে কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কারেরও এই নিয়ে কথা হয়েছে। কমলাকান্তও জয়গোপালের দেবী চণ্ডীর উপরে বইটির প্রশংসা করছিলেন। সাহেব জেমস প্রিন্সেপের সঙ্গে কমলাকান্তের সম্পর্ক খুবই ভাল। তাঁরা অতি সম্প্রতি পাথরে খোদিত অশোকের শিলালেখ-এর পাঠোদ্ধার করছেন। আর তা করতে গিয়ে, তাঁদের ভাবতে হচ্ছে, একটি শৃঙ্খলার কথা। যে শৃঙ্খলার উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বর্ণমালা। বর্ণগুলোকে আলাদা করে চিহ্নিত করতে করতে এগোচ্ছেন কমলাকান্ত। দিল্লি আর ইলাহাবাদের দু’টি স্তম্ভে উৎকীর্ণ বক্তব্যের প্রথমে দ আর ন চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন কমলাকান্ত। তার পরে আ-কার, ই-কার, উ-কার স্থির করলেন। তার পরে অন্য বর্ণ থেকে শব্দ, শব্দ থেকে বাক্য।
কমলাকান্তকে জয়গোপাল খুবই স্নেহ করেন। কলকাতার আরপুলি লেনে কমলাকান্তের টোল ছিল। জয়গোপালের সঙ্গে তাঁর আলাপ সংস্কৃত কলেজে। জয়গোপালের মনে পড়ল, বছর পাঁচেক আগে ১৮২৪ সালে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে জয়গোপাল সেখানে সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, তর্কবাগীশের মতো কমলাকান্তও তখন নিযুক্ত হয়েছিলেন অলঙ্কারের অধ্যাপক। বেতন ছিল ৬০ টাকা। তবে কমলাকান্তের বরাবরই পুরাতত্ত্বের প্রতি ভালবাসা ছিল। ১৮২৭ সালের মে মাসে কমলাকান্ত জিলা মিদনাপুরের ল পণ্ডিত হয়ে চলে যান। কিন্তু তাঁর সঙ্গে জয়গোপালের সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। তাতেই তিনি জানতে পেরেছেন, বারাণসীতে জেমস প্রিন্সেপের সঙ্গে কাজ করছেন কমলাকান্ত। কোলব্রুকের কাছ থেকেও সে কথা শুনেছেন জয়গোপাল। একটি একটি করে বর্ণ থেকে বাক্য গেঁথে গেঁথে কমলাকান্ত ও প্রিন্সেপ অশোকের শিলালেখ উন্মোচন করছেন। সেই লিপির সঙ্গে বাংলা লিপির সাদৃশ্য রয়েছে, তা-ও কমলাকান্তই প্রথম বলেছিলেন।
জয়গোপাল কমলাকান্তের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন, এই যে একই রাজা একটি বিরাট জায়গা জুড়ে রাজত্ব করেন, তিনি কী করে নানা ভাষাভাষী বিভিন্ন জনপদের প্রজাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন? কোনও একটি শৃঙ্খলা তো তাঁকে মানতে হবে, যে শৃঙ্খলায় রাজার সব প্রজারই সমানাধিকার। নানা ভাষা, নানা সংস্কৃতির বৈচিত্রে সেই শৃঙ্খলাটি কী করে রূপ পায়? বিশেষ করে এই রাজা যে নানা জায়গায় পাথরের স্তম্ভ করে সেখানে নিজের বক্তব্য সাধারণ প্রজাদের জন্য লিখেছেন, সেখানে কী শৃঙ্খলায় তিনি বৈচিত্রের মাঝে মিলনের সেতু তৈরি করছেন? নইলে যে সমানাধিকারের কথাটিও সমস্যায় পড়ে যায়!
জয়গোপাল এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে, রাজা তাঁর নিজের বক্তব্যটি একই রাখছেন। সেই কথাটি তিনি কেবল নানা ভাষায় বলছেন —এটিই শৃঙ্খলা। কিন্তু তার পরেই তাঁর মনে পড়ে যায়, যাঁদের ভাষা এবং সংস্কৃতি আলাদা, তাঁদের কি একই নির্দেশ ও তথ্য দেওয়া যায়? সমানাধিকার যে লঙ্ঘিত হয় তাতেও! এই ইউরোপীয়রাও কি সকলে একই রকম?
তর্কবাগীশকে জয়গোপাল বললেন, ‘‘যদি বৈপরীত্যের সমাহারের উপরেই জোর দাও, নৌকাঘাটে আমাকে দেখে তোমার কেন তবে মনে হল, আমি নৌকা করে কেবল বাড়িই যেতে পারি?’’ তর্কবাগীশ শিশুর মতো সরল হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললেন, ‘‘প্রকৃতি! সাহেবদের সঙ্গে কাজ করো বলে কী আর শরৎ থেমে থাকবে ভায়া! আকাশের দিকে একবার চোখ তুলে তাকাও। নদীর দিকে একবার দৃষ্টি ফেল। এই বার আপন গৃহে একবার যে যেতেই হয়! ’’
(এই কাহিনি আদ্যন্ত কাল্পনিক। চরিত্রেরা অনেকেই ঐতিহাসিক। অঙ্কন: কুনাল বর্মণ)