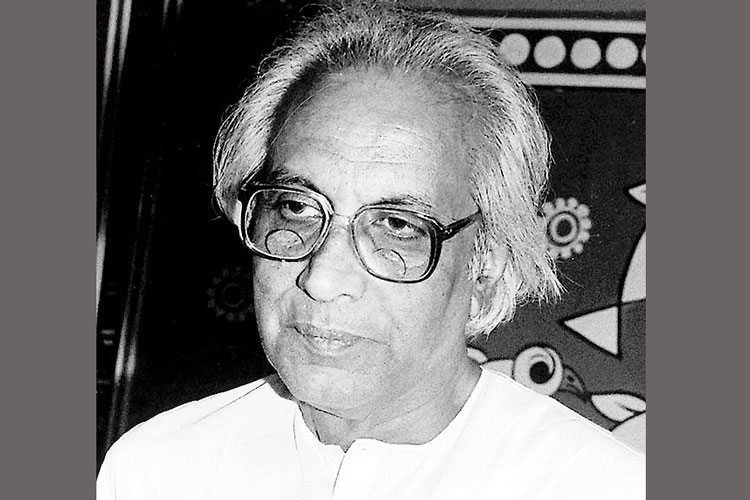নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মনে করতেন, ‘‘কঠিন ভাষা যারা বলে, শোনে ও বোঝে, সহজ ভাষা বলে শোনে ও বোঝে তার চতুর্গুণ মানুষ। আর তাই আমার কবিতা যদি অনেক লোকের কাছে পৌঁছে দিতে হয় তো ভাষার স্তর নির্বাচনে কোনও ভুল করলে আমার চলবে না, সহজ বাংলার জনপথ ধরেই আমাকে হাঁটতে হবে।’’ কবি, লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, বাংলা ভাষার নীতি-নির্ধারক হিসেবে তিনি যা কিছু করেছেন তার মূল নীতিই ছিল লেখা ‘‘আরও অনেকের কাছে পৌঁছে দিতে চাই।’’
বাংলা ভাষার কর্মীদের প্রধান কাজ যে আরও অনেকের কাছে পৌঁছে যাওয়া এই ভাবনা উনিশ শতকে বাংলা ছাপাখানার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই দৃঢ় হয়েছিল। ‘বাঙ্গালার পাঠক পড়ান ব্রত’ নামের অস্বাক্ষরিত লেখায় বঙ্গদর্শন পত্রে মন্তব্য করা হয়েছিল— ছাপাখানা আসার আগে কথকেরা পড়তে-না-জানা মানুষের কাছেও বলার গুণে তাঁদের বার্তা পৌঁছে দিতেন, এখন লেখক সম্পাদকের দায়িত্ব পড়তে-জানা-মানুষদের পাঠক হিসেবে গড়ে তোলা। আনন্দমেলা-র সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ এই পত্রিকার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ পাঠকদের রুচি গড়ে তুললেন। এখন পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যবর্তী যে বাঙালিরা বিশ্বের নানাখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন তাঁদের অনেকেই এই পত্রিকা পড়ে বাংলা ভাষায় মজেছেন। বাংলা শিশু-কিশোর পত্রিকার আদিপর্বের অনেক পত্রের মতো এটি পারিবারিক পত্রিকা ছিল না, কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় সাহিত্য পত্রিকাটিকে ছড়িয়ে দিয়ে ভবিষ্যৎ পাঠক নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মধ্যবিত্ত সেই বামশাসনের প্রথম পর্বে খানিক স্থিতিশীলতার মুখোমুখি। এই মধ্যবিত্ত পরিবারের কিশোর-কিশোরীদের পাঠ-চাহিদাকে নীরেন্দ্রনাথ-সম্পাদিত আনন্দমেলা যেমন পূর্ণ করেছিল, তেমনই তাদের পাঠ-পরিধিকে সম্প্রসারিত করেছিল। অহিভূষণ মালিক ছিলেন নীরেন্দ্রনাথের ‘সত্যযুগ’ পর্বের বন্ধু। আনন্দমেলা-র পাতায় অহিভূষণ নোলেদাকে নিয়ে ধারাবাহিক ভাবে ছবিতে গল্প লিখেছিলেন, নোলেদার মুখের সঙ্গে অহিভূষণের আঁকা ঘনাদারও অনেক মিল। নোলেদা এক্কেবারে উত্তর-কলকাত্তাইয়া দাদার দুষ্টুমিতে ভরা। বাংলা জানা সাহেবকে মুখের বাংলা বলে কাত করে, পেলেদাকে বলে বলে গোল খাওয়ায়। তবে আনন্দমেলা-কে কলকাতা উত্তরেই আটকে রাখতে চাননি সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখা প্রথম কিশোর উপন্যাস মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি যে রহস্যময় রংদার মফস্সলের ধারণা সৃষ্টি করেছিল সেই মফস্সলেও আনন্দমেলা গোগ্রাসে পড়ত পাঠকেরা। সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্র নামের মাধ্যমটির যে দলাদলি নেই গলাগলি আছে সম্পাদক হিসেবে তা বিশ্বাস করতেন বলেই গুপী বাঘার গান ছাপা হয়েছিল আনন্দমেলার পাতায়। শরদিন্দুর সদাশিব তরুণ মজুমদারের ‘চিত্রনাট্য’য় বিমল দাসের ছবিতে অনবদ্য। কিশোর-কিশোরীদের জন্য পত্রিকা চালাতে গেলে যে শুচিবায়ুগ্রস্ত হতে নেই, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উদার হতে হয় এই কাণ্ডজ্ঞান তাঁর ছিল। তাই বিদেশি টিনটিনকে বাঙালি করে তুলতেও এই পত্রিকা দ্বিধা করেনি। সেই কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন স্বয়ং সম্পাদক।
পাক্কা বাঙালি বিদ্যাসাগর তো স্বভাবে এক দিকে খাঁটি ইংরেজ। শেক্সপিয়রের কমেডি অব এরর্স বিদ্যাসাগরের গদ্যানুবাদে ভ্রান্তিবিলাস, পড়লে বোঝাই যাবে না এ বিলিতি। বিদ্যাসাগরের নিজের চরিত্রে দেশি-বিদেশির এমন মিলমিশ বলেই বিলিতি গদ্য দিশি হয়ে ওঠে। নীরেন্দ্রনাথের কাজটা আরও শক্ত। টিনটিনের মূল ছবি তো বজায় থাকবে, তা বজায় রেখেই কেবল ভাষার গুণে ক্যাপ্টেন-টিনটিন-ক্যালকুলাস বাঙালি হয়ে উঠল। অনুবাদে বাংলা ভাষার সীমাকে যেমন তিনি সম্প্রসারিত করলেন তেমনি বাংলা ভাষার অল্পবয়স্ক পড়ুয়াদের ভাষাটির প্রতি মনোযোগী করে তোলার জন্য কাজে লাগালেন ভাষাবিদ পবিত্র সরকার ও কবি শঙ্খ ঘোষকে। ইস্কুলে ইস্কুলে তখনও ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের মতোই তেতো বাংলা ব্যাকরণ পড়ানো হত, আনন্দমেলার পাতায় কিন্তু প্রকাশিত হত ‘বাংলা বলো’। মুখের সজীব বাংলার রীতি-নীতি তাই ‘আমেরিকা ফেরত’ পবিত্র সরকারের লেখার বিষয়। শঙ্খ ঘোষ কুন্তক ছদ্মনামে লিখতেন শব্দ নিয়ে খেলা। ‘বানানের শুদ্ধি-অশুদ্ধি বিচার’ নিয়ে এমন সহজ-গভীর বই বাংলায় দু’টি নেই। ভাষার ছন্দ-ব্যাকরণ যে ক্লাসঘরে গম্ভীর মুখে আলোচনার বিষয় নয়, তা যে বৈঠকি-মেজাজে আড্ডার উপকরণ তা বিশ্বাস করতেন বলেই তো নীরেন্দ্রনাথ নিজেও কাগজের পাতায় লিখতে সাহস পেয়েছিলেন কবিতার ক্লাস। এমন মুচমুচে ছন্দ শেখার বইও বাংলা ভাষায় দু’টি হবে না।
বাংলা ভাষার প্রমিত রূপ নির্মাণের যে চেষ্টা তাঁর সম্পাদনায় আনন্দমেলার পাতায় শুরু হয়েছিল, পরে তা সম্প্রসারিত রূপ পেল। বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন নামের বিধিগ্রন্থ নীরেন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছিলেন। ঢাকা বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত দু’খণ্ডের প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণের অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন তিনি। চলিতের প্রতি, পথচলতি মানুষের প্রতি তাঁর বরাবর পক্ষপাত। তখন তিনি ল কলেজের ছাত্র, আজ়াদ-হিন্দ ফৌজের বন্দি সেনাদের মুক্তির ছাত্র-আন্দোলনে পুলিশি হামলা। রাস্তার ওপর চাপ-চাপ রক্ত, ছেঁড়া বইখাতা, চপ্পলের পাটি, ভাঙা চশমা। নিহত হলেন তরুণ রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৪৫-এর নভেম্বর মাসের সেই ঘটনা নিয়ে লেখা কবিতা ‘শহিদ রামেশ্বর’। দেশ পত্রিকায় পাতা জুড়ে ছাপা হল। নীরেন্দ্রনাথের বহুশ্রুত জনপ্রিয় কবিতাগুলিতে পথ ও মানুষ মিশে যায়। সমস্ত শহর যারা মন্ত্রবলে থামিয়ে দিতে পারে সেই কলকাতার জিশুদের নানা ভাবে দেখতেন তিনি। পথের মানুষদের সম্বন্ধে বিশ্বাস দৃঢ় ছিল বলেই এক সময় জীবনানন্দের কবিতায় তিনি দেখেছিলেন ‘আত্মঘাতী ক্লান্তি।’ জীবনানন্দ সমালোচনায় ক্রুদ্ধ না হয়ে ‘শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রীতিভাজনেষু’ লিখে বার্তা বিভাগে রেখে এসেছিলেন অনুজের জন্য এক কপি ধূসর পাণ্ডুলিপি। মতভেদ হতেই পারে, সৌজন্য বজায় থাকবে না কেন!
বিশ্বভারতীতে বাংলার শিক্ষক