আলোকদায়িনী কথাটা শিখেছিলাম সেই কোন ছেলেবেলায় আমার বুড়ি দিদিমার কাছ থেকে। যদিও একটু ভিন্ন গোত্রের আঞ্চলিক শব্দমালায়। টুকটুকে ফরসা, ভারি মধুরদর্শনা আমার দিদিমা ছিলেন ঠাকুর-দেবতা বিষয়ে যাকে বলে একেবারে জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া। তা, দিদিমাই আমায় জানিয়েছিলেন, মহালয়ায় মা দুগ্গার কাছে ‘পোস্টোকাড’ যায় ‘পিথ্থিমী’ থেকে— যাতে খুলেমেলে লেখা থাকে: ছেলেপুলে আর জামাই বাবাজিকে নিয়ে দুগ্গা যেন অবশ্যই ষষ্ঠীর দিন সকাল সকাল চলে আসেন আমাদের এই ‘পোড়া মাইন্ষের দ্যাশে’, কোনও ভুল না হয় তাতে। আর বাপের বাড়ির সেই ‘বচ্ছরকার’ আমন্ত্রণ ফেরাতে পারেন না বলেই ফি-বছর দুর্গা মা আসেন প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে— আমাদের মাঝে ক’দিন কাটিয়ে যাওয়ার তাগিদে।

আমার তখন বয়স কম। সবে ক্লাস থ্রি বা ফোর। উত্তেজনায় কয়েকটা কথা তাই না জিজ্ঞেস করে পারিনি দিদিমাকে। যেমন ওই পোস্টকার্ড মা’কে পাঠায় কে? তাতে কোন ঠিকানাই বা লিখে দেয় ইত্যাদি ইত্যাদি। জবাবে দিদিমা একেবারে হায় হায় করেই বলেছিলেন, “ওরে বাবা, সে সব হল গে কাশী-বেন্দাবনের বড় বড় মহারাজদের চিঠি। কৈলাশের কোন গোপন গুহার কোন থানে পাঠান তাঁরা, আমারে-তোমারে কি বলবে? তা ছাড়া, ও সব জানারও তো ‘মেলা বেপদ’— ঘরবাড়ি ছেড়ে সাধুসন্ত হয়ে ‘একবস্তে’ চলে যেতে হয়! বালাই ষাট, তুমি ও-ভাবে যাবে কেন দাদু? ‘পড়ালেখা’ শিখে তুমি হবে কিনা ‘ম্যাজিস্টার’! তোমার অমন শিবের বাড়ি খোঁজায় কাম কী?”
কৈলাসের ঠিকানা নিয়ে কিছুটা লুকোছাপা থাকলেও আমায় অবশ্য দুগ্গা মায়ের পৃথিবীতে আসার গোপন রাস্তাটা চিনিয়ে দিয়েছিলেন দিদিমাই। খুব ভোরে সূর্য ওঠারও আগে আবছা মেঘের গায়ে যখন সবে ‘পাটকিলে গাইয়ের বকনা বাছুরের’ রং লাগে, ঠিক তখনই নাকি এক একটা মেঘের স্তূপে পা ফেলে ফেলে মা নামতে থাকেন ধরাধামে। এ দিকে মায়ের সেই পদ্মকলি পায়ের ছোঁয়া লাগতেই মেঘের রং অমনি একেবারে ‘দুধে-আলতা বন্ন’ হয়ে ওঠে— আর সকাল হয়ে গেছে টের পেতেই মন্দিরে মন্দিরে পূজারীরা ‘মা, মা’ করে ‘পেন্নাম’ ঠোকে, শাঁখ বাজে, কাঁসর বাজে! লোকে বুঝে যায়, রাজরানির বেশে রাজার-দুলালী মা এসে গেছেন এ বার ঘোর কাঙালের দেশে!
আকাশে-বাতাসে মাঠে-ময়দানে গ্রাম কি শহরে, গঞ্জ বা মফসসলে মায়ের আগমনের এই ছবিখানা পঞ্চাশ বছর আগে আমার ছেলেবেলায় যেমন ছিল, আজও দেখি তা একটুও বদলায়নি। এ জন্যই মাঝে মাঝে কেমন মনে হয়, যে যা-ই বলুক না কেন, আগেকার পুজো আর এখনকার পুজোয় তেমন কিছুই বড়সড় তফাত নেই। এই এখন যেমন পুজোর আগে আকাশ মেঘলা দেখলে ছোট ছেলেমেয়েদের চোখে জল আসে, তখনও ঠিক তেমনই ছিল। সেই একই মেঘ, রোদ, বকাঝকা বা একটু আদর— এই পরীক্ষার ভয়ে জড়সড় তো ওই ছুটির আনন্দে থরোথরো। হুবহু একই ব্যাপার। এমনকী, জামাকাপড়ের নতুন গন্ধের সঙ্গেই নতুন জুতোর নতুন নতুন ফোস্কাদেরও দিব্যি গলাগলি, ঢলাঢলি। তা হলে আর আলাদা কী রইল?

আপনারা হয়তো বলবেন, কেন, এখন যে প্রায় সব জায়গাতেই ‘থিম পুজো’ হয়, তখন কি এ সব ছিল? তো, এ ব্যাপারে আমার একছিটে নিবেদন আছে। তা হল, ‘থিম’ শব্দের প্রয়োগ তো এ-ক্ষেত্রে ‘মূল ভাবনা’ বোঝাতেই— মানে কিনা ভাবনীয় যে বিষয়টিকে বিশেষ ভাবে উপস্থাপিত করা হচ্ছে, তার বাহাদুরি নিয়েই যত কেতা দেখানো! তা, সে ব্যাপারে আমাদের কালের একটু গ্রাম্য ও সাদাসিধে কালীবাবুরাই বা ক্রেডিট-লাইন পাবেন না কেন, শুনি? একটু বুঝিয়ে বলি। আমার শৈশবের গ্রাম পল্লিশ্রীর প্রায় সব পুজোতেই কালীবাবুর আঁকা বহুবর্ণ একেকটি ‘ব্যাকড্রপ’ থাকত পৌরাণিক নানা টগবগে কাহিনির বর্ণনায় ভরা। যেমন কোনও প্যান্ডেলে মা-দুগ্গার পিছনে আকাশপথে দেবাসুরের যুদ্ধ তো আর এক প্যান্ডেলে নিজের চোখে তির বিঁধিয়ে রামচন্দ্রের ১০৮ খানা নীলোৎপল জোগাড়ের চেষ্টা। কোথাও মায়ের দু’পাশে ওলটানো ধনুকের মতো দশমহাবিদ্যার দশ রকম রূপ তো কোথাও বা সতীর দেহ পিঠে নিয়ে বাঘছাল পরা মহাদেবের এক লাথিতে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের ভিস্যুয়াল। আহা, নিছক কিছু একটেরে টাইপ ‘ক্লথ পেন্টিং’ হলেও বিলকুল উড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপার নয় নিশ্চয়ই! এই কালীবাবুকেই তো দেখেছি, কালীপুজোয় শ্মশানবাসী পিশাচিনী বনাম অসুরদের কী সাংঘাতিক ‘বোল্ড অ্যান্ড বেয়ার’ লড়াই-দৃশ্য আঁকতে। আবার সরস্বতীপুজো এলে সেই ভাবনার অভিমুখকেই একেবারে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে নিয়ে, কালিদাসকে যত দূর সম্ভব বোকা বোকা মুখে নিজ বৃক্ষশাখা-ছেদনের কাজে লাগিয়ে দিতে! তা, এত বছর পর সে-সব ভাবনাচিন্তা একটু বেশি রকম হাস্যকর ঠেকলেও— তখনকার কালীবাবুরাই কি আজকের এই সব থিম্যাটিক পুজোর বেবাক ক্রিয়েটিভ শিল্পীর ‘ফোরফাদার’ নন? কথাটা একটু ভেবে দেখবেন।
অবশ্য এই সব থিমটিমের ব্যাপার ছেড়ে এ বার নয় গত অর্ধশতক ধরে আমার দেখা নানা মাপ ও মানের মাতৃবন্দনা ও তার আলোড়ন-আয়োজন নিয়ে একটু বলি। ষাটের দশকের প্রায় পুরোটা জুড়েই পার্বতীর পিত্রালয়ে আগমনের আনন্দ-অনুষ্ঠান বলতে আমার কাছে যেন দুর্মূল্য ডাকটিকিটের মতোই এক একটি বিরল স্মৃতির সঞ্চয়! এখনকার ছেলেমেয়েরা কি কখনও ভাবতে পারবে— বাতাসে পুজোর গন্ধ লাগতে না লাগতেই, আকাশে ক’টুকরো সাদা মেঘ কি নীচে ক’খানা সাদা কাশ-শিউলি জাগতে না জাগতেই পাড়ায় পাড়ায় অদ্ভুত এক একটি সাজে বহুরূপীরা এসে হাজির হত গৃহস্থের দরজায়! কখনও শিবদুর্গা তো কখনও রামসীতা বা রাধাকৃষ্ণর জুটি। এ ছাড়াও নানা সাধুসন্ত, মুনিঋ
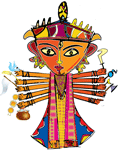
ষির বেশে, এমনকী স্রেফ বাঘ, সিংহ বা ভক্ত হনুমান সেজেও পাড়ায় ঢুকতে দেখেছি ওই বিচিত্র পেশার মানুষজনকে। আজ হয়তো অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু ওরা এলে এমন কোনও বাড়ি দেখিনি যেখানে মা-মাসিরা কপালে একবার হাত ছুঁইয়ে চাল-আনাজ-টাকাপয়সা সাধ্যমতো যা-হোক কিছু অন্তত না দিয়েছেন। পড়াশোনা গোল্লায় দিয়েও পাড়া-বেপাড়ার অচেনা পথেঘাটে ওই সঙের পিছনে কত যে ঘুরে বেড়িয়েছি, তা শুধু ঈশ্বরই জানেন!
আগে না পরে ঠিক মনে নেই, তবে মোটামুটি পুজোর সময় দিয়েই গ্রামে বহুরূপীর চেয়েও আকর্ষক একটা ব্যাপার ঢুকে পড়েছিল ওই ষাট দশকেরই গোড়ার দিকে। তা হল, মাঠেঘাটে বড় একখানা ঝ্যালঝেলে সাদা পরদা টাঙিয়ে, তাতে পুরনো কোনও সাদা-কালো বাংলা ছায়াছবি দেখানো। ঠিক ও ভাবেই আমাদের বাগানবাড়ির জমিতে বসে ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে এক রাতে ‘ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ দেখাটা ছিল আমার প্রথম সিনেমা দর্শন! পরে ‘লালু ভুলু’ বা ‘বাদশা’ও মাঠ-মেহফিলের ওই একই পথ ধরে, মনে আছে।
আর একটা ব্যাপার ছিল গ্রাম্য বা মফসসলি দুর্গাপুজোর একেবারে বাঁধা ব্যাপার। তা হল মেলা। পুজোর শামিয়ানার গা ঘেঁষেই বা হয়তো বড়জোর পাশের মাঠে পেট্রোম্যাক্সের আলোয় কী জমজমাট যে সেই মেলা চলত ষষ্ঠী থেকে একেবারে দশমীর রাত পর্যন্ত, তা আর বলার নয়। হাজারো জিনিসের বেচাকেনা, হরেক খাবারের পশরা উপচেও নাগরদোলা আর চাঁদমারির পাশে ভিড় যেন কমতেই চাইত না। আজও ভোররাতের স্বপ্নে কখনও-সখনও সেই মেলার হ্যাজাক জ্বলতে দেখি, চার পাশে সংখ্যাহীন পোকার ওড়াউড়ি নিয়ে। বেলুনওয়ালার যে রঙিন বেলুনগুলো কখনও কিনতে পারিনি, সেগুলোই সুতো ছিড়ে দূরে উড়ে যায়। ইয়াব্বড় জিলিপির দোকানিটি আমার দিকেই খুব হাতছানি দেয়। আর হঠাৎই সে সব মুছে, রংচটা পুরনো নাগরদোলার এক কেঠো সিংহাসন থেকে ‘ডালিয়া’ নামে কবেকার নওল কিশোরী এক প্রতিমার মতো তার পানপাতা মুখ তুলে বলে, ‘ভিতু কোথাকার!’

আর এক মেগা ইভেন্টের কথা অবশ্য কিছুই বলা হয়নি এখনও। পুজোর জলসা। তবে তারও আগে বোধহয় পুজোর গান নিয়ে কিছু বলা দরকার। ষাটের দশকের প্রায় পুরোটা জুড়েই টিপিক্যাল পুজোর গন্ধ বলতে আমার কাছে শুধুই গান আর গান। মনে রাখতে হবে, সে এক এমন যুগের কথা, যখন টিভি-কম্পিউটার-মোবাইল-ইন্টারনেট আমাদের কাছে গ্রহান্তরের ব্যাপার— এমনকী, সামান্য একটা রেডিও বা টেলিফোনও সারা গ্রাম ঘুরলে দু’টির বেশি জোটে না। তা, এ হেন কালেই পঞ্চমী বা ষষ্ঠীর রাতে হঠাৎ যখন ‘যুগবাণী’ বা ‘যুবসংঘ’র ব্যাটারি লাগানো মাইক থেকে ভেসে আসত ‘কে যায় সাথীহারা মরু সাহারায়’, ‘তুমি আর ডেকো না’ কিংবা ‘যদি কোনও দিন ঝরা বকুলের গন্ধ’ গোছের পাগল-করা কোনও গান— সত্যি বলতে কী, তা ছিল আমার মতো বানভাসি ছেলের পক্ষে এক গভীর সর্বনাশ! ঘুমহীন রাতের পর রাত এ জন্যই উড়েপুড়ে গেছে ওই সুরের নিশিডাকে!
তা, এ সব গানের প্রায় অধিকাংশ গায়ক-গায়িকাকেই তখনকার পুজো-জলসায় প্রায় হামেশাই দেখা যেত পাড়ায় পাড়ায়। ছেলেবেলায় আমি বেশির ভাগ জলসাই দেখেছি মহাষ্টমীর রাতে। মনে আছে, সেখানে বাঁশের সীমানার দু’পাশে দর্শকাসনের পুরুষ ও মহিলাদের থইথই ভিড়ের মধ্যে গোড়ার দিকেই স্টেজে উঠতেন সনৎ সিংহ, মৃণাল চক্রবর্তী, ইলা বসু, বনশ্রী সেনগুপ্ত কি পিন্টু ভট্টাচার্য। তার পর একে একে দ্বিজেন, সতীনাথ, উৎপলাও স্টেজ ছাড়ার পর ভারি হাসিমুখে গাইতে বসা তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় কি মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়— এবং তাঁরাও মাতিয়ে যাওয়ার পর কোকিলকণ্ঠী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় যখন শ্রোতাদের প্রায় অবশ করে দিয়ে বিদায় নিচ্ছেন, তখনই অনুষ্ঠানের ‘শেষ আকর্ষণ’ হিসাবে ঘোষণা করা হত শ্যামল মিত্র বা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নাম। ওঁদের নেশা ধরানো অজস্র গান শেষ হতে প্রায়ই ভোর হয়ে যেত।
এই সব বারোয়ারি আয়োজনের পাশে এ বার নয় পুজো নিয়ে কিছু ঘরোয়া আলোড়নের কথা বলি। মহালয়ার কাকভোরে বাবার একরত্তি ট্র্যানজিস্টর সেট থেকে গায়ে কাঁটা দেওয়া ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ শোনারও কম করে দিন দু’-তিনেক বাদে বাবা পুজোর বাজার করতে নিয়ে যেতেন আমাদের বেশ দূরের এক ‘মন্দের ভাল’ জনপদে। সেখানে বাবার ভয়ে আমরা পিঠোপিঠি তিন ভাই যেতাম একেবারে বোবার মতন। কেননা বাবার কড়া নির্দেশ ছিল, পছন্দ-অপছন্দ তো দূর অস্ত—বাজারঘাটে একটা টুঁ শব্দও করা যাবে না কেনাকাটা নিয়ে। যাই হোক, এ বার একটু জানানো যাক সেই কেনাকাটার বাহারের কথা। তিন ভাইয়ের জন্য দু’টি করে শার্ট আর দু’টি করে হাফপ্যান্টের কাপড়, সাদা আর নীল রঙে— যা কিনা আদতে আমাদের স্কুল ইউনিফর্মেরই রং এবং কাপড়ের ওই দোকানিই যা সেলাই করে দিত আমাদের তেরাত্তির পোহানোর আগেই। জানি না, এখনকার ছেলেরা কেউ ভাবতে পারবে কি না, কলেজে ওঠা পর্যন্ত কমবেশি গোটা একটা দশক ধরেই এই ছিল শ্মশান থেকে রাজদ্বারে যাওয়ার একটাই বেশ আমাদের! কেন না বাবার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, পুরুষের পক্ষে অতিরিক্ত সাজগোজ মানেই মূর্খতার চাষবাস করা! সেই একই যাত্রায় অবশ্য মা ও দিদির জন্য বেশ দামি পোশাকই কেনা হত এবং আমরা তা নিয়ে বেশ গর্বও করতাম বন্ধুদের কাছে। যদিও এই ব্যাপারে শেষ কথাটি এই যে—ওই পুজোর বাজার থেকে কদাপি নিজের জন্য একটি গেঞ্জিও কিনতে দেখিনি বাবাকে। যা কিনতেন, তা বছরের অন্য সময়ে। হয়তো সস্তা বাজারের সুবিধাতেই। নিজের বিশ্বাসটুকু নিজের জীবনেই পালন করে দেখানোর মতো অমন দুঃসাহস আর দেখিনি কোথাও!

পুজোর দিনগুলোয় বাঙালির বাড়িতে বাড়িতে যে নানা ঘরোয়া মিষ্টান্ন তৈরি হয়, তার সবটুকু তো করেন বাড়ির মহিলারাই, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের বাড়ি ছিল একেবারেই ভিন্ন গোত্রের। নারকেল ছাড়ানো থেকে ক্ষীর বানানো, গুড়ের পাক দেওয়া, নাড়ু তৈরি বা ছাঁচের সন্দেশ তৈরির প্রতিটি ধাপেই মায়ের পাশে যেন ছায়ার মতোই জড়িয়ে থাকত বাবার সম্পূর্ণ অহংহীন, নিপুণ হাতের ছোঁয়া।
এ বার নয় সটান মণ্ডপের ভিতরেই ঢোকা যাক। ধূপের গন্ধে, ধুনোর সুবাসিত মাদকতায় কেমন এক দৈবী ভাবের আজব ঘোর লেগে থাকত যেন সেখানে। আমাদের এলাকার সবচেয়ে অভিজ্ঞ পুরোহিত ছিলেন অক্ষয় চক্রবর্তী। কণ্ঠশিল্পী পিন্টু ভট্টাচার্যের অত্যন্ত নিকট আত্মীয় এই সহজ-সরল ও সদালাপী মানুষটির কী অসাধারণ নিষ্ঠা ছিল মন্ত্রপাঠ ও পূজাচারে, এখনও যেন স্পষ্ট টের পাই। তখনকার প্রতিমা হত মূলত দু’ধরনের। এক রকম তো ছিল আটচালার ঠাকুর— মাটির বা শোলার। আর এক রকম শুরু হয়েছিল কিছুটা পরের দিকেই— নানা ভঙ্গিমার আলাদা আলাদা সব ঠাকুর। সেগুলোকে বলা হত ‘আর্টের ঠাকুর’! এই ধরনটাই এখনও রয়ে গিয়েছে দেখি, নানা ভাবে মডিফায়েড হতে হতেও। তবে মাইকের ব্যবহার এখন অশ্লীল রকম বেড়ে গেলেও অন্য দু’ একটা ব্যাপার যে যথেষ্ট কমেছে, তা বেশ টের পাই ‘ঢাকের লড়াই’, ঢাক কাঁসরের ‘সওয়াল-জবাব’ কিংবা ‘আরতি প্রতিযোগিতা’র খামতি দেখতে দেখতে। এই আরতি নিয়ে কিছুটা হাস্যকর একটা স্মৃতি আছে আমার। ‘আমার’ বলতে অবশ্য আমার পরের ভাই দেবনকে নিয়ে। ধারালো চেহারায় একেবারে কৃষ্ণ ঠাকুরটির মতোই মুখচোখ হলেও অল্প বয়সে ভারী মুখচোরা ছিল ও। তা, আটষট্টির শেষাশেষি পল্লিশ্রী ছেড়ে আমরা বহু দূরের এক মফসসল শহর গৌরীপুরে চলে যাওয়ার ঠিক পরের বছরেই ওখানকার এক দুর্গাপুজোর আসর থেকে ও আমাদের একেবারে চমকে দিয়েই বড়সড় একটা কাপ জিতে আনে ‘দ্বিতীয় পুরস্কার’ হিসাবে। অথচ আমরা কিনা কখনও জানতামই না যে ও অত ভাল নাচতে পারে। অবশ্য আমাদের না জানা আর একটা ব্যাপারও ওই প্রতিযোগিতার বিচারকই মাইক-মারফত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন— “নাচের মধ্যে অন্তত এক বার প্রতিমার দিকে পশ্চাৎভাগ প্রদর্শন করার জন্যই দেবন বসুকে প্রথম পুরস্কার দেওয়া গেল না!” না, শেখার কি আর শেষ আছে?


তো, পর দিন সকালে কোনও প্যান্ডেলে নয়, মন্দিরে নয়— স্রেফ আমাদের পুবের বারান্দাতে দাঁড়িয়েই আমার দেবীদর্শন হয়ে গিয়েছিল, যখন আমার মা এক রকম জোর করেই তপনের হাতে আমার সে বছরের দুটো সাদা শার্টের একটা তুলে দিতে দিতে বলেছিল, “আহা বাবা, ধরো না তুমিও আমার একটা ছেলেই! মা ছাড়া আর কে দেবে ছেলেকে!”









