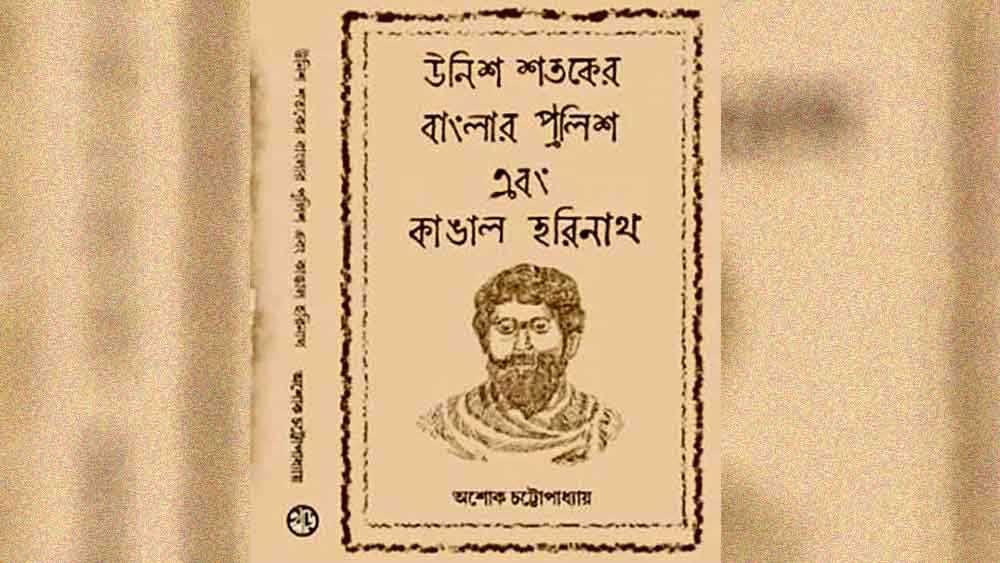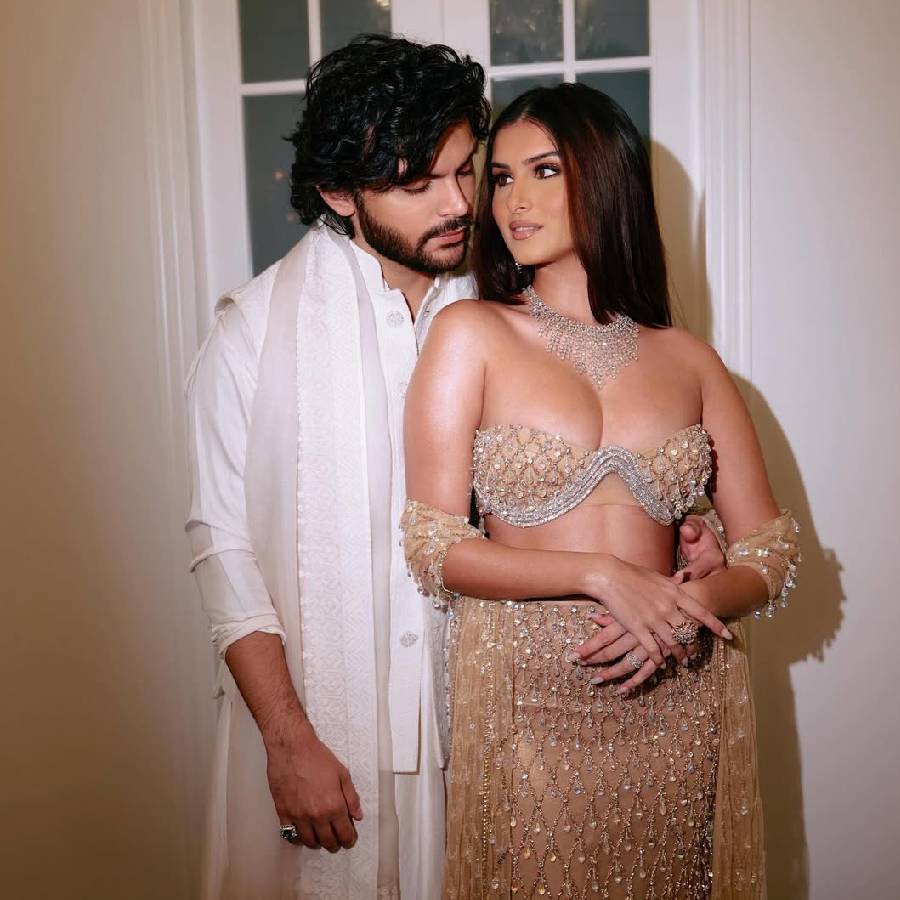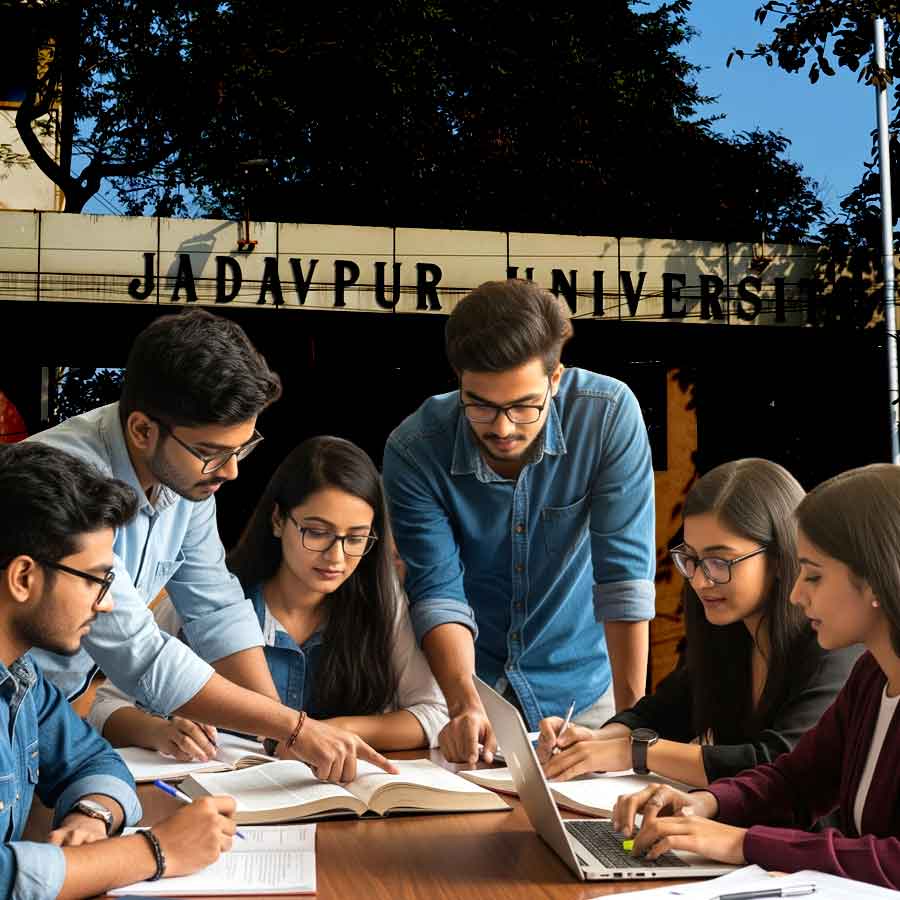উনিশ শতকের বাংলার পুলিশ ও কাঙাল হরিনাথ
অশোক চট্টোপাধ্যায়
২৭৫.০০
খড়ি প্রকাশনী
বিশ শতকের গোড়ায় বাংলাদেশে একটা কথার চল ছিল: “মারের শেষ ঝাঁটার বাড়ি, চাকুরির শেষ দারোগাগিরি।” বেকারত্বের জ্বালা যতই হোক, পুলিশের চাকরিতে কেউ যোগ দিতে চাইত না। এমনকি যাঁরা এই জীবিকায় যুক্ত তাঁরাও প্রার্থনা করতেন, কোনও ভদ্রসন্তান যেন এই চাকরিতে না আসেন। কারণ, তিক্ত অতীত।
রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “পুলিস একবার যে চারায় অল্পমাত্র দাঁত বসাইয়াছে সে চারায় কোনও কালে ফুলও ফোটে না, ফলও ধরে না। উহার লালায় বিষ আছে।” উনিশ শতকের পুলিশি কার্যকলাপ তার যথার্থ সাক্ষ্য দেয়। পল্লিগ্রামে পুলিশ উপস্থিত হলে রাতারাতি পাড়া খালি। তদন্তের নামে নির্বিচার ধরপাকড়, জবানবন্দি আদায়ের জন্যে নির্যাতন, কথায়-কথায় নজরানা দাবি। জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে গৃহস্থের বাড়ি হাজির হয়ে গোড়ায় কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য না পেলেই সিঁদুরে মেঘ। অবশ্য মুড়ি-মিছরির দর এক নয়। পদমর্যাদার সঙ্গে গৃহকর্তার তবিল হালকা হত। ছিল উৎসব উপলক্ষে পার্বণী, নতুন দারোগার জন্য চৌকিদারপিছু নজর-সেলামি, মরসুমি উপরির বন্দোবস্ত। অতিরিক্ত আয়ের যোগফলে মাইনে বেড়ে যেত সাত-আট গুণ। ব্রিটিশ প্রশাসনে দুর্নীতি ও দারোগাগিরির সমীকরণ নতুন নয়। এর পিছনে দায়ী করা যায় অপর্যাপ্ত বেতন কাঠামো ও অযোগ্য কর্মচারী নিয়োগকেও। আশ্চর্য যে, সামান্য সাত টাকা মাইনে পেতে কনস্টেবলদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল ১৮৯০ পর্যন্ত। আবার, উঁচুতলায় ব্রিটিশ-নেটিভ বেতন অসাম্য। ফলে শিক্ষিত বাঙালিদের মূলত আগ্রহ ছিল কেরানিগিরিতে। দারোগা গিরিশচন্দ্র বসু পুলিশি অত্যাচারের কারণ হিসেবে আঙুল তুলেছিলেন ম্যাজিস্ট্রেটদের দিকেও। দ্রুত মামলার নিষ্পত্তির জন্য কখনও দারোগাদের সময় বেঁধে দেওয়া হত। আশু কার্যসমাধায় অকুস্থলে আকছার তাণ্ডব চলত। এই পূর্বস্মৃতিই সাধারণ মানুষের থেকে থানাদারদের ক্রমশ দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।
এর স্মৃতিকার কারা? গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ, একাধিক সাংবাদিক। তাঁদেরই এক জন কাঙাল হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬)। গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা-র পাতায় শুধু রাজকর্মচারী নয়, জনতার প্রতিনিধি হিসেবে যিনি বার বার প্রশ্ন রাখেন রাজার কাছেই। গ্রাম-মফস্সলের মর্মন্তুদ ছবি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে বাধার সামনে পড়েছেন, অর্থের বিনিময়ে সত্য চাপা দেওয়ার জন্য তাঁকে কিনে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন জমিদারেরা। তবুও ভূস্বামীদের দাপটে গ্রামবাংলার রায়ত-প্রজার দুরবস্থা বিবৃত করার পাশাপাশি প্রশাসনের নগ্ন দিকটি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তিনি। নানা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে দুর্নীতির সঙ্গে পুলিশের সংযোগ, নীলকরদের সঙ্গে যোগসাজশ, জেলবন্দিদের উপর অত্যাচার, উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের চারিত্রদৌর্বল্য। হরিনাথ নিন্দায় নির্মম, প্রশংসায় অকুণ্ঠ। শিরদাঁড়ার জোরে জানিয়ে যাওয়া খবরগুলো সামনে রেখে উনিশ শতকের গ্রামবাংলায় ব্রিটিশ পুলিশ-প্রশাসনের বাস্তব চিত্র হাজির করেছেন গবেষক অশোক চট্টোপাধ্যায়। স্বল্পায়তন গ্রন্থে গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা-র পাশাপাশি ইংরেজি ও বাংলা সংবাদপত্রের প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে উনিশ শতকের পুলিশিব্যবস্থার বিবর্তনের পর্যায়কেও ধরার চেষ্টা করেছেন। পরিশিষ্ট অংশে সংবাদপত্রের প্রতিবেদনগুলির পূর্ণাঙ্গরূপ ও বিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জি গুরুত্বপূর্ণ। কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের জীবন সাহিত্য ও সমকাল, উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলন কাঙাল হরিনাথ ও ‘গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা’-র পরে লেখকের এই বই উল্লেখযোগ্য সংযুক্তি।