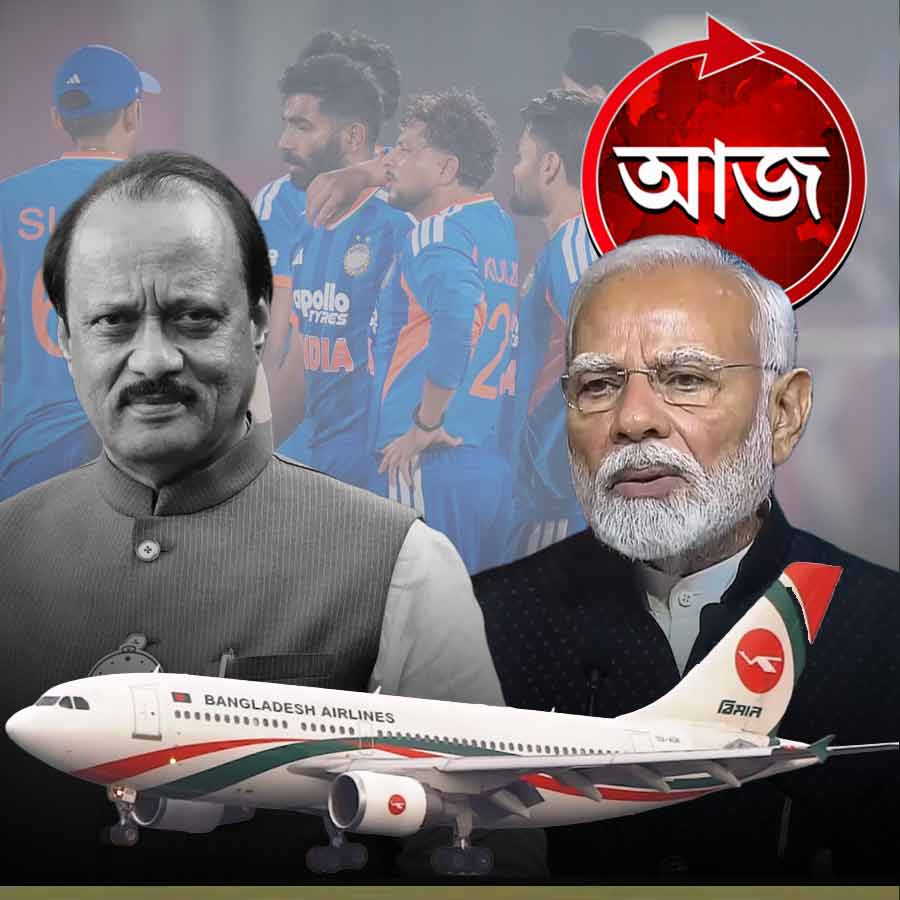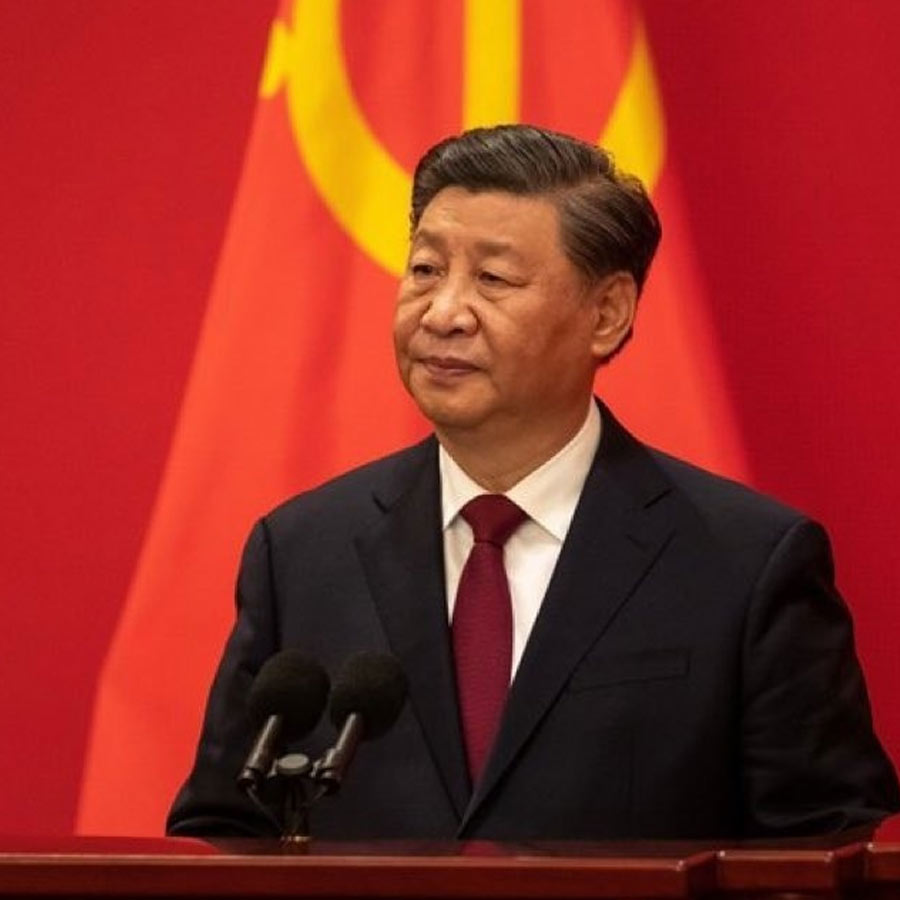সারা পৃথিবীর মতো আমাদের দেশেও অধিকাংশ ব্যবসাই চলে ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণের ওপর ভিত্তি করে। এই ঋণভিত্তিক অর্থায়নের প্রক্রিয়ায় ব্যবসায়ীদের ঋণের একটা নির্দিষ্ট অংশ নিয়মিত সুদ সমেত পরিশোধ করে চলতে হয়। যদি সেই নিয়মে ছেদ পড়ে, ঋণের ওপর সুদের অঙ্কটা বাড়তে থাকে লাফিয়ে লাফিয়ে— যার পুরোটাই পরবর্তী কালে পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক। কোনও ব্যবসায়ী যদি তা না করতে পারেন, তা হলে তাঁকে ডিফল্টার বা ঋণখেলাপি বলে চিহ্নিত করা হয়।
এই দীর্ঘ লকডাউনের জন্য আমাদের দেশে বহু ব্যবসায়ীই— বিশেষ করে, ছোট বা মাঝারি মাপের ব্যবসায়ী (মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ়েস বা এমএসএমই)— এক রকম বাধ্য হয়েই কয়েক মাসের মধ্যে ঋণ খেলাপের পথে হাঁটবেন, এমন একটা আশঙ্কা তীব্র হচ্ছিল। তার কারণ, লকডাউনের দরুন দীর্ঘ দিন ব্যবসা বন্ধ থাকার ফলে তাঁরা নিয়মিত ঋণের কিস্তি ও সুদ পরিশোধ করতে পারছেন না। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে যাঁরা ব্যবসা করছেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় ৪৪% মার্চ মাসে সুদ পরিশোধ করতে পারেননি। এই ঋণ জমতে জমতে যখন কয়েক মাসের মধ্যে ঋণের পাহাড়ে পরিণত হবে, তখন এঁদের ঋণখেলাপি হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের কোভিড-১৯ প্যাকেজে এমএসএমই ক্ষেত্রকে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, অনুমান, তার পিছনেও আছে এই আশঙ্কা।
এটা ঠিকই যে ব্যবসায়ীদের ঋণখেলাপি হওয়াটা অস্বাভাবিক কোনও ঘটনা নয়। তবে যেটা অস্বাভাবিক, সেটা হচ্ছে বহু ব্যবসায়ীর একই সঙ্গে ঋণখেলাপি হয়ে পড়াটা। এই ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্য রকমের বেশি এই দীর্ঘ লকডাউনের পরবর্তী কালে। সাধারণ সময়ে কিছু ব্যবসায়ী ঋণ খেলাপ করলেও, বাকিরা কিন্তু ঠিক সময়ে নিয়মমাফিক তাঁদের ঋণ পরিশোধ করে চলেন। যার ফলে, ঋণখেলাপিদের জন্য ব্যাঙ্কগুলির যে আর্থিক ক্ষতি হয়, সেটা পূরণ হয়ে যায় অন্য ব্যবসায়ীদের ঋণ পরিশোধ করার ফলে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে, বহু ব্যবসা এক সঙ্গে ঋণখেলাপি হয়ে উঠতে পারে বলে, সেই ক্ষতিপূরণ হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। এর ফলে ভারতের গোটা ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, যা এমনিতেই অনুৎপাদক সম্পদের সমস্যায় জর্জরিত, তার অবস্থা বেশ শোচনীয় হয়ে উঠতে পারে। ব্যাঙ্কগুলোও হয়তো ঋণ দিতে অসম্মত হবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই।
এমএসএমইগুলোকে চাঙ্গা করার জন্য যে আর্থিক প্যাকেজের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে কি এই ধরনের বিপর্যয় এড়ানো যাবে? বলা হয়েছে, যে এমএসএমইগুলির ব্যাঙ্কে বকেয়া ঋণের পরিমাণ ২৫ কোটি টাকা বা তার কম, তাদের তিন লক্ষ কোটি টাকার নতুন ঋণ দেবে সরকার। এ ছাড়াও ঘোষিত হয়েছে ২০,০০০ কোটি টাকার সাবঅর্ডিনেট ঋণ। ব্যাঙ্কে যাঁদের ঋণ অনাদায়ী হয়ে আছে, তাঁরাও এই ঋণের সুবিধা পাবেন। এই ঋণগুলির জন্য সরকার ১০০% গ্যারান্টি কভার দেবে বলে জানানো হয়েছে। অর্থাৎ, ঋণ নিয়ে যদি কোনও এমএসএমই পরিশোধ করতে না পারে, তবে তার হয়ে সরকার ব্যাঙ্ককে সেই টাকা শোধ করে দেবে।
ধরা যাক, একটি এমএসএমই এই নীতির সুযোগে ঋণ নিয়ে তার একটা অংশ দিয়ে ব্যাঙ্কে তার আগের যা বকেয়া ঋণ ছিল, তা পুরোপুরি বা আংশিক ভাবে মিটিয়ে দিল। বাকি টাকা সংস্থার অংশীদারদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে ব্যবসার ঝাঁপ বন্ধ করে দিল। আজকের এই অনিশ্চয়তার পরিস্থিতিতে এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া মুশকিল। এর ফলে, এই সংস্থাটি যে নতুন ঋণ পেয়েছিল, তার পুরোটাই ব্যাঙ্কের কাছে অনাদায়ী হয়ে গেল। সেই ঋণের বোঝা, ঘোষণা অনুযায়ী, সরকারকে বহন করতে হবে।
এমএসএমইগুলো যদি ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির পথে না-ও হাঁটে, সরকারের ঘাড়ে বহু ঋণের দায় চাপতে পারে। কোভিড-১৯’এর প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য যদি ফের লকডাউন ঘোষিত হয়, ভবিষ্যতে যদি ফের দীর্ঘ দিনের জন্য ব্যবসা বন্ধ রাখতে হয়, তা হলে এমএসএমইগুলির পক্ষে নতুন ঋণ পরিশোধ করা দুঃসাধ্য হবে।
যদি ধরেও নিই যে ঘোষণামাফিক সরকার কোনও ভাবে এই খেলাপি ঋণের বোঝা বহন করতে সক্ষম হল এবং ব্যাঙ্কগুলি এ বারের মতো তাদের পুরনো ও নতুন ঋণের অনাদায়ী অংশটুকু সরকারের কাছে থেকে পেয়ে গেল, ব্যাঙ্কগুলি কি অদূর ভবিষ্যতে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের— যাঁদের ব্যবসা করার জন্য সত্যি ঋণের প্রয়োজন— আবার নতুন ঋণ দিতে চাইবে? যদি না চায়, তা হলে কিন্তু এই বিপুল ত্রাণ-ঘোষণায় ঋণের মূল সমস্যার সমাধান হবে না।
তা হলে, এই মুহূর্তে করণীয় কী? চাই অত্যন্ত দক্ষ ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা। যেমন ধরা যাক, সরকার আগামী কয়েক বছরের জন্য সম্পূর্ণ নতুন একটি স্বাধীন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারে (বা কোনও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে পুনর্গঠিত করতে পারে), যা কেবল কোভিড-১৯’এর ফলে ঋণখেলাপি ও অন্যান্য যে সমস্ত অর্থনৈতিক সঙ্কট, তার মোকাবিলা করার জন্য কাজ করবে। কোভিড-১৯’এর ফলে সৃষ্টি হওয়া আর্থিক সঙ্কটের চরিত্র আর পাঁচটা আর্থিক সঙ্কটের মতো নয়। তাই এর মোকাবিলা করার জন্য বর্তমান অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির (যাদের আরও নানা রকম কাজ থাকে) বদলে এই রকম একটি প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করাটাই সরকারের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
এই প্রতিষ্ঠানটি রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যাঙ্কগুলিকে দেওয়ার বন্দোবস্ত তো করবেই, তা ছাড়াও, এর কাজ হবে অর্থনীতির চাকা ঘুরতে শুরু করলে, বিভিন্ন পন্থায় গ্রহীতাদের থেকে ঋণ আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা (ঋণ পুনর্গঠন করা, ইত্যাদি)। আমাদের বিশ্বাস, সরকারের তরফ থেকে এই ধরনের পদক্ষেপ সম্ভাব্য বিপুল ঋণখেলাপির ফলে ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে ওঠাকে ঠেকাতে পারবে। এবং একই সঙ্গে এই সঙ্কটের সময়ে অর্থনীতির ভিত্তিকে মজবুত করতে সাহায্য করবে।
ইউনিভার্সিটি অব নটিংহাম বিজ়নেস স্কুল, ইংল্যান্ড