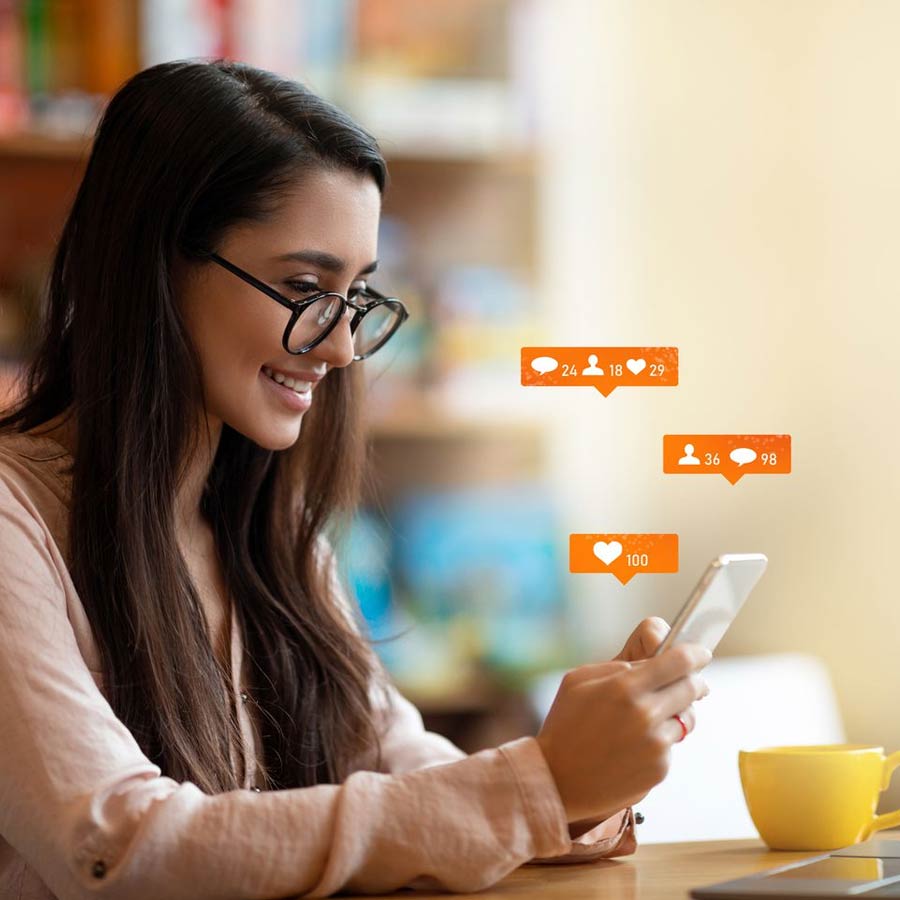‘‘তখন গড়পাড়ের বাড়িতে থাকি। ‘সন্দেশ’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আমার কাকা সুবিনয় রায়। সে সময় সন্দেশের দফতরে লেখা ও ছবি জমা দিতে আপনি নিজেই আসতেন। আর পরদার আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতাম আমি। আপনার সঙ্গে গল্প করে কাকা উঠে যেতেন আপনাকে এগিয়ে দিতে। আমি এক ছুটে ঘরে গিয়ে ছোঁ মেরে টেব্্লের উপর থেকে তুলে নিতাম সে ছবি। চাইতাম, আপনি আর আমার কাকা দেখার পর তিন নম্বর মানুষ যেন আমি হই, ওই ছবি দেখার অধিকারী। আপনার ড্রয়িংয়ের উপর মকশো করেই আঁকা প্র্যাকটিস করতাম আমি। ছবির প্রত্যেকটা লাইন আপনার কাছ থেকে শেখা,’’ সত্যজিৎ রায়ের গলার স্বরে তখন আনন্দ-শ্রদ্ধা মিলেমিশে একাকার। বিশপ লেফ্রয় রোডের বিখ্যাত বাড়িতে দীর্ঘদেহী সে মানুষটির সামনে বসে আমার বাবা। শৈল চক্রবর্তী। তাঁর চোখের জল সে দিন বাঁধ মানেনি। মানিকদা বলে চলেছেন, ‘‘আপনি বিরাট মাপের শিল্পী...’’ বাবার গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। আর আমি পাশে নিশ্চল। মানিকদা তখন গগনচুম্বী এক নাম, কিন্তু বাবা তত ‘বড়’ নন। সে দিন ওঁর চোখ দিয়ে বুঝেছিলাম, কী বিরাট গুণী মানুষ আমার বাবা!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি গল্পের ইলাস্ট্রেশন করেছিলেন বাবা
বন্ধুবান্ধব বা আর পাঁচজন পরিচিত মানুষের বাবারা যে রকম ছিলেন, তার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা রকমের মানুষ ছিলেন তিনি। ফ্রিলান্স শিল্পী হিসেবে সারাটা জীবন কাটিয়েছেন। রোজগারের অনিশ্চয়তা থাকলেও, বিষাদ তাঁকে কোনও দিন গ্রাস করেনি। জন্মেছিলেন হাওড়া জেলার মৌরিগ্রামে। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে অঙ্কে অনার্স নিয়ে পাশ করেছিলেন। বাবা লেখাপড়া শেষ করে প্রসাধন তৈরির একটা ছোট কারখানা বাড়িতেই বানিয়ে নিয়েছিলেন। সাবান, আলতা, সিঁদুর তৈরি করে বাড়ি-বাড়ি বিক্রি করতেন। কিন্তু সে ব্যবসা চলেনি। এ সময় বাবার সঙ্গে বিজ্ঞাপন জগতের একটা যোগাযোগ তৈরি হয়। এবং আঁকা, যা ছিল তাঁর শখ, ধীরে-ধীরে সে-পেশার দিকে অনুপ্রবেশের পথ তৈরি হতে থাকে।
যদিও আঁকা শেখায় বাবার কোনও শিক্ষাগুরু ছিল না। আর্ট কলেজে পা রাখেননি কোনও দিন। তবে অবজারভেশন ছিল তুখোড়। পত্রপত্রিকায় ইলাস্ট্রেশন করতে শুরু করেন ১৯৩০-এর দশকে। কমিক ছবির ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে এর আগে বাবার মতো সফল বোধ হয় আর কেউ হননি। যাই হোক, শুরুর দিকে বাবা গুরুত্ব দিয়েছিলেন ইলাস্ট্রেশনকে। এবং ইলাস্ট্রেশন করতে করতে এমন একটা জায়গায় পৌঁছন, যেখানে ঘনাদার যে চেহারাটা উনি দেন, সেই পোর্ট্রেটই চলে আসছে। ওঁর আঁকা শিবরাম চক্রবর্তীর চেহারা আজও মানুষের মনে গেঁথে রয়েছে। আসলে শিবরামকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন বাবা। আমাদের বাড়িতে নিয়মিত আসতেন উনি। কলারওয়ালা সিল্কের শার্ট, ধুতির কোঁচা লুটিয়ে পড়া, ঘাড় অবধি চুল, যার সরু একগোছা মুখের পাশে ঝুলে পড়েছে... ওই মানুষটাকে যে কী অপূর্ব দক্ষতায় জীবন্ত করে তুলতে পারতেন! আর শিবরামের সঙ্গে তাঁর দুই ভাই হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন। গায়ে কালো বিরাট এক কোট, একমাথা কোঁকড়া চুল ও ঝুপো গোঁফের হর্ষবর্ধন আর খোঁচা চুলের ভ্যাবাচ্যাকা চেহারার গোবর্ধন। এঁদের নিয়ে খুব মজার অসংখ্য সিচুয়েশন এঁকেছিলেন বাবা! শিবরামের পাশাপাশি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদা সিরিজেরও অনেক ছবি বাবার আঁকা। পটলডাঙার টেনিদাকে চোঙা প্যান্ট এবং ধুতি-শার্ট দুটোই পরিয়েছিলেন তিনি।

শৈল চক্রবর্তীর তুলিতে গোবর্ধন ও শিবরাম
বলতে গেলে, বাবা কিন্তু এ বঙ্গে স্ট্রিপ কার্টুনেরও জনক। বাবার ‘লিটল ডাকু’ এবং প্রতুলচন্দ্র লাহিড়ীর ‘খুড়ো’ স্ট্রিপ কার্টুনের পায়োনিয়ার। ‘লিটল ডাকু’ এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে, অমৃতবাজারে টানা ষোলো বছর ধরে বেরিয়েছে। যদিও দুটোই অবশ্য ইংরেজিতে বেরোত। লিটল ডাকুর সঙ্গে আমার একটা মিল আছে জানেন। আমার কপালে চুল যেমন হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকত, ডাকুরও তাই। বাবা বলতেন, সেই মুখ আর চুল নাকি আমার চেহারা দেখে আঁকা। এ জন্য ছোটবেলায় আমাকে ‘ডাকু’ বলে ডাকত সকলে। বাবা ছিলেন প্রকৃতি রসিক। আর সে রসবোধ জারিত হয়েছিল কার্টুনে। বিভিন্ন মানুষের কথা, হাসি, অঙ্গভঙ্গি নকল করে আমাদের হাসাতেন অনায়াসে।
বাবার মুনশিয়ানা শুধু স্ট্রিপ কার্টুনেই নয়, ইলাস্ট্রেশনেও ছিল অসাধারণ বৈচিত্র। অসম্ভব ভাল আঁকতেন গল্পের ছবি, বুক কভার। একটা ঘটনা বললে বুঝতে পারবেন, বাবার ইলাস্ট্রেশন কোন লেভেলের ছিল! অনেকেই হয়তো জানেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কখনও নিজের গল্পের ছবি কাউকে আঁকতে দিতেন না। উনি মনে করতেন, এখানে এমন শিল্পী নেই, যিনি তাঁর ভাবনাকে তুলি-কলমে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন। কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটেছিল দু’বার। ‘প্রগতি সংহার’ এবং ‘ল্যাবরেটরি’ গল্পের ক্ষেত্রে। আনন্দবাজার পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক বাবাকে দিয়ে গুরুদেবের ‘ল্যাবরেটরি’ গল্পের ছবি আঁকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে ছবি দেখে উনি অত্যন্ত খুশি হয়ে ছাপার অনুমতি দেন পুজোসংখ্যায় (১৯৪০)। তার পরের বছর আবার আনন্দবাজারের শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের আর একটি গল্প ‘প্রগতি সংহার’-এর ছবিও এঁকেছিলেন বাবা! পরপর দু’বার। এখানে বলে রাখি, সত্যজিৎ রায়ের প্রথম মুদ্রিত গল্পের ছবিও কিন্তু বাবার আঁকা।
পুজোসংখ্যা প্রসঙ্গে আরও একটা কথা মনে পড়ে গেল। ছোটবেলায় আমাদের কাছে দুর্গাপুজো মানে শুধু নতুন জামা নয়, অন্য ধরনের আর একটা আনন্দও ছিল। বাবা হয়তো ৬৪টা ছবি এঁকেছেন বিভিন্ন পুজোসংখ্যায়, সেই সব বই আসত। প্রথমে খাটের পাশে বইগুলো রাখা হত। এক সময় পুরো খাট বইয়ে ঢেকে যেত। বইয়ের নতুন গন্ধ বড্ড ভাল লাগত। কতগুলো বই বাড়িতে এসেছে, কে ক’টা পড়েছে... এ নিয়ে আমাদের সাত ভাইবোনের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যেত।
দিনরাত বাবাকে ছবি আঁকতে, লিখতে দেখেছি। ছড়া, ছোটদের গল্পও ভাল লিখতেন উনি। বাবার লেখা ও আঁকা ছবির বই ‘গাড়ি ঘোড়ার গল্প’, ‘মানুষ এল কোথা হতে’, ‘মুখোশ’, ‘কালো পাখি’ রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিল। বাবার সূত্রে কী সব গুণী মানুষদের যাতায়াত ছিল আমাদের বাড়িতে! পি সি সরকার (সিনিয়র) নিয়মিত আসতেন। ওঁর একটা অদ্ভুত অভ্যেস ছিল। যে ছবিগুলো উনি বাবাকে আঁকতে দিতেন, বাবা সেটা টেব্লে বসে আঁকতেন এবং উনি খাটে বসে থাকতেন। একটা ইন্টারন্যাশনাল বুলেটিনে তিনি ম্যাজিক শেখাতেন, তার জন্য বাবাকে দিয়ে আঁকাতেন। বাবা যেহেতু ভীষণ ব্যস্ত, তাই এক দিনে বসে সব ছবি আঁকিয়ে নিয়ে যেতেন। পি সি সরকার অনেকটা সময় থাকতেন বলে, মা বারবার চা আর জলখাবার দিয়ে যেতেন। সে সময়টুকুতে আমাদের ম্যাজিক দেখাতেন। উনি জাপান থেকে খুব ভাল পেপার নিয়ে আসতেন, আমাকে দিয়ে বলতেন, ‘‘একখান বাঘ কাটো তো দেখি। ল্যাজ থিকা শুরু করবা।’’ কাগজের বিভিন্ন জায়গা থেকে কেটে আমাকে একটা জন্তু বানাতে বলতেন। শিবরাম চক্রবর্তীও ছিলেন এ রকম। বসে থেকে আঁকা শেষ করাতেন। তার পর ফুল পেমেন্ট করে বেরোতেন।
বাবা আর একটা ব্যাপার খুব পছন্দ করতেন, তা হল ফ্যান্টাসি। বলতেন, কল্পনা যেন বাঁধ না মানে। এ জন্য আমাদের বহু ধরনের বিদেশি গল্প শোনাতেন। বায়রন, কিটসের কবিতা সরল করে বুঝিয়ে দিতেন। আমাদের কাছে বাবা মানে শুধু খুশি, আনন্দ। শাসন নয়। উনি অ্যানুয়ালি এক-একটা জিনিস করতেন। যেমন, দশমীর দিন আমাদের নিয়ে জিভেগজা বানানো। আসলে খুব ভাল রান্না করতেন উনি। কোনও দিন হয়তো বললেন, ঝোলটা বেশি পাতলা হয়ে গিয়েছে। উঠে গিয়ে খানিকটা আটা নিয়ে ছড়িয়ে দিলেন। এটা মা ওঁর কাছ থেকে শেখেন। যাই হোক, দশমীর দিনে বানানো সে জিভেগজার নানা রকম শেপ হত। বাবার বিশেষত্ব হল, উনি যা কিছু আমাদের দিয়ে করাতেন, সবেতে ওঁর আর্টিস্ট মনটা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকত। যে দিন এই জিভেগজা বানানোর পর্ব চলত, সে দিন মায়ের খুব ঝামেলা হত। প্রচুর ময়দা মাখতে হত। আমাদের সবাইকে একটা করে ময়দার তাল দিয়ে দেওয়া হত। বেলার পর চামচের পিছন দিয়ে কেটে-কেটে প্রত্যেককে এক-একটা শেপ বানাতে হত। ফুল, পাখি, কাঠবিড়ালি... আসলে উনি চাইতেন, এখানেও আমরা ক্রিয়েটিভিটি কাজে লাগাই। বানানো হলে, বাবা সেগুলো ভাজতে বসতেন, রসে ফেলতেন। আমাদের পুরো আগ্রহটা ছিল, কখন বাবা সেখান থেকে আমার বানানো জিভেগজাটা বের করে আনবেন। স্বাভাবিক ভাবে বাবার বানানো জিভেগজার মতো সুন্দর হত না আমাদেরটা। বাবা যে কাঠবিড়ালিটা বানাতেন, সকলের নজর থাকত তার দিকে। যাতে ওটা ফুলে না যায়, তার জন্য ওর গায়ে খাঁজ কেটে দিতেন, আর তা হয়ে যেত কাঠবিড়ালির গায়ের রোম!
আবার এক-একদিন হত আঁকার ওয়র্কশপ। ফিঙ্গার পেন্টিং করতে দিতেন আমাদের। পেনসিল, তুলি এ সব নিয়ে আঁকা মোটেই মুখের কথা নয়, তাই বলতেন ও সব নয়, ফিঙ্গার পেন্টিং করো। এটাও ছিল মায়ের জন্য আর এক ঝামেলার দিন। সে দিন মাকে এক হাঁড়ি অ্যারারুটের আঠা বানাতে হত। প্লেটে রং থাকত। সেই রং ওই আঠার সঙ্গে মিশিয়ে, আঙুলে নিয়ে গাছ, ফুল, পাখি আঁকা চলত। সত্যি, বাবার কাছ থেকে কত কী যে শিখেছি!
একটা ঘটনা তো কোনও দিনই ভুলব না। আমরা তখন কালীঘাটের ভাড়াবাড়ি থেকে ঢাকুরিয়ায় বাবার তৈরি বাড়িতে উঠে এসেছি। বাবা চৌকির উপর বসে আঁকছিলেন, আমি একটা ব্লেড দিয়ে বটলের কর্ক কেটে-কেটে একটা মানুষ বানাচ্ছি। সেটা করতে গিয়ে, হঠাৎ হাত কেটে ফেলি। রক্ত পড়তে লাগল। বাবা তখন সে সব পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে, আবার আঁকতে বসলেন। আর আমি সেই কেটে যাওয়া আঙুলটা নেড়েচেড়ে দেখছি। তখন বাবা বললেন, ‘‘কী হল, ওটা শেষ করবে না? শেষ করো,’’ বলে উনি সেই কর্কটায় কম্পাস দিয়ে ফুটো করে, একটা দেশলাই কাঠি ঢুকিয়ে দিলেন, যাতে একটা গ্রিপ পাই। আবার ব্লেড দিয়ে কর্কটা কাটতে শুরু করলাম। হাত কেটে ফেললেও বাবা কিন্তু ছেলেকে বকলেন না, উলটে উৎসাহ দিলেন। বুঝলেন, এবার আর ও হাত কাটবে না।
আসলে ক্রিয়েটিভ যে কোনও কাজে বাবার প্রবল উৎসাহ ছিল। তাঁর শিল্পী মনের ভাবনা যে কত দিকে ছড়িয়ে ছিল! পোশাকের ব্যাপারেও তিনি ভীষণ পরিপাটি ছিলেন, কিন্তু বিলাসী নন। সাধারণ ধুতি-পাঞ্জাবি পরেই যাতায়াত করতেন। বাড়িতে পরতেন লুঙ্গি। কিন্তু যখন বাইরে বেরোতেন, তখন পায়ের নিউকাট বা অ্যালবার্ট জুতোর পালিশ ঠিক আছে কি না, সে দিকে কড়া নজর থাকত।
প্ল্যানচেটও করতে পারতেন বাবা। মাঝেমাঝেই বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাড়িতে প্ল্যানচেটে বসতেন। সেখানে অবশ্য আমাদের প্রবেশ নিষেধ ছিল।
বাবার স্বভাবে একটা অদ্ভুত বৈপরীত্য হল, শিল্পী হলেও সাংসারিক বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। নিয়মিত বাজার করা, ছেলেমেয়েদের প্রতি যত্ন... অবহেলা ছিল না কোনও দিকেই। প্রতি বছর পুজোর ছুটিতে বেড়াতে যাওয়া ছিল রুটিন। বেডিং বাঁধা, গোছগাছ... সে এক ‘কর্মযজ্ঞ’। ঝাড়গ্রাম, মধুপুর, পুরী, বারাণসী, লখনউ... এই জায়গাগুলোতে কয়েকবার গিয়েছি।
আমরা ধীরে-ধীরে বড় হচ্ছি। সে সময় আমাদের বাড়িতে রবিবাসরীয় সাহিত্যবাসর বসত। তখন ‘রবিবাসরীয়’ বলে সাহিত্যিকদের একটা ক্লাব ছিল, তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় নাটক করতেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, মনোজ ঘোষ, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, রমেন মল্লিক... তখনকার গুণিজনরা সবাই তার অংশ ছিলেন। সপ্তাহে বা মাসে একদিন করে সেই সভা হত। আমাদের বাড়িতে কখনও-কখনও সেই সভা বসত। বাবা সেখানে পাপেট শো করতেন। বাবাকে ভারতে মডার্ন পাপেট্রির পথপ্রদর্শক বলা যায়। মন্দার মল্লিক এবং বাবা এ দেশে প্রথম কার্টুন ফিল্ম তৈরি করেন। অ্যানিমেশন ফিল্ম। ‘চ্যাঙা ব্যাঙা’ বোধ হয় তার নাম ছিল।

স্ট্রিপ কার্টুন লিটল ডাকু
শেষ দিকে বাবা ব্যস্ত ছিলেন পাপেট্রি নিয়ে। সেটাও শুরু করেছিলেন ছেলেমেয়েদের জন্য। সন্তানদের ব্যাপারে খুব যত্নবান ছিলেন তিনি। পাপেট শো-এর জন্য বাড়িরই একটা ছোট গোল টেব্ল নেওয়া হত। জানালার পরদাগুলো সরিয়ে, সেখানে শাড়ি টাঙানো হত। টর্চ লাগিয়ে, তাতে আলো ফেলা হত। টেব্লের নীচের ফাঁকে আলো দেওয়া হত। তার পর শাড়ি দিয়ে ঢেকে শুরু হত পাপেট্রি। দু’পাশ থেকে মঞ্চে আনা হত পুতুল। সেই পুতুলগুলোও বানাতেন বাবা নিজে। প্লাস্টিসিন অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল ক্লে দিয়ে পুতুলের মাথা বানাতেন। তার উপর কাগজ লাগানো হত আঠা দিয়ে। সেটা শুকনো হয়ে গেলে ভিতর থেকে প্লাস্টিসিন বের করে নেওয়া হত। আঠা দিয়ে জোড়া কাগজও শক্ত হয়ে যেত। এ ভাবে তৈরি হত পেপিয়ামেশি পুতুল (কাগজের পুতুল)। বাবা তখন সিএলটির কমিটি মেম্বার। তাই কর্তৃপক্ষ তাঁকে তখন পাপেট্রি শেখার জন্য চেকোস্লোভাকিয়া যাওয়ার কথা বলেন। কিন্তু বাবা বলেন, পাপেট্রি তাঁর কাজের একটা অংশ, প্রধান নয়। অতএব তিনি যাবেন না। যদিও সকলে পছন্দ করায় আমরা কিন্তু ধীরে-ধীরে অনেক জায়গায় পাপেট শো করতে শুরু করেছি। বেথুন কলেজ, রামকৃষ্ণ মিশন, মহাজাতি সদনের মতো জায়গায় শো করেছি। ক্রমশ ব্যাপারটা এত জনপ্রিয় হয়ে যায় যে, প্রবীর মজুমদার নামে এক বিখ্যাত সংগীত পরিচালক এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেন। তৈরি হয় আমাদের দল ‘পুতুল রঙ্গম’। পরে এটা অনেক বড় হয়। এই কাজে আমরা ছেলেমেয়েরা খুব ইনভলভড ছিলাম। ভারী ভারী টেপ রেকর্ডার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস বয়ে-বয়ে নিয়ে যেতাম। সেই শোয়ে আমি আট রকম গলা করতে পারতাম। আমার অভিনয়ের প্রাথমিক পাঠ কিন্তু এই পাপেট শো থেকেই।
আমাদের বাড়ির ‘রবিবাসরীয়’ আসরে সাহিত্যিকরা এসে বসলে, সাবলাইম পাপেট্রি করতাম বাবা এবং আমরা ভাইবোনেরা মিলে। যেমন একটা গল্প ছিল, একজন মানুষ একটা প্রজাপতির পিছনে ছুটে চলেছে। একটা সময় সে সেটা ধরতে পারে এবং মেরে ফেলে। তার পর সে কাঁদতে থাকে। মানুষ কীভাবে স্বপ্নের পিছনে ছুটতে গিয়ে তাকেই মেরে ফেলছে, সেটাই ছিল অন্তর্নিহিত অর্থ। বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা সকলের সামনে ব্যাখ্যা করতেন।
প্রায় চার দশক ধরে দাপিয়ে কাজ করে গিয়েছেন বাবা। ১৯৮৯ সালে তিনি মারা যান। মারা যাওয়ার কয়েক বছর আগেও আমেরিকার নিউ জার্সিতে তাঁর আঁকা ছবির একক প্রদর্শনী হয়েছিল, তার আগে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরোতে। দু’ জায়গাতেই বাবার সব ছবি বিক্রি হয়ে যায়। কর্পোরেশনের লোগোটিতে এখনও বাবার আঁকা ছবি উজ্জ্বল। কিন্তু এমন কর্মমুখর জীবনে, তিনি বোধ হয় তাঁর প্রাপ্য খ্যাতি পাননি। বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়িতে যে দিন মানিকদা’র সঙ্গে বাবার দেখা করাতে নিয়ে গিয়েছিলাম (লেখার গোড়ায় যে সাক্ষাতের কথা বলেছি, যদিও মানিকদার কাছে যাওয়ার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম বাবার তাঁকে লেখা একটি চিঠির সৌজন্যেই), তিনিও সে দিন বলেছিলেন, আপনি যে কত বড় মাপের শিল্পী, তার মূল্যায়ন কিন্তু হল না। কিন্তু সে দিন মানিকদার সঙ্গে দেখা করে ও-বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়ও বাবার চোখে জল দেখিনি, মুখে হাসি দেখেছিলাম।
অনুলিখন: পারমিতা সাহা
সৌজন্য: শৈল চক্রবর্তী সমগ্র,
শৈল চক্রবর্তী অমনিবাস