বুদ্ধ হেসেছেন”— ১৯৭৪ সালের ১৮ মে এ ভাবেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে ভারতের প্রথম সফল পারমাণবিক শক্তি-পরীক্ষার খবর পাঠালেন পরমাণু বিজ্ঞানী রাজা রমন্না। এই খবরে প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তাও বেড়েছিল বিপুল এবং উদ্বেগে ভুরু কুঁচকেছিল ভিন্ন রাষ্ট্র। কিন্তু বুদ্ধ কেন হাসবেন? বুদ্ধপূর্ণিমার দিন তাঁর কর্মভূমি ভারত মারণক্ষমতায় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ হয়ে উঠল বলে? প্রতিটি যুদ্ধই নাকি শান্তি প্রতিষ্ঠার নিরুপায় অস্ত্র, অন্তত যুদ্ধবাজেরা তাই বলেন। অথবা যেমন রাষ্ট্রনীতি বলে থাকে, পরমাণুশক্তিধর হয়ে ওঠা আসলে সম্ভাব্য আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরোধ। সেই জন্যেই হয়তো পোখরানেই ১৯৯৮ সালের ১১ এবং ১৩ মে পাঁচটি ধারাবাহিক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ঘোষিত হয়েছিল— বুদ্ধ আবার হেসেছেন। কিন্তু বুদ্ধ কি সত্যিই হাসতেন? শান্তি প্রতিষ্ঠার এই যুক্তি কি তাঁর গ্রাহ্য হত?
আনুমানিক ৫৬৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কপিলবস্তু রাজ্যের শাসক শাক্যবংশীয় শুদ্ধোদনের পুত্ররূপে মায়াদেবীর গর্ভে সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম হয়। সুদীর্ঘ অপেক্ষার পর রাজার পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধ হওয়ায় সদ্যোজাতের নাম রাখা হল সিদ্ধার্থ। জন্মের সাত দিনের মধ্যে মাতৃহারা হয়ে বিমাতা গৌতমীর কাছে পালিত হওয়ায় তিনি গৌতম। দেবল নামক মহর্ষির ভাগ্যগণনা— এই ছেলে সংসারে থাকলে রাজচক্রবর্তী হবে, গৃহত্যাগী হলে মানুষের পরিত্রাতা। ‘ললিতবিস্তার’ গ্রন্থ থেকে আমরা আরও জানতে পারি, বালক সিদ্ধার্থকে কপিলাবস্তু নগর থেকে দূরের এক গুরুগৃহে বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠানো হয়। চৌষট্টির অধিক লিপির ব্যবহার তাঁর অধিগত হয়েছিল। এই তথ্য অন্তত আমাদের ভারতের ভাষাবৈচিত্রের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পুত্রের গৃহত্যাগের আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে ত্রস্ত পিতা শাক্য বংশেরই অন্য এক ধারার কন্যা গোপা বা যশোধরার সঙ্গে সিদ্ধার্থের বিয়ে দিলেন। কুমারের ভ্রমণপথে সমস্ত অপ্রীতিকর বস্তু অপসারণের নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন শুদ্ধোদন। কিন্তু যেন নিয়তির নির্দেশেই ভ্রমণপথে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুদৃশ্য সিদ্ধার্থকে সংসারে দুঃখের অস্তিত্ব বিষয়ে সচেতন করে তুলল। এবং গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রশান্ত মুখাবয়ব তাঁকে জানাল, দুঃখ-বিনাশের উপায়ও আছে। এক রাতে সিদ্ধার্থ, যশোধরা এবং পুত্র রাহুলকে ঘুমন্ত রেখে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করলেন। ইতিহাসে এই ঘটনা বুদ্ধের মহানিষ্ক্রমণ নামে খ্যাত। তখন সিদ্ধার্থের বয়স ঊনত্রিশ। তার পরের ঘটনাও আমাদের জানা। বহু পথ ও পন্থা ঘুরে অবশেষে মধ্যম পথে, গভীর ধ্যানে সিদ্ধার্থ আবিষ্কার করলেন প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব— বিশ্বের সব কিছুই কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, দুঃখও তার ব্যতিক্রম নয়। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে বোধিপ্রাপ্ত হয়ে বুদ্ধ হলেন তিনি। দ্বাদশ-নিদান-চক্রের আবর্তনে আদি-কারণ স্বরূপ কোনও ঈশ্বরের কল্পনার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেননি। এই চক্র থেকে মুক্তির উপায় স্বরূপ নৈতিক পথেরও নির্দেশ করলেন তিনি, অষ্টাঙ্গিক মার্গ।
সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের সঙ্গে চতুর্দৃশ্যের সম্বন্ধের এই আখ্যান পৃথিবীতে বিখ্যাত ও প্রিয়। বিশ্বাস্য কী? জীবনের আটাশটি বছর পার করে তবেই কি তিনি জানলেন জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুকে? না কি নিউটনের আপেলের মতোই চতুর্দৃশ্য কিংবদন্তি মাত্র? হতে পারে পরিচিত দৃশ্যও সহসা গভীরতর বোধে আমাদের অভিভূত করে কখনও কখনও, হতে পারে গৃহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে জরা-মরণের দৃশ্য সিদ্ধার্থের সিদ্ধান্তকে ত্বরান্বিত করেছিল, কিন্তু চতুর্দৃশ্যকেই গৌতমের বৈরাগ্যের একমাত্র কারণ হিসেবে গ্রহণ করা সঙ্গত নয়। ঊনত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত সিদ্ধার্থ তো গৃহবন্দি ছিলেন না। বরং অপর একটি আখ্যান অধিক যুক্তিসঙ্গত। এই আখ্যানে আছে শাক্য এবং কোলীয়, এই দুই জ্ঞাতি বংশের দ্বন্দ্বের ইতিহাস। পুরাণ-ধর্মগ্রন্থ-লোককথার মিশ্রণে নির্মিত এই কাহিনিতে নির্মোহ পাঠক কিছুটা ইতিহাসও খুঁজে পেতে পারেন।
পুরাকালে সাকেত (অযোধ্যা) নগরের পশ্চিমে সুজাত নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক রাজা রাজত্ব করতেন। ইক্ষ্বাকু বৈবস্বত মনুর পুত্র, এবং মনু আবার সূর্যের পুত্ররূপে বর্ণিত বলে ইক্ষ্বাকুবংশ সূর্যবংশ নামেও পরিচিত। পুরাণবর্ণিত রামচন্দ্রও এই বংশের সন্তান। রাজা সুজাত জেন্তী নামক এক বারবিলাসিনীর প্রতি আসক্ত হন এবং কালক্রমে উভয়ে জেন্ত নামক এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। তৃপ্ত সুজাত বর দিতে চাইলে জেন্তী নিজের পুত্রকেই যুবরাজ হিসেবে দেখতে চাইলেন। নিরুপায় সুজাত তাঁর ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভজাত প্রিয় পাঁচটি সন্তানকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করলেন। অনেক প্রজা ও স্বজন জনপ্রিয় এই পাঁচ কুমারের অনুগমন করেছিলেন। নানা দেশ ঘুরে পঞ্চকুমার সদলবলে উপস্থিত হলেন হিমালয়ের এক পার্বত্য প্রদেশে, আশ্রয় নিলেন কপিল ঋষির আশ্রমে। সেখানে অবস্থান কালে রাজপুত্ররা নিজেদের বোন, ভাগনি ইত্যাদি আত্মীয়দের সঙ্গেই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে শুরু করেন, পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতার কারণেই হয়তো। কুমারদের এই বিবাহ ধর্মসঙ্গত, অর্থাৎ শক্য কি না, এই প্রশ্ন ওঠায় শাস্ত্রজ্ঞরা রায় দিলেন রাজপুত্রদের এই আচরণ শক্য। এই থেকেই নাকি ইক্ষ্বাকু বংশের এই শাখার নাম হয়ে দাঁড়ায় শাক্যবংশ। অবশ্য ‘শাক্য’ নামের অন্য ব্যাখ্যাও আছে। শাক্যরা যে নিজেদের আত্মীয়ের মধ্যেই বিবাহ করতেন, তার উল্লেখ একাধিক। পরবর্তী কালে কপিলের দেওয়া ভূখণ্ডে জনপদ নির্মাণ করে শাক্যেরা সেখানেই নিজেদের পুনর্বাসিত করেন। তাঁদের রাজ্যের নাম কপিলাবস্তু হওয়ার তাৎপর্য বোঝাই যাচ্ছে। পঞ্চকুমারের জ্যেষ্ঠপুত্র ওপুর, ওপুরেরই কয়েক প্রজন্ম পরের বংশধর সিংহহনু, যাঁর পুত্র শুদ্ধোদন। সিংহহনুর একমাত্র কন্যা, অর্থাৎ শুদ্ধোদনের বোন অপরূপা সুন্দরী অমিতার দুরারোগ্য কুষ্ঠরোগ সারিয়ে তুলে কোল নামক এক ঋষি সন্ন্যাস ভুলে তাঁকে বিবাহ করেন। এঁদেরই বংশধরেরা কোলীয় নামে খ্যাত, যাঁরা পার্শ্ববর্তী কোল রাজ্যেই বাস করতেন। তবে কোল প্রদেশের অস্তিত্ব আরও আগে থেকেই থাকা সম্ভব। হতে পারে শাক্য কোল এবং অন্যান্য আরও পার্বত্যজাতি বহু পূর্বে ভারতে প্রবেশ করে বসতি স্থাপন করেছিলেন। পুরাকালে ভারতের বাইরে থেকে প্রবিষ্ট যে কোনও জাতিই শক নামে অভিহিত হত এবং সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মনে করেন ‘শাক্য’ নামকরণ সেই কারণেই। সিদ্ধার্থর স্ত্রী যশোধরাও একাধিক গ্রন্থে শাক্যকন্যা হিসেবে বর্ণিত। যাই হোক, কোলীয় বংশেরই দুই কন্যা মায়া ও মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে শুদ্ধোদন বিয়ে করেন। এই মায়ারই পুত্র গৌতম বুদ্ধ। শাক্য ও কোলীয়দের মধ্যে যে জ্ঞাতি সম্পর্ক ছিল, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহের অবকাশ নেই।
কপিলবস্তু এবং কোল এই দুই রাজ্যের বিভাজিকা রোহিণী নদী। কৃষিকাজের জন্য এই দুই রাজ্যই রোহিণীর জল ব্যবহার করে আসছে দীর্ঘ দিন, এবং এদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ইতিহাসও দীর্ঘ। কোনও এক সময় জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য নদীর উপর একটি বাঁধ নির্মিত হয়। উভয় রাজ্যে বিবাদের সূত্রপাত তার পর থেকেই। জ্যৈষ্ঠ মাসেই ধরিত্রী সবচেয়ে রুক্ষ শুষ্ক হয়ে ওঠেন, গাছ ও শস্য তৃষ্ণার্ত থাকে এই সময়েই সর্বাধিক। জলের প্রয়োজন কোন রাজ্যের বেশি, কী ভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে প্রবাহ, এই সব নিয়ে বিবাদ এক জ্যৈষ্ঠে চরমে উঠল। সহ্যের সীমা পেরিয়ে শাক্যরা কোলীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ঊনত্রিশ বছরের যুবরাজ সিদ্ধার্থ যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন। এই অবস্থান আসলে নিজের দেশের জনমতের বিরুদ্ধেও। এ দিকে শুদ্ধোদন রাজা হিসেবে বর্ণিত হলেও, শাক্যদেশ সম্ভবত একটি গণরাজ্য ছিল। সংখ্যালঘু হিসাবেই সিদ্ধার্থকে সংখ্যাগুরুর মতের কাছে নতি স্বীকার করতে হল। এই বৈশিষ্ট্য তো গণরাজ্যেরই। তিনটি বিকল্পের মধ্যে একটি বেছে নিতে হবে গৌতমকে— সশস্ত্র যুদ্ধে যোগদান, মৃত্যুদণ্ড বা নির্বাসন অথবা দেশের ভিতরেই সপরিবার সামাজিক ভাবে ব্রাত্য হয়ে থেকে সমস্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেওয়া। শান্তির পক্ষে অবিচল থেকে তিনি দ্বিতীয় বিকল্পটিই বেছে নিলেন। নিজেকে নির্বাসন দিলেন। এই আখ্যানে আমরা জানতে পারি, সিদ্ধার্থের এই সিদ্ধান্তে যশোধরার সম্মতি ছিল। অপর একটি ভাষ্যে, শাক্য ও কোলীয়দের মধ্যে রোহিণীর জলকে কেন্দ্র করে এই বিবাদের ঘটনাটি ঘটে সিদ্ধার্থর বোধি লাভের পরে। যুদ্ধ পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে বুদ্ধ শ্রাবস্তী থেকে অলৌকিক ক্ষমতাবলে বিবদমান দুই পক্ষের মাঝখানে শূন্যে ভাসমান অবস্থায় ঐক্যবদ্ধ থাকার উপকারিতা বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দেন এবং শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষই অস্ত্র ত্যাগ করে। ফলে যে কারণেই সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করুন না কেন, যুযুধান দুই পক্ষের মাঝে দাঁড়িয়ে রোহিণীর তীরে তিনি যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ কম।
যুদ্ধের বিরুদ্ধে বুদ্ধ আজীবন অবিচল। মগধরাজ বিম্বিসার ও বুদ্ধ পরস্পরের সুহৃদ ছিলেন। গৃহত্যাগ করার অব্যবহিত পরে এবং বুদ্ধত্ব লাভের আগেই রাজগৃহে বিম্বিসারের সঙ্গে সিদ্ধার্থের সাক্ষাৎ এবং সখ্যের সূত্রপাত। বোধিলাভের পরে শীঘ্রই পুনর্বার তিনি রাজগৃহে আসেন এবং বিম্বিসারকে নতুন ধর্মে দীক্ষা দেন। ভিক্ষুসঙ্ঘ রাজানুগ্রহ থেকে কোনও দিন বঞ্চিত হয়নি। এ-হেন বিম্বিসার যখন রাজপুত্র অজাতশত্রুর হাতে নিহত হলেন, ব্যথা বেজেছিল নিশ্চয়ই করুণাঘনের হৃদয়ে। অজাতশত্রু দেবদত্তের প্ররোচনায় বুদ্ধ ও সঙ্ঘের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র করেছিলেন। কিন্তু শেষ অবধি অপরাধবোধে জর্জরিত রাজা সেই তথাগতের কাছেই এলেন শান্তি খুঁজে পেতে। ক্ষমা করে দিলেন দিলেন বুদ্ধ, সুহৃদের খুনী ও ষড়যন্ত্রকারী অজাতশত্রুকেও। তিনিই না বলেছিলেন: “পিয়তো বিপ্পমুত্তস্স নত্থি সোকো কুতো ভয়ং।” যিনি প্রিয়বস্তু থেকে বিপ্রমুক্ত, তিনি শোক ও ভয় থেকেও মুক্ত (ধম্মপদ)।
বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষিত হলেও অজাতশত্রু ক্ষাত্রধর্ম ভুলতে পারেননি, বৃজি গণরাজ্য ধংস করতে উদ্যত হলেন তিনি। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ নামে কোনও একটা দেশ ছিল না, ছিল ভারতীয় সভ্যতার অন্তর্গত অনেকগুলি স্বশাসিত রাষ্ট্র। বুদ্ধের সমসময়ে ভারতে এমনই কয়েকটি রাষ্ট্রকে একত্রে বলা হত ষোড়শ মহাজনপদ, বৃজি তাদের মধ্যে অন্যতম। বৃজি ছিল একটি প্রজাতন্ত্র, রাষ্ট্র হিসেবে যুক্তরাজ্য ধরনের, বিদেহ, বৃজি, লিচ্ছবি ইত্যাদি তাদের অন্যতম। সমগ্র যুক্তরাজ্যের রাজধানী বৈশালী ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ নগর। একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী অজাতশত্রু বৃজি জাতিকে ধ্বংস করা মনস্থ করলেন।
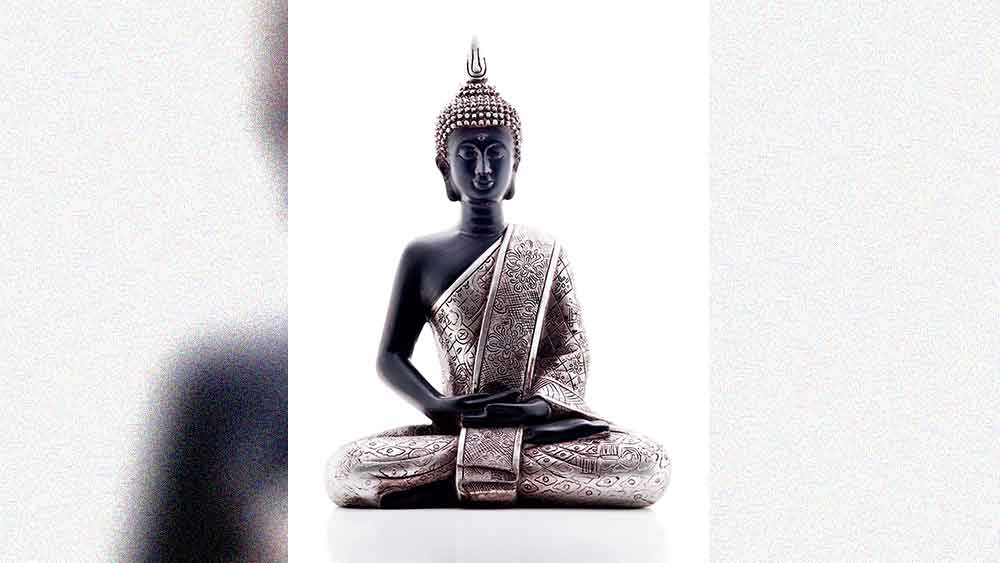

অহিংস তথাগতের কাছেই বর্ষকার নামক রাজমন্ত্রীকে পাঠিয়ে বৃজি ধ্বংসের উপায় জানতে চাইলেন। বুদ্ধ বলেছিলেন, যত দিন ঐক্যবদ্ধ থেকে বৃজিগণ ধর্ম পালন করবে, তত দিন তাদের ধ্বংস নেই। ধর্ম বলতে বুদ্ধ মূলত নৈতিক আচরণকেই বুঝিয়েছেন। অজাতশত্রু বুঝলেন, বৃজিদের ঐক্য বিনষ্ট না করলে তাদের বিনাশ করা অসম্ভব। অজাতশত্রুকে নিরস্ত না করে বুদ্ধ কি সত্যিই বৃজিদের ধ্বংসের উপায় নির্দেশ করলেন? আবাল্য অহিংস ও যুদ্ধবিরোধী বুদ্ধের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। আসলে প্রচ্ছন্ন ভাবে বৃজিদেরই ঐক্যবদ্ধ থাকার বার্তা দিলেন। রাজ-অমাত্যের সঙ্গে বুদ্ধের এই সাক্ষাৎ গোপন ছিল না, আনন্দ উপস্থিত ছিলেন সেখানে। অমাত্যের প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই বুদ্ধ আনন্দকে নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজগৃহের ভিক্ষুদের সমবেত করতে। সমাবেশে বুদ্ধ ধর্মাচরণ বিষয়ে প্রায় একই উপদেশ দিলেন যা তিনি দিয়েছিলেন রাজমন্ত্রীকে। উল্লেখ্য, উভয় ক্ষেত্রেই উপদেশের সংখ্যা সাত। ফলে অনুমান করা যায়, ঐক্যবদ্ধ ও ধর্মপথে থাকার বার্তাটি বৃজিদের কানে পৌঁছে দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তা ছাড়া আমরা এটাও জানি, বুদ্ধের বচন শোনার পর, অজাতশত্রুর বৈশালী আক্রমণ করতে বেশ কিছু দিন সময় নিয়েছিলেন। বুঝেছিলেন, বৃজিদের পরাজিত করা সহজ নয়। বৃজিদের এই সময়টুকু দেওয়াও বুদ্ধের অভিপ্রায় হতে পারে। এই প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, “যাহাতে এই নিরীহ জাতির স্বাধীনতা বিনষ্ট না হয় তাহার মনোগত অভিপ্রায়ে তাহাই ছিল, এ কথা তাঁহার উত্তরের ভাবার্থে স্পষ্টতই বোঝা যায়।”
অজাতশত্রু বৃজি জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন শেষ পর্যন্ত, কিন্তু জয় পেতে তাঁর দীর্ঘ ষোলো বছর লেগেছিল। এই ঘটনার পর বুদ্ধ আর বেশি দিন বাঁচেননি।
বৌদ্ধশাস্ত্র বলে, বুদ্ধ ফিরে আসবেন মৈত্রেয় হয়ে। আমাদের পাপের ঘড়া কি যথেষ্ট পূর্ণ হয়নি? ইউক্রেন সীমান্তে দঁড়িয়ে রাশিয়ার দিকে আঙুল তুলে আর এক জন বুদ্ধ কি বলবেন না— ভুলে যেয়ো না, শাক্য ও কোলীয়দের মতোই তোমরা জ্ঞাতি, তোমাদের ভাষার ইতিহাসও এক। এই গণকবরতন্ত্র কখনও সভ্যতার ভিত্তি হতে পারে না।
আমরা জানি না, উভয় দেশের মধ্যে ভেদ সৃষ্টিতে শুধুমাত্র ‘নেটো’ তথা রাজনৈতিক পশ্চিমকে কতটা দায়ী করব, কিন্তু পৃথিবীর যে কোনও ভূখণ্ডের নিরপরাধ মানুষের উপর যুদ্ধ নামিয়ে আনা যে অপরাধ, সে কথা তো জানি। বুদ্ধের শরীর
নেই, সে ভাবে হয়তো সঙ্ঘও নেই। কিন্তু অস্ত্র নামিয়ে রেখে যে ধর্মের সূত্রপাত, তাও কি নেই? বুদ্ধের উপদেশাবলি থেকে আমরা বুঝতে পারি, বুদ্ধ ও সঙ্ঘের থেকেও ধর্মের গুরুত্ব তাঁর কাছে অধিক। বুদ্ধকে না দেখলেও, বুদ্ধের উপদেশ না শুনলেও সংসারে এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁরা ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত হন না— এই কথা শিষ্যদের তিনি বলেছিলেন। বুদ্ধের বচন শুনে ধর্মকে আশ্রয় করবেন যাঁরা, বুদ্ধ তাঁদের জন্যেই শিক্ষা দিয়েছেন। আর এক শ্রেণির লোক আছেন, যাঁরা বুদ্ধের কথা জানলেও ধর্মের নিয়ম লঙ্ঘন করেন। গৌতম বুদ্ধের কালের আড়াই হাজার বছর পর আমাদের পৃথিবীতে আর এক জন বুদ্ধ কি পৃথিবীর প্রাপ্য নয়?










