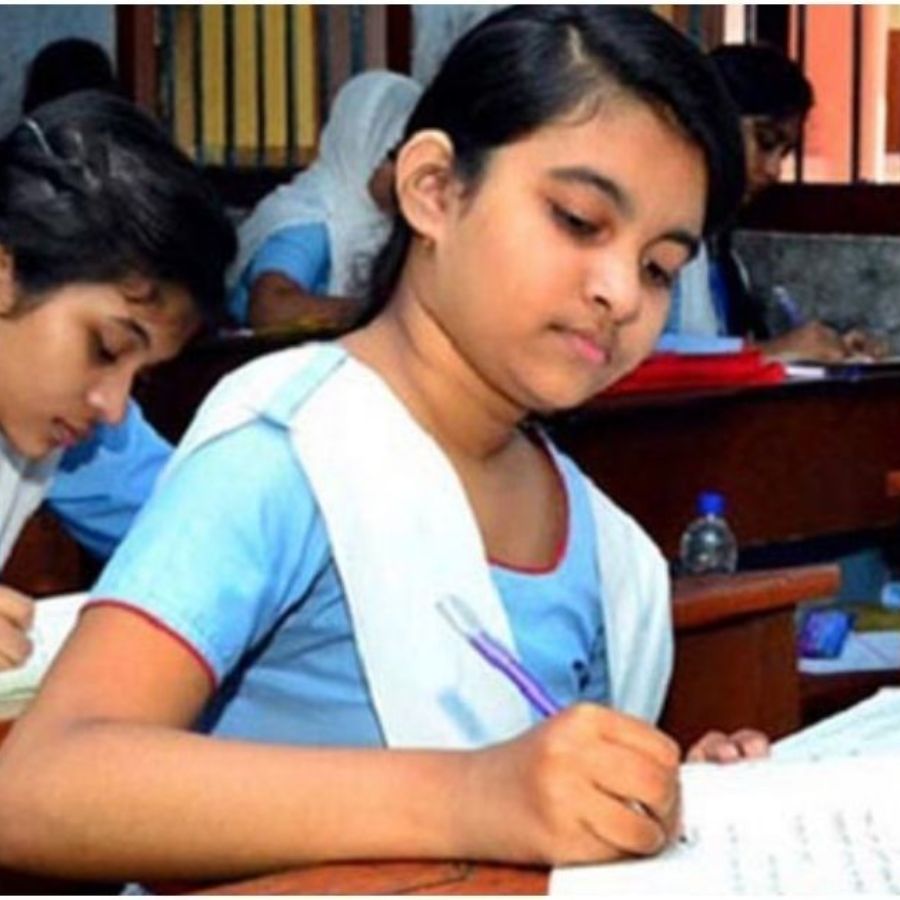আমার বর্তমান বয়স ৮৩ বছর ৪ মাস। ১২ বৎসর ৩ মাস বয়স পর্যন্ত পরাধীন ভারতে কাটানোর পর ৭১ বৎসর ১ মাস স্বাধীন ভারতে বসবাস করছি। পরাধীন ভারতের তুলনায় স্বাধীন ভারতে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট প্রাচুর্য ও উন্নতি ঘটেছে, অনস্বীকার্য। কিন্তু স্বাধীন দেশে সাধারণ নাগরিকরা কতটা স্বাধীন ও কতটা শান্তিতে বসবাস করেন, তা সম্প্রতি বাংলা বন্ধের চিত্রটা তুলে ধরলেই অনুমান করা যায়। বন্ধের পক্ষে ও বিপক্ষে উভয় দলেরই সশস্ত্র বাহিনী তাদের জয় সুনিশ্চিত করতে পথে নেমে পড়ল। ফলে দোকানদার দোকান খুলুন বা বন্ধ রাখুন, গাড়ির চালক গাড়ি চালান বা না চালান, কর্মীরা তাঁদের কর্মক্ষেত্রে কর্ম করুন বা না করুন— যে কোনও ক্ষেত্রেই এক পক্ষের সশস্ত্র বাহিনীর হাতে তাঁদের প্রহৃত, আহত কিংবা নিহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। পরাধীন দেশে একটি শাসক দল ছিল। স্বাধীন দেশে সরকারপক্ষ ও বিরোধী পক্ষ— উভয়ের শাসনের ভয়ে জনতাকে অব্যক্ত যন্ত্রণাভোগ করতে হয়। বন্ধ-শেষে উভয়পক্ষই তাদের সাফল্য দাবির সঙ্গে, সফলতার জন্য জনগণকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। সাধারণ মানুষ প্রহৃত, আহত, নিহত যা-ই হোন, উভয়পক্ষের কাছ থেকে ধন্যবাদটুকু পাচ্ছেন, এটাই বা কম কী!
মদনমোহন সেনগুপ্ত, রাধামোহনপুর, বাঁকুড়া
ধর্মের আক্রমণ
মিলন দত্তের ‘একা যেতে ভয় করে’ (১৫-৯) নিবন্ধটি একটি বহুপ্রতীক্ষিত লেখা। গোটা ভারতবর্ষে তো বটেই, এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও মুসলমানরা যে সংখ্যালঘু হিসেবেই বাস করেন, এটা ভাবা আর বলা দুটোই খুব জরুরি। বহু দিন ধরে আমরা নিজেদের চোখ ঠেরেছি এই বলে যে আমরা এই সব মানসিকতার ঊর্ধ্বে। কিন্তু আজ যখন ‘হারে রে রে’ করে হিন্দুত্ববাদীরা পশ্চিমবঙ্গ দখল করতে নেমে পড়েছে, তখন নিরপেক্ষ ভাবে দেখলে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, ভিতরে ভিতরে আমরা অনেকেই সংখ্যাগুরুর গরিমা উপভোগ করি।
আরও একটা কথা বলা জরুরি। যে কোনও ধর্মের মানুষের মধ্যেই, ধর্মে বিশ্বাস করেন না বা তা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মনে করেন না এই রকম মানুষ অনেক আছেন। তাঁদের অস্তিত্বও আজ সঙ্কটের মুখে। উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সংখ্যাগুরুর ধর্মের গরিমার মিশেলে তৈরি হয়েছে নতুন দেশপ্রেমিকের রাজনৈতিক ধারণা। তার বিচারে তাঁরাও বিদ্রোহী।
রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, সব দিক থেকে ধর্মের এমন সাঁড়াশি আক্রমণ আগে কখনও হয়েছে বলে মনে পড়ে না। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলে সরকার পরিচালিত একটি স্কুলের শিশুরা আমাকে বলেছিল যে রোজ তাদের ক্লাসে ঢোকার আগে ‘জয় শ্রীরাম’ বলতে হয়। আর এক জন শাসক দলের নেতা আমার মুখে সে কথা শুনে বলেছিলেন, কাজটা ঠিক নয়, কিন্তু রামের নাম করায় ক্ষতি তো নেই। এই মানসিকতা আমাদের সমাজেরও। কথাটা হল, কেন সরকার পরিচালিত একটি স্কুলে আমাদের শিশুরা— একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশের ভাবী নাগরিকরা— রামের নামে জয়ধ্বনি দিতে বাধ্য থাকবে? ‘আল্লা হু আকবর’ বলারও দরকার নেই। আবার রামের নামে জয়ধ্বনি দিতে বাধ্য করাও বেআইনি। যুক্তি খোঁজা বাতুলতা। সবটাই গা-জোয়ারি। স্কুলের প্রাতিষ্ঠানিকতা শক্তিশালী, তাই শিশু বাধ্য বলতে। রাষ্ট্র ক্ষমতাবান, তাই অধিবাসীরা মাথা নিচু করে ধর্মের মানবাধিকার-বিরোধী ব্যবহার মেনে নেবেন। এটাই মূল ভাবনা।
বোলান গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা-৩
মনের চিকিৎসা
সীমন্তিনী মুখোপাধ্যায় ও অচিন চক্রবর্তীর নিবন্ধ ‘দরকার চিকিৎসকের সাহায্য ’ (২০-৯) প্রসঙ্গে জানাই, ১৯৭৭-৭৮ সালে আমরা একটি সমীক্ষা করেছিলাম কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। উদ্যোক্তা এসএসকেএম হাসপাতাল সংলগ্ন মানসিক চিকিৎসা বিভাগ। অধ্যাপক অজিতা চক্রবর্তীর নির্দেশনায় তিন পরিদর্শকের অধীনে ১২ জন সমাজকর্মী বাড়ি বাড়ি তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন ‘নমুনা সমীক্ষা’ রীতিতে। আমরা জেনেছিলাম, শতকরা ছ’জন কোনও না কোনও মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। মানসিক প্রতিবন্ধকতা ও মৃগী রোগ এই সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই রোগীদের শতকরা দশ ভাগ মাত্র আধুনিক চিকিৎসা করাতেন। বাকি ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্র, তাবিজ, কবচ অথবা অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দেওয়া আমজনতা। অনেকে জানতেনই না যে এর আধুনিক চিকিৎসা আছে। সত্যিই মানসিক রোগের চিকিৎসা প্রয়োজনের তুলনায় কম। কলকাতার পাঁচটি বড় হাসপাতালে বহির্বিভাগ আছে। ভর্তি করার ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। গোবরা-র পাভলভ হাসপাতালে আছে কিন্তু যাতায়াত সুবিধাজনক নয়। আর দু’টি আছে পুরুলিয়া ও মুর্শিদাবাদে। আগে তো রাঁচীতে নিয়ে যেতে হত মানসিক রোগগ্রস্তদের। সবার অবশ্য ভর্তি করে চিকিৎসা করাতে হয় না।
গ্রামাঞ্চলের হাসপাতালগুলিতে মানসিক রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। আমার জেলা হাওড়ায় সদর হাসপাতালে দু’জন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বহির্বিভাগে দেখেন। বাকি কোথাও, উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতাল (উদ্যোগ করা হচ্ছে শুনেছি) ছাড়া, গাববেড়িয়া, আমতা, উদয়নারায়ণপুর, জগৎবল্লভপুরে মানসিক রোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। কলকাতা থেকে কেউ কেউ আসেন সপ্তাহে এক বা দু’দিন পরিষেবা দেওয়ার জন্যে। কিন্তু প্রয়োজন মেটে না। তা ছাড়া সকলের আর্থিক অবস্থায় কুলায় না। তাই বিনামূল্যে গ্রামের মানুষের কাছে মানসিক রোগের চিকিৎসা পৌঁছক।
সনৎকুমার কর, ইমেল মারফত
পাশে দাঁড়ানো
নিজে দীর্ঘ দিন ডিপ্রেশনে ভুগে ও চিকিৎসায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে এবং আর পাঁচ জনকে সঠিক দিশা দেখিয়ে ভাল করার অভিজ্ঞতা থেকে কিছু কথা বলি। সাধারণ মানুষ থেকে বুদ্ধিজীবী, অনেকেই এই রোগকে কেবল মনখারাপের রোগ বলেই ধরে নেন। চিকিৎসা করান না। তা পরে জটিল আকার ধারণ করে। বাড়ায় আত্মঘাতী প্রবণতাও। হু-র হিসেবে ভারতে প্রায় ছ’কোটি মানুষ এ রোগে ভুগছেন, প্রকৃত সংখ্যা দশ কোটির নীচে হবে না। এই রোগে সব চেয়ে দরকার: আত্মীয় বা বন্ধুদের রোগীর পাশে দাঁড়ানো এবং অবশ্যই চিকিৎসা করানো। প্রয়োজনে দীর্ঘ দিন চিকিৎসা চালাতে হতে পারে। ডাক্তারের কথা না শুনে, ভাল হয়ে গিয়েছে মনে করে ওষুধ বন্ধ করে অনেককে বিপদে পড়তে দেখেছি।
সুদর্শন নন্দী, রাঙামাটি, মেদিনীপুর শহর
প্রয়াণ
সম্প্রতি প্রয়াত হলেন বুদ্ধদেব বসুর কনিষ্ঠা কন্যা দময়ন্তী বসু (সিংহ)। উনি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপিকা ছিলেন। তিনি ১নং বিধান সরণিতে বিকল্প প্রকাশনী স্থাপন করে বুদ্ধদেব বসু ও অন্যান্য খ্যাতিমান লেখকের উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশ করেছেন। বুদ্ধদেব বসুর রচনাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণে তিনি নিজেকে আমৃত্যু নিয়োজিত রেখেছিলেন।
চন্দন চট্টোপাধ্যায়, ভদ্রকালী, হুগলি
লিঙ্ক নেই
জনগণের বড় আতঙ্ক— ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসে গিয়ে এই কথাটি শোনা: লিঙ্ক নেই। পোস্ট অফিসে আজ প্রিন্টার খারাপ তো কাল প্রিন্টারের ফিতে নেই, বেশির ভাগ সময় জানালায় আতঙ্কের বোর্ড: লিঙ্ক ফেল। ওই সব সংস্থার কর্মীদের কাছে এটা স্বর্গের উপহার।
দেবপ্রসাদ সরকার, মেমারি, বর্ধমান
চিঠিপত্র পাঠানোর ঠিকানা
সম্পাদক সমীপেষু,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০০১।
ইমেল: letters@abp.in
যোগাযোগের নম্বর থাকলে ভাল হয়। চিঠির শেষে পুরো ডাক-ঠিকানা উল্লেখ করুন, ইমেল-এ পাঠানো হলেও।