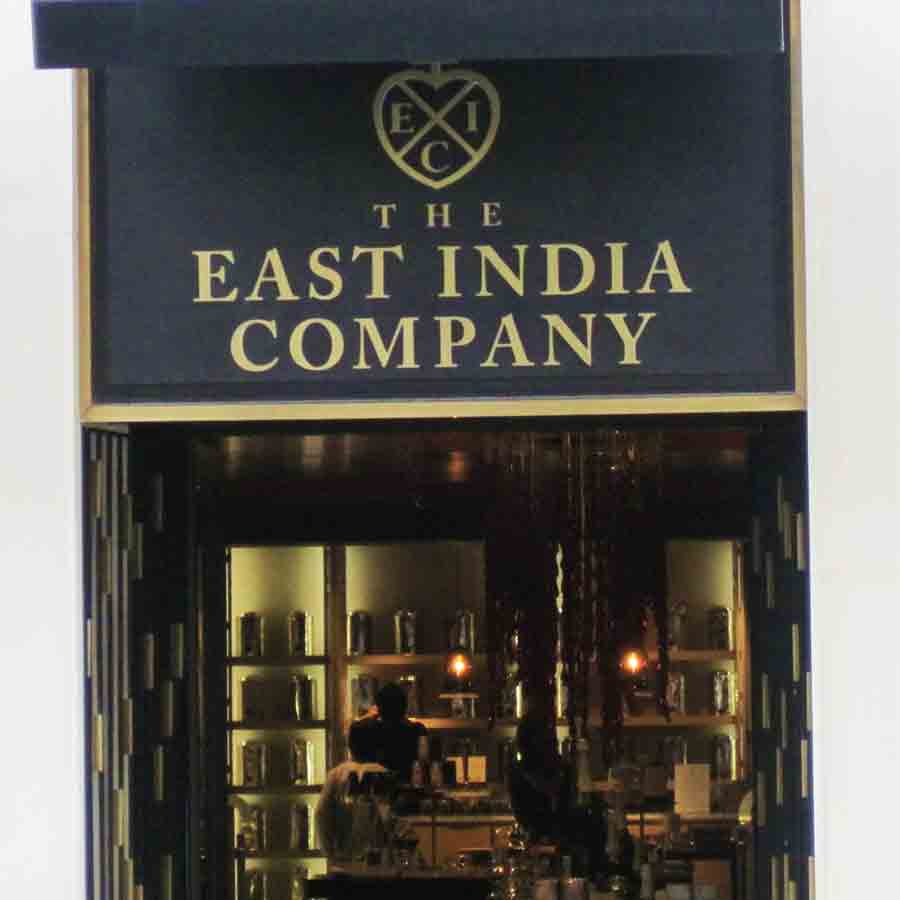একটি ধাঁধাকে যদি সরিয়ে রাখা যায়, তবে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক রিপোর্টে ভারতের আনন্দিত হওয়ার বিলক্ষণ কারণ রয়েছে। রিপোর্ট বলছে, ২০১১-১২ সালের তুলনায় ২০২২-২৩ সালে ভারতে চরম দারিদ্র কমেছে বিপুল হারে। ২০১১-১২’তে দেশের মোট জনসংখ্যার ২৭.১% চরম দারিদ্র ছিল; ২০২২-২৩’এ অনুপাতটি দাঁড়িয়েছে ৫.৩ শতাংশে। সংখ্যার হিসাবে, আগের সময়কালটিতে ভারতে চরম দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ছিল ৩৪.৪৫ কোটি; পরের সময়কালটিতে তা কমে হয়েছে ৭.৫ কোটি। সত্যিই যদি এই রকম হারে দারিদ্র কমে থাকে, তা হলে তা এক বিপুল সাফল্য। কিন্তু, ধাঁধাটি হল, যে সময়কালের কথা বলা হচ্ছে, তাতে ভারতীয় অর্থব্যবস্থা বেশ কয়েকটি ধাক্কার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। ২০১৬ সালের নোট বাতিল, ২০১৭ সালে জিএসটি প্রবর্তন, এবং ২০২০-২১’এর অতিমারিজনিত আর্থিক মন্দা। পরিসংখ্যানে স্পষ্ট যে, ২০১৬-১৭ থেকে পর পর চার বছর ভারতে আর্থিক বৃদ্ধির হার আগের বছরের তুলনায় কম থেকেছে; অতিমারির ধাক্কায় বৈশ্বিক বৃহৎ অর্থব্যবস্থাগুলির মধ্যে ভারতের বৃদ্ধির হারই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। তা হলে, এই সময়কালে দারিদ্র এতখানি কমল কোন মন্ত্রে, এই ধাঁধাটির উত্তর খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত দারিদ্র হ্রাসের সাফল্য বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া মুশকিল। বিশেষত খেয়াল রাখা প্রয়োজন, এই একই সময়কালে ভারতে আর্থিক বৈষম্যের মাত্রাও বেড়েছে বলে গবেষকদের মত। কেউ এ কথাও মনে করিয়ে দিতে পারেন যে, এই সময়কালেই দেশের ভোগ্যপণ্য উৎপাদক সংস্থাগুলি বাজারে চাহিদার অভাব নিয়ে অভিযোগ করেছে; এই সময়কালেই কর্মসংস্থানহীনতার হার স্মরণকালের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে; মানুষের প্রকৃত আয়বৃদ্ধির অভাব নিয়ে সরব হয়েছেন সরকারি নীতি আয়োগের কর্তাও। তা হলে?
এই প্রশ্নের উত্তরটিও বিশ্ব ব্যাঙ্কের রিপোর্টেই রয়েছে। যে পরিসংখ্যানের উপরে নির্ভর করে দারিদ্রের হার হিসাব করা হয়েছে, সেটি ২০২২-২৩ সালের হাউসহোল্ড কনজ়াম্পশন এক্সপেন্ডিচার সার্ভে। গত বছর প্রকাশিত এই নমুনা সমীক্ষা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন উঠেছিল। তার মধ্যে প্রধানতম সমালোচনাটি হল, এই সমীক্ষায় চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের সম্ভাবনা তুলনায় কম। কারণ, শহরাঞ্চলে যাঁদের গাড়ি নেই তাঁদের সবাইকেই ধরে নেওয়া হয়েছে সর্বনিম্ন আয়ের ‘স্ট্রেটা’ হিসাবে; গ্রামাঞ্চলে যাঁদের মালিকানায় থাকা জমির মাপ একটি নির্দিষ্ট স্তরের নীচে, তাঁরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এই তালিকায়। যত লোকের গাড়ি নেই, তাঁরা সকলে যে সমান গরিব নন, সেটা বুঝতে অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হয় না। যে-হেতু দরিদ্রের এই বিচিত্র ‘স্ট্রেটা’ থেকে নমুনা চয়ন করা হয়েছে, ফলে এই সমীক্ষায় যাঁদের কথা এসেছে, তাঁরা কতখানি ‘গরিব’, সে প্রশ্ন থাকছেই। এবং, সেই তথ্যের উপরে ভর করে পাওয়া দারিদ্র হ্রাসের স্বীকৃতিও কতখানি উল্লেখযোগ্য, তা ভাবতে হবে বইকি।
তবে, এ কথা বলাও অন্যায় হবে যে, দারিদ্র হ্রাসের পুরো হিসাবটাই পরিসংখ্যানের খেল। গত কয়েক বছরে বিভিন্ন অর্থশাস্ত্রীর কষা দারিদ্রের হিসাবের সঙ্গে বর্তমান পরিসংখ্যানকে মিলিয়ে দেখলে স্পষ্ট হবে যে, দারিদ্র সত্যিই অনেকখানি কমেছে। তার একটি অংশ ধারাবাহিকতার ফল— রাজনৈতিক ভাবে স্থিতিশীল যে কোনও উন্নয়নশীল দেশেই দারিদ্র ধারাবাহিক ভাবেই কমে। ভারতেও কমেছে। সেই হ্রাসকে আরও গতিশীল করার দায়িত্ব সরকারের। দেশের অর্থনৈতিক নীতির কেন্দ্রে সম্পদের সুষ্ঠুতর পুনর্বণ্টনকে রাখা প্রয়োজন। ভাবা দরকার যে, আর্থিক বৃদ্ধির সুফল সর্বাপেক্ষা বেশি মানুষের কাছে কোন পথে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। গণতন্ত্রে সেই কাজটি হচ্ছে কি না, সে দিকে নজর রাখার দায়িত্ব সকলের। হঠাৎ চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া পরিসংখ্যান নয়, আসল গুরুত্ব দারিদ্র হ্রাস করার ধারাবাহিক, নীতিগত পদক্ষেপের।
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)