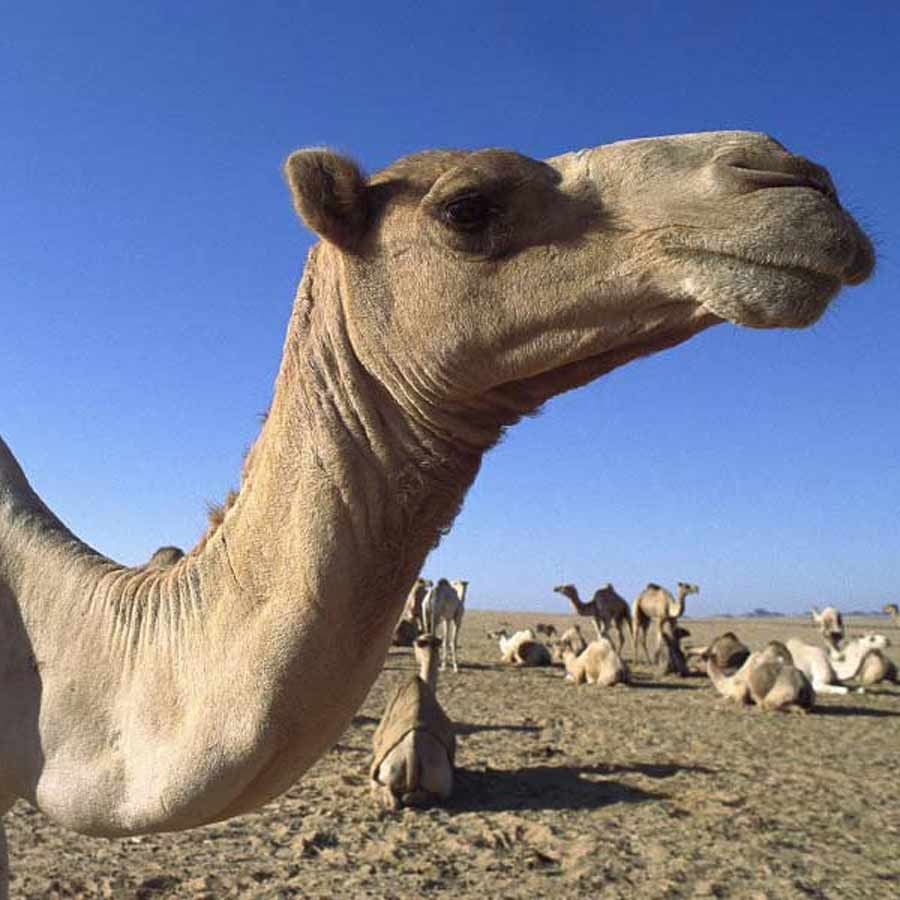নিধিরামের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে বুরুন আর সব বিষয়ে মোটামুটি ভাল নম্বর পেয়েছিল, শুধু অঙ্কে পেয়েছিল তেরো। সে তো ছিল গল্প। আর গল্পের, বিশেষত কিশোরপাঠ্য কাহিনির অনেকটাই যে ইচ্ছাপূরণের, কে না জানে। গোসাঁইবাগানের সেই নিরীহ ভূতের সঙ্গে বন্ধুতার পর ইস্কুলে কঠিন অঙ্ক বা দাঁতভাঙা ট্রান্সলেশন, ক্রিকেটে সেঞ্চুরিও জলভাত হয়ে গিয়েছিল বুরুনের, অশরীরী বন্ধুটিই সে-সব করে দিত। বাস্তব অন্য রকম, সেখানে পড়ুয়াদের নিজেদের জোরেই পরীক্ষায় নম্বর পেতে হয়। তবে নম্বরের ছড়াছড়ির এই যুগে ‘মেধা তালিকা’ই সব, তাতে জায়গা করে নেওয়া ‘সফল’ ছাত্রছাত্রীদের ঘিরে আনন্দ-হুল্লোড়ই ‘নিয়ম’, কম নম্বর পাওয়া বা ফেল করা পড়ুয়ারা সেখানে গুরুত্বহীন, অনাদৃত। আর নিয়মের ব্যতিক্রম বলেই অন্তত দু’টি ঘটনা প্রচারমাধ্যমে নজর কাড়ল সম্প্রতি— কর্নাটকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছ’টি বিষয়ে ফেল করার পরেও এক ছাত্রের মা-বাবা রীতিমতো কেক কেটে তা ‘উদ্যাপন’ করলেন; মহারাষ্ট্রেও দেখা গেল, সিবিএসই পরীক্ষায় মাত্র ৩৫ শতাংশ নম্বর পাওয়া একটি ছেলের পরিজন-প্রতিবেশীরা তাকে মালা পরিয়ে, মিষ্টি খাইয়ে ‘অভিনন্দন’ জানালেন।
ধন্দ জাগতে পারে, এ কি তবে ‘ব্যর্থতার উদ্যাপন’? সাফল্য যখন সুদূরপরাহত, তখন ব্যর্থতাকেই অস্ত্র করে, দেখনদারি-সর্বস্ব সময়ের দাবি মেনে প্রচারের আলো পাওয়ার চেষ্টা? সমাজমাধ্যমে বহু মানুষ ব্যঙ্গবিদ্রুপে বিদ্ধ করছেন দুই পড়ুয়া ও তাদের পরিবারকে, কেউ বলছেন ব্যর্থতাকেও এ ভাবে ফুল-মিষ্টি আদর-আপ্যায়নে বড় করে তুললে বরং ছোট করা হয় সাফল্যকেই। আর এমন ভাবে চলতে থাকলে তো এও এক নিয়ম হয়ে দাঁড়াবে— সফল মানুষের সংখ্যাই বিশ্বে কম, অধিকাংশই আপাত-সাফল্যের মোড়কে মাঝারিয়ানা বা ব্যর্থতারই প্রতিমূর্তি; ‘হেরো’দের মাথায় তোলা মানে তো নৈতিকতার, যোগ্যতার জলাঞ্জলি! উল্টো মতটি বলছে, সাফল্য বলতে সমাজ সাধারণত যা ভাবে তা কখনওই প্রকৃত সাফল্য নয়। পরীক্ষায় ভাল নম্বর যে দীর্ঘ-আচরিত এক মাপকাঠি বা সূচক বই বেশি কিছু নয় তা সবার জানা, পরীক্ষা আর জীবনের সাফল্যে বিস্তর তফাত। আবার এও ঠিক যে, কেবল কম নম্বর পাওয়া বা ফেল করা পড়ুয়াই অবসাদে ডুবে যায় না, বেশি নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রীরাও সমান অবসাদের শিকার হতে পারে— দুর্দান্ত নম্বর আর চমৎকার ফলই পরে হয়ে উঠতে পারে তাদের মানসিক ও পারিপার্শ্বিক চাপের কারণ। এই ঘটমান বাস্তবের মুখে দাঁড়িয়ে আপাত-ব্যর্থদের বরণ করে নেওয়া বরং আপাত-সফলকেও এই আশ্বাস জোগাতে পারে যে, কোনও দিন সে-ও ব্যর্থ হলে সব শেষ হয়ে যাবে না, কেউ না কেউ নিশ্চয়ই পিঠ চাপড়ে আদরে কাছে টেনে নেবে তাকে।
সমস্ত যুক্তি-প্রতিযুক্তি, মত-মতান্তর পেরিয়ে এই ‘পাশে থাকা’র বার্তাটিই দিনশেষে আসল কথা। কর্নাটকের ছাত্রটির বাবা বলেছেন, তাঁর মনে হয়েছে বকুনি দিয়ে ‘শিক্ষা দেওয়া’র চেয়ে কেক কাটার মতো আনন্দঘন মোড়কে ‘শেখালে’ তাঁর ছেলে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারবে সহজে, সেই সঙ্গে উৎসাহও পাবে আবার পরীক্ষায় বসার, পাশ করার— হয়তো অনেক ভাল নম্বর নিয়ে, কে বলতে পারে! মহারাষ্ট্রের পড়ুয়াটি ঠিক ততটুকুই নম্বর পেয়েছে যার সামান্য কম হলে মার্কশিটে ‘ফেল’ শব্দটি জ্বলজ্বল করত। সে নিজে এবং তার বাড়ির লোকও মনে করেছিল বুঝি সেই ফেলের খবরটিই আসবে, কিন্তু ওই ৩৫ শতাংশ নম্বর তাদের সবার কাছে অপ্রত্যাশিত, আনন্দবহ এবং সেই কারণেই উদ্যাপনীয়ও হয়ে উঠেছে। প্রতিবেশীরা আনন্দ-মিছিল করেছেন, বড়রা করেছেন আশীর্বাদ। সবচেয়ে বড় কথা, ছেলেটি নিজে বলেছে সে খুব খুশি, ভবিষ্যতে সে আরও ভাল করার চেষ্টা করবে, আইটিআই-তে তার পড়ার ইচ্ছা। দু’টি ক্ষেত্রেই শিক্ষণীয় ও প্রাপ্তি অনেক কিছুই। অধিকাংশ মানুষের কাছে যেখানে সমাজ-সমর্থিত সাফল্যের সংজ্ঞাটিই প্রথম ও শেষ কথা, ব্যর্থতার ছায়াও যেখানে পড়তে পথ পায় না, সেখানে এই দুই পড়ুয়ার মা-বাবা, আত্মীয়-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশী ছাত্র দু’টির তথাকথিত ব্যর্থতাকে শুধু মুক্তকণ্ঠে স্বীকারই করেননি, এক ধাপ এগিয়ে তাকে বরণ করেছেন, দু’টি কিশোরমনকে অভয় জুগিয়েছেন। দুই কিশোরও ফুল মিষ্টি কেক হাসিতে গড়া উৎসবের নিহিত বার্তাটি বুঝেছে, আগামী দিনে কোমর বেঁধে এগোনোর প্রণোদনা পেয়েছে। ভবিষ্যতে কর্মজীবনে ও মানুষ হিসেবে এদের সাফল্য কীর্তিত হবে কি না তা পরের কথা, কিন্তু সেই সম্ভাবনার ভিত্তিপ্রস্তরটি যে আজ এই অন্য রকম উৎসবের আড়ালে স্থাপিত হল না, কে বলতে পারে!
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)