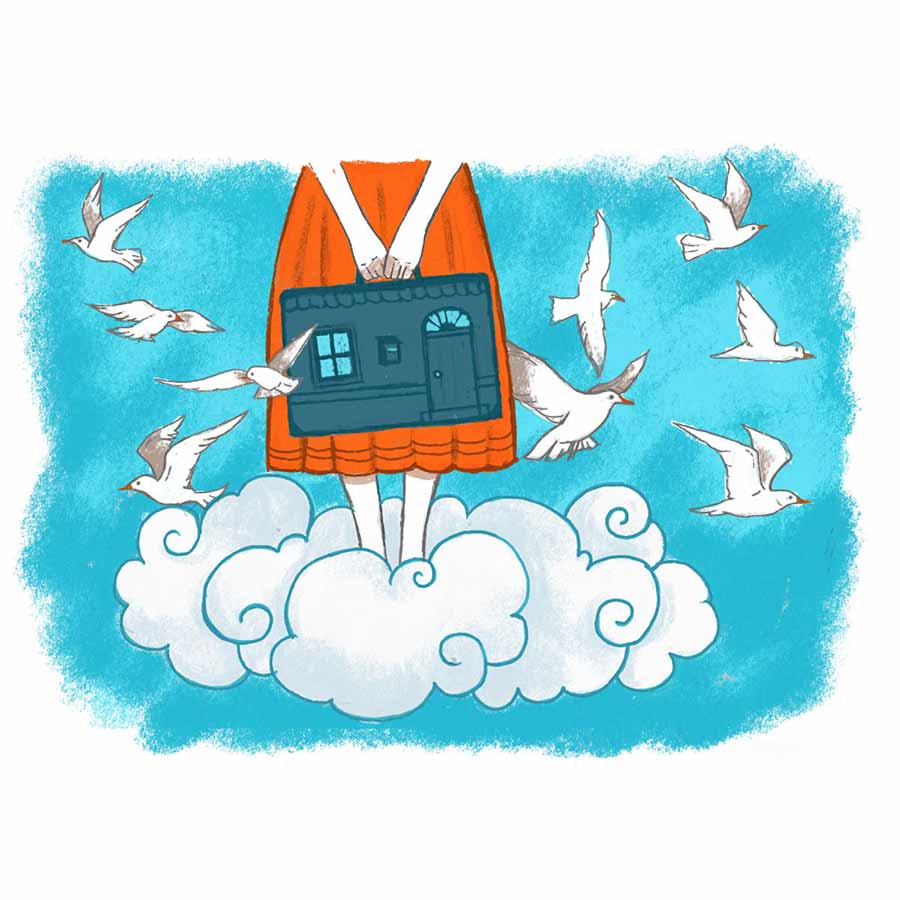তুই ফেলে এসেছিস কারে,
মন মন রে আমার?
নাকছাবি হারানোটা মেয়েদেরই একমাত্র? না কি যে মানুষের চেতনা বস্তুত অর্ধনারীশ্বর, সেই মানুষেরই? যে মানুষের মাথায় রয়ে গেছে যাযাবর-জীবনের যৌথ স্মৃতি? ঘরহারা, অসহায়, পরিযায়ী সমস্ত মানুষ, শুধু ঘর গড়ে আর ফেলে আসে, এই তার ভবিতব্য। অবশ্য লক্ষ বছরের ইতিহাসে, মানুষ শব্দটা কেটে দেশ বসিয়ে দিলেও কি তাই নয়? ভারতের ক্ষেত্রেও প্রাগৈতিহাসিক দিনের স্মৃতি তো আসলে ভাঙন আর হারানোর স্মৃতিই। ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে ওঠা, কচি ছোঁড়া হিমালয়দাদা থেকে শুরু করে বুড়ো বিন্ধ্যদাদু, সবারই আছে নড়েচড়ে বসার ইতিহাস। ভূমি হারানোর সুনামি। গোটা গোটা মহাদেশের আছে গা-মোড়ামুড়ি, পাশ ফিরে শোয়া, কন্টিনেন্টাল শিফট।
তবু মানুষের উৎখাত হওয়ার প্রক্রিয়া আর হারিয়ে ফেলা অপ্রতিরোধ্য অনিবার্য। তা-ই আমাদের কবিতা-গল্প-উপন্যাস দিয়েছে। দিয়েছে ট্রমা থেকে আনন্দ-উত্তেজনার রামধনু রং-বিস্তৃতি। গভীর, গভীরতর ছিন্নমূল জীবনের গাথা তৈরি হয়েছে। আর সেই গাথা আমারও। শুধু মানুষের সন্তান বলেই নয়, এই দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত, দেশভাগছিন্ন, নানা বাত্যাবিক্ষুব্ধ বঙ্গভূমির তনয়া বলেও। আমিও বহন করি অন্তর্গত রক্তের ভিতরে হারানোর বেদনা। অথবা শতচ্ছিন্ন এক মায়াবোধ। ফেলে এসেছি কত কিছু। যার কোনও হিসেব নেই।
প্রকৃত অর্থে মানুষমাত্রের ছিন্নমূল অস্তিত্বের শুরু সেই দিন, যে দিন মাতৃক্রোড় থেকে মা সন্তানকে মাটিতে নামিয়ে রাখেন। মায়ের দুগ্ধধারা তৈলধারাবৎ নিরবচ্ছিন্ন নয়। সেখানেও টান পড়ে। ভালবাসা, স্নেহ, সে সবও শেষ হয়। বার বার এ রকম ঘটবে এর পর। প্রথমে কোল থেকে বিছানায় নামিয়ে দেবেন মা, তার পর নরম বিছানার ঘেরাটোপ থেকে পা রাখতে হবে শক্ত মেঝেতে। পড়ে গিয়ে আঘাত পেতে হবে। তার পরও হাঁটা শিখতে হবে নিজের পায়ে। মনস্তত্ত্বের ভাষায়, স্তন্যপায়ীর পরনির্ভরতা থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের চেতনা। আত্মনিয়ন্ত্রণ পাওয়ার প্রথম পর্ব, হাঁটা। এ আনন্দ পেতে হয় মাতৃস্তন্যত্যাগের বেদনার বিনিময়ে।
আগেকার জন্মনিরোধকহীন সময়ে, দেড়-দু’বছর বয়স হতেই হতেই, তত দিনে মায়ের কোলে এসে যেত পরের সন্তান। ভাই বা বোন। তাকে জায়গা ছাড়তে হত। এখনকার কালে মায়েদের, বাবাদের কোলে-পিঠে চাপার জন্য সময়ই পাওয়া যায় না আর। প্লে-স্কুল থেকে বড় ইস্কুলের দরজা খুলে যায়। তার পর তো সন্তান দূরে দূরে ক্রমশ ছড়িয়েই যেতে থাকবে। বাবা-মা টেনে বেঁধে রাখতে চাইলেও থাকবে না। একটি সফল সন্তান বাবা মাকে ছেড়ে যাবে। যাবেই। সাফল্যের এও এক মাপকাঠি। যত দূর অবধি যায় সন্তান, বাবা-মাও যেন ততই গর্বিত।
কিন্তু এই দ্বৈত, মানে টানা আর ছুড়ে ফেলা, দু’হাতে বাজানো দু’রকম সুর, মানুষের ভবিতব্য। অন্য গন্তব্য টান দেয়, টানে নতুন বন্ধু, প্রেম, যুবক-যুবতীর সাহচর্য। বেড়ে ওঠার অনিবার্য ফলাফল।
ঠিক যে ভাবে ‘পথের পাঁচালী’র অপুর মাকে ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়া। তাই তো সে অপরাজিত। এখানে সেই একই টানা আর হাত ছাড়িয়ে চলা। মা চাইছে, অপু গ্রামেই থাকুক। এক পুরোহিত হয়ে গৃহস্থ যজমানের কলাটা-মুলোটা পাবে। এটা মায়ের স্বপ্ন, কেননা খাওয়া-পরার ভাবনা নেই তাতে। কিন্তু অপুকে ডাক দিচ্ছে হাতে ধরা একটি বিশ্ব। সেই জিয়োগ্রাফি ক্লাসের ভূগোলক। এই দোটানায়, তার সমস্ত পৃথিবী এক দিকে হয়ে যাচ্ছে, আর মা অন্য দিকে। বিদ্যার্জন, ইংরেজি ভাষাশিক্ষা, বড় ইস্কুলে পড়ার আনন্দ, হস্টেল-বাসের উত্তেজনা... সেই অদৃশ্য সুতোর হাতছানি। হয়তো এত বেশি স্পষ্ট করে আর কেউ লেখেননি বিভূতিভূষণ ছাড়া। ‘কামিং অব এজ’ কাহিনি সমস্ত পৃথিবীর সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু আজও। ব্যক্তির বড় হয়ে ওঠা, ব্যক্তিত্ব অর্জনের তিক্ত-কষায়-মিষ্ট কাহিনি। ‘পথের পাঁচালী’র শেষে যে অপুকে, তার নিশ্চিন্দিপুর ছাড়ার মুহূর্তে— “পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন— মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায় কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায়? তোমাদের সোনাডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হয়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে, পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে... দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে, সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশ্যে...”
নিজের ভিতর থেকে নিজেকে হারানো। যে বড় হল, সে সামনের দিকে অনেকটা বিস্তৃত এক পৃথিবীকে দেখতে পায়। যারা পড়ে থাকে, সেই প্রজন্ম ক্রমশ বিবশ হয়ে যায় বেদনায়। সেই প্রজন্মকে দেখলে তেমনই করুণা হয়, যেমন সর্বজয়াকে দেখে অপুর মনে হয়েছিল— “একুশ বছর ধরিয়া মায়ের যে শাসন চলিয়াছিল আজ তাহা শিথিল হইয়া পড়িতেছে, দুর্বল হইয়া পড়িতেছে, নিজের অধিকার আর বোধহয় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না কখনও...” আর তারও পর, ক’জনই বা স্বীকার করতে পেরেছে যে, বাঁধন ছেঁড়া আসলে এক উল্লাসের জন্মও দেয়, স্ববিরোধিতার উৎস হয়ে ওঠে।
“সর্বজয়ার মৃত্যুর পর কিছুকাল অপু এক অদ্ভুত মনোভাবের সহিত পরিচিত হইল। প্রথম অংশটা আনন্দ-মিশ্রিত-এমনকি মায়ের মৃত্যু-সংবাদ প্রথম যখন সে... জানিল, তখন প্রথমটা তাহার মনে একটা আনন্দ, একটা যেন মুক্তির নিঃশ্বাস... একটা বাঁধন-ছেঁড়ার উল্লাস... অতি অল্পক্ষণের জন্য-নিজের অজ্ঞাতসারে। তাহার পরই নিজের মনোভাবে তাহার দুঃখ ও আতঙ্ক উপস্থিত হইল।”
আমার চোখে এই উপাখ্যান সমস্ত শিকড়ছেঁড়া বাঙালিরও বলে মনে হয়। কেননা, ইংরেজি-শিক্ষিত নবজাগরণের বাঙালিরা দেশের পুব প্রান্তের আজব এক জাতি। মূল ভূখণ্ডের ভারতীয়দের তুলনায় অনেকটা বেশি করে, দু’-তিন প্রজন্মের মধ্যেই তারা নিজেদের প্রথা, সংস্কার, রীতি, অনেক কিছুকে ছিঁড়ে এক নিরালম্ব বায়ুভূত অবস্থানে পৌঁছেছে। সে দায় খানিক তো এই গাঙ্গেয় অববাহিকার অতিকর্ষণের। আর খানিক ইংরেজ নাবিক-ব্যবসায়ী এসে নেমে, তাদের ‘কাদামাখা পায়ে’-র তলার তিন গ্রামের কলিকাতা গড়ে তোলার গল্প। কেরানি প্রস্তুতির কারণে ‘শিক্ষিত’ বাঙালির আলোকপ্রাপ্তির উপাখ্যানও বটে। গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালির চিরবিচ্ছেদের মূল সূর।
এক তুমুল হারানোর কাহিনি।
ফিরব বললে ফেরা যায় নাকি?
একটা স্বপ্ন দেখেছি।
নিউ ইয়র্ক সিটিতে ফেলে এসেছি আমারইঅন্য অংশটাকে।
ফিরে যেতে হবে এখন সেটা আনতে।
কিন্তু নড়তে পারছি না।
কেবল ভাবনা হচ্ছে
জানালাগুলো বন্ধ করে এসেছি তো
ফুলগুলোকে ঝরে যেতে দিয়ে এলাম না তো
খাবারগুলো পচে যাচ্ছে না তো
— (নাতালি হান্দাল, আমেরিকার প্রেমেরস্বপ্ন, রোমে)
প্যালেস্টাইনি-আমেরিকান কবি নাতালি হান্দালের কবিতা বার বার বলে শিকড় ছেঁড়ার বেদনার কথা। গোটা প্যালেস্টাইন হারানোর গাথা। আর আজকের গাজ়া ভূখণ্ডের বেদনা শুধু এক গোষ্ঠীর নয়, সারা পৃথিবীর সঙ্কট। প্যালেস্টাইনি সত্তার বেদনাকে আমরাও ধরতে-ছুঁতে পারি। কেননা উৎখাত হওয়া আর বার বার ঘর গড়ে তোলার প্রবল উচ্চাবচ আন্দোলন তার মানবিক মুখ সমেত আমাদের উপর ঝাঁপায়। যে ভাবে গাজ়ার যুদ্ধবিধ্বস্ত ভাঙচুরের ভিতরে মানুষ ব্যবহার্য কিছু খুঁজে নিচ্ছেন, এ বুকভাঙা দৃশ্য টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পাওয়া যায়, মৃত ও আহত ও রুগ্ণ অভুক্তের সারিবদ্ধ ছবির পাশেই।
বাঙালিরও দিনগত পাপক্ষয়ের অংশ না-খেয়ে থাকার যৌথ স্মৃতিও। জোর করে খুঁচিয়ে তোলা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হতেই পারে, তবু আজও তা চলেছে সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। আর ১৯৪৭-পরবর্তী কয়েকটি তরঙ্গে ও-পার বাংলা থেকে উৎখাত মানুষের স্রোত পুনঃ পুনঃ আছড়ে পড়েছে এ বাংলায় দেশভাগের পর থেকে। বার বার দুর্ভিক্ষতাড়িত বা দাঙ্গাসন্ত্রস্ত মানুষের দল এসেছেন। স্টেশন চত্বরে বা হঠাৎ কলোনিতে, জবরদখল বাড়িতে গড়ে উঠেছে উদ্বাস্তু বাঙালির নতুন নতুন ঘরবাঁধা। পাতের কোণে একটাও ভাতের চাল না ফেলার অঙ্গীকার-সহ। আর কোনও এক সুবাতাসের দিনে এক চিলতে পুঁইমাচার স্বপ্ন-সহ।
দেশে দেশে অবশ্য যত দিন যাচ্ছে, তত বাড়ছে শরণার্থীর দল। হয়তো ধর্ম, হয়তো জাতিসত্তা, হয়তো অন্য কোনও বিশেষ পরিচিতির কারণে স্বভূমি থেকে উৎখাত মানুষের সংখ্যাটা ঠিক কত? কাজের জন্য পরিযায়ী অথবা গৃহযুদ্ধে বিতাড়িত, নানা ভাবে ভিটেছাড়া মানুষ এখন পৃথিবীর জনসংখ্যার চার শতাংশ। ১৯৯০ সালে যে সংখ্যা ছিল ১৫ কোটি ৪০ লক্ষ, এখন তা ৩০ কোটিরও বেশি। ১২ কোটি ৩০ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের মধ্যে চার কোটির উপর শরণার্থী।
বাঙালি মানসিক, আত্মিক, আবেগতাড়িত জাতি। বহু যুগ থেকেই স্বপ্ন, বাঙালির ভাতের সঙ্গে মেখে খাওয়ার একটি আবশ্যিক পদ। খাটের তলার নারকেলের স্তূপের গল্প করতে করতে, আমের সময়ে কাঁসার জামবাটিতে আমের কথা কইতে কইতে, পুকুর-ভর্তি মাছ আর খেত-ভর্তি ধানের কথা বলতে বলতে, প্রতি সংক্রান্তিতে মা-দিদিমার হাতের অজস্র পিঠেপুলির স্বপ্ন দেখতে দেখতে হারানো দিনের জন্য হাহাকার, এমন একটা লালমোহনবাবু-সুলভ নামের গর্তে ঢুকে গেছে বাঙালি।
তবে আমাদের প্রজন্মই বোধ হয় শেষ প্রজন্ম, যাদের সর্বদা দু’নৌকায় পা। পরের প্রজন্মের অত লটবহর, আজকের ভাষায় ‘ইমোশনাল ব্যাগেজ’ নেই। স্মৃতি নেই, তাই স্মৃতিকাতরতাও নেই।
আমাদের সেই সব কৌমজীবন কৃষিভিত্তিক নেই। এক প্রজন্মেই হারিয়ে ফেললাম নলসংক্রান্তি, ধানের পোয়াতি হওয়ার সাধভক্ষণ, আদাড়বাদাড় থেকে কুড়িয়ে, অকৃষির ফসল দিয়ে রান্না করা গাড়ুর ডালের সংস্কৃতি। হারালাম নবান্ন পালন। ভোররাতে কলাপাতায় দুধ, নতুন আতপ চাল ভেজানো, নারকেল-কোরা আর সদ্য ওঠা কমলালেবুর কোয়া ছাড়িয়ে, মেখে, কাকেদের গিয়ে ছাতে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করানো— ‘কৌয়া কো কো কো, আমাগো বাড়িতে আজ শুভ নবান্ন।’
আমরা তো হারিয়ে ফেলছি আমাদের ভাষাও। ভাষার উঠোনে অনেক রোদ্দুর। উঠোনের এক দিকে বিছানো সাদা কাপড়ের উপর আচার ও বড়ি। আমসত্ত্ব। হাতে করে পাকা আম আর গুড় ঘুঁটে সেই তরলকে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে সূর্যকিরণের মহিমার তলায়। বেতের জালি বা চাটাই কিংবা কুলো-ধামা ইত্যাদির উপর। ফলে শুকোনোর পর সেই পাতলা কালচে অসামান্য স্বাদের আমসত্ত্বের এক পিঠে খাঁজকাটা কাটা দাগ, প্যাটার্ন তৈরি হয়েছে। ছিঁড়ে ছিঁড়ে সেই আমসত্ত্ব খেতে হয়।
যদিও স্বীকার করি না, ঘরে-বাঁধা অজস্র মেয়েদের অবিরত শ্রমদানের বদলে পাওয়া গিয়েছিল ওই সংস্কৃতিটি। স্বীকার করি না, শারীরিক শ্রমের বিকল্প নেই এই স্বপ্নের উঠোনটায়, যেটা আর কোথাও নেই। এ শুধু শান্তা সেনের ‘পিতামহী’, রাণী চন্দের ‘আমার মা’র বাপের বাড়ি’ বা সুনন্দা শিকদারের ‘দয়াময়ীর কথা’ বইতে পড়া।
আসলে স্মৃতি তো ভাষাবিশ্বও। গল্পগুলোই থাকে ভাষায়, আর ভাষার বিলোপে সেগুলোও হারায়। এ ভাবেই অজস্র বাঙালি বা বাংলা-ভাষাভাষী নিজেদের শিকড়ের ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন। তিন প্রজন্ম আগে হয়তো বলা হত সিলেট বা চাটগাঁর ভাষা, এখন মান্য কলকাতাইয়া ভাষা বলা হয়। অথবা আরও পরের কোনও প্রজন্ম হিন্দি বা ইংরেজিতেই কথা বলছে শুধুই।
বরিশালের স্থানীয় ভাষার অনবদ্য এই গল্পটি পুনরায় বলি। যার মূলে আছে এই বিলুপ্ত তথ্য যে, বাড়ির গাছের কাঁঠাল পাকার পর, খাজা কোয়াগুলো খাওয়ার পর জড়ো হত কাঁঠালের বীজ। আর কাঁঠালের বীজ প্রথমে রোদে শুকিয়ে তার পর উনুনের নীচের ছাইয়ের মধ্যে মরা আঁচে ভাজা ভাজা করে, অথবা শুকনো কড়াতে তেলে বা খোলায় ভাজা হত। তার পর সেগুলো হয়ে যেত, যখন-তখন ঘুরতে-ফিরতে ছোটদের চেখে খাওয়ার জিনিস। আমাদের আজকের ভাষায় ‘স্ন্যাক্স’।
এ আমার দিদিমার বলা গল্প। পরে তপন রায়চৌধুরীর ‘রোমন্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তর পরচরিতচর্চা’তেও এ গল্পের অনুরূপ কিছু পাই। বাচ্চা ছেলে, জেঠিমার কাছে কাঁঠালের বীজ চেয়েছে খেতে। জেঠিমা ব্যস্ত, বলেছে জেঠার কাছে চাইতে। বাচ্চা বলেছে, ‘জেঠা শালায় ত দিল না।’ জেঠিমা ক্ষিপ্ত। বলেন, ‘জেঠাকে শালা বলিস? যা প্রণাম কর গিয়ে।’ প্রণাম করা হল সে ভাষায় ‘হোগা উপুত করে হ্যাবা দেওয়া’। হে অর্বাচীন পাঠক, এখানে ‘হোগা’ পশ্চাদ্দেশ এবং ‘হ্যাবা’ সেবা বা প্রণাম—
জ়েডিমা লো জ়েডিমা মোগে এউগ্যা কাডালের আডি দে,
চা গিয়া তোর জ়্যাডাড্ডে
হে হালায় ত দিলে না
জ়্যাডারে কও হালা
হোগা উপুত কইরা হ্যাবা দে হ্যাবা দে।
এই ভাষাবিশ্বটাও লোপাট হয়েছে তাদের বসবাস, তাদের ব্যবহারিক অভ্যাসের মতো।
তবু নিউটনের তৃতীয় সূত্রের মতো, দেশ-ছাড়া বাঙালি এখন বেশি বেশি স্মৃতিকাতর। এমনকি, বিশ্ব-নাগরিক বাঙালি এখন বাংলার মা-দিদিমার হাতের পুরনো রান্নার ভ্লগ বানিয়ে তুমুল লাইক পাচ্ছেন, যার অনেকগুলিই ‘কনটেন্ট’ হিসেবে সংরক্ষণ করছেন পুরনো রেসিপি, পুরনো প্রথা। বিদেশে বসবাসকারী, মগজ-বেচা, ডায়াস্পোরার বাঙালির দ্বিতীয় প্রজন্ম, না-ঘর কা না-ঘাট কা হয়েও কাতর হয়েছেন মধ্যবয়সের ঝোঁকে, বাড়ি-জমি কিনেছেন। ফিরে আসার স্বপ্নও দেখেন।
“ফিরব বললে ফেরা যায় নাকি? হারিয়েছ দেশ কাল জানো না কি...”
আমি হারিয়ে ফেলেছি আমার ভূগোল
“দি আর্ট অব লুজ়িং ইজ়ন্ট হার্ড টু মাস্টার;/ সো মেনি থিংস সিম ফিলড উইথ দ্য ইনটেন্ট/ টু বি লস্ট দ্যাট দেয়ার লস ইজ় নো ডিজ়াস্টার...” (এলিজ়াবেথ বিশপ ‘ওয়ান আর্ট’)
এলিজ়াবেথ বিশপ লিখেছিলেন, তাঁর ‘ওয়ান আর্ট’ কবিতায়, হারিয়ে ফেলাও এক শিল্প। খুব একটা কঠিন শিল্প নয়। হারিয়ে যায় কত স্মৃতি, মুখ, নাম। এমনকি নিজের ভূগোলও। বিশপ বলছেন, ঘরের চাবি থেকে শুরু করে, কত জায়গাও হারিয়ে যায়। যে যে বাড়িগুলোতে থেকেছি জীবনের কোনও না কোনও সময়ে, দুটো বাড়িই হারিয়েছি। হারিয়েছি দু’টি সুন্দর শহর। হারিয়েছি কিছু জগৎ, যা আমার ছিল। দুটো নদীকে হারিয়েছি, একটা মহাদেশকেও। এদের জন্য কষ্ট হয়, কিন্তু ভয়ানক কিছু নয়। হারিয়ে ফেলা খুব সহজ। এমনকি তোমাকেও!
এলিজ়াবেথ বিশপের মতো আমি একটা গোটা মহাদেশ হারাইনি। নিজের ভিতর থেকে হারিয়েছি শুধু কিছু ভূগোল। আমার ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়স অবধি একটা ভূগোল ছিল। সে ভূগোলে দক্ষিণ কলকাতার গলি, মসজিদের আজান, মোড়ের আলুর চপের দোকান, ফিশফ্রাইয়ের গন্ধ, বাসের ধুলো-ধোঁয়া। সে ভূগোলে পুরনো বাড়ি, পঁয়ত্রিশটা অবধি পোষা বেড়াল, খুব ঝুল-ভর্তি কিছু বড় বড় ঘর, অনেক দরজার সমান জানালা ছিল। ছিল অনেক হাওয়া, একটা একলা বসার ছাদ, সন্ধেবেলা সে ছাদের উপরের আকাশটা দিয়ে উড়ে যাওয়া কিছু বালিহাঁস, যারা কঁক-কঁক করে অদ্ভুত বিষণ্ণ একটা ডাক ডাকত। সে ভূগোলে ছিল অনেক বই, ধুলো-জমাট। ছিল মায়ের আঁকা পেন্টিং-এর ক্যানভাসে বোঝাই একটা ঘর। সে ঘরের কোণে এক চিলতে জায়গায় আমার ছোট্ট বসবার ঘর তৈরি করার প্রচেষ্টা, পুরনো ফার্নিচার দিয়ে সাজিয়ে। সেই বেতের চেয়ারগুলো, ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করা। জীবনের প্রথম ছেলেবন্ধুদের সঙ্গে সেই ঘরে নীরব, অর্ধনীরব কথা-চালাচালি। বিমূঢ় বা বিভ্রান্ত। নার্ভাস, অকওয়ার্ড। জীবন বাঁচা প্র্যাকটিস হয়নি তখনও হয়তো। তাই।
আমি হারিয়েছি আমার দেখা সত্তর দশকের কলকাতা, কমলাগন্ধী বর্তুল আকারের লজেন্স, যা গলায় ঢুকলে শ্বাসরোধ অনিবার্য, তবু শিশুদের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। হারিয়েছি আরও নানা স্বাদ-গন্ধের লজেন্স, ‘আনন্দমেলা’র মতো আরও শিশু-কিশোর পত্রিকা, অরেঞ্জ স্কোয়াশ বা ঝাঁঝালো নরম পানীয়-শাসিত শৈশব কৈশোর।
হারিয়ে ফেলেছি নকশাল আমল, বাংলাদেশের যুদ্ধ, ইন্দিরা গান্ধীর ‘ইমার্জেন্সি’র আলোচনা, শৈশবে যার কিছুই বুঝিনি। হারিয়েছি পঁচাত্তর সালে প্রথম ঘরে ঘরে ঢুকে আসা দূরদর্শন সম্প্রচারের থিম মিউজ়িক-সহ বোকাবাক্সের দিন, পেলের খেলা দেখতে পাশের বাড়িতে ধাওয়া করা দিন, সে সব দিনে রবিবারের ‘মহাভারত’ সিরিয়ালের সময়ে পাড়া থমথমে হয়ে যেত। হারিয়েছি রেডিয়োতে শোনা বিবিধ ভারতীর হিন্দি গান। রাহুল দেব বর্মণ-আশা ভোঁসলের দেওয়া একমাত্র রিলিফ, পাশের বাড়ির জানালা থেকে ভেসে আসা, অন্তহীন অনুশীলনীর অঙ্কের ভিতরে।
দক্ষিণ কলকাতায় বড় হয়ে ওঠা আর উত্তর কলকাতার মামাবাড়ির শৈশবস্মৃতি চলে গেছে ঠুনকো বাসনের মতো আলমারির কোণে, আর লবণহ্রদের শ্বশুরবাড়িতে যেতে হয়েছে যখন, আবার ভূগোল হারানোর বিবশতা চেপে বসেছে। মনে হয়েছে আশপাশে দোকান-বাজারহীন মরুভূমি, এখানে লোকে বাস করে কী ভাবে? তথাপি সন্তানের ইস্কুল, নাচ-গান-আঁকার ইস্কুল ধরে ধরে পা টিপে টিপে চেনা হয়েছে লবণ হ্রদ। তার উদ্ভট ব্লক-তত্ত্ব, এ বি সি ডি-র দু’টি দু’টির জুটি দিয়ে সাজানো চতুষ্কোণ লবণ হ্রদ। চিরকাল হারিয়ে যাওয়ার জায়গা ছিল সবার এই ভেড়ি-বুজিয়ে-তৈরি নব্য আবাসস্থলটি। ঠিকানা দেখে বাড়ি খোঁজার সেই সব দুর্বোধ্য ধাঁধা সমাধান করতে শিখেছি অনায়াসে।
চাকরির জন্য বার বার বাসাবদল ঘটেছে। অসংখ্য ট্যুরে পৃথিবীর নানা কিনারায় যাওয়াও সম্ভব হয়েছে। আর ক্রমশ বুঝেছি, প্রতিটি নতুন ঘরেই বার বার শূন্য থেকে শুরু করতে হয়। আসলে কোনও বাড়ি নেই, গৃহ নেই। বাসা আছে। তা সাজিয়ে তুলতে হয় উনুন, উনুনের পাশে হলুদ নুনের কৌটো, জিরে ধনে মুসুর ডালের কৌটো রেখে। প্রতিটি আলাদা বাড়ির আছে সূর্যালোকিত এক-একটা ভিন্ন জানালা, প্রতি বাড়ির আছে নিজস্ব ইঁদুর বা ব্যাং ঢোকার গোপন সুড়ঙ্গ, প্রতি বাড়িতেই রচিত হবে স্মৃতি। বেলাশেষে, গোছগাছ করে বেরিয়েও যেতে হবে, আর প্রতি বারই ঘর-বদলের সময়ে সারা ঘরে উড়ে বেড়াবে শ্মশান-বৈরাগ্যের ছেঁড়া প্লাস্টিক, টুকরো প্যাকিং কেস, পুরনো খবরের কাগজ।
প্রতি বার উদ্বাস্তু হই আমি আর প্রতি বার আমার ভিতরে টান দেয় সেই পুরনো নিরাপত্তাহীনতা। নিজস্ব কোনও ঘর নেই আমার। বাপের বাড়িতেও ফিরতে পারি না, আর শ্বশুরবাড়িও আপন হয় না। দিনের পর দিন ধরে থাকা শুধু অভ্যাস হয়ে যায়। অনেকটা দিনযাপনের মধ্যে স্বর্গীয় এক-একটা দুপুরে এক-একটা পরিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত হয়। দু’-তিনটি গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতের স্মৃতি থেকে যায়।
ভারতের নানা প্রান্তের বৈশিষ্ট্য খুঁটে চলি। রাঁচির ডোরান্ডাবাজারের স্তূপীকৃত লাল গাজরের রং বা অসমের রঙালি বিহুর দিনে অফিসে বিতরণ হওয়া জ্যান্ত মুরগি, লটারির প্রথম প্রাইজ়... কিছুই ভুলি না। তবু কোথাও নোঙর থাকে না সত্তার।
মেয়েদের হারানো আর পাওয়া
তোমাকে দেওয়া হল একটা নম্বর।
যেমন দেয় কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে।
ঢুকে পড়, স্বাধীন হয়ে যাও
একমাত্র সম্ভাব্য স্বাধীনতা।...
একটা বেসিন, একটা খাট। একটা আলমারি।
ছাই ছাই রঙের ওয়ালপেপার।
এক্কেবারে নৈর্ব্যক্তিক।
কিন্তু এখানেই এসে তুমি নিজেকে খুঁজে পেলে।
— ব্লাগা দিমিত্রোভা/ হোটেলের ঘর(ভিয়েনা, ১৯৬৬)
মেয়েরাই হারায় সবচেয়ে বেশি। এ বিষয়ে সন্দেহের জায়গা কোথায় আর! সংসার, সন্তান হেঁশেল সামলানোর জৈবিক, সামাজিক ও আন্তরিক দায়ভার নিয়ে, তারা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে চায় সবাইকে। বেড়াল-মায়ের মতো ঘেঁটি ধরে ধরে বাসা-বদলের সময়ে প্রতিটি জিনিস তুলে আনতে চায় নিপুণ ভাবে। আর ছিন্নমূল হওয়ার সময়ে সবচেয়ে বেদনা যায় তাদের শরীর ও মনের উপর দিয়ে। ঠিক যেমন সব যুদ্ধ লড়া হয় মেয়েদের শরীরের উপর দিয়ে। তেমন, বাঁটোয়ারাও হয় মেয়েদের হৃদয়ের ভিতর দিয়ে। আর সব শেষে তারা দেখে, তাদের আসলে কোনও গৃহ নেই। সে ভারতের মেয়ে হলেও নেই, আর ব্লাগা দিমিত্রোভার মতো বুলগেরিয়ার বামপন্থী নেত্রী কবি হলেও নেই।
সিরিয়ার মা-কে দেখেছি লেবাননের, বেইরুটের ফুটপাতে, প্যাকিং বক্সের ভাঁজ-করা কার্ডবোর্ড বক্সের আসন পেতে বসে থাকতে। সঙ্গে ফুটফুটে দেবশিশুর মতো বাচ্চা। একটা রুটি চাইছে হাত পেতে। বড় বড় ভাঁজ করা রুমালি রুটি বা স্থানীয় পিটা ব্রেড, প্লাস্টিকে বন্দি, অল্পদামে কিনে দিয়ে যাচ্ছে পথচারী। সারা দিনের খাদ্য সেই। সিরিয়ার মা-টির শরীরের উপর দিয়ে গৃহযুদ্ধ বয়ে গেছে। আরও কত এমন মা পৃথিবীর কোন কোন কোণে, শীতলতম আকাশের তলায়, সন্তানকে বুকে আঁকড়ে ভিক্ষারত। হয়তো দেহ বিক্রিতেও সম্মত, শিশুর মুখে খাবার তুলে দিতে। নিজে আধপেটা খেয়ে থেকেও।
মেয়েদের নিজস্বতা অর্জনের পথে বায়োলজিক্যাল ক্লকটি সর্বাপেক্ষা বড় বাধা তো বটেই। আমাদের নিজস্বতা নিয়ত বহু আয়না-যুক্ত ঘরের মতো, ভেঙে ভেঙে যায়। আমরা কখনও মা, কখনও স্ত্রী, কখনও কন্যা হিসেবে, পুত্রবধূ অথবা অন্য সম্পর্কের নিরিখে নিজেদের ‘আত্মীকরণ’ করছি, আর কোথাও কেন্দ্রীভূত অসন্তোষ জমছে। আশাপূর্ণা দেবী ‘উৎসব’ গল্পে দেখিয়েছেন কী কঠোর সত্য। পরিবারের মা-টি, নিজের স্বামী, সন্তান কারও কাছে সম্পূর্ণ আদর সম্ভ্রম বা প্রত্যাশিত পূর্ণ আনন্দটি পান না, অথচ তিনি ঘর-ভরা এক উৎসব রচনা করতে চেয়েছিলেন। শেষ অবধি সবার নিজেদের মধ্যে রেষারেষি, ঝগড়াঝাঁটি থেকে যায়। এ সব আশাপূর্ণা যে ভাবে এক্স-রে চোখে দেখান, তা অনবদ্য। দৈনন্দিন ও সামান্য হলেও এ সার্বিক পরিবারের সত্য।
ঠিক সেই সত্যের অপর রূপ আমরা দেখেছি মেয়েদের আত্মজীবনীর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। আজ যে বই বিশেষ অনুধ্যানের, সেই মেয়েদের বাংলায় লেখা প্রথম আত্মজীবনীকার রাসসুন্দরীর উপমা ব্যবহার বলে দিয়েছে, নীরবে থেকেও সমাজের প্রতিটি অন্যায়কে চিরে দেখা যায়। বিবাহের কনের কান্নার সঙ্গে বলির পশুর ‘ম্যা-ম্যা’ ডাকের মিল পেয়েছিলেন তিনি। পরিবারে আবদ্ধ বধূর ‘দায়মালী কারাগারে’ বন্দিত্বের উপমা দিয়েছিলেন। বিনোদিনী দাসী ‘আমার কথা’-য়, নিজের অভিনয়জীবনের কথা লেখেন আত্মসচেতন ভঙ্গিতেই, কিন্তু নিজস্বতা অর্জনের পথটা খুব কঠিন থেকে যায় তাঁরও। ‘সংসারী মেয়েরাই মেয়েদের স্টিরিওটাইপ’, তাই বিনোদিনী সংসারহীনতার, বা চোরাবালি-র কথা বলেন। অথবা সাহানা দেবী ‘স্মৃতির খেয়া’-য় বলেন ‘সংসার করতে ভাল লাগত না।’ মনীষা রায়ের ‘আমার চার বাড়ি’, এক অর্থে কোনও মেয়ের নিজস্ব বাড়ি খুঁজে পাওয়ার যাত্রা যেন। নিজস্ব ঘরের অন্বেষণ, যা ভার্জিনিয়া উলফের ‘আ রুম অব ওয়ান’স ওন’-কে মনে করায়।
বেড়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে নিজেকে খোয়াতে খোয়াতে চলার, মেয়েসত্তার লৌহমুখোশের তলায় নিজেকে হারিয়ে ফেলার কাহিনি লিখে গেছেন সারদাসুন্দরী, মনোদা দেবী, প্রিয়বালা গুপ্তা, পূর্ণশশী দেবী, লীলা মজুমদার, সুদক্ষিণা সেনেরা। উপদেশ আর ঔচিত্যের তলায় হারিয়ে যাওয়া শৈশবের কথা খুঁজে পাব ঊনবিংশ শতকের মেয়েদের লেখায়, পাব মেয়েলি খেলা খেলতে বাধ্য হওয়া মেয়েদের পরবর্তী প্রজন্মের কথাও, যদিও শিক্ষায় আর বাধা ছিল না তখন। পাব হেমন্তবালা দেবীর ব্যতিক্রমী কণ্ঠ, স্বামী বা পতিভক্তির আদর্শের সমালোচনামুখর। শান্তা দেবী, সীতা দেবী, শান্তিসুধা ঘোষদের স্মৃতিকথা থেকেও তুলে আনা যায় সাহিত্য-স্বপ্ন-নিজস্বতা অর্জনের ব্যক্তিগত ভ্রমণপথগুলি। স্ত্রী, মা, বধূ, বোন, কন্যা— নানা সম্পর্কের ভিতরে বন্দিত্ব। এর ভিতরে কোথায় হারায় নারীর ব্যক্তিগত স্বর, যা অপ্রকাশ্য বাইরের ওই সব লেবেল লাগানো জীবনে। আত্মজীবনীতেও ‘রিডিং বিটুইন দ্য লাইন’ করে খুঁজে নিতে হয় মেয়েদের নিজের কথাটি। স্বামীর বংশের স্তুতিলিখন, বা ঈশ্বরের প্রশস্তির মাঝে, জীবনানন্দ-মাতা কুসুমকুমারীকে তাঁর ডায়েরিতে, বা শোভা ঘোষকে তাঁর স্মৃতিকথায় খুঁজে পেতেহয় আমাদের।
আসলে নাকছাবি হারিয়েই থাকে, খুঁজে পায় না মেয়েরা। কয়েক জন মাত্র চেষ্টাটুকু করে, যে ভাবে গীতা চট্টোপাধ্যায় লেখেন—
বাড়ির গোপন এক কুঠুরির মধ্যে চোরা সিঁড়ি বেয়ে
হীরে পান্না গাছের দেশে একটি মরচে চাবি খালি
হারিয়ে গেছে জীবনভর সে-সন্ধানও তো দিয়ে যাবো
বেহালা ট্রাম গড়ের মাঠে হাত ধরে মন,শীতের সকাল,
পশমবোনা কপিপাতা স্কার্টটা দেখিস দিয়ে যাবো।
বড় আফসোস ছিল ছোটবেলায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নবীন কিশোরকেই কেবল দিয়ে গেছেন ভুবনডাঙার মেঘলা আকাশ! কিন্তু গীতা চট্টোপাধ্যায় আমাদের ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন সেই মরচে-ধরা চাবির সন্ধান, যা দিয়ে খোলা যাবে নিজস্ব গোপন কুঠুরিটি।
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)