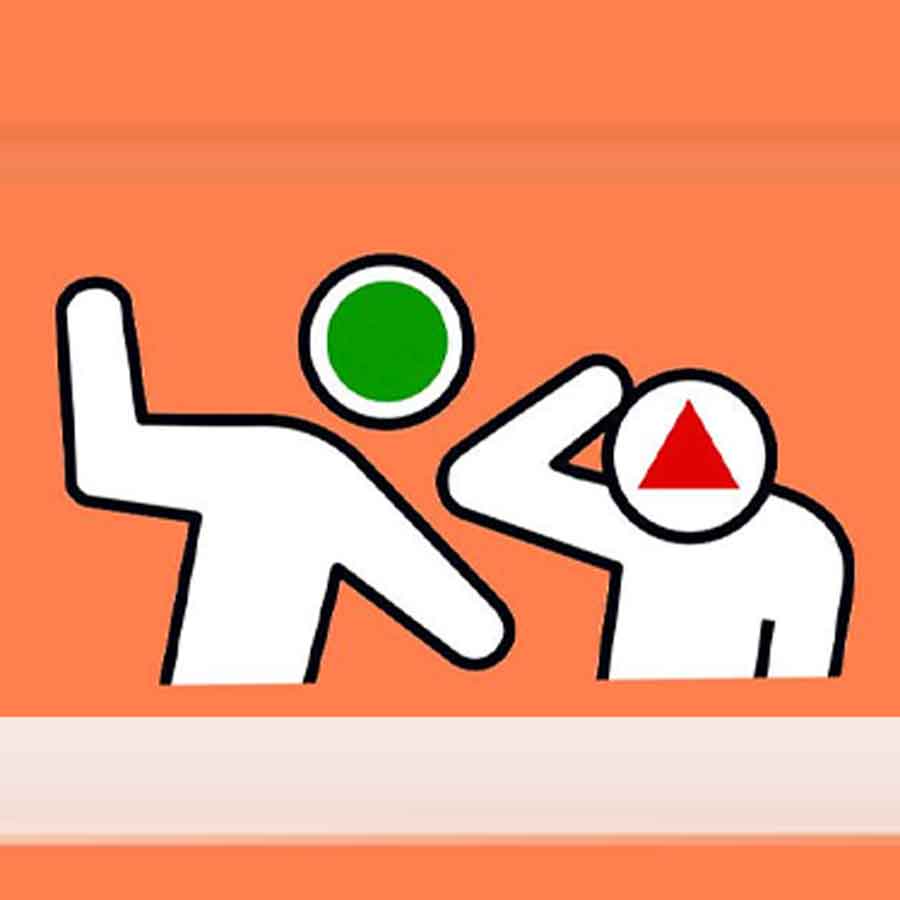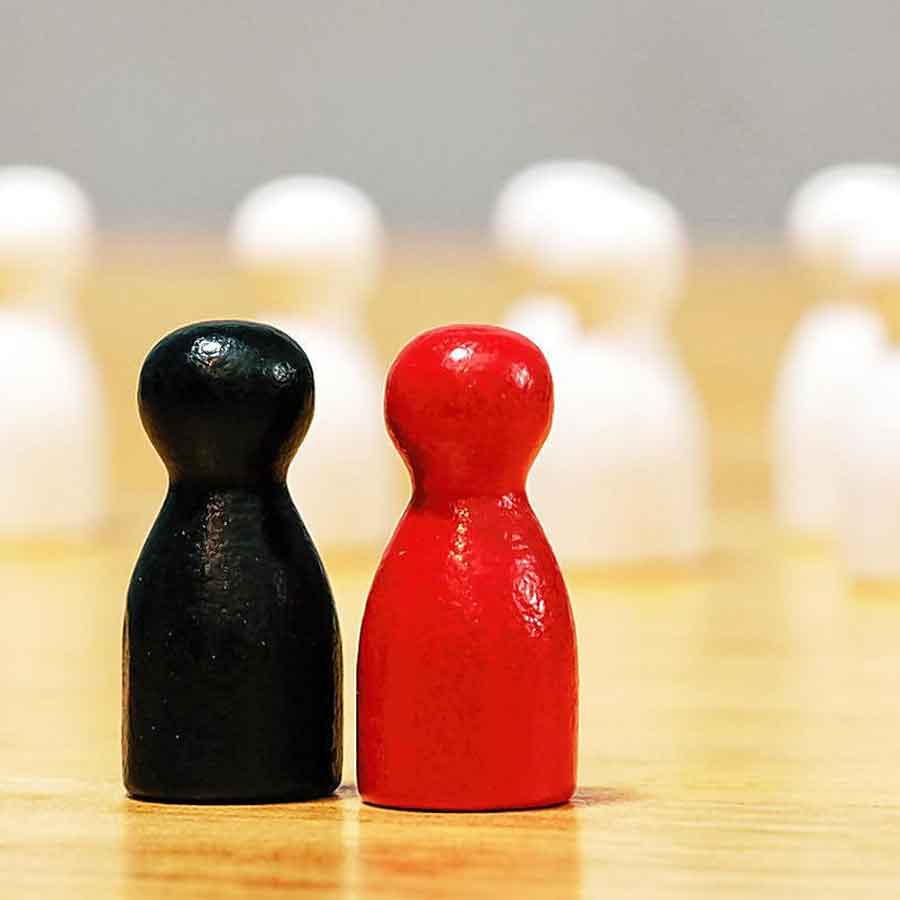ছোটবেলা থেকেই পাপিয়ার একটা নিজস্ব কোলবালিশের খুব শখ। পুঁচকে বয়সের কথা ওর এখনও আবছা-আবছা মনে পড়ে। বিছানার এক পাশে বাবা, অন্য পাশে মা, মাঝে ও আর ওর দুই পায়ের মাঝে চেপে রাখা নতুন নরম কোলবালিশটা। গায়ে লেমন গ্রিন সুতির খোল জড়ানো। সেই তাজা সবুজ ঘাসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লাল স্ট্রবেরিগুলো দেখে মনে হত, ওদের টুকটুকে গায়ে হাত ছোঁয়ালেই ওরা যেন জীবন্ত হয়ে উঠবে। তার পর দু’আঙুলে তুলে নিয়ে এক বার গালে পুরলেই মুখের ভিতরটা ভরে উঠবে টসটসে স্বাদু রসে।
কোলবালিশ কোলে দিনগুলো ভালই কাটছিল পাপিয়ার। কিন্তু সে যখন পাঁচ বছরের খুকি, তখন তার ভাইয়ের আগমন ঘটল। ছোট থেকেই দুরন্ত আর জেদি। দিদিকে কিছুতেই ওই কোলবালিশের দখল নিতে দেবে না। দেখা গেল সে জন্য ভাইকে বকাবকি করা তো দূরের কথা, কিছু বলতে গেলেই মা কেমন রেগে উঠছেন পাপিয়ার উপর। ওর একমাত্র সাপোর্টার বাবা তত দিনে রাতে শোওয়ার সময় বাইরের ঘরের সোফা-কাম-বেডে ট্রান্সফার নিয়েছেন। পাপিয়া পড়ল ভারী মুশকিলে। স্কুল থেকে ফিরে বা গরমের ছুটির দুপুরগুলোয় ও কাতর চোখে তাকিয়ে থাকত ওর সাধের কোলবালিশটার দিকে। ভাইয়ের অত্যাচারে সেটার একদম আলুথালু অবস্থা। ফ্যাকাসে হয়ে আসা ঘাসের বিছানায় পড়ে থাকা স্ট্রবেরিগুলোর কী পানসে চেহারা! মা গো!
তার পর সেই পুরনো কোলবালিশ ভেঙে সবটা তুলো বার করে ফেলে আবার নতুন করে গড়া হল। সেই সঙ্গে ভাইও তরতরিয়ে লম্বা হল। ঠোঁটের উপরে হালকা গোঁফের রেখা। অঙ্কে ব্রিলিয়ান্ট! স্বপ্ন অ্যাস্ট্রোফিজ়িক্স নিয়ে পড়ার। রাত জেগে পড়াশোনার জন্য ভাই গিয়ে আশ্রয় নিল দোতলার চিলেকোঠার ঘরে। সঙ্গে গেল সেই কোলবালিশ। সেখান থেকেই এক দিন কোলবালিশ পাড়ি দিল পুণের হস্টেলে। পাপিয়ার তখন গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট। সরকারি চাকরির চেষ্টা চালাচ্ছে। এর মধ্যেই খান তিনেক এসে যাওয়া সম্বন্ধের ভিতরে একখানা বেশ ক্লিক করে গেল। ছেলে প্রাইভেট ব্যাঙ্কের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। পরের বৈশাখেই বিয়ের দিন ঠিকঠাক।
মেয়ের কোলবালিশের প্রতি অসম্ভব টানের কথা পাপিয়ার মা মৌসুমির মোটেই অজানা নেই। তিনি তো রাতের পর রাত দেখেছেন, তুলতুলে কোলবালিশে শরীরটাকে প্রায় ডুবিয়ে রাখা ঘুমন্ত ভাইয়ের দিকে হ্যাংলার মতো তাকিয়ে আছে ছোট্ট পাপিয়া। ওকে আলাদা একটা কোলবালিশ বানিয়ে দেওয়ার জন্যও মায়ের কাছে কত যে আবদার করেছে মেয়ে! বিরক্ত হয়ে মৌসুমি এক দিন মেয়েকে বলেছিলেন, “সংসারে এত খরচ, তুই আর জ্বালাস না তো বাপু। আজ নয় কাল ভাই তো বাইরে চলেই যাবে পড়তে। তখন কোলবালিশটা শুধু তোর। হয়েছে শান্তি?”
“ভাই কবে বাইরে যাবে মা?” আকুল স্বরে তাঁকে জিজ্ঞেস করল দুই বেণি দোলানো ক্লাস এইটের পাপিয়া।
“আহ্! যাবে, যাবে! ভাইটাকে বাড়িছাড়া না করলে শান্তি নেই তোমার, তাই না?” মেয়ের উপর ঝাঁঝিয়ে উঠে মৌসুমি মনে মনে ভেবেছেন, ‘ওই তো একটুখানি খাট। দু’-দু’টো কোলবালিশ গুঁজলে নিজেরা শোব কোথায় শুনি? তা ছাড়া মেয়েদের এত বিলাসিতা ভাল নয়।’
ছোটবেলায় ভাই বাড়িতে না থাকলেই পাপিয়া এক ছুটে শোওয়ার ঘরে গিয়ে কোলবালিশটাকে জড়িয়ে ধরত। এক বার ভাই গিয়েছে মায়ের সঙ্গে মামাবাড়ি। সে দিন ওকে আর পায় কে! সাধের কোলবালিশে এক বার মাথা রাখছে, আয়েশ করে টেনে নিচ্ছে বুকের নীচে, আবার কখনও জাপটে ধরে মুখ গুঁজে দিচ্ছে ওতে। কোলবালিশ জড়িয়ে গল্পের বই পড়তে কিংবা ছবি আঁকতে কী যে আরাম! ভাই চিলেকোঠার ঘরে চলে যাওয়ার পরেও কখনও কখনও কলেজ থেকে ফিরে বিকেলের দিকে ছাদে গিয়ে জামাকাপড় তুলে আনার সময়ে সে টুক করে উঁকি দিত ভাইয়ের ঘরে। কিন্তু তখন কোলবালিশের চরিত্র বদলেছে। ছোট্টবেলার মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধটা উধাও। বরং সিগারেটের কড়া গন্ধে বমি আসত পাপিয়ার। কান্নাও পেত।
আচ্ছা, ও নিজে কি কখনও একটা আস্ত কোলবালিশের মালিক হতে পারে না?
মেয়ের আকুল প্রার্থনা মৌসুমির হৃদয়েও বেজেছিল হয়তো। পাপিয়ার বিয়েতে এ বাড়ি থেকে দেওয়া ঝকঝকে খাট, ড্রেসিং টেবিল, আলমারি ও নতুন তোশক-বালিশের পাশে দেখা গেল যে একটা নয়, বর-কনে দু’জনের জন্যই দু’-দু’টো কোলবালিশ শোভা পাচ্ছে। সেটা দেখে এত দিনের চেনা জগৎ ছেড়ে চিরতরে অন্যের বাড়ি চলে যাওয়ার চাপা কষ্টের পাশাপাশি পাপিয়ার মনে এক তীব্র আনন্দ পাক খাচ্ছিল। এত দিনে তবে স্বপ্নপূরণ ঘটল!
পাপিয়ার বরের নাম সম্রাট। বিয়ের সপ্তাহখানেক পর পুরী থেকে মধুচন্দ্রিমা সেরে এসে বাড়ির সকলের জন্য ব্রেকফাস্টে ফুলকো লুচি ভাজতে ভাজতে কী একটা কাজে নিজেদের বেডরুমে ঢুকে বিছানার মাথার কাছে বালিশের স্তূপের দিকে তাকিয়ে পাপিয়া অবাক হয়ে গেল। একটা নতুন কোলবালিশ হাওয়া। কী ব্যাপার? মনোর মা কি তবে অন্য কোথাও সরিয়ে রেখেছে জিনিসটা?
মনোর মা তখন রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে বেজার মুখে লুচির জন্য সেকেন্ড রাউন্ডের ময়দা ঠেসছিল। নতুন বৌদির কথায় অবাক হয়ে বলল, “জানি নে তো বাপু! তোমাদের ঘরের কোনও কিছুতে কখনও হাত ঠেকাই নে। তুমি বরং তোমার শাশুড়িকে জিজ্ঞেস করো দিকি।”
গরম গরম লুচিগুলো ঝাঁকায় তুলে ডাইনিং টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াতেই কোলবালিশ অন্তর্ধান রহস্যের সমাধান ঘটল। শাশুড়িমা একগাল হেসে পাপিয়াকে বললেন, “কী ভাল জিনিসই না দিয়েছেন বেয়াই-বেয়ান। এ বাড়িতে তো কোলবালিশের চল ছিল না। তোমার শ্বশুরমশাই তো মিলিটারি মেজাজ। রোজ সকালে উঠে লেকের ধারে তিন পাক দেবেন আর বলবেন, শরীরকে আয়েশি করে তুললে চলবে না। তা আনকোরা জিনিসদুটো পড়ে ছিল। একটা নিলাম শুভর জন্য। ও রাত জেগে খাটে শুয়েবসে লেখাপড়া করে। একটু আরাম পাবে। তোমাদের তো আর একটা রইলই। কী বলো?”
“না জানিয়েই তোমার কোলবালিশ ক্যাপচার করেছি কিন্তু বৌদি, রাগ করলে না তো?” চশমা চোখে ইন্টেলেকচুয়াল হেসে পাপিয়াকে জিজ্ঞেস করল শুভব্রত ওরফে শুভ। সম্রাটের পিঠোপিঠি ভাই। পাপিয়ার একমাত্র দেওর। সিটি কলেজে ইংরেজি পড়ায়। একটি মাঝারি মানের লিটল ম্যাগাজ়িনের সম্পাদক ও এক জন যশোপ্রার্থী কবি। শোনা যায়, বিয়ে-টিয়ে সে করবে না।
এই সব ক্ষেত্রে শ্বশুরবাড়িতে নতুন বৌয়ের যা করা সাজে, সেটাই করল পাপিয়া। মিষ্টি হেসে ঘোমটাটা আরও একটু টেনে শুভকে বলল, “না না, বেশ করেছ ভাই। তোমায় আর দুটো লুচি দিই?”
রাতে শোওয়ার সময় যদিও সম্রাট দরাজকণ্ঠে বৌকে বলল, “আরে, আমাদের এ-সবের অভ্যেস নেই। তোমার মা দিয়েছেন তোমার জন্য, তুমিই ইউজ় করো।”
কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, রোজই ঘুমের ঘোরে কখন যেন কোলবালিশটি সম্রাটের গায়ে সেঁটে যাচ্ছে আর সে পরম আবেশে ‘আহ্’ বলে সেটাকে জাপটে ধরে শুচ্ছে।
আর এটাই ঘটতে থাকল। রোজ।
*****
বিয়ের পর পর পাপিয়া একটা এনজিও-তে জয়েন করল। ঢাকুরিয়ায় হেড অফিস। কাজের চাপ নেই বললেই চলে। সপ্তাহে তিন দিন বিকেলে মাত্র তিন-চার ঘণ্টার জন্য অফিসে হাজিরা দেওয়া। স্যালারি সামান্যই। প্লেন গ্র্যাজুয়েশনে এর চেয়ে বেশি কে দেবে? বাড়ির বৌমা চাকরি করবে শুনে শ্বশুর-শাশুড়ি প্রথমটা একটু গজগজ করলেন বটে, তবে তা আড়ালে। পাপিয়ার মিষ্টি স্বভাব। বড়দের সেবাযত্নের কোনও ত্রুটি নেই। সারা দিন খাটছে। এটা ঝাড়ছে, ওটা মুছছে। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর্ব মিটলে ইউটিউব দেখে জিভে জল আনা সব রেসিপি বানিয়ে রাখছে। সন্ধ্যায় দুই ভাই বাড়ি ফিরে এলে জলখাবারে নিত্যনতুন সারপ্রাইজ়। তার উপর যার বৌ তারই যখন কোনও আপত্তি নেই, শ্বশুর-শাশুড়ি কিছু বলে খারাপ হতে যাবেন কেন খামোখা?
সম্রাট নিজেও ব্যস্ত মানুষ। অফিসের টার্গেট নিয়ে ভেবেই তার দিন কাটে। উইকএন্ডে ছাড়া বৌকে সময় দেওয়ার উপায় নেই। সুতরাং পাপিয়াকে এনজিওতে জয়েন করতে দেখে সে যেন উল্টে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দিনগুলো তার পর ফড়িঙের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে কাটতে থাকল। গঙ্গার বুকেও জল গড়িয়ে চলল নিজের খুশিতে।
বছরখানেক পরে গন্ডগোলটা বাধল। পাপিয়ার একটা প্রোমোশন হয়েছে। আর হেড অফিসে নয়, ওকে এখন থেকে সকালেই চলে যেতে হবে কোন এক ধ্যাদ্ধেড়ে গোবিন্দপুরে। সেখানে সারাটা দিন কাজের তদারকি সেরে একেবারে সন্ধ্যাবেলায় ফেরা।
তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল সম্রাট, “রোজ চার ঘণ্টার জার্নি! স্যালারি বাড়িয়ে কি মাথা কিনেছে? আজকেই অফিসে গিয়ে রেজ়িগনেশন লেটারটা জমা দিয়ে এসো তো।”
“যাহ্! এমন করতে নেই। এই মাসের তো আর ক’টা দিন বাকি। সামনের মাস থেকে যাবও না। এ রকম যে হবে কে জানত বলো?” ভুরু কুঁচকে কথাগুলো বলল বটে পাপিয়া, কিন্তু ক্যালেন্ডারে পরের মাসের খোপগুলো একের পর এক পেরিয়ে যেতে থাকলেও চাকরি ছাড়ার কোনও রকম লক্ষণ তার মধ্যে দেখা গেল না। না, সম্রাটের হাজার অনুরোধেও নয়।
বাড়ির লোকজনও অবাক। হল কী শান্তশিষ্ট মেয়েটার! এ দিকে দিব্যি হাসিখুশি। বাড়ির কাজেকর্মে গাফিলতি নেই। শুধু সপ্তাহের ওই তিনটে দিন। ভোরে উঠে স্নান সেরে চা-জলখাবার বানিয়ে মনোর মাকে বিকেলের জলখাবারের খুঁটিনাটি বুঝিয়ে কোনও মতে নাকেমুখে গুঁজে নিজের ঢাউস ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে পাপিয়া ছুটছে সদর দরজার দিকে।
রোজকার মতো আজও চায়ের কাপ হাতে হাঁ করে দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন ওর শ্বশুরমশাই। তার পর উঠে গিয়ে ল্যান্ডফোন থেকে একটা নম্বরে ডায়াল করলেন।
*****
অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী সাধনবাবু যখন চম্পাপুকুর নামের ছোট্ট নিরিবিলি স্টেশনটায় এসে নামলেন, তখন ঘড়ির কাঁটা একটা ছুঁই-ছুঁই। তিনি এগারোটা দশের শিয়ালদা-হাসনাবাদ লোকালটা ধরেছিলেন। আসার সময় পথের দু’পাশের সবুজ চোখ জুড়িয়ে দিয়েছে। তাঁর মেয়ে এ রকম একটা জায়গায় সপ্তাহে তিন দিন আসছে কিসের টানে? তাও স্বামী, শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে গিয়ে? এই সবুজের আকর্ষণে নয় তো?
সাধনবাবুর আর একটি পরিচয় হল, তিনি পাপিয়ার বাবা। সে দিন সকালে বেয়াইয়ের কাছ থেকে ফোনটা পেয়েই মনে মনে স্থির করে ফেলেছিলেন যে, চাকরি না ছাড়ার কারণটা মেয়ের পেট থেকে বার করার একটাই উপায়, তার সঙ্গে খোলামনে কথা বলা। আর সেটা বাড়ির সকলের সামনে নয়, এমনকি ওর মায়ের সামনেও নয়, একা। তাই আজ এখানে এসেছেন মেয়েকে আগাম না জানিয়েই।
একটা ভ্যানে চেপে খুঁজতে খুঁজতে মেয়ের অফিসের ঠিকানায় এসে পৌঁছতে আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগল না। কলা আর সুপুরিগাছে ঘেরা ছোট্ট অফিসঘর। সামনে একটুখানি বারান্দা। পিছনে এক চিলতে এক্সটেনশন। আর একটা ছোট্ট পুকুর। লোকজন বিশেষ নেই। বারান্দায় একটা কাঠের চেয়ারে বসে পাপিয়া একমনে সামনের টেবিলে রাখা কাগজপত্রে সই করছিল। এক পাশের বেঞ্চে দু’টি মহিলা বসা। সাধনবাবুকে আসতে দেখে পাপিয়ার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেই পরমুহূর্তে সেখানে উদ্বেগের ছাপ পড়ল।
“তুমি? এখন, এখানে? বাড়িতে সব ঠিক আছে তো?”
“হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোকে দেখতে ইচ্ছে করল। তাই চলে এলাম। জানি এই সময়টায় তোর ব্রেক।” কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে মেয়েকে আশ্বস্ত করলেন সাধনবাবু। তার পর মুগ্ধচোখে পাশের পুকুরটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। পুকুরের স্থির জলে চার পাশ থেকে ঝুঁকে থাকা নারকেল গাছেদের ছায়া পড়েছে। সেই সবুজ আয়নায় সাঁতার কাটছে তিনটে বাচ্চা সমেত একটা মা-হাঁস। গাছের ডালে বসে ‘বৌ কথা কও’ ডেকে চলেছে একটানা। ছোটবেলার দেশের বাড়ির কথা মনে পড়ে যায়।
“এই জায়গাটার মধ্যে জাদু আছে বাবা। এ হল রূপকথার দেশ।”
“ঠিক বলেছিস। আমি সব বুঝেছি মা। তুই ভাবিস না। আমি ওদের বুঝিয়ে বলব।”
পাপিয়া বলে, “বাবা, চা খাবে? আমি বানিয়ে আনছি। ভিতরের ঘরে ব্যবস্থা আছে। তার পর আমার আনা টিফিনটা ভাগ করে খাব দু’জনে।”
“না না...” ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সাধনবাবু, “আমি ভাত খেয়েই বেরিয়েছি। এখন ফিরব। তুই খেয়ে নে। কোন সকালে এসেছিস। আমি শিয়ালদায় নেমে চা খেয়ে নেব’খন।”
মেয়ের ওজর-আপত্তি কানে না তুলে রিজ়ার্ভ করে রাখা ভ্যানটায় চেপে বসে ফেরার পথ ধরলেন উনি। স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছে আফসোসে জিভ কাটলেন। ইস! বড্ড ভুল হয়ে গেছে। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় পাড়ার মিষ্টির দোকান থেকে মেয়েটার জন্য মোতিচুরের লাড্ডু কিনেছিলেন। সেটা কাঁধের ঝোলাতেই রয়ে গেছে। এই লাড্ডু ছোটবেলায় খুব ভালবাসত পাপিয়া। ভ্যানওয়ালাকে বললেন, “ফেরাও ভাই।”
*****
সেই নিঝুম অফিসঘর। সূর্য কিছুটা ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। নারকেল গাছের ছায়ারা আরও দীর্ঘ হয়েছে। বারান্দার টেবিলে চাপা দেওয়া কাগজগুলো বাতাসে নড়ছে। সাধনবাবু পায়ে পায়ে অফিসের ভিতরে ঢুকলেন। কেউ কোথাও নেই। ভিতরের ঘর থেকে শুধু টেবিল ফ্যানের ঘরঘর আওয়াজ কানে ভেসে আসছে। দরজায় দাঁড়িয়ে পর্দাটা হাত দিয়ে সরিয়ে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। ঘরে আবছা আঁধার। এক পাশে নিচু টেবিলে সদ্য খালি করা টিফিনবাক্স। আর দেওয়াল ঘেঁষে রাখা চৌকির উপর ফুলেল ওয়াড় পরানো একখানা মাঝারি সাইজ়ের কোলবালিশ দু’হাতে আঁকড়ে ধরে তাঁর মেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।
এ বার ঘুমের মধ্যেই এক বার ফিক করে হেসে উঠল পাপিয়া। ঠিক ছোট্টবেলায় যেমন করত।
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)