বিদ্যা অর্জনের তিন অন্তরায়— শ্রবণে অনিচ্ছা, অনধ্যবসায় এবং অহঙ্কার। কুমার রাণার সাম্প্রতিক প্রবন্ধ-সঙ্কলনে ‘ক্ষিতিমোহন সেন ও যুক্তসাধনার অগ্রাধিকার’ রচনাটি শুরু হচ্ছে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের এই উক্তিটি উদ্ধৃত করে। বইটি পড়লেই বোঝা যায়, কুমার রাণা তাঁর পড়াশোনা এবং লেখালিখিতে এই দোষগুলির ফাঁদ সচেতন ভাবে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। তাই প্রথিতযশা ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহের প্রবন্ধ ‘চন্দ্রা’জ় ডেথ’-এর পাঠ ও অনুধাবনে অবতারণা করেছেন সুন্দরবনে বাঘের পেটে যাওয়া মহিলা-পুরুষদের নিয়ে সুরঞ্জন মিদ্দের গুরুত্বপূর্ণ অথচ অল্পশ্রুত সমকালীন গবেষণা। এই বইয়ের রসদ বা উপাদান হিসাবে মহাশ্বেতা দেবী বা অমিতাভ ঘোষের লেখার পাশাপাশি জায়গা পেয়েছে হীরা ডোমের কবিতা। অন্নদাশংকর রায়ের ছড়া থেকে লেখক তুলে এনেছেন বিভাজনদীর্ণ সমাজে সুযোগবঞ্চনার অন্যায্যতা। “জাতপাত যদি পথ জুড়ে থাকে/ জাতির ঘটবে পরাজয়”— অন্নদাশংকরের লেখনীনিঃসৃত এই আর্ষবাক্যটি আজকের ভারতের প্রেক্ষিতে মিলিয়ে দেখতে ব্যবহার করেছেন রুক্মিণী এস-এর সাম্প্রতিক বই হোল নাম্বারস অ্যান্ড হাফ ট্রুথ।
তত্ত্ব ও তথ্যের সঙ্গে নিজস্ব জীবনের অভিজ্ঞতাও লেখক সুচারু ভাবে মেলাতে পেরেছেন বলে লেখাগুলি সরস ও সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক ভারতে পরিচিতির রাজনীতি বিষয়ে আলোচনায় উঠে এসেছে তাঁর গ্রাম ছেড়ে চলে আসা তেলি জাতির এক পুরুষের কথা। ভাতের হোটেলে ফাইফরমাশ খাটতে খাটতে রান্নার কাজ শিখে ফেলেন তিনি। রান্নার ঠাকুর হতে গেলে ব্রাহ্মণ হতে হয়, তাই গলায় পৈতে পরে চক্রবর্তী পদবি ব্যবহার করতে শুরু করেন তিনি। কঠিন পরিশ্রম করে একটি হোটেলও কিনে ফেলেন। দুঃখের কথা, ব্যবসা জমে ওঠার আগেই ফাঁস হয়ে যায় তাঁর জাতি-পরিচয়। প্রবল হেনস্থার পরে গ্রামে ফিরে গিয়ে ফের চাষবাসের কাজে যোগ দেন তিনি।
ভগ্নসন্ধি সময়ের ভাবনা
কুমার রাণা
৪০০.০০
অনুষ্টুপ
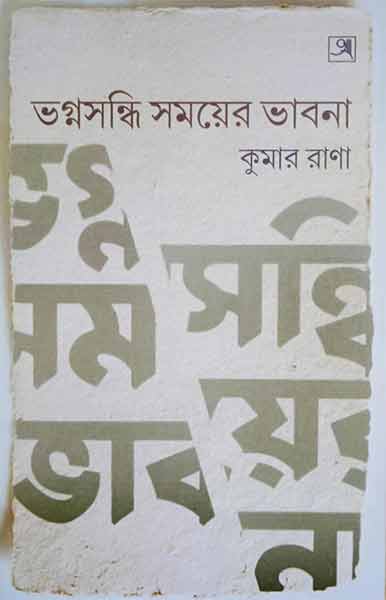

বইটির প্রবন্ধগুলির বিষয় বিবিধ, কিন্তু জাতিবিভাজিত সমাজে প্রান্তিক জীবনকে বুঝতে চাওয়ার প্রয়াস সমস্ত লেখাকে যেন একটি সূত্রে গেঁথে রেখেছে। পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, বিষয়বৈচিত্রই এ বইয়ের গুরুত্ব।
বইটিতে সঙ্কলিত হয়েছে সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে লেখকের কয়েকটি বক্তৃতাও। পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সঙ্গে এই লেখাগুলির সুর কিঞ্চিৎ ভিন্ন। বক্তৃতাগুলি পরিমার্জন করে প্রকাশিত প্রবন্ধের আকার দিলে আর একটু সমঞ্জস হত। ভাষাচর্চায় লেখকের উৎসাহ সুবিদিত। বাংলায় মৌলিক লেখালিখি এবং অনুবাদ, দুই ক্ষেত্রেই তিনি নিরলস ভাবে চর্চা করে চলেছেন বহু দিন যাবৎ। সরস গদ্যরচনার মাধ্যমেই তিনি বাংলায় ফিরিয়ে আনেন পুরনো শব্দ, চালিয়ে যান নতুন শব্দের সন্ধান। ‘চিন্তানুশীলক’, ‘কর্তব্যদায়’, ‘সুযোগবিচ্ছেদ’-এর মতো শব্দ চোখের আরাম এবং ভাবনার খোরাক জোগায়। তবু কোথাও কোথাও ভাষা নিয়ে এই প্রশংসনীয় নিরীক্ষা যেন একটু মাত্রাচ্যুত হয়। যেমন ক্ষিতিমোহন সেন ও যুক্তসাধনার অগ্রাধিকার প্রবন্ধে (পৃ ৫৪-৫৫) নয় লাইনের একটি বাক্য বা ‘স্বাভাবিকভাবে দুর্বল একটি গোষ্ঠীর ওপর যখন দৈহিকভাবে নির্মূলীকরণের খাঁড়া ঝুলিয়ে রাখা হয়’-এর মতো বাক্যাংশ। ভাষার নিরন্তর একাগ্র চর্চার কারণেই হয়তো বইটিতে মুদ্রণপ্রমাদ প্রায় নেই বললেই চলে। বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ-প্রকাশনার গড় মানের নিরিখে এ-ও কম কথা নয়।
নজরে
পোড়া খাল্লি: এই শব্দদ্বয় মহারাষ্ট্রের এক অংশে বললে তার অর্থ ‘বাচ্চারা কি খেয়েছে’, আর ওই রাজ্যেরই অন্যত্র বললে তার অর্থ ‘বাচ্চাদের কি খেয়ে ফেলা হয়েছে’। কেন এ রকম? কেননা, ‘দক্ষিণী’ প্রভাবে ওই রাজ্যের একাংশের ভাষায় এক রকম প্রভাব, অন্য অংশে সেটা নেই। পার্থক্য ঘটে যায় একই শব্দের উচ্চারণেও। এই যে মাস পুরোলেই রোজা শুরু হবে, সে কি রমজ়ান, না কি রামাদান? উত্তর ভারতের মুসলমানরা পারসিক প্রভাবে বলেন প্রথমটা, আর দক্ষিণের মুসলমানরা আরবি ধারা অনুযায়ী বলেন দ্বিতীয়টা। দুই উচ্চারণই চলে গোটা দেশে, পাশাপাশি, মিলেমিশে।
ফাদার টাং, মাদার ল্যান্ড: দ্য বার্থ অব ল্যাঙ্গুয়েজ ইন সাউথ এশিয়া
পেগি মোহন
৬৯৯.০০
পেঙ্গুইন, অ্যালেন লেন
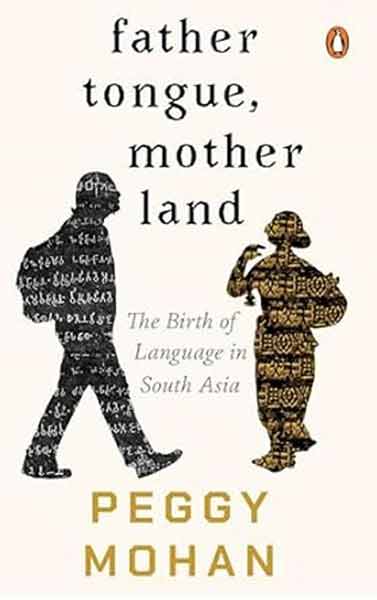

কেন দক্ষিণে আরব প্রভাব বেশি? আরবের বণিকরা সেই কবে থেকেই দক্ষিণ ভারতে আসা-যাওয়া করে, ইসলাম ধর্ম এই দুনিয়ায় আসারও অনেক শতক আগে থেকে। অতঃপর ইসলামের আবির্ভাব, আরববাসীর ধর্ম পরিবর্তন, সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে আরবি পরিবার-পরিজনদেরও ধর্মে, সংস্কৃতিতে, ভাষায় পরিবর্তন। ভারতের অন্য অংশের সঙ্গে সেই দক্ষিণী ধারার দেনাপাওনা কম। তাই পালনের ধর্ম এক হলেও ভাষার ধর্ম আলাদা হয়ে যায় উত্তরে আর দক্ষিণে। ভাষার ধর্মই প্রবহমানতা, মিশ্রতা, পরিবর্তনশীলতা। কোনও ভাষাই একক বিশেষ চরিত্রের অধিকারী নয়, সব ভাষার মধ্যেই মিশে বহু ভাষার শব্দ, অর্থ, উচ্চারণ, ব্যঞ্জনা। মানুষ যেমন হাতে হাতে এক খড় থেকে আর এক খড়ে আগুন লাগিয়ে ছড়িয়ে দেয়, এক সলতে থেকে আর এক সলতে ধরায়— সেই ভাবেই ভাষাও ছড়িয়ে পড়ে, পাল্টাতে পাল্টাতে।
এই হল ‘ক্রেওল’ ভাষা। আমেরিকার দক্ষিণ দিকে যেমন নানা ভাষার মিশ্রণে ক্রেওল তৈরি হয়েছিল, তেমনই ভারতের প্রায় সব ভাষাই ক্রেওল। অভিবাসী হয়েযারা এল, তাদের ভাষা জুড়ে গেল পুরনো প্রচলিত ভাষার সঙ্গে: ভাষার উপরটা পাল্টাল, ভিতরের গঠন, ব্যাকরণ থেকে গেল পুরনো ভাষারই মতো। যে ভাষা আসছে বাইরে থেকে, তাকেই লেখক বলছেন ‘ফাদার টাং’, আর পুরনো ভাষা যেখান থেকে আসছে, সে তো ‘মাদারল্যান্ড’ বটেই। এই বইয়ে ভাষা-ইতিহাসের বিশ্লেষণ এমনই নতুনত্বে ভরপুর। ভাষাতাত্ত্বিক থেকে অজ্ঞানতিমিরচারী, সকলের জন্যই সহজপাঠ্য।
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)










