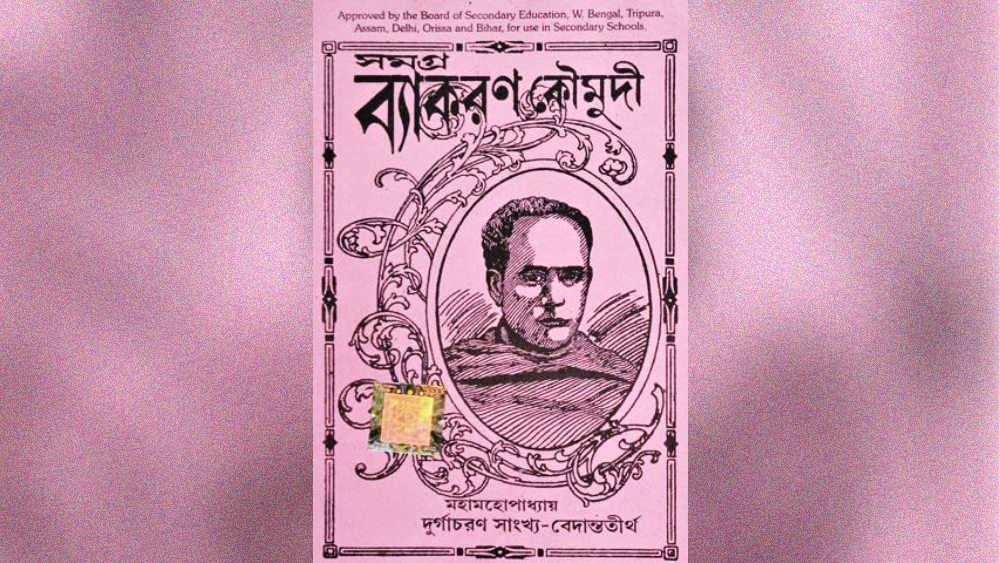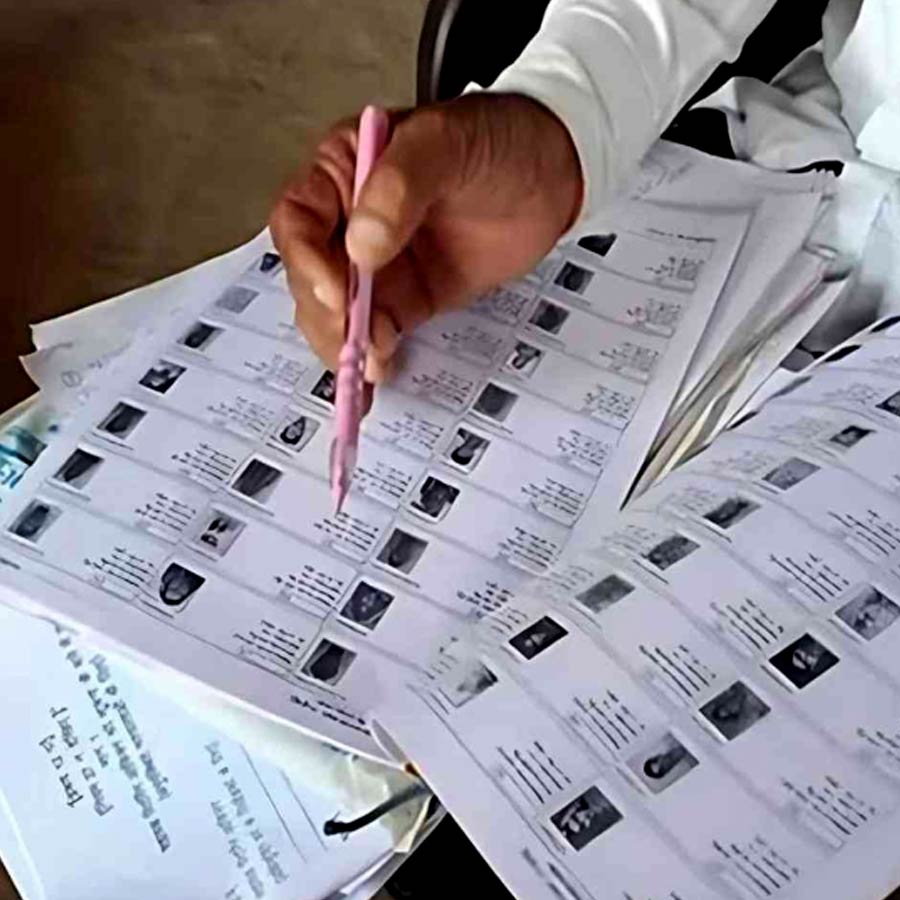আমার অনেক দিনের চিন্তা— বিদ্যাসাগরের লেখালিখির মধ্যে আমাদের আধুনিকতার চেহারাটা ধরতে চেষ্টা করা যায় কী ভাবে। আসলে আমরা যখন আধুনিকতার কথা ভাবি, আমাদের ভাবনায় তার সঙ্গে পাশ্চাত্যবাদ মিশে যায়। অথচ রামমোহন থেকে শুরু করে পরবর্তী কালের অনেকের মধ্যেই কিন্তু আধুনিকতাবাদের চেহারাটা ঠিক পাশ্চাত্যের স্ট্যান্ডার্ড আধুনিকতার মতো ছিল না। একটা আলাদা চরিত্রের আধুনিতার ছাঁদ তৈরি হচ্ছিল। পার্থক্যটা বুঝতে গেলে ছুটে গিয়ে উত্তর-আধুনিক তত্ত্বের শরণাপন্ন হওয়ার দরকার নেই— আমার মনে হয়, ওতে যেন এক দিকে বেশি করে হেলে গিয়ে একটা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। আধুনিকতার বড় গল্পটাকে ছেড়ে না দিয়ে বরং আমরা বুঝতে চাইতে পারি, কী ভাবে ওই বড় গল্পটার ভিতরেই তার ছোট ছোট চেহারা ফুটে উঠছিল।
সাধারণত বিদ্যাসাগরের কথা ভাবলেই আমরা তাঁর ‘সংস্কারক’ দিকটার উপর জোর দিই। লেখক বিদ্যাসাগর, চিন্তক বিদ্যাসাগরের কথা আমরা বেশি ভাবি না। অথচ সেটা ভাবা উচিত। তাঁর একটা বড় পরিচয় সাহিত্যরচনা। আর সাহিত্যরচনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর ব্যাকরণভাবনা। ফলে এই দিকটা ভাবতে হলেই উঠে আসে পাণিনি-মুগ্ধবোধ-কলাপ চর্চার কথা। বিদ্যাসাগর মশাই যে নতুন ব্যাকরণ আদর্শের দিকে গেলেন, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ভাবনার রকমটা বোঝার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এ বিষয়ে আমার অধিকার নেই, তা-ও তাঁর সংস্কৃত-ভাবনা ও ব্যাকরণ-ভাবনা নিয়ে কয়েকটা কথা বলতে ইচ্ছে করে।
সংস্কৃত শাস্ত্রের বেশ কিছু বিষয় নিয়ে বিদ্যাসাগরের সমালোচনা ছিল, যেমন বেদান্ত। তবে তাই বলে সংস্কৃতের ঐতিহ্যের গুরুত্ব তাঁর কাছে কম ছিল না। স্মৃতির উপর খুব জোর দিতেন, সংস্কৃত কলেজে স্মৃতি পাঠদানের বিষয়ে তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। যুক্তি দিতেন— স্মৃতি পড়লে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের চাকরি বাড়বে, হিন্দু বিধিতে তাদের পারদর্শিতা জন্মাবে! ফলে কিছু কিছু বিষয়ে তাঁর আপত্তি থাকলেও প্রাচীন বিদ্যার ঐতিহ্য বিষয়েই উনি ‘ক্রিটিক্যাল’ ছিলেন, এ কথা আমার মানতে ইচ্ছে করে না। তিনি ভাবতেন, ‘ট্র্যাডিশনাল’ বিদ্যার অনেকটাকেই আজকের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব। এবং এই জন্যই তিনি অন্য পথে গিয়ে ব্যাকরণ শিক্ষার সন্ধান শুরু করলেন, যাতে প্রাচীন শাস্ত্রে অধিকারটা আরও সহজ হয়। তৈরি হল ব্যাকরণ কৌমুদী।
ব্যাকরণ কৌমুদী আজ পর্যন্ত একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী বই হয়ে থেকে গিয়েছে, কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, বৈয়াকরণরা খুব গুরুত্ব দিয়ে এর আলোচনা করেননি। দুর্ভাগ্য বলতে হবে। কেননা, আমার মনে হয়, যেটা ঘটল— পুরনো ভারতীয় ব্যাকরণের জোরের জায়গাটা, শব্দসিদ্ধি বা শব্দসাধনের জায়গাটা বিদ্যাসাগরের ভাবনায় অনেকখানি পাল্টে গেল। সংস্কৃতে সূত্র থেকে শব্দ-নিষ্পত্তির যে ধারা, সেই ধারাটা উনি সহজ-সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করলেন, সূত্রগুলিকে একটা ‘স্ট্রাকচার’ বা ধাঁচায় নিয়ে এলেন। একটা নতুন প্যারাডাইম তৈরি হল। আধুনিকতার ভাবনা দিয়ে, সংস্কারীর মন দিয়ে তিনি যা করলেন, তাকে একটা ‘বিকল্প ব্যাকরণ প্রকল্প’ বলা যায়। এও একটা আধুনিকতার লড়াই। অথচ বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কারের আলোচনায় কিন্তু এটা ঢুকল না, বিনয় ঘোষ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্তও নয়।
এই দিক দিয়ে ভাবলে, বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রে তাঁর প্রাচীন শাস্ত্র আলোচনাটা কেবলমাত্র ‘স্ট্র্যাটেজিক’, কৌশল মাত্র— এটাও আমি মানতে পারি না। না, এটাকে আমার কৌশল বা ফন্দি বলে মানতে ইচ্ছে করে না। মনে হয়, শাস্ত্রের উপর ভর না করে তিনি নিজেই এগোতে রাজি ছিলেন না। বিদ্যাসাগর ধুতি-চাদর পরিহিত সাহেব ছিলেন— কথাটা এক অর্থে ঠিকই, কিন্তু ধুতি-চাদরকে তো উনি বহন করতে চাইতেন মনের ভিতর থেকেই। তাই, সেই যে অমলেশ ত্রিপাঠীর ১৯৭৪ সালে লেখা বই বিদ্যাসাগর: দ্য ট্র্যাডিশনাল মডার্নাইজ়ার, ট্র্যাডিশনাল মডার্নাইজ়ার বর্ণনাটার একটা অর্থ পাই আমি, সে যতই পুরনো শুনতে হোক। বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তিকাটিতে তিনি নিজেকে শাস্ত্রে নিয়োজিত করেছিলেন। দ্বিতীয় পুস্তিকাটিতে প্রতিটি সমালোচনার উত্তর দিয়েছিলেন। এখন, যিনি সংস্কার-কাজে নেমেছেন, তিনি কি এতটা নিজেকে নিয়োগ করতে পারতেন শাস্ত্রবচন উদ্ধারে ও বিশ্লেষণে, যদি তাঁর নিজের কাছে এর একটা অর্থ না থাকত? না, সবটা ‘কৌশল’ হতে পারে না। তাঁর আধুনিকতার প্রোজেক্টে শাস্ত্রজ্ঞান ও তার প্রয়োগের জায়গাটা ছিলই, এই আমার বিশ্বাস। ‘পিছুটান’ বলা যেতেই পারে। কিংবা আরও ভাল হয়, যদি ‘সামনে’-‘পিছন’-এর ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে বলি ‘পাশের টান’।
ব্যাকরণ কৌমুদী-তে সূত্রের সংক্ষেপিত স্ট্রাকচার দিয়ে ব্যাকরণ আয়ত্ত করার যে কাণ্ডটা করলেন উনি, আশ্চর্যই বলতে হবে। অাসলে এটা তো বলা হয় যে, গ্রিক সভ্যতাতে যেমন জ্যামিতি, ভারতীয় সভ্যতাতে ব্যাকরণও তেমন। পণ্ডিতরা বেজায় বিরক্ত হলেন। তাঁরা ভাবলেন, এত শর্টকাট-এ কি ব্যাকরণ শেখা যায়? এ ভাবে কি ভাষাটাকে জোলো করে ফেলা যায়? উল্টো দিকে বিদ্যাসাগর ভাবলেন, কী ভাবে ভাষাটা নতুন করে শেখানো যায় ‘ইন আ মডার্ন ওয়ে’। পাশ্চাত্য শিক্ষাকে বাদ দিয়ে নয়, পুরনোকে বাদ দিয়েও নয়। সংস্কৃত টেক্সটগুলি তুলে নিলেন নতুন পাঠের যোগ্য করার জন্য— তার থেকেই এল শকুন্তলা সম্পাদনা ইত্যাদি।
এই জন্য ব্যাকরণ শিক্ষার মধ্যে কী ভাবে আধুনিকতাকে দেখা হচ্ছিল, সেটা বোঝা আমাদের কাছে জরুরি। ল্যাটিন গ্রামার থেকে ইংরেজি গ্রামারকে সরিয়ে আনার চেষ্টা তো হয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিংবা আজ পবিত্র সরকার— এঁরাও সংস্কৃত থেকে সরিয়ে এনে বাংলাকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে চেয়েছেন। ব্যাকরণ কৌমুদীর লক্ষ্যটাও ছিল সেই রকম। কলেজের ছাত্রদের জন্য তৈরি হয়েছিল এই বই, যা দেখে পণ্ডিতরা মুখ বাঁকাতেন। অথচ শতাব্দী পেরিয়েও এই বইটাই তো রয়ে গেল। দেওয়াল-লিখন বা সময়ের চিহ্ন দেখতে পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। বুঝেছিলেন, সময় পাল্টাচ্ছে।
বর্ণপরিচয় নিয়ে কিছু কথাবার্তা হয়েছে, বাংলা ভাষার ‘প্রাইমার’ হিসেবে। কিন্তু ব্যাকরণ কৌমুদীর আলোচনা বিশেষ কিছু হল কি? সংস্কৃত শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক বিশ্লেষণের যোগের জায়গাটা ঠিকমতো বোধ হয় এল না। কিন্তু ব্যাকরণের দিক থেকে এর বিশ্লেষণ হলে কত লাভ হত!