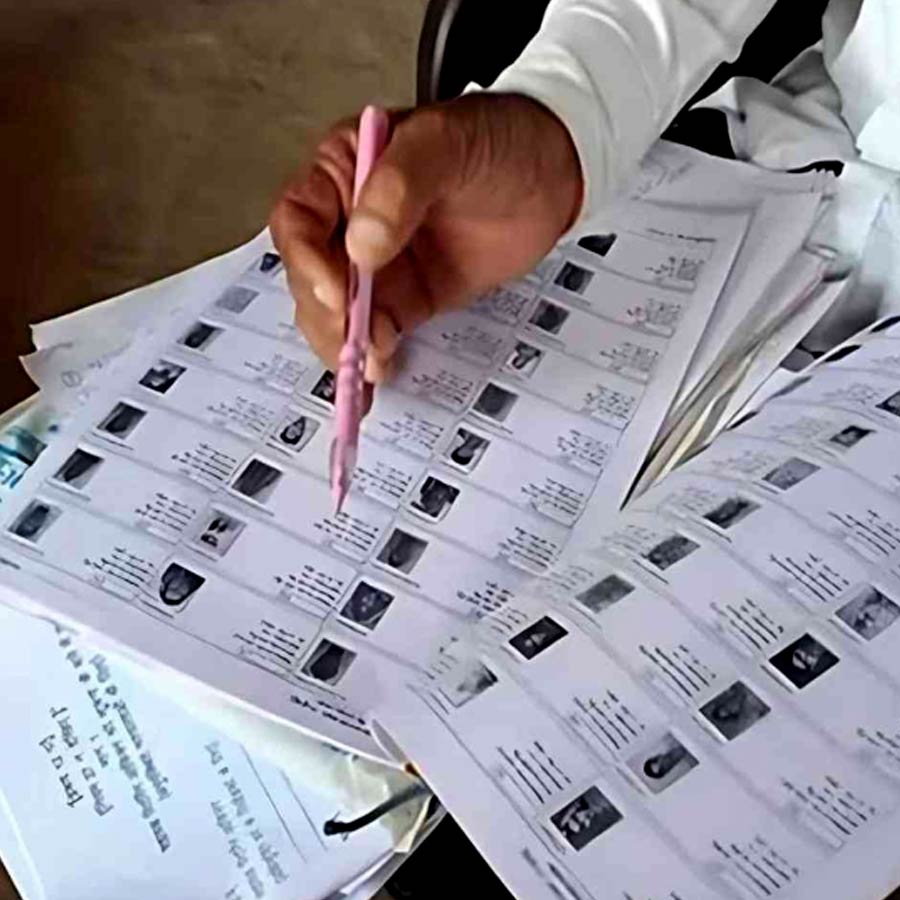বছর কুড়ি আগে হাতে এসেছিল লীলা গুলাটি ও যশোধরা বাগচি সম্পাদিত একটি সঙ্কলন, আ স্পেস অব হার ওন: পার্সোনাল ন্যারেটিভস অব টুয়েলভ উইমেন (সেজ়, ২০০৫)। সেখানে নানা পেশার বারো জন ভারতীয় নারী পূর্বমাতৃকাদের সূত্র ধরে নিজেদের চলার পথকে ফিরে দেখেছেন, খোলাখুলি আলোচনা করেছেন তাঁদের অন্তরমহলের টানাপড়েন ও সম্পর্কের মিথস্ক্রিয়ায় হয়ে-ওঠার কথা। অন্তরঙ্গ ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে সামাজিক ইতিহাসচর্চার ও রকম নজির আমি তার আগে আমাদের দেশ থেকে প্রকাশিত কোনও বইয়ে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। বিশেষ করে মনে গেঁথে আছে নবনীতা দেব সেনের ‘দ্য উইন্ড বিনিথ মাই উইংস’ ও মেরি রয়-এর ‘থ্রি জেনারেশনস অব উইমেন’ শিরোনামের লেখা দু’টি, যেখানে লেখকেরা তাঁদের বাঙালি হিন্দু ও মালয়ালি সিরিয়ান খ্রিস্টান পরিবারের মধ্যেকার সম্পর্কের নকশাগুলো বুনেছেন অপূর্ব দক্ষতায়, নানা জটিলতা অক্ষুণ্ণ রেখে।
মেয়েদের কথা মায়েদের কথা পড়তে পড়তে বার বার আ স্পেস অব হার ওন বইটির কথা আমার মনে হয়েছে, কারণ সম্পাদকের ভূমিকা অনুসারে এই সঙ্কলন আমাদের সময়ের কয়েকজন গুণী মানুষের, স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত কয়েকজন নারীর স্মৃতিপথ ধরে তাঁদের মায়েদের কথা ও বহির্যাত্রার সঙ্গে অন্দরের বহুমাত্রিক সম্পর্ক অনুভব করতে চেয়েছে। দুই খণ্ডে বিন্যস্ত সঙ্কলনে মোট তেইশ জনের লেখা পাই আমরা, যাঁদের মধ্যে দার্শনিক, বিজ্ঞানী, রাজনৈতিক কর্মী, সমাজকর্মী, শিল্পী, শিক্ষক, লেখক, খেলোয়াড়, সংগ্রাহক, সেবিকা, সাংবাদিক, নাট্য পরিচালক ও চিত্রনির্মাতা মেয়েরা আছেন।
দু’টি খণ্ড মিলিয়ে যদি দেখি তা হলে মনে হয় যে, কিছু লেখায় আপন হৃদয়পানে চাওয়া আছে, আলোছায়ার দোলা আছে, আর কয়েকটি লেখা যেন বাহিরপানে মুখ ফিরিয়ে বড় রাস্তা দিয়ে সটান হেঁটে গেছে, সেখানে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কোনও চিহ্ন নেই। আর একটি দিক লক্ষ করলাম— লেখকদের মধ্যে যাঁরা সত্তরোর্ধ্ব বা ষাটোর্ধ্ব, তাঁদের লেখায় পূর্বমাতৃকাদের কথা অনেক বেশি জড়িয়ে আছে। এর ব্যতিক্রম আছে এ সঙ্কলনেই, কিন্তু সাধারণ ভাবে এটা লক্ষ করে ভাবতে চেষ্টা করছি ষাট-সত্তর বছর আগে বাঙালি মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের সংজ্ঞা ও রূপ অনেকটাই আলাদা ছিল বলে কি এমনটা ঘটে থাকতে পারে।
স্বল্প পরিসরে এ আলোচনায় মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের বাইরে যে লেখাগুলো আমাদের নিয়ে যায়, শুধু সেগুলো নিয়েই দু’-একটি কথা বলছি, যদিও আরও অনেক লেখাই আমাকে ঋদ্ধ করেছে। বিশেষ করে অগ্রজদের মধ্যে শেফালী মৈত্র, গোপা দত্ত ভৌমিক, বোলান গঙ্গোপাধ্যায়, শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পূর্ণা ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথাগুলির উল্লেখ করতে হয়।
কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আমার নকশালবাড়ি’ এই বইয়ের সবচেয়ে দীর্ঘ স্মৃতিকথা। আন্দোলনের অত্যন্ত জরুরি সামাজিক দলিল তো বটেই, তা ছাড়া নিজেদের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের মা-জেঠি-কাকিদের কথার পাশাপাশি কৃষ্ণা বুনেছেন রাজনীতির সূত্রে অন্তরঙ্গ ভাবে চেনা সমাজের নানা স্তরের ‘অনাত্মীয়’ মেয়েদের কথা এবং জেলজীবনে কাছ থেকে দেখা কিছু সাধারণ বন্দিনির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা। কৃষ্ণার মৌখিক বয়ান থেকে সযত্নে লেখা তৈরি করেছেন গার্গী বসাক, যদিও তাঁদের দু’জনের কথোপকথনের ছাপ এখানে নেই, যেটা থাকলে আর একটা পরত ধরা পড়ত। সম্ভবত এটা এই বইয়ের একমাত্র মৌখিক আখ্যান। পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, সঙ্কলনের মধ্যে আরও কিছু মৌখিক আখ্যান থাকলে, লিখিত ও মৌখিক দু’ধরনের আখ্যান নিয়ে দু’টি ভাগ থাকলে মন্দ হত না। বিশেষ করে যাঁদের লেখার অভ্যেস নেই অথবা নিজেদের কথা লিখতে যাঁরা কুণ্ঠিত হয়েছেন, আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের নিরিখে সম্পাদকের সঙ্গে কথোপকথনে সেই বয়ানগুলো অন্য রকম হত কি না ভাবছি।
মেরুনা মুর্মুর ‘গোপন, গভীর, “প্রান্তিক” আমি’ ও আয়েষা খাতুনের ‘যতনে রেখেছি স্বপন’ লেখা দুটো আমাদের চেনা দুনিয়ার বাইরে নিয়ে গিয়ে কিছু কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। বীরভূমের হেরুকা গ্রামের মা-মেয়েদের কথা প্রসঙ্গে আয়েষার সুফিসাধক ও শিক্ষক বাবা জুড়ে থাকেন নিবিড় ভাবে, তাঁর কথা পড়তে পড়তে মনে হয় যেন আয়েষার বাবাই ওই গ্রামের মেয়েদের ধাত্রীমাতা। মেরুনা মা-মেয়ের সম্পর্কের জটিলতার দিকটি— ‘ডিফিকাল্ট মাদার-ডটার রিলেশনশিপ’— নিয়ে আসেন লেখায়, তাঁর মা শেলী মণ্ডলের (মুর্মু) ডায়েরি উদ্ধৃত করে নিজেকে খোঁজেন। লেখকের মনের উথালপাথাল স্পর্শ করে পাঠককে।
তবে এই সঙ্কলনে যে লেখাটি আমাকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছে, তার নাম ‘বাসা বদল’, লিখেছেন স্বাতী ঘোষ। এটি একটি অন্য রকম পরিবারের গল্প বলে— যেখানে লেখক তাঁর দিদিমা, মা ও নাবালক পুত্রকে নিয়ে থাকতেন। চার প্রজন্মের একত্রে বসবাসের এই গল্পে আসন পাতেন তাঁদের সংসারের সহায়িকারা। তাঁর সঙ্গে সহায়িকাদের সম্পর্ক ও সুখ-দুঃখের আদানপ্রদানকে লেখক চৌকাঠের ও-পারে রেখে ভিতরে ঢুকতে পারেন না, তা তাঁর নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়ার অঙ্গ হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবীবিদ্যার গবেষণা পদ্ধতি নিয়ে পড়ানোর দায়িত্ব পেয়ে, সেই কোর্সে নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি থেকে সরে এসে নতুন এক দেখার চোখ তৈরি করার সময়কার ভাবনা-চিন্তাগুলো এসে পড়ে তাঁর আত্মসমীক্ষায়— জুড়ে যায় মায়েদের কথার সঙ্গে। এই বোঝাপড়া করতে করতে লিখে চলার মধ্যে তাঁর দিক থেকে উঠে আসে একটি গভীর প্রশ্ন— কী ভাবে লিখব। নিজের সঙ্গে একান্ত আলাপকে কী ভাবে পরিবেশন করবেন পাঠকের জন্য, নিজের মধ্যে ওঠা সেই প্রশ্নকে তিনি ভাগ করে নেন এখানে। আর অন্তরঙ্গ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই একই প্রশ্ন নিয়ে ভাববার একটা সুযোগ ঘটে আমাদেরও।
শর্মিষ্ঠা দত্ত গুপ্ত
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)