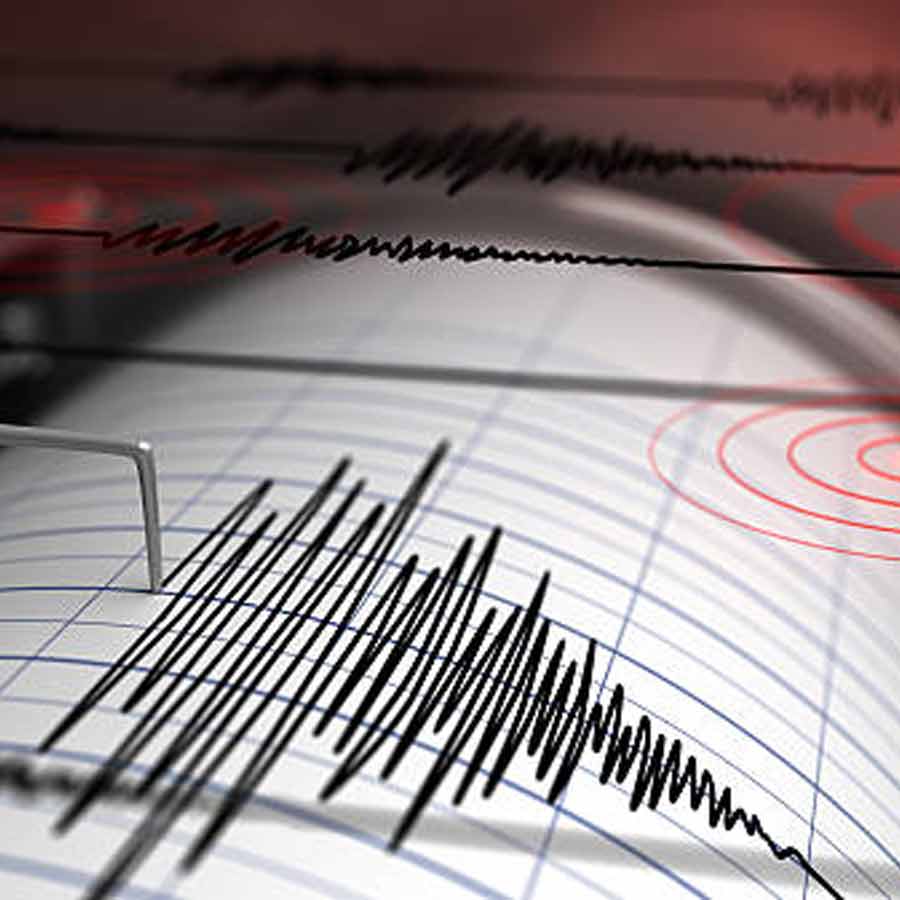বয়স তখন তিয়াত্তর। বাপুর সঙ্গে পুণের কাছে আগা খান প্রাসাদে অন্তরিন কস্তুরবা গাঁধী। বহু বছর পর মোহনদাস আবার কস্তুরবাকে পড়াশুনা শেখাতে উদ্যোগী হয়েছেন। তরুণ বয়সে স্ত্রীকে অক্ষর পরিচয় করাতে উদ্যোগী হতেন— কস্তুরের ঘোর অনিচ্ছা। মোহনদাসের অধ্যবসায় ভেসে যেত মিলনবাসনায়। এখন স্মৃতিশক্তি আর আগের মতো নেই। স্লেেট লিখে কুলিয়ে উঠতে পারেন না। একদা নিরক্ষর তরুণী কিছুটা গুজরাতি, ইংরেজি লিখতে পড়তে শিখেছেন এত দিনে। বাপুকে বলেছিলেন, আমার একটা নোটবুক চাই, তাতে লিখব। নানা সমস্যার চিন্তায় গাঁধীর সে দিন মেজাজ উত্তপ্ত। বললেন, আগে ঠিক করে লিখতে শেখো, তার পর নোটবুক পাবে। ক্ষুব্ধ কস্তুরবা নিজের স্লেটখানিও ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, আমার লেখাপড়া শেষ। পরে বাপু নোটবই আনিয়ে দিয়েছিলেন, কস্তুরবা নেননি। ১৯৪৪ সালে অন্তরিন অবস্থায় চলে যান কস্তুরবা। স্ত্রীর মৃত্যুদিন পর্যন্ত খাতাটি কাছে রেখে ছিলেন গাঁধীজি, ভুলতে পারেননি সেই আহত চাহনি। সামান্য ঘটনা। এমন কত অভিমান তরঙ্গ সংসারে ওঠে আর ভেঙে যায়। ওই বয়সে খাতায় কতই বা লিখতেন কস্তুরবা? তবু, পঁচাত্তর বছর আগে চলে যাওয়া এই অসামান্যা নারীর কথা ভেবে মনে হয়, এমন কত না-পাওয়া নোটখাতার অভাবে নারীর জীবন পরিণত হয় অগ্রন্থিত মৌখিক ইতিহাসে।
ভারতীয় রাজনীতিতে, জনমানসে গাঁধীর প্রভাব যত বেড়েছে, সময় এগিয়েছে, কস্তুর পরিণত হয়েছেন কস্তুরবা এবং পরিশেষে বা-তে। তাঁর নিজস্ব সত্তা লীন হয়ে গিয়েছে গাঁধীর সুবিশাল ব্যক্তিত্বের ছায়ায়। ১৮৯৭ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত তিন দশকের বেশি জুড়ে যিনি দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলন, ভারতে অসহযোগ ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন, বহু বার কারাবরণ করেছেন, লিখেছেন জাতির প্রতি বার্তা, এমনকি বিপুল জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন ১৯৪২ সালে গাঁধী গ্রেফতার হওয়ার পর, তাঁকে গাঁধী জীবনীকাররা সুশীল শান্ত পতির অনুগমনকারিণী ‘বা’তে পরিণত করে রেখেছেন। সুবিচার কি গাঁধীও করেছেন? তাঁর নিজের লেখায় যতটা এসেছে নিজের সিদ্ধান্ত, অনুশোচনা, নিজের মনোভাবের বিশ্লেষণ, ততটাই উহ্য থেকেছে কস্তুরবার মনের কথাগুলি।
কেমন ছিল কস্তুরবার ভাবনা? কী ভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে বোঝাপড়া করেছেন তিনি? সাত বছর বয়সে বিবাহ। ১৫ বছরে প্রথম বার মা হওয়া। সদ্যোজাত সন্তানের মৃত্যুশোক। তখনও কস্তুরবার বাইরের জগৎ ছিল না। স্কুলপড়ুয়া স্বামীর সত্য নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা আর কামনাবাসনার উচ্ছ্বাস, তার সঙ্গে নানা সন্দেহে বিপর্যস্ত মন। স্বামীর বিরহ ছিল জীবনের অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ। দেশান্তরি হলে কবে ফিরবেন জানা নেই। অহিংসার সঙ্গে আলিঙ্গন করেছেন স্বেচ্ছাদারিদ্রকে। ডারবান যাত্রায় জাহাজে পুরোটা সময় গাঁধী স্ত্রীপুত্রদের ইউরোপীয় কেতা, চলনবলন শেখালেন। শেষে বর্ণবিদ্বেষী জনতার হিংস্র আক্রমণের ভয়ে জাহাজ আটকানো হল। তাও শেষ রক্ষা হল না, পথে আক্রান্ত হলেন গাঁধী। বন্ধুর বাড়ি স্ত্রীপুত্র-সহ আশ্রয় নিলেন, ঘিরে থাকল জনতা। জোহানেসবার্গের বড় বাড়িতে সবে গুছিয়ে বসেছেন, ভারতীয়দের কলোনিতে হানা দিল বিউবোনিক প্লেগের মহামারি। গাঁধী কিছু বলার আগেই কস্তুরবা যেতে চাইলেন প্লেগ-আক্রান্তদের কাছে, সেবার জন্য। গাঁধী স্ত্রীকে বুঝিয়েসুজিয়ে পাঠান, ভারতীয় পরিবারগুলির কাছে গিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য সচেতনতার কথা বোঝাতে। সেই প্রথম কস্তুরবার অন্য পরিমণ্ডলে প্রবেশ। যেন এক নতুন মানুষ। পতি-অনুগামিনী নন, নিজের বিশ্বাসের শক্তিতেই কস্তুরবার জনসেবায় প্রথম অংশগ্রহণ।
অল্প বয়সে চেয়েছিলেন নিজের ঘর, একার সংসার— যেখানে অন্য বর্ষীয়সীরা নন, সিদ্ধান্ত নেবেন কস্তুর নিজে। সে ঘরের রূপ বদলেছে অকল্পনীয় বৈচিত্রে। দক্ষিণ আফ্রিকার ফিনিক্স সেট্লমেন্টে একটি সংবাদপত্রকে চালিয়ে যাওয়ার লড়াই জারি রাখতে গাঁধী গড়ে তুললেন এক বসত। স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে এবড়োখেবড়ো খেতের জমি পেরিয়ে দুই মাইল হাঁটা। কস্তুরের স্বপ্নের বাড়ি স্থানান্তরিত হল সেখানেই, সামূহিক জীবনযাপনে। ১৯১৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিল, খ্রিস্টান ধর্ম ছাড়া অন্য মতে সম্পাদিত বিবাহ দক্ষিণ আফ্রিকায় বেআইনি। তার ফলে বহু ভারতীয় স্ত্রীকে ফিরে যেতে হবে দেশে, সন্তানরা হয়ে যাবে অবৈধ, তাদের সম্পত্তিতে অধিকার থাকবে না। স্থানীয় ভারতীয় সম্প্রদায়ের জন্য বিরাট আঘাত। নাটালের ফিনিক্স বসত থেকে গাঁধী সূচনা করলেন সত্যাগ্রহের। কারাবরণ করার প্রস্তাব দিলেন গাঁধী, কিন্তু মনস্থির করেছিলেন কস্তুরবা নিজেই— বাল্যস্মৃতি থেকে সীতা, রানি লক্ষ্মীবাই প্রমুখের কাহিনি মনের মধ্যে মন্থন করে। স্বামীর আদেশে নয়, নিজের লড়াই বলে দেখেছিলেন বলেই, সঙ্গিনীদের নিয়ে ট্রেনে ট্রান্সভাল এসে কারাবরণ করতে তাঁর বাধেনি। মারিত্সবুর্গ জেলে অনেক কষ্ট, খাবারের অভাব, রক্ষীদের উৎপীড়ন, সব সহ্য করে ভাঙা স্বাস্থ্য নিয়ে জেল থেকে বেরোলেন তিন মাস পর। সন্তরমণী হতে চাননি, দোষেগুণে এক স্বাভাবিক নারী হতে চেয়েছিলেন, ফলে নিজের জীবনের সঙ্কটগুলির মোকাবিলা তাঁকে নিজেকেই করে নিতে হয়েছে।
এক ‘নিম্নবর্গ’-এর অতিথির শৌচপাত্র বহনের সময় মুখ নিরানন্দ ছিল, সেই অপরাধে ক্রুদ্ধ বাপু কস্তুরবাকে হাত ধরে বাড়ির বাইরে বার করে দিতে গিয়েছিলেন ডারবানে। কস্তুর মেনে নেননি, নিজের মতো করে প্রতিবাদ করেছিলেন। ন্যূনতম হিংসাও যে দাম্পত্য সম্পর্কে অমার্জনীয়, তা স্ত্রীর কাছেই সে দিন শিখেছিলেন গাঁধী। অন্যত্র তিনি লিখেছেন, অহিংসার শিক্ষা আমি কস্তুরবার কাছেই পেয়েছি। পরবর্তী কালে, সাবরমতী আশ্রমে অস্পৃশ্যতার সম্পূর্ণ বর্জনের জন্য গাঁধী যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আশ্রমের কিছু সদস্য তা মানতে পারেননি। কস্তুরও তাঁদের এক জন। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে সংঘাতে না গিয়ে, নিজের চেষ্টায় মনকে তৈরি করেছিলেন। যথেষ্ট শক্তি না থাকলে তা সম্ভব নয়। জীবনে এমন বহু বার ঘটেছে, বিভিন্ন জেলে কারাবন্দি গাঁধী, কস্তুর, তাঁর সন্তানেরা। মা হিসেবে যে টানাপড়েন তাঁকে সইতে হয়েছে, জাতির পিতা তার থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন বলেই মনে হয়। পিতার নীতি মানতে না পেরে জ্যেষ্ঠ সন্তান চলে গেলেন। আর এক সন্তানকে পাঠানো হল দক্ষিণ আফ্রিকায় পিতার অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করতে। মা হিসেবে কত কষ্ট পেয়েছিলেন এ সবে, তার কোনও বিবরণ কোথাও নেই। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার সময়ই হারান নিজের বাবা, মা, ভাই, ভ্রাতৃবধূকে। মাতাপিতার বিয়োগে গাঁধীর শোকপ্রকাশের বিবরণ আছে, কস্তুরবার নেই। সাবরমতী আশ্রমে অজস্র কাজ থাকত তাঁর। গাঁধীর সঙ্গে যেতে পারতেন না সর্বত্র। কাছাকাছি গ্রামে তবু নিজেই যেতেন, চরকাটি সঙ্গে নিয়ে। বলতেন, ঘরে ঘরে যদি মেয়েরা সুতো কাটে, বদলে যাবে দেশ।
১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলনে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়েছিলেন কস্তুর। তত দিনে তিনি বুঝে গিয়েছেন, নানা ভাবে আন্দোলনের অভিমুখ বদলালেও স্বরাজই একমাত্র লক্ষ্য। বিদেশি পণ্যবর্জন আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলে মহিলারা এসেছিলেন আন্দোলনের পুরোভাগে। ১৯২২ সালে রাওলাট আইনের বিরোধিতার পর গাঁধীর প্রহসনসদৃশ বিচার হয়, ছয় বছরের কারাবাসও হয়। সেই সময় অবিচলিত (সম্ভবত অন্তরে বিধ্বস্ত) কস্তুরবা লিখেছিলেন জাতির প্রতি তাঁর আবেদন। ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের আরম্ভে গ্রেফতার হন গাঁধী। দেশব্যাপী নিষ্পেষণে নির্বিচারে জেলবন্দি মানুষ। শিবাজি পার্কে গাঁধীর ভাষণ দেওয়ার কথা সে দিন বিকেলে— শ্রোতারা এসেছেন, বক্তা কই? কস্তুর বললেন, আমি করব সম্ভাষণ। সুশীলা নায়ারের সঙ্গে বসে লিখে ফেললেন সেই অমোঘ ভাষণ। “গাঁধীর আদর্শ অনুসরণ ছাড়া আমাদের অন্য পথ নেই। ভারতের মেয়েরা তাঁদের শক্তির পরিচয় দিন। তাঁরা সবাই আন্দোলনে যোগ দিন, জাতিবর্ণের বিভেদ ভুলে। সত্য ও অহিংসাই হোক আমাদের মন্ত্র।” ১৯৪৪-এ আগা খান প্রাসাদে অন্তরিন অবস্থায় মৃত্যু হয় কস্তুরবার। সারা দেশ শোকাচ্ছন্ন, কিন্তু সরকার মানুষকে ভিতরে এসে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের অনুমতি দেয়নি। গাঁধী তাঁর সন্তানদেরও ভিতরে আসতে দিলেন না, যাতে দেশবাসীর চেয়ে এক তিল বেশি সুবিধে যেন তাঁরা শোকপালনেও না পান। ‘‘হয় সমস্ত দেশ শোকপালন করবে, নয়তো কেউ না।’’ নির্জনে, কারাগার প্রাঙ্গণে সৎকার হল অন্তরে-বাইরে সংগ্রামে লিপ্ত এক নারীর। ১৯৪৪ সালে শোকে উদ্বেল দেশ তাঁকে অভিধা দিল ‘জাতির মাতা’র।
জাতির পিতার সার্ধশতবর্ষে আমাদের মনে পড়ে কি, ১৮৬৯-এর এপ্রিলে কস্তুরবারও জন্ম? যদিও কোনও নথি নেই, তবু এ কথা মোহনদাস কস্তুরবা দুই জনেই জানতেন, জানতেন উত্তরসূরিরাও। স্বামীর চেয়ে তিনি কয়েক মাসের বড়, এই নিয়ে কস্তুর পরিহাসও করেছেন। কস্তুরবার সার্ধশতবর্ষ উদ্যাপনের কোনও উদ্যোগ কিন্তু চোখে পড়েনি। নারীর অলিখিত ইতিহাস এই ভাবেই অস্পষ্ট হয়ে যেতে থাকে।