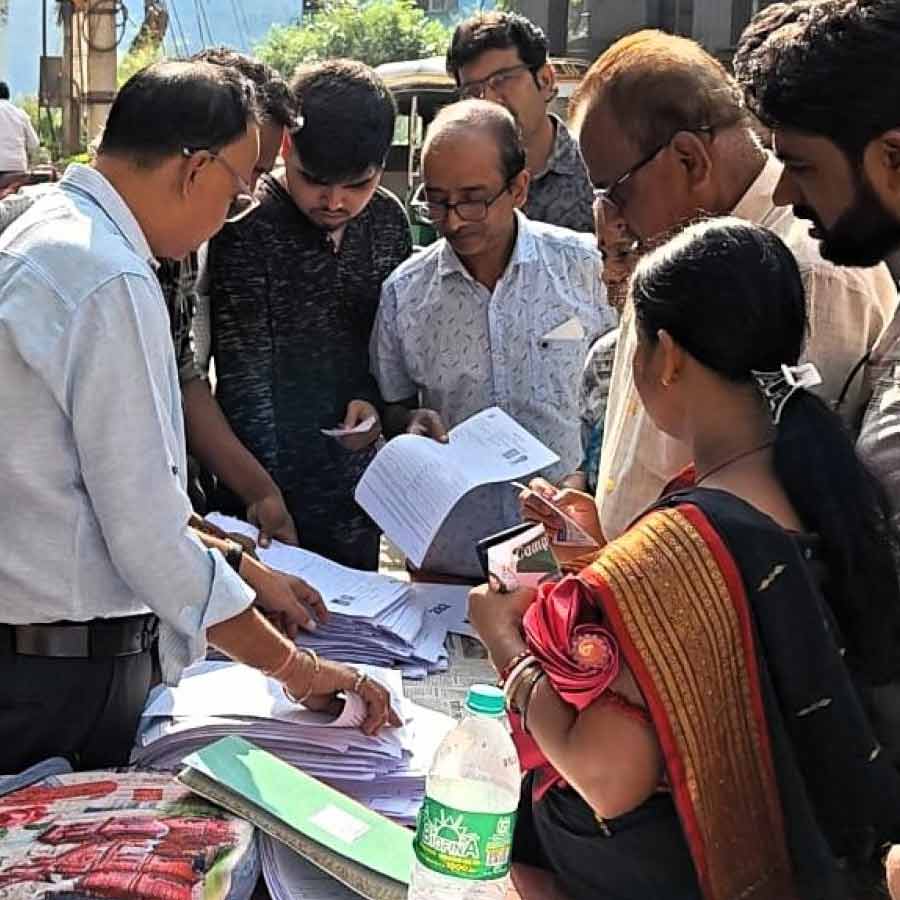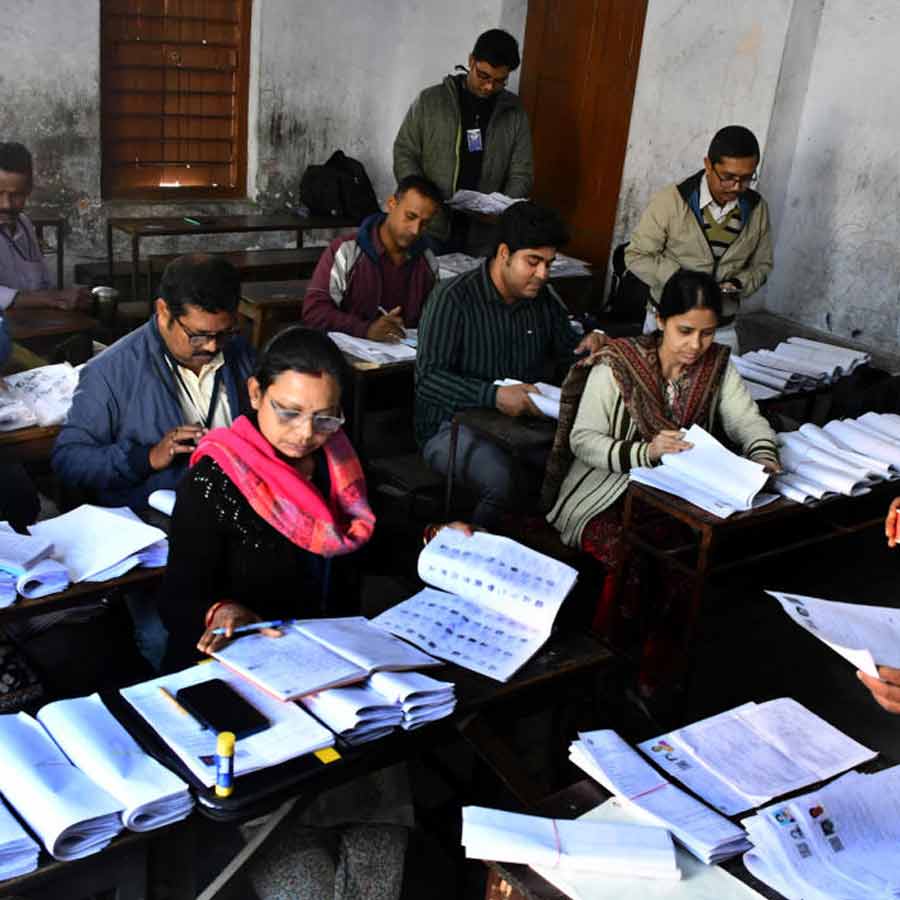প্রশ্ন: আপনার নতুন বই (পলিসিমেকার্স জার্নাল, সাইমন অ্যান্ড শুস্টার, ২০২১) থেকে একটা কথা খুব স্পষ্ট ভাবে ফুটে ওঠে— প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ বা অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের শোনার অভ্যাস ছিল। আপনার সঙ্গে তাঁরা যখন একমত হননি, তখনও আপনার কথা মন দিয়ে শুনেছেন।
কৌশিক বসু: একেবারেই। তবে আমি বলব, এই ব্যাপারে মনমোহন সিংহ ছিলেন সবার চেয়ে আলাদা। তার একটা বড় কারণ ছিল যে, তিনি পেশাদার রাজনীতিক ছিলেন না। রাজনীতিকদের মূল লক্ষ্য থাকে পরের নির্বাচনে জয়লাভ। মনমোহন সিংহ এই উদ্দেশ্যে চালিত ছিলেন না। তবে, প্রণববাবুও শুনতেন। আমার সৌভাগ্য, যে দু’জন রাজনীতিকের সঙ্গে আমায় নিয়মিত কাজ করতে হত, সেই মনমোহন সিংহ ও প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই ভাল ছিল, কাজ করতে কখনও অসুবিধা হয়নি। ডক্টর সিংহের পুরো মনোযোগটাই ছিল দেশের প্রগতির দিকে। ফলে, তাঁর সঙ্গে যত খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা করা যেত, সেটা অন্য কারও সঙ্গে কার্যত অসম্ভব। একটা উদাহরণ দিই। মোবাইল ফোনের থ্রি-জি স্পেকট্রাম বণ্টনের সময় আমি আধুনিক নিলামের প্রস্তাব করলাম। নিলাম জিনিসটা অত্যন্ত জটিল— একটা নিলাম প্রক্রিয়া তৈরি করার জন্য বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভর করতেই হয়। প্রধানমন্ত্রী আমার পরামর্শ পুরোটা শুনেছিলেন, এবং সম্মত হয়েছিলেন। গোড়ায় অনুমান ছিল, এই স্পেকট্রাম বিক্রি করে সরকার ৭০০ কোটি ডলারের মতো আয় করতে পারবে। নিলামের ফলে সরকারের আয় হল ১৫০০ কোটি টাকা। এই যে বাড়তি ৮০০ কোটি টাকা এল, সেটা কিন্তু মনমোহন সিংহের বিচক্ষণতার জন্যই।
তোমার প্রশ্নে ফিরি। কেন আমি মনমোহন সিংহকে সম্মান করি, তাঁর সঙ্গে কাজ করতে কখনও সমস্যা হয়নি কেন, তার একাধিক কারণ আছে। প্রথমত, তাঁর কিছু নৈতিক মূল্যবোধ আছে, কোনও রাজনৈতিক লাভের জন্যই যা তিনি বিসর্জন দেবেন না। এই কথাটা দুনিয়ার খুব কম রাজনৈতিক নেতা সম্বন্ধে বলা যায়। দ্বিতীয়ত, সব কিছু ছাপিয়ে তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতের উন্নয়ন ও আর্থিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করা, ভারতীয়দের কল্যাণসাধন— তিনি পরিচালিত হতেন মূলত এই তাগিদেই। এবং, এই কারণেই তাঁর সময়ে ভারত এত ভাল ভাবে চলছিল। তবে, তাঁর সঙ্গে আমার সুসম্পর্কের পিছনে আরও একটা কারণ আছে— মনমোহন সিংহ আসলে এক জন বাঙালি বুদ্ধিজীবী!
প্র: আপনার কি মনে হয় যে, বর্তমান জমানায় সেই শোনার অভ্যাসটাই চলে গিয়েছে?
উ: এখন কী হচ্ছে, সেই ভিতরের খবর তো আমি জানি না; কিন্তু বিভিন্ন সিদ্ধান্ত দেখে মনে হয় যে, কোনও পেশাদার অর্থনীতিবিদ, কোনও অভিজ্ঞ আমলা— বস্তুত, যে কোনও কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ— তেমন সিদ্ধান্তে সায় দিতে পারবেন না। দুটো উদাহরণ দিই। প্রথমটা ডিমনিটাইজ়েশন। সম্পূর্ণ অবান্তর একটা জিনিস, যেটা করে অর্থব্যবস্থার সর্বনাশ হল। আমি শুনেছি যে, রঘুরাম রাজন ডিমনিটাইজ়েশনের সিদ্ধান্তে রাজি হননি। তিনি রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে সরে যাওয়ার পরে সরকার এই কাজটা করল। দ্বিতীয়টা হল গত বছরের লকডাউন ঘোষণা। মার্চের শেষে যখন সিদ্ধান্ত ঘোষিত হল, আমি তখন ভেবেছিলাম যে, সরকার নিশ্চয়ই সব দিক ভেবে, বিস্তারিত পরিকল্পনা করে তবেই লকডাউন ঘোষণা করেছে। এক সপ্তাহের মধ্যে দেখলাম, কোথায় কী! কোনও পরিকল্পনা নেই। এমন অপরিকল্পিত ভাবে যে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব, সেটা কার্যত অবিশ্বাস্য। আমার মনে হয়, ভারতীয় অর্থব্যবস্থা যে ক্রমেই খারাপ থেকে খারাপতর অবস্থায় যাচ্ছে, তার পিছনে অরাজনৈতিক চিন্তকদের কথা না শোনার, পরিকল্পনা না করার একটা মস্ত ভূমিকা আছে। আমাদের দেশে কিন্তু প্রতিভাবান, দক্ষ, বিশেষজ্ঞ মানুষের অভাব নেই। কিন্তু তাঁদের যদি ব্যবহারই না করা হয়, সেই প্রতিভা থেকেও কোনও কাজ হচ্ছে না। দেশের পক্ষে এটা খুবই দুঃখের কথা।
প্র: অথচ, দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ায় ভারতের সুনাম ছিল।
উ: সেই সুনামের ইতিহাস দীর্ঘ। প্রধানমন্ত্রী নেহরু এই কথাটা একেবারে ঠিক ভাবে বুঝেছিলেন যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শুধু রাজনীতিকদের উপর নির্ভর করলে চলবে না, সেই কাজে বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন। যোজনা কমিশন, এবং বিশেষ করে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের হাতে উন্নয়নের দায়িত্ব দেওয়াটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটা ঘটনা বলে আমি মনে করি। ভারতে পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও তার ব্যবহারের কাজটা এত ভাল ভাবে হয়েছিল যে, গোটা দুনিয়া সে দিকে নজর দিয়েছিল। অ্যাঙ্গাস ডিটনের মতো অর্থনীতিবিদ বারে বারেই সেই কথাটা মনে করিয়ে দেন। পরবর্তী কালে সুখময় চক্রবর্তীও খুব দক্ষ ভাবে এই দায়িত্ব সামলেছিলেন। আমি এমন দাবি করছি না যে, সেই সময় কোনও ভুল হয়নি। পরবর্তী কালে আমরা জেনেছি যে, কিছু কাজ অন্য ভাবে করলে ভাল হত। কিন্তু সেটাই তো জীবনের ধর্ম— ভবিষ্যতের নতুন জ্ঞানের আলোয় অতীতের ভুল ধরা পড়ে। আমি যখন মনমোহন সিংহের সঙ্গে কাজ করেছি, তখন যোজনা কমিশনের গুরুত্ব অনেকটাই কমে এসেছিল, কিন্তু বিস্তারিত পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার কথা সরকার ভুলে যায়নি। তার ফল ভারত পেয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীন হয়েছে, এমন দেশগুলোর মধ্যে ভারতই একমাত্র, যেখানে গণতান্ত্রিকতা বজায় রেখেও যথেষ্ট আর্থিক বৃদ্ধি হয়েছে। বিশেষত ১৯৯৫ সালের পর থেকে আর্থিক বৃদ্ধির হার রীতিমতো তাক লাগানো।
প্র: সেই অর্থব্যবস্থা এমন মুখ থুবড়ে পড়ছে কেন?
উ: সেই দোষ অনেকটাই বর্তমান সরকারের। নরেন্দ্র মোদীর সরকারের রাজনৈতিক নীতিকে আমি সমর্থন করি না, এ কথা অনেক বার বলেছি। ভারতের যে একটা সর্বজনীনতা ছিল, সবাইকে নিয়ে চলার পরিবেশ ছিল— অন্তত সেই চেষ্টাটুকু ছিল— তাঁরা এটা নষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে, আমি ভেবেছিলাম, তাঁরা অর্থব্যবস্থার পরিচালনা করবেন দক্ষ হাতে। সেটাও হল না। তার একটা বড় কারণ বিস্তারিত পরিকল্পনার অভাব। ভাল লোক নেই। রঘুরাম রাজন যত দিন ছিলেন, শুনেছি তিনি সরকারকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। এখন রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস আর্থিক নীতির দিকটা যথেষ্ট ভাল ভাবেই পরিচালনা করছেন, কিন্তু তার বাইরে তিনি সম্ভবত পরামর্শ দেন না, বা দিতে সাহস করেন না। ফলে, ভারতীয় অর্থনীতি সম্পূর্ণ দিশাহীন ভাবে চলছে। অতিমারির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে লাভ নেই— কারণ, অতিমারির আগে থেকেই পরিস্থিতি খারাপ। দেশে বেকারত্বের হার যেখানে পৌঁছেছে, তার সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার গৃহযুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশগুলোর তুলনা করা চলে।
এখানে একটা কথা বিশেষ ভাবে বলা প্রয়োজন। দেশের আর্থিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে শাসনের চরিত্রের একটা সম্পর্ক আছে। দেং জিয়াওপিং এবং তাঁর পরবর্তী সময়ের চিন বা লি কুয়ান ইউ-এর সিঙ্গাপুরের মতো দু’একটা উদাহরণ বাদ দিলে সর্বত্রই দেখা গিয়েছে যে, শাসক যদি একাধিপত্যকামী হন, তা হলে অর্থব্যবস্থাও মুখ থুবড়ে পড়ে। রিচেপ এর্ডোয়ানের তুরস্ক, বেন আলির টিউনিশিয়া, খোমেইনির ইরান— পর পর উদাহরণ দেওয়া যায়, যেখানে একনায়কতন্ত্রী শাসন অর্থনীতির সর্বনাশ করেছে। তার একটা কারণ হল, এই সর্বাধিপত্যকামী শাসকরা নিজেদের সামান্য অভিজ্ঞতায়— হয়তো কোনও ব্যবসা পরিচালনার অভিজ্ঞতা, অথবা কোনও ছোট প্রদেশের শাসনের অভিজ্ঞতা— ধরে নেন যে, তাঁরা দেশের অর্থব্যবস্থা সামলানোর ক্ষমতাও রাখেন। একটা রাজ্য চালানো আর দেশ চালানো কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। দেশের ক্ষেত্রে রাজস্ব নীতি, আর্থিক নীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি— এমন অজস্র জিনিস সামলাতে হয়। একনায়কদের যুক্তিহীন অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এই নীতিগুলির ক্ষতি করে। ফলে, অর্থব্যবস্থা ধাক্কা খাবে, এটাই স্বাভাবিক।
তবুও একটা প্রশ্ন থেকে যায়— যে দেশে একাধিপত্যকামী শাসকরা সফল ভাবে অর্থনীতি পরিচালনা করতে পারলেন, তাঁরা কী ভাবে সফল হলেন? আমি বলব, এটা মূলত ভাগ্যের ব্যাপার। অর্থাৎ, তাঁরা যে নীতির দিকে জোর দিয়েছেন, ভাগ্যক্রমে সেই দেশের পক্ষে সেটাই ঠিক নীতি। কিন্তু, ভাগ্যের হাতে অর্থনীতির হাল ছেড়ে দেওয়াটা কাজের কথা নয়।
প্র: আপনি কি মনে করেন যে, ইউপিএ সরকার আর্থিক ভাবে যতটা সফল হয়েছিল, সেই সাফল্যকে তারা ঠিক ভাবে বিপণন করতে পারেনি?
উ: সাফল্যের কথাটা ঠিক বলছ। গ্রামীণ কর্মসংস্থান যোজনাই হোক বা তথ্যের অধিকার আইন, ইউপিএ আমলে এমন বেশ কিছু জিনিস হয়েছিল, যেগুলো আক্ষরিক অর্থেই যুগান্তকারী। কিন্তু, সেই সাফল্যের কথা ঠিক ভাবে প্রচার করতে পারলেই তারা আবার ক্ষমতায় ফিরত কি না, তা নিয়ে আমার সংশয় আছে। তার কারণ একটাই— মূল্যস্ফীতি। আমি বলব, কোনও সরকারের পক্ষে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল মূল্যস্ফীতি। বেকারত্বের চেয়েও অনেক বেশি। কারণ, যাঁর চাকরি গেল, বেকারত্বের প্রত্যক্ষ আঁচ শুধু তাঁর গায়ে লাগল। বাকিরা শুনলাম যে, পাড়ার অমুকের চাকরি গিয়েছে, অথবা মাসির ছেলের চাকরি হচ্ছে না। কিন্তু, তার প্রভাব আমাদের জীবনে পড়ল না। অন্য দিকে, রোজ সকালে বাজারে গেলেই মূল্যস্ফীতির আঁচ সরাসরি গায়ে এসে লাগে। ইউপিএ সরকারের আমলেই ভারতে মারাত্মক মূল্যস্ফীতি হয়েছিল। এবং, সাধারণ মানুষ যা-ই বিশ্বাস করুন না কেন, ঘটনা হল, মূল্যস্ফীতির অনেকটাই সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। পরিস্থিতিটা এমনই দাঁড়াল যে, দশ শতাংশ হারে মূল্যস্ফীতির পরও যে অর্থনীতি নয় শতাংশের চেয়ে বেশি হারে বৃদ্ধি পেল, এই কথাটা মানুষের মনে থাকল না। অন্য দিকে, মোদী সরকারের আমলে ভারতের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের এমনই অবস্থা, আগের তুলনায় কম মূল্যস্ফীতি সত্ত্বেও প্রকৃত বৃদ্ধির হারে ধাক্কা লাগছে অনেক বেশি।
প্র: একটু প্রসঙ্গান্তরে যাই। এ বছর বিশ্ব ব্যাঙ্ক তাদের ইজ় অব ডুয়িং বিজ়নেস প্রকাশ করেনি; জানিয়েছে যে, বিভিন্ন দেশের চাপে রিপোর্টের তথ্যে কারচুপি হয়েছে। এই বিতর্কের আবহেই মনে পড়ল, গত কয়েক বছরে এই সূচককে নরেন্দ্র মোদীর সরকার যতখানি গুরুত্ব দিয়েছে, ভারতে তার আগে এই রিপোর্টকে কখনও ততখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কেউ যদি বলেন যে, প্রকৃত অর্থনীতিতে যে খামতি থেকে গিয়েছে, এই রিপোর্টের সাফল্যকে দেখিয়ে মোদী সরকার সে দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছে, সেটা কি ভুল বলা হবে?
উ: তোমার প্রশ্নের উত্তরে যাওয়ার আগে একটু এই সূচকটার কথা, এবং যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তার কথা বলি। আমি বিশ্ব ব্যাঙ্কে থাকাকালীন আমার তত্ত্বাবধানে এই রিপোর্ট প্রকাশিত হত। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, এই রিপোর্টের পরিসংখ্যানে কারচুপি করা মুশকিল— তথ্য সংগ্রহ করা হয় অত্যন্ত যত্নসহকারে। কিন্তু, এই সূচকে অর্থনীতি বিষয়ক তথ্যের চেয়ে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেশের আইন। ধরো, কোনও দেশে যদি চুক্তিখেলাপি হয়, তবে তার প্রতিকারের কী ব্যবস্থা দেশের আইনে আছে, এই সূচকের ক্ষেত্রে সেটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃত পরিস্থিতিতে কী ঘটছে, তার থেকে। ফলে, কোনও দেশ চাইলে এই সূচকে নিজের অবস্থান ভাল করার জন্য শুধু খাতায়-কলমে আইন সংশোধন করতে পারে। কার্যক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না হলেও, শুধু আইনের পরিবর্তনের ফলে সূচকে সেই দেশের উন্নতি ঘটবে। কিন্তু, বিতর্কটা তা নিয়েও নয়। সূচকের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কোনটার আপেক্ষিক গুরুত্ব কত হবে, তার অদলবদলেও কোনও দেশের অবস্থান তুলনায় ভাল হয়ে যেতে পারে। খবরে প্রকাশ, চিন আর সৌদি আরব বিশ্ব ব্যাঙ্কের উপর চাপ তৈরি করে এই জাতীয় অদলবদল ঘটিয়েছে। সেখানেই বিতর্ক।
এই বার তোমার প্রশ্নের উত্তরে আসি। যে হেতু এই সূচকের সঙ্গে প্রকৃত অর্থনীতির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ক্ষীণ, ফলে প্রকৃত অর্থনীতিতে বিন্দুমাত্র উন্নতি না হলেও এই সূচকে উন্নতি ঘটতেই পারে। এবং, কোনও সরকার চাইলে সেই উন্নতিকেই প্রকৃত উন্নতি বলে চালিয়ে দিতে পারে। আমি যখন বিশ্ব ব্যাঙ্কে ছিলাম, তখন পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো এই সূচক নিয়ে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল। চিন আগ্রহী ছিল। এশিয়ার মধ্যে বিশেষ করে বলব মালয়েশিয়া এবং শ্রীলঙ্কার কথা। খেয়াল করে দেখলে, এই দেশগুলোর কোনওটাই প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক নয়। আবার, এই সূচকে পিছিয়ে থাকলেও আমেরিকার কখনও খুব তাগিদ দেখিনি নিজেদের অবস্থানের উন্নতি ঘটানোর জন্য ধরাকরা করায়। ফলে, গণতন্ত্রহীন শাসনব্যবস্থার সঙ্গে এই সূচকের উন্নতির উপর সবিশেষ জোর দেওয়ার একটা সম্পর্ক থাকতে পারে, সেটা বলা যায়। ভারতের বর্তমান শাসকদেরও এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যেতে পারে।
প্র: ভারতে যে ক্রমেই গণতন্ত্রের পরিসর খণ্ডিত হচ্ছে, অর্থব্যবস্থার পক্ষে সেটা কতটা বিপজ্জনক?
উ: বিপজ্জনক এবং দুঃখের। ভারতে হিন্দুত্ববাদীরা বারে বারেই পাঁচ হাজার বছরের পুরনো অতীত নিয়ে গর্বিত হন। আমি তো বলব, গর্ব যদি করতেই হয়, তবে স্বাধীনতার পরে ভারতে যে গণতন্ত্রের উদ্যাপন হল, তা নিয়ে গর্বিত হওয়া উচিত। অন্য কোনও উপনিবেশ-উত্তর স্বাধীন দেশ কিন্তু একই সঙ্গে গণতন্ত্র আর আর্থিক বৃদ্ধি বজায় রেখে চলতে পারেনি। ভারতীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে, বা তারও আগে অর্থনীতিবিদ হিসাবে আমি যখন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বৈঠকে যেতাম, রীতিমতো গর্বিত বোধ করতাম। সেটার সর্বনাশ হল। অল্প কথায় একটা জিনিস মনে করিয়ে দিই— গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ভুলে ‘সংস্কার’ করলে তার ফল মর্মান্তিক হতে পারে। ভারতে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাক্ট ছিল, সেটা ১৯৪৭ সালের, দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেকার। ফলে, উত্তরাধিকার সূত্রে ভারত আর পাকিস্তান, উভয় দেশই সেই আইন পেয়েছিল। ১৯৫০-এর দশকে, আয়ুব খানের আমলে পাকিস্তানে সেই আইন সংস্কার হয়, অগণতান্ত্রিক পথে। তার ফল মারাত্মক হয়েছিল। গত বছর ভারত যে শ্রম আইন সংস্কার করল, তার প্রক্রিয়াও কিন্তু গণতন্ত্রকে পাশ কাটিয়েই হল। এই প্রবণতা বিপজ্জনক। এবং, কথাটা শুধু নরেন্দ্র মোদী সরকারকে মাথায় রেখেই বলছি না। আগামী দিনেও যাঁরা দেশে শাসনক্ষমতায় আসবেন, তাঁরা যদি গণতন্ত্রকে সম্মান না করতে পারেন, তার ফল দেশের জন্য মারাত্মক হবে।
সাক্ষাৎকার: অমিতাভ গুপ্ত