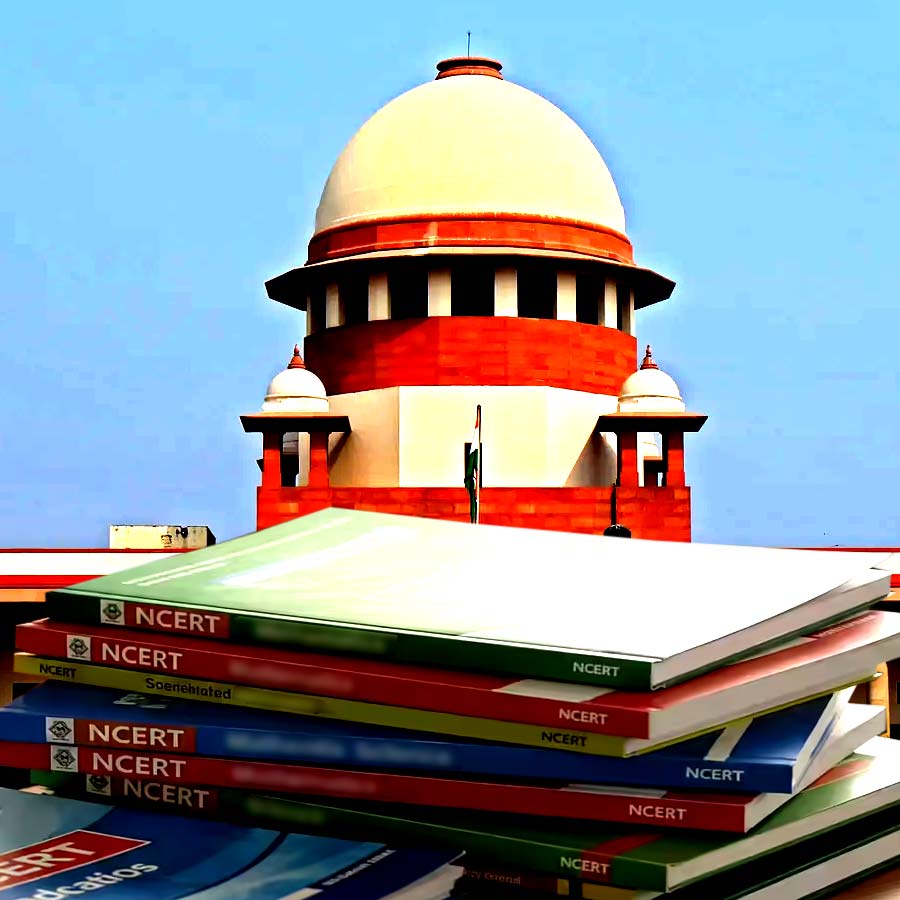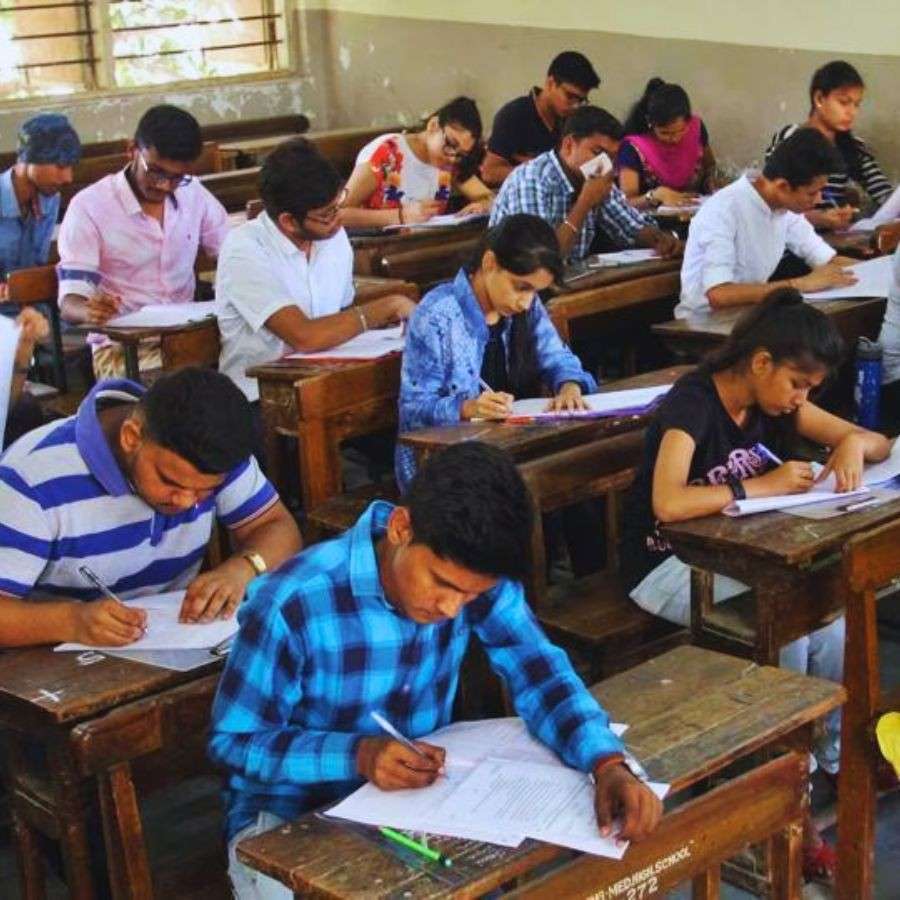গত দু’মাসে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন গোটা দুনিয়ার বিরুদ্ধে যে বিপুল শুল্ক-যুদ্ধ আরম্ভ করেছে, তাতে বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার মাত্রা বেড়েছে বহুলাংশে। আমেরিকান সরকার আমদানি শুল্কের হার পাল্টেছে ঘন-ঘন, ফলে অন্যান্য দেশের সরকারের বিপুল সময় এবং শ্রম ব্যয় করতে হয়েছে তার পাল্টা কৌশল স্থির করতে। এমন পরিস্থিতি আগে কখনও তৈরি হয়নি। বৈশ্বিক অর্থনীতির সঙ্গে এখন ভারতের যোগ যথেষ্ট। ফলে, এই অনিশ্চয়তা এবং দোলাচলের আঁচ ভারতের গায়েও লাগাই স্বাভাবিক। কিন্তু, মুহূর্তে ভারতীয় নীতিনির্ধারকরা যদি নিজেদের হাতে থাকা অস্ত্রগুলিকে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করতে পারেন, তুরুপের তাসগুলি বুঝেশুনে খেলেন, তা হলে ভারতের পক্ষে এই সঙ্কটের মুহূর্ত হয়ে উঠতে পারে একটি সুবর্ণসুযোগ। ভারতীয় অর্থব্যবস্থার গতি এখন তুলনায় শ্লথ— ফলে, এই মুহূর্তে এ সুযোগটির গুরুত্ব আরও বেশি।
বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থার সঙ্গে কোনও দেশ সংযুক্ত হতে পারে তিনটি ভিন্ন পথে— পণ্যের বাণিজ্যের মাধ্যমে, পরিষেবার বাণিজ্যের মাধ্যমে, এবং আন্তর্দেশীয় পুঁজির চলাচলের মাধ্যমে। গত তিন দশক ধরে ভারতীয় অর্থব্যবস্থার বৃদ্ধি এই তিনটি পথ থেকেই বিপুল ভাবে লাভবান হয়েছে। কিন্তু, সম্প্রতি তিনটি পথে সাফল্যের পরিমাণ সমতুল নয়।
২০০৫ সালে পরিষেবা ক্ষেত্রে গোটা বিশ্বে মোট যত রফতানি হত, ভারত থেকে হত তার ২ শতাংশেরও কম। ২০২৪ সালে সেই অনুপাতটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ শতাংশের বেশি। পুঁজির চলাচলের ক্ষেত্রেও ভারত বিশ্ব মঞ্চে আরও বেশি সম্পৃক্ত হয়েছে। কিন্তু, পণ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সে ভাবে উন্নতি ঘটেনি। পণ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ২০১৪ সাল অবধি যথেষ্ট দ্রুত গতিতে উদারীকরণ ঘটেছিল, কিন্তু তার পর থেকে ভারত ক্রমশ রক্ষণশীল পথে হেঁটেছে— ফলে বিশ্ব বাজারের তার দখলও ক্রমেই কমেছে। ২০১৩ সালে ভারতে আমদানি শুল্কের গড় হার ছিল ৬ শতাংশ; ২০২৩ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১২%— বিশ্বের বৃহৎ অর্থব্যবস্থাগুলির মধ্যে এটিই গড় আমদানি শুল্কের সবচেয়ে চড়া হার। গত এক দশকে পরিষেবা রফতানির পরিমাণ বছরে গড়ে ৯ শতাংশ হারে বেড়েছে; সেখানে পণ্য রফতানি বেড়েছে বছরে ৪ শতাংশেরও কম হারে।
উল্টো দিকে, ২০০১ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজ়েশন বা ডব্লিউটিও) যোগ দেওয়ার পরে চিন পণ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি করেছে। ২০০১ সালে বিশ্বের মোট পণ্য রফতানির ৪ শতাংশ ছিল চিনের দখলে; ২০২৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ শতাংশে। এর প্রভাব পড়েছে সে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির উপরেও— সে দেশের অর্থব্যবস্থার আয়তন এখন ২০০১সালের ১১ গুণ।
অবশ্য, চিনের বিশ্বের বৃহত্তম পণ্য রফতানিকারী দেশ হয়ে ওঠা নিয়ে বিতর্কও কম নয়। বারে বারেই অভিযোগ উঠেছে যে, চিন ডব্লিউটিও-র বিধি ভঙ্গ করছে— কর ছাড়, সস্তা ঋণ এবং অন্যান্য ছাড় দিয়ে উৎপাদনকারী সংস্থাগুলিকে অন্যায্য সুবিধা দিচ্ছে। আরও অভিযোগ যে, চিন বিদেশি পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ করে, এবং জোগান-শৃঙ্খলকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, যাতে অন্তর্বর্তী পণ্যের তুলনায় অন্তিম পণ্যের রফতানি বাড়ে। দীর্ঘ দিন ধরে চিনের বেশির ভাগ বাণিজ্যসঙ্গী দেশ এ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায়নি; যদিও চিনের বৃহত্তম বাণিজ্যসঙ্গী আমেরিকা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় চিনের বিরুদ্ধে বাজার প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপের ২৩টি অভিযোগ (মোট অভিযোগের সংখ্যা ১১৭) দায়ের করে। কিন্তু, কোভিড-১৯ অতিমারির সময় পরিস্থিতি পাল্টায়— চিনের উপরে তাদের অর্থনৈতিক নির্ভরতা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে, গোটা দুনিয়াই তা টের পায়, আমেরিকা তো বটেই।
অতিমারির সময় চিন কঠোর লকডাউন আরোপ করে, যা চলে প্রায় তিন বছর। এই সময়ে বৈশ্বিক জোগান-শৃঙ্খল বিপুল ভাবে ব্যাহত হয়। চিনের উপরে অতি-নির্ভরতা আমেরিকার অর্থব্যবস্থার জন্য কী ধরনের ঝুঁকি তৈরি করেছে, তা স্পষ্ট হয়। সম্ভবত এর থেকে একটা রাজনৈতিক অস্বস্তি তৈরি হয়, এবং চিন-নির্ভরতা কমানোর জন্য চাপ বাড়ে। ট্রাম্প-জমানায় আমেরিকার বাণিজ্য নীতির আমূল পরিবর্তন তারই ফল। সব দেশের আমদানির উপরেই আমেরিকা শুল্ক বাড়িয়েছে— প্রথম তিন মাসের জন্য, অর্থাৎ জুলাই অবধি, সেই শুল্কের হার ১০%— কিন্তু, চিনের ক্ষেত্রে সে হার ৩০%, এমনকি সাম্প্রতিক বৈঠকের পরেও।
এই পরিস্থিতিতে ভারত কোথায় দাঁড়িয়ে?
কোভিড-এর পর থেকেই বৈশ্বিক উৎপাদকরা ‘চিন+১’ নীতি অনুসরণ করতে শুরু করে— তাদের উৎপাদন-শৃঙ্খলের একটি অংশ চিনের বদলে অন্য কোনও দেশে সরিয়ে নিতে শুরু করে, যাতে চিনের উপরে নির্ভরতা কমে। ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, মেক্সিকো এবং ফিলিপিনসের মতো দেশ এর থেকে লাভবান হয়েছে। কিন্তু, দেশের অভ্যন্তরীণ নীতির কারণে ভারত এর সুবিধা নিতে পারেনি। ২০১৭ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বৈশ্বিক রফতানির ক্ষেত্রে ভিয়েতনামের অবদান যেখানে ১.৫% থেকে বেড়ে ১.৯% হয়েছে, ভারত সেখানে আটকে রয়েছে ১.৭-১.৮ শতাংশের ঘরেই।
বিশ্ব বাণিজ্যের মঞ্চে আবার যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, তা ভারতের সামনে আরও এক বার সুযোগ এনে দিয়েছে— বৈশ্বিক বাণিজ্যে নিজের ভূমিকা বৃদ্ধির, এবং তার মাধ্যমে আর্থিক বৃদ্ধির উচ্চতর কক্ষপথে পৌঁছে যাওয়ার। প্রশ্ন হল, ভারত কি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে প্রস্তুত?
এখানে এসেই একটা প্রশ্ন করা প্রয়োজন: গত তিন দশকে যেখানে পরিষেবা রফতানির ক্ষেত্রে ভারতের সুস্থায়ী এবং ধারাবাহিক বৃদ্ধি ঘটেছে, সেখানে পণ্য রফতানির ক্ষেত্রে ভারত যথেষ্ট সফল হল না কেন? উত্তরে তিনটি কথা বলতে হবে। এক, পণ্যের তুলনায় পরিষেবা ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ কম হয়ে থাকে, ক্ষেত্রটির চরিত্রের কারণেই। দুই, পরিষেবা ক্ষেত্রে তুলনায় কম মূলধন প্রয়োজন। এবং তিন, পরিষেবা ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিনিয়োগের প্রয়োজনও কম। এই তিনটি কারণের দরুন পরিষেবা ক্ষেত্রে ‘ইজ় অব ডুয়িং বিজ়নেস’ ধারাবাহিক ভাবেই বেশি। অন্য দিকে, পণ্য উৎপাদনের জন্য কারখানা এবং যন্ত্রপাতির জন্য বড় অঙ্কের প্রাথমিক বিনিয়োগ প্রয়োজন, তুলনায় অনেক বেশি পুঁজি প্রয়োজন, এবং বহু কারণে এই ক্ষেত্র সরকারি লাল ফিতের গ্রাসে পড়ে— যেমন, জমি অধিগ্রহণের জটিলতা, কঠোর শ্রম আইন, পরিবেশগত ছাড়পত্র, আমদানি শুল্ক, এবং বাণিজ্যের পথে বিবিধ বাধা।
অর্থাৎ, এই মুহূর্তে বিশ্ব বাজারে যে সুযোগটি তৈরি হয়েছে, তাকে কাজে লাগাতে গেলে ভারতীয় নীতিনির্ধারকদের কর্তব্য হল, এ দেশের উৎপাদন ক্ষেত্রটিকে বিদেশি লগ্নিকারীদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা। ২০১৪ সালে গৃহীত ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ নীতির লক্ষ্য ছিল দেশের জিডিপি-তে উৎপাদন ক্ষেত্রের অবদানের অনুপাত বৃদ্ধি করা, কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। ২০১৫ সালে দেশের জিডিপি-র ১৬% এসেছিল উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে; ২০২৩ সালে অনুপাতটি দাঁড়িয়েছে১৩ শতাংশে।
এখন ভারতে কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন। অবিলম্বে যে কাজগুলি করতে হবে, তা হল— উৎপাদন ক্ষেত্রের জন্য জমি পাওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা কমানো, এবং শ্রমিক নিয়োগের পদ্ধতি সহজতর করা; বিবিধ ছাড়পত্র পাওয়ার প্রক্রিয়াকে দ্রুত করা; এবং এমন ভাবে বিভিন্ন আইন ও বিধি সংস্কার করা, যাতে তা বেসরকারি ব্যবসার পক্ষে অনুকূল হয়, প্রতিকূল নয়। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ সংক্রান্ত নিয়মগুলি আরও শিথিল করা প্রয়োজন। সবচেয়ে বড় কথা, ভারতের একটি স্পষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য বাণিজ্য নীতি চাই— আমদানি শুল্ক কমাতে হবে, শুল্ক-অতিরিক্ত বাধাগুলি দূর করতে হবে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যসঙ্গীর সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি তৈরি করতে হবে, এবং আমেরিকার সঙ্গেও গ্রহণযোগ্য বাণিজ্য সম্পর্কে পৌঁছতে হবে।
ট্রাম্পের শুল্কনীতি বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থার ছবিটি পাল্টে দিয়েছে। স্বল্পমেয়াদে প্রতিটি দেশই এই নতুন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করবে, নতুন ভাবে সম্পর্ক তৈরির উদ্যোগ করবে— এর ফলে হয়তো সবারই বৃদ্ধির হার কমবে। কিন্তু, ভারতের কর্তব্য উইনস্টন চার্চিলের পরামর্শ মেনে চলা: ‘কখনও একটা ভাল সঙ্কটকে নষ্ট হতে দিয়ো না’। ভারতের নীতিনির্ধারকদের কর্তব্য, এই সঙ্কটের সুযোগে বৈশ্বিক উৎপাদন ক্ষেত্রের বাজারটির বৃহত্তর অংশ দখল করা। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত উন্নত অর্থব্যবস্থা হয়ে উঠতে চাইলে এমন সুযোগ কোনও মতেই হাতছাড়া করা চলে না।
অর্থনীতি বিভাগ, ইন্দিরা গান্ধী ইনস্টিটিউট অব ডেভলপমেন্ট রিসার্চ
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)