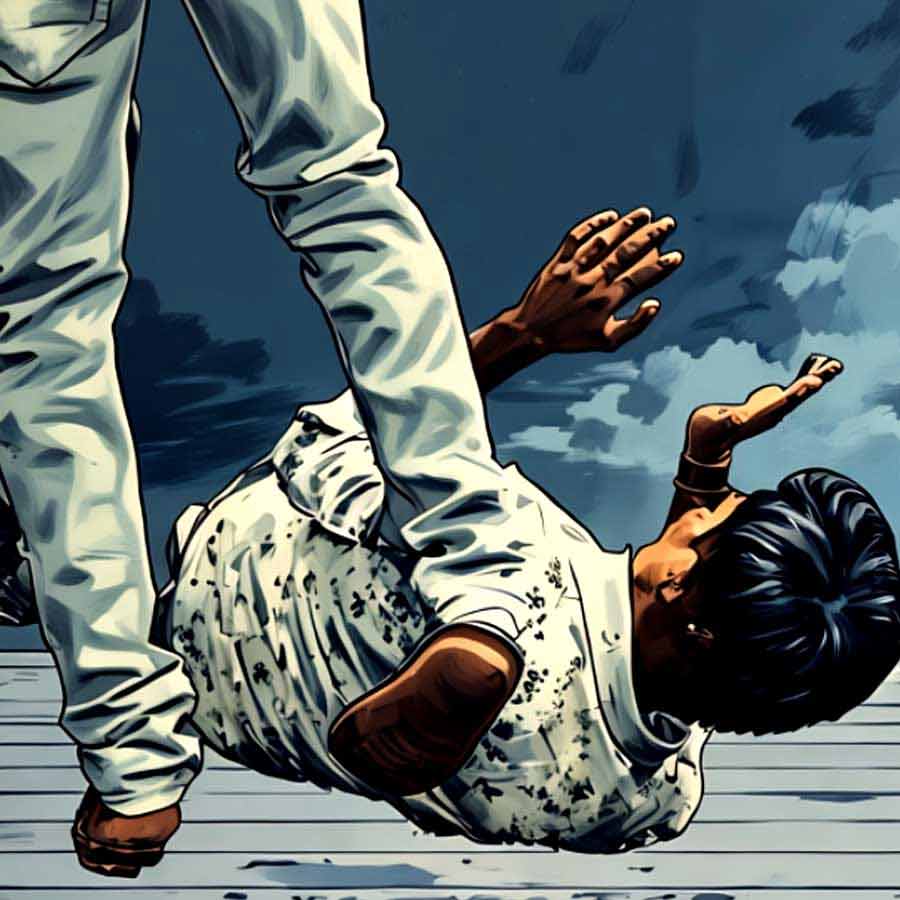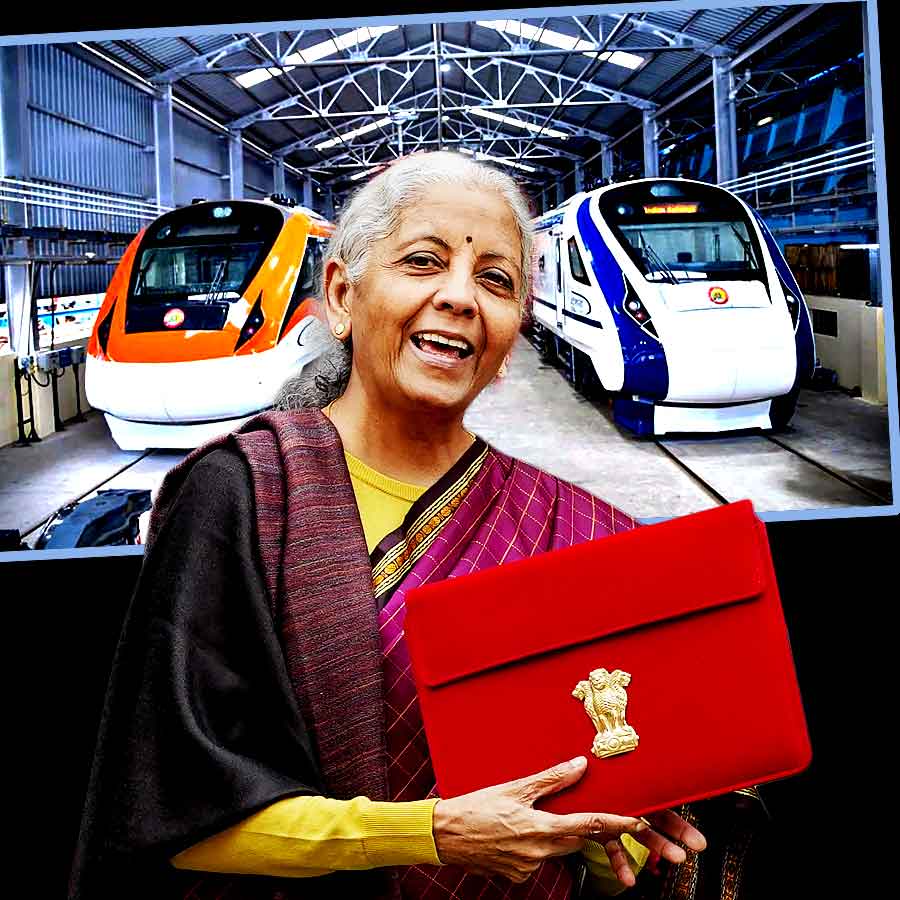ঋত্বিক ঘটকের যত বাণিজ্যিক ব্যর্থতা, তার মধ্যে কোমল গান্ধার ছিল সবচেয়ে মর্মন্তুদ। হলগুলো থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে ছবিটা তুলে নেওয়া হয়। ছবির প্রযোজকও ছিলেন ঋত্বিক। স্ত্রী সুরমা ঘটক এবং কন্যা সংহিতা লিখেছেন এই ব্যর্থতার ফলে ওঁর এবং গোটা পরিবারের জীবনে নেমে আসা বিপর্যয়ের কথা। সুরমার ভাষায়, “কোমল গান্ধারের পরে যে আঘাত জীবনকে চুরমার করে দিয়েছিল— কিছুতেই সে বেদনার শেষ হল না।” নানা জনের সাক্ষ্যে পাওয়া যায়, ঋত্বিকের নিজের সবচেয়ে প্রিয় ছবি ছিল কোমল গান্ধার। বলতেন, এ ছবি লোকে ত্রিশ বছর পরে বুঝবে। অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভৃগু) ও চিত্রা সেন (জয়া) জানিয়েছেন, ছবি চলাকালীন হলের কাছাকাছি যেতে ওঁরা ভয় পেতেন, যদি লোকে গালমন্দ করে! কিন্তু পরিচালককে সবচেয়ে ব্যথিত করেছিল কমিউনিস্ট পার্টির কাগজ স্বাধীনতা-র আক্রমণাত্মক সমালোচনা।
এই সব প্রতিক্রিয়া আজ ফিরে দেখতে গেলে মনে হয়, দলের প্রশ্নটাই সবচেয়ে গুরুতর ছিল। স্বাধীনতা-র সমালোচক লিখেছিলেন, পরিচালক “এক ব্যক্তিকে সমষ্টির ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠা করবার হঠকারিতায় বিভ্রান্ত হয়েছেন। এই বিভ্রান্তির কলুষে ব্যক্তি প্রাধান্যের নীচে সত্য দলিত হয়েছে।” ১৯৬১-র এই সমষ্টির কথা ১৯৮৫-তে এক মার্ক্সবাদী সমালোচকের লেখা পার্টির কথায় পরিণত হল। ফিল্ম সোসাইটির পত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন, ঋত্বিকের মূল সমস্যা “কমিউনিস্ট পার্টির উপর তাঁর আদ্যন্ত আস্থা ছিল না। নিজের মতো মার্কসবাদ বুঝতে চেয়েছিলেন।” ঘুরে-ফিরে কথাটা এসেছে। চিত্রভাষ পত্রিকা কোমল গান্ধার নিয়ে যে মূল্যবান সংখ্যা প্রকাশ করেছে, তাতে ২০১৩ সালে আর এক জন সমালোচক লিখছেন, এই ছবির পরিচালক “বৃহত্তর রাজনীতি ও বামপন্থী নাট্যদলের সম্পর্ক নিয়ে আদৌ ভাবিত নন, তাঁর কাছে ব্যক্তিক প্রেমটাই যেন সবচেয়ে বড় বিষয় হয়ে উঠেছে।”
স্বাধীনতা-র লেখক গোড়াতেই মনে করিয়ে দিয়েছেন, কার জন্য ছবি করেন, এই প্রশ্নের জবাবে ঋত্বিক বলেছিলেন, “আমার জন্য।” উল্টো কথাটাও বহু বার বলেছেন। ‘ছবির ছন্দ ও গ্রন্থনা’ (১৯৬৪) প্রবন্ধে এ-ও লিখেছেন যে কোমল গান্ধার-এ তাঁর ‘করণীয় কর্ম’ ছিল “গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তিকে বিলোপ করে দেওয়া।” তবে এ ক্ষেত্রে ‘আমি’ একটা সমস্যা বটে। ভৃগু-অনসূয়ার ব্যক্তিজীবন শুধু নয়, পরিচালকের নিজের গল্প বলে বসাটা ছিল আরও বড় সমস্যা। সিনেমায় কেউ আত্মজীবনী লিখছেন, এমনটা খুব বেশি কেউ দেখেনি। ঋত্বিক দু’বার এ কাজ করেছিলেন, পরের বার যুক্তি তক্কো আর গপ্পো-তে। কোমল গান্ধার-এ নিজের বিয়ের গল্পসুদ্ধ বলে বসলেন, যুক্তি-তে সেই বিয়ে ভাঙার গল্প। তখনকার প্রায় সমস্ত সিরিয়াস শিল্পী কমিউনিস্ট রাজনীতির কাছাকাছি রয়েছেন। তাঁদের শিল্পে যৌথতা আর বহুর অভ্যর্থনা। সেখানে এই কাজ নিতান্ত বিসদৃশ লাগতেই পারে।
পরিচালকের নিজের লেখা নাটক দলিল-এর সংলাপ ঢুকে পড়েছে ভৃগুর নাটকে (‘এখানকার আকাশটাও ধোঁয়া,’ ইত্যাদি), বা পরেও তার মুখে শোনা গেছে। ভৃগুদের নাটকে অনসূয়ার ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়া থেকে শুরু করে অনসূয়ার প্রবাসী প্রেমিক আর ভৃগুকে ঘিরে সম্পর্কের টানাপড়েন তৈরি হওয়া— অনেকেই জানতেন এ ঋত্বিকের জীবন থেকে সরাসরি তুলে আনা। ছবিটা এতটা অসহ্য ঠেকার কারণ কিছুটা সেটাও।
অস্পষ্ট আরও নিজের কথা বলা ছিল। সুরমা লিখেছেন ঋত্বিককে ওঁর মায়ের ডায়েরি পড়তে দেওয়ার কথা। সেই স্মৃতি প্রায় অবিকল উঠে এসেছে বোলপুরে খোয়াইতে ভৃগুর হাতে অনসূয়ার মায়ের ডায়েরি তুলে দেওয়ার দৃশ্যে। এই সব গল্প জেনে আমরা ছবি দেখি না বটে, কিন্তু ব্যক্তি আমি-র হস্তাক্ষর সন্ধানে এ সব তথ্য কাজে লাগতে পারে। প্রশ্ন হল, এই উপাদানগুলো নানা ছবি জুড়ে কোন নকশা তৈরি করে, আর সেই নকশায় গাঁথা থাকে চিন্তার কোন প্রবাহ। আজ মনে হয়, এক আর বহু, ব্যক্তি আর সমষ্টির লাইন-টানা বিভাজন মেনে এই চিন্তাপ্রবাহকে ধরা যায় না। একটা অন্যটায় অলক্ষ্যে রূপান্তরিত হয়, আর সেই রূপান্তর অনূদিত হয় ছবির চলনে। কোনও মুহূর্তে একটিই সত্তা এক ও অনেক হয়ে উঠছে, তা-ও বিরল নয় ঋত্বিকের ছবিতে। না হলে ওঁর নিজের কথা বলার অবসর হত না।
ঈশ্বর যখন উদ্বাস্তু কলোনির লড়াই ছেড়ে এক নির্জন দেশে চাকরি নিয়ে চলে যায়, সম্ভবত তখনই সুবর্ণরেখা-র ট্র্যাজেডির সূত্রপাত। ছোটনাগপুরের নিসর্গ ঈশ্বর সীতা অভিরামের ব্যক্তিজীবন চিত্রায়িত করার পটভূমি হিসাবে এসেছে। কিন্তু সেখানে জনতার সখ্য দুর্লভ। পরে যখন সীতা অভিরামের সঙ্গে পালিয়ে যাবে, একাকিত্বের অভিশাপ ঈশ্বরকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেবে। এই সবের মধ্যে আবার জড়িয়ে পড়েছিল গোষ্ঠী পরিচয়: অভিরাম বড় হয়ে আবিষ্কার করে সে বাগদির ঘরে জন্মেছে।
যে হরপ্রসাদ ঈশ্বরকে ‘পলাতক’ বলে ভর্ৎসনা করেছিল সে-ও গোষ্ঠী, পরিবার সব হারিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ দেয়। দুই একা হয়ে যাওয়া বন্ধু আবিষ্কার করে মজায় মত্ত শহরের কোনও স্মৃতি নেই— মন্বন্তর দাঙ্গা দেশভাগ অ্যাটমবোমা, কিছুই যেন ঘটেনি। ঋত্বিক বিশ্বাস করতেন, সমষ্টিগত কোনও অবচেতনে এই ভুলে যাওয়া সব কিছু জমা হয়; ধ্বংসের সঙ্কেত হয়ে হঠাৎ উঠে আসে। মন থেকে ইতিহাস মুছে যাওয়া যে একাকিত্বের জন্ম দেয়, এই শিল্পীর দেখা দেশে তার সহজ নিরাময় নেই। সে জন্যই সুবর্ণরেখা-র অপবাদ জুটেছিল অবক্ষয় আর হতাশার ছবি হিসাবে। রবীন্দ্রনাথের শিশুতীর্থ-র সঙ্গে ছবি জুড়ে যে সংলাপ চলেছে তার সূত্র ধরেই মত্ততার রাত্রি এসেছিল, তার পরে ভোর। সে সব লক্ষ করার মতো খুব বেশি কেউ ছিলেন না। একা মানুষের সর্বনাশের কাহিনির পিছনে বস্তুত অনেকের কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল। ছবির শব্দপথে মন দিলে সেটা টের পাওয়া যায়। একে ঋত্বিকের ছবির কোরাস ধর্ম বলা যায় হয়তো। নেপথ্যে একের আর্তি অনেক স্বরে মিশে যায়, প্রতিবাদের স্বর আর কথকতার স্বর মিশে যেতে থাকে, কখনও তীব্রতায়, কখনও প্রতিধ্বনির ব্যবহারে। মেঘে ঢাকা তারা-য় নীতার হাঁটার উপর শোনা যায় ‘হো হো’ ধ্বনি, তার শেষ চিৎকার প্রতিধ্বনিতে বহুস্বরের মতো হয়ে ওঠে। কোমল গান্ধার-এ ‘দোহাই আলি’র যৌথ ধ্বনি আসার আগে ওই দৃশ্য জুড়ে বার বার কোরাস থেকে সোলো থেকে কোরাসে সঞ্চার ঘটতে থাকে। সুবর্ণরেখা-তে কাটা জন্তুর মতো ছটফট করে মরে যাওয়া সীতার মুখের উপর গান্ধীজির উচ্চারিত শেষ শব্দ শোনা যায়— ‘হে রাম’।
আত্মজীবনীই কি সমবায়ের অভিজ্ঞান হতে পারে না? এক আর বহু এক হতে পারে না? এই রকম কোনও একটা প্রশ্ন ঋত্বিককে নিশ্চয়ই ভাবিয়েছিল। বিজন ভট্টাচার্যকে দেখেছি এই পর্যায়ের ছবিগুলিতে অনেক দূর ঋত্বিকের প্রতিনিধি হয়ে অবতীর্ণ হতে। গণনাট্যের এই নায়ক শুধু সেই আন্দোলনের যৌথতার সঙ্কেত বহন করেন না, তাঁর নিজের কাজ, নিজের জীবন ঋত্বিকের সঙ্গে মিশে যায়। বিজনের গোত্রান্তর নাটকের হরেন মাস্টার অনেকটা মিশে আছে হরপ্রসাদে। বিজন তাঁর তৃতীয় নাটক নবান্ন থেকে আঙ্গিকের বদল ঘটিয়ে সঙ্গীতময় এক মিশ্র রীতি অবলম্বন করেছিলেন। ঋত্বিক সেই পথ গ্রহণ করলেন মেঘে ঢাকা তারা থেকে, ইংরেজি লেখায় যাকে উনি বলেছেন, ‘ক্যালেইডোস্কোপিক, পেজেন্ট-লাইক, রিল্যাক্সড, ডিসকার্সিভ’, ওঁর মতে যেটা ‘এপিক জনতা’র শৈলী।
আরও এক স্তর আছে ঋত্বিকের ছবিতে, যেখানে একের বিভাজনকেই অস্বীকার করা হয়। সেখানে চরিত্রেরা প্রথম আশ্রয়— জন্মের আশ্রয়— হারাতে চায় না; সামাজিক অর্থে ব্যক্তিও হতে চায় না। সেখানে প্রাথমিক বন্ধন ভাই-বোনের। ছবির পর ছবিতে দেখব রোম্যান্টিক যুগল অপ্রধান— মেঘে ঢাকা তারা, সুবর্ণরেখা তো বটেই, এক অর্থে নাগরিক আর যুক্তি তক্কো-তেও। রোম্যান্টিক যুগল নির্মাণ সম্পন্ন হয় একমাত্র কোমল গান্ধার-এ। কিন্তু সেখানে অনসূয়া প্রেমের স্বীকারোক্তির মুহূর্তে ভৃগুকে বলে, ‘তুমি আমার মায়ের ছেলে’!
এক আর বহুর সন্দর্ভ, আত্মতার খতিয়ান, অন্য কোনও শিল্পের তুলনায় কবিতার কাছ থেকে শেখাটাই স্বাভাবিক। ‘কোমল গান্ধার’ নামটা রবীন্দ্রনাথ আর বিষ্ণু দে-র কথা মনে রেখে দেওয়া। বিষ্ণু দে-র নাম রেখেছি কোমল গান্ধার (১৯৫৩) বইয়ের দীর্ঘ কবিতা ‘বহুবড়বা’ থেকে কয়েকটি লাইন মনে করা যাক, যেখানে ওই সন্দর্ভের কথা বলা আছে: “কোমল গান্ধার! জাগো বহুর বাড়বে/ ব্যাপ্ত দেয়ালিতে মেলো সত্তার অগম অন্ধকার/অন্ধকারে আনো কোজাগরী।/ ব্যক্তিস্বরূপের দীপে দীপে জ্বালো তারায় তারায় রূপের আরোপে/ বিরহে মিলন আর দুর্ভিক্ষে বসুধা/ সূর্যে চন্দ্রে মানুষে মানুষে গোষ্ঠীর আসর।”
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)