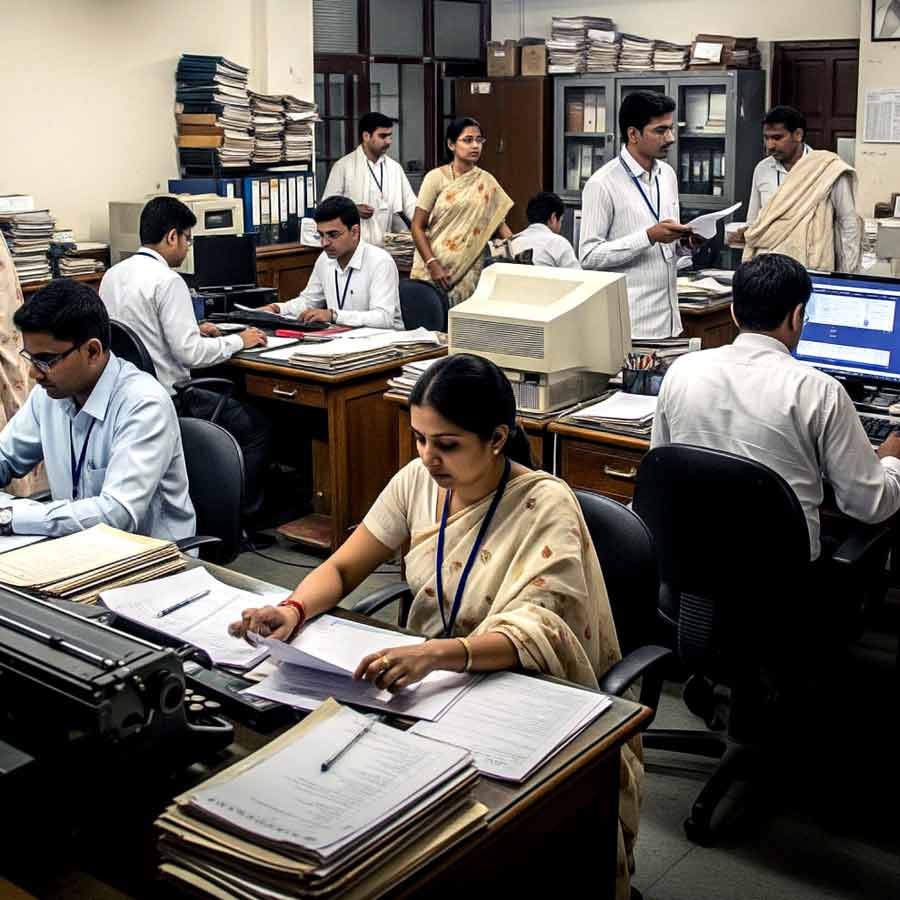কিংশুক সরকার তাঁর ‘নয়া বিধি, পুরনো নীতি’ (১৯-৫) প্রবন্ধে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের কর্মস্থলে স্থায়িত্ব ও অনিশ্চয়তার কথা বলেছেন। বেশ কয়েক বছর ধরেই দেশের বিভিন্ন সরকারি বা আধা সরকারি সংস্থায় বিভিন্ন পদে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। আসলে সর্বভারতীয় অথবা রাজ্য স্তরে যে সব প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পদে এমনকি নিম্নপদেও কর্মী নিয়োগ করা হত, সে সব পদের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধ রয়েছে। গুটিকতক প্রতিষ্ঠানে কিছু নিয়োগ এখনও হয় বটে, তবে তা অতি নগণ্য।
সরকারি খরচ কমানো ও অতিরিক্ত কাজ আদায় করে নেওয়ার প্রবণতা— মূলত এই দু’টি কারণে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। বেকারত্ব বৃদ্ধির কারণে চুক্তিভিত্তিক কর্মী স্বল্প বেতনে তাঁর প্রায় পাঁচ-ছয় গুণ বেশি বেতনভুক স্থায়ী কর্মীর জায়গায় কাজে ঢুকছেন। এবং তাঁকে দিয়ে যাবতীয় কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। দক্ষতা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কাজ না পাওয়ার কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অতিরিক্ত কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন তিনি। এমনও দেখা গিয়েছে যে, প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে দক্ষ ব্যক্তি প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রের বাইরে চুক্তিভিত্তিক কাজে যোগ দিচ্ছেন বাধ্য হয়ে। সমাজে এমন উচ্চশিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েদের সহজলভ্যতার কারণেই সংস্থাগুলি স্থায়ী নিয়োগ বন্ধ করে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগে মেতেছে। এমন নিয়োগ এক দিকে শ্রমিক শোষণ এবং অন্য দিকে শিক্ষিত বেকারদের প্রতি সরকারের উদাসীনতারই ইঙ্গিতবাহী।
অথচ দেখা গিয়েছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যে সব চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক বিভিন্ন সংস্থায় দশ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে কাজ করছেন, তাঁদের দক্ষতা স্থায়ী-কর্মচারীদের থেকে কোনও অংশে কম নয়। বরং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাঁদের কাজের উপর স্থায়ী-কর্মীদের চেয়ে বেশি নির্ভরশীল। তার পরও তাঁদের প্রতি কর্তৃপক্ষের নজর পূর্বে যা ছিল, আজও তেমনই রয়ে গিয়েছে। অথচ, গত এক দশকে কিছু মামলার রায়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের স্বীকৃতি ছিল ‘সমান কাজের জন্য সমান বেতন’। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে মান্যতা দিয়ে যদি সরকারি বা বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থায় চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করা যায়, তবে তা হবে প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু সে চিত্র মেলে কই?
চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের কিছু সুবিধা অবশ্যই দেওয়া উচিত। যেমন, প্রাত্যহিক কাজের নির্দিষ্ট সময়সীমার পরে অব্যাহতি, যত বছরের চুক্তি তার আগে তাঁকে কাজ থেকে সরানো যাবে না, সমতুল্য পদের জন্য স্থায়ী-কর্মীদের সমান বেতন আর তাঁর প্রাপ্য অন্যান্য সুবিধার সমষ্টিগত অর্থ (চুক্তিকালীন সময়ের জন্য) প্রদান ইত্যাদি। আর চুক্তিভিত্তিক কাজের শেষে কর্মীদের কাজের নিরিখে শংসাপত্র প্রদান অবশ্যই বাধ্যতামূলক হওয়া চাই, যাতে পরবর্তী কোনও সংস্থায় তাঁর নিয়োগকালে সেই শংসাপত্রের গুরুত্ব বিবেচিত হয়।
স্বরাজ সাহা, কলকাতা-১৫০
চুক্তির ফাঁদে
কিংশুক সরকার তাঁর প্রবন্ধে চুক্তি-কর্মীদের সমস্যার বেশ কিছু দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বেকার সমস্যা ক্রমবর্ধমান। তাই শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের কম পারিশ্রমিক দিয়ে চুক্তি-কর্মী হিসাবে কাজ করিয়ে নেওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে সর্বত্র। কর্মজগতের সর্বত্রই যে-হেতু এঁদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, তাই এঁদের সুরক্ষার ব্যাপারটি শ্রম বিধিতে অগ্রাধিকার পাওয়ার দরকার ছিল। এ ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব থাকলেও, তারা এ ব্যাপারে কোনও রকম ভূমিকা পালন করে না। চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের নিয়মিতকরণের প্রশ্নটিকে কোনও পক্ষই আমল দিচ্ছে না। বরং, নতুন শ্রম বিধিতে নির্দিষ্ট মেয়াদি কর্মসংস্থান বা ‘ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট’কে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ন্যূনতম মজুরির চেয়েও কম মজুরির ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে ‘ফ্লোর ওয়েজ’-এর মাধ্যমে। যখন কোনও বেকার ছেলে বা মেয়েকে নিয়োগ করা হয়, তখন চাকরি দেওয়ার জন্য তাঁদের থেকে কিছু আদায় করে নেওয়ার সুযোগ থাকে বলেই নতুন নিয়োগের ব্যাপারটা সংস্থাগুলির কাছে অধিকতর গুরুত্ব পায়। এর পর রয়েছে যখন তখন ছাঁটাই। শ্রম আদালতে গেলেও সেখানে সব সময় সুবিচার মেলে না। বিচারের বাণী এ সব ক্ষেত্রে নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
প্রবন্ধকার এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার দিক তুলে ধরেছেন। অধিকাংশ ঠিকাদার আইন মেনে লাইসেন্স নেন না। তাঁর অধীনে নিযুক্ত কর্মীদের নাম সে কারণে আইনসম্মত ভাবে নথিভুক্ত হয় না। ফলে ওই স্বীকৃতিহীন কর্মী ও শ্রমিকরা দুর্ঘটনা বিমা থেকে শুরু করে ন্যায্য মজুরি— কিছুই পান না। নতুন আইন আবার ঠিকাদারদের নথিভুক্তির শর্ত শিথিল করেছে। আগে যেখানে ২০ জন শ্রমিক সরবরাহ করলেই লাইসেন্স লাগত, এখন সেখানে ৫০ জন শ্রমিক সরবরাহ করলে তবে লাইসেন্স নিতে হবে। শুধু তা-ই নয়, আইনভঙ্গকারী ঠিকাদারদের শাস্তির যে ব্যবস্থাপনা শ্রম আইনে ছিল, নতুন শ্রম বিধি তাও কমিয়ে বস্তুত চুক্তি-কর্মীদের উপর সব রকম দমনের রাস্তাকে আরও প্রশস্ত করেছে। ফলে চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা যে তিমিরে রয়েছেন, শ্রম বিধি চালু হলে সেই তিমিরেই থেকে যাবেন।
গৌরীশঙ্কর দাস, সম্পাদক, অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ় ইউনিটি ফোরাম
অধিকারহীন
কিংশুক সরকারের প্রবন্ধ বিষয়ে এই পত্র। প্রবন্ধকারের বক্তব্যে কিছু ত্রুটি থেকে গিয়েছে বলে আমার অভিমত। তিনি লিখেছেন, “আমাদের দেশের বেশ কিছু শ্রম আইন তৈরি হয় পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে। তখন মালিক বা সংস্থাগুলি সরাসরি কর্মী নিয়োগ করত। কর্মচারী বলতে স্থায়ী কর্মচারী বোঝাত। ষাটের দশকের শেষের দিক থেকে ক্রমশ শ্রমিক আর মালিকের মাঝে ঠিকাদার এসে পড়ে। নব্বইয়ের দশকে ঠিকাদারদের প্রভাব বাড়ে, স্থায়ী-কর্মীর কাজের জন্য চুক্তি-কর্মী নিয়োগ শুরু হয়।”
বিষয়টি একটু বিশদে ব্যাখ্যা করা যাক। চুক্তি শ্রমিক ও ঠিকা শ্রমিক এক নয়। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে ঠিকা শ্রমিকদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাওয়ার পর, এটিকে আইনগত করার জন্য ১৯৭০ সালে একটি আইন তৈরি হয়। সেটি হল ‘কনট্র্যাক্ট লেবার (রেগুলেশন অ্যান্ড অ্যাবলিশন) অ্যাক্ট’। যদিও চারটি শ্রম কোডে এই আইনকে অকার্যকর করে দেওয়া হয়েছে। এ দিকে, চুক্তি শ্রমিক বিষয়টি ফিরে আসে ১৯৯০-৯১ সালে, নয়া উদারীকরণ নীতির যুগে। স্থায়ী, ক্যাজুয়াল, ঠিকা শ্রমিকের পর চুক্তি শ্রমিক হুহু করে বাড়তে থাকে সরকারি ও বেসরকারি, উভয় সংস্থাতেই। নির্দিষ্ট সময় অন্তর চুক্তি করা এবং কম মজুরিতে কাজ করানো— এটাই চুক্তি শ্রমিকদের বৈশিষ্ট্য। কাজ পছন্দ না হলে চুক্তি শেষ। কোনও আইনি সুবিধা নেই। কিন্তু পুরনো শ্রম আইনে এটি লিপিবদ্ধ ছিল না। নতুন শ্রম কোডে এই শ্রমিক-বিরোধী প্রথাকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস কোড, ২০২০-তে ‘ফিক্সড এমপ্লয়মেন্ট টার্ম’-এর শর্তাবলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে লেখা আছে, শ্রমিক মালিকের সঙ্গে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ করার লিখিত চুক্তি করবেন। এই সময় স্থায়ী শ্রমিকদের মতো সুবিধা পাবেন ও কাজের এক বছর পর থেকেই গ্র্যাচুইটি পাবেন। এখানে গ্র্যাচুইটি আইনও সংশোধন হল। কারণ আগের গ্র্যাচুইটি আইনে টানা পাঁচ বছর কাজ করলে তবে কেউ গ্র্যাচুইটি পাওয়ার অধিকারী হতেন। সমস্যা হল, কর্তৃপক্ষের পছন্দ না হলে চুক্তি পুনর্নবীকরণ হত না। কাজ হারাতে হত। কিন্তু স্থায়ী শ্রমিকের ক্ষেত্রে তা করা যাবে না।
এই শ্রম কোডে চুক্তি শ্রমিকদের অধিকারহীনতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে তাকে আইনি করে দেওয়া হয়েছে। এতে চুক্তি শ্রমিকরা এত দিন আইনের দরজায় যে কড়া নাড়তে পারতেন, সেই অধিকারটুকুও গেল। প্রবন্ধকার এই দিকটা তুলে ধরেননি।
কুশল দেব নাথ, গার্ডেনরিচ, কলকাতা
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)