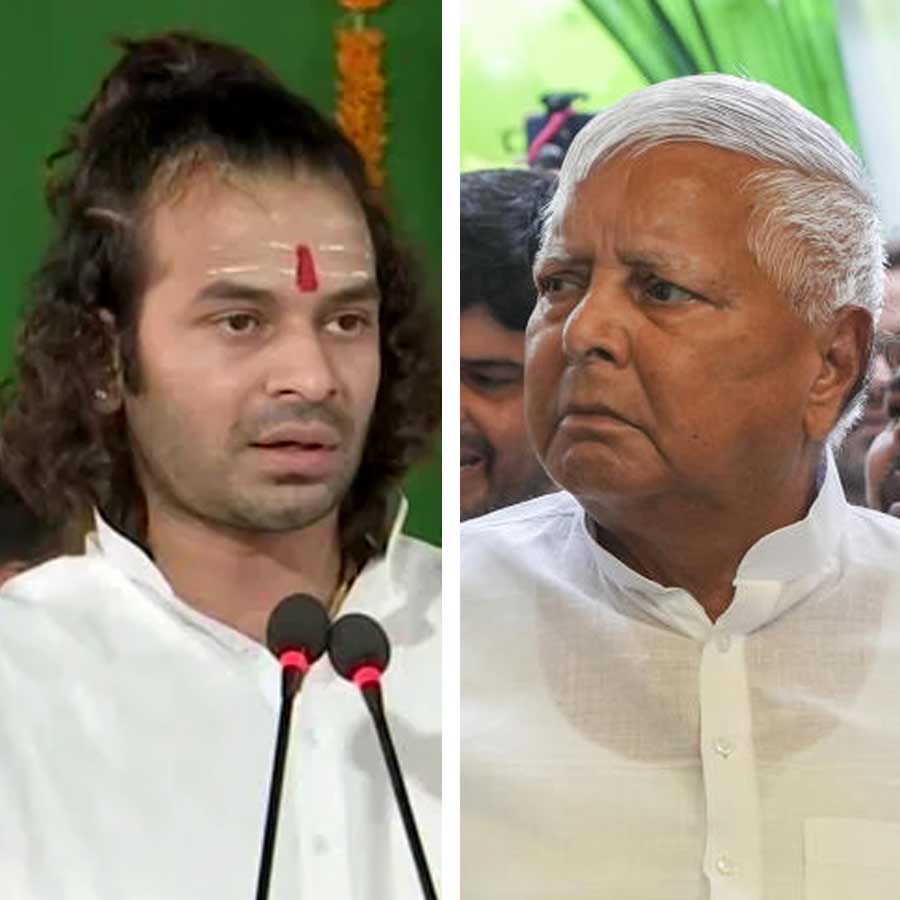‘কলকাতার কুম্ভমেলায়’ (রবিবাসরীয়, ২৬-১) শীর্ষক গৌতম চক্রবর্তীর প্রবন্ধে কলকাতার আন্তর্জাতিক বইমেলাকে কুম্ভমেলার সঙ্গে তুলনা করে সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে। প্রয়াগের মহাকুম্ভকে ‘পুণ্য লাভের মেলা’ আর কলকাতার বইমেলাকে ‘জ্ঞান লাভের মেলা’ আখ্যা যথার্থ বলে মনে হয়েছে। প্রায় দু’সপ্তাহ ধরে চলা কলকাতা বইমেলাও মহাকুম্ভের ন্যায় আন্তর্জাতিক মেলা হিসাবে স্বীকৃত। মহাকুম্ভের মতো এই মহামিলনের মেলায় বইয়ের সাগরে ডুব দেওয়া কয়েক লক্ষ মানুষের জ্ঞান অর্জনের তৃষ্ণা পুণ্য লাভের প্রত্যাশায় সাধু-সন্ন্যাসীদের ধ্যানমগ্নতার অনুরূপ। তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করে থাকা লাখ লাখ বইপোকা মানুষ কলকাতার বইমেলার শুরুর দিনের দিকে তাকিয়ে থাকেন, যেমনটি কুম্ভমেলার জন্য সাধু-সন্ন্যাসীরা বছরের পর বছর অধীর অপেক্ষা করে থাকেন। প্রবন্ধকার প্রয়াগ সঙ্গমের নৌকার সঙ্গে কলকাতার ‘বইমেলা’ সাঁটা বাস, স্নানের ঘাটের সঙ্গে বইমেলার নম্বরওয়ালা প্রবেশদ্বারের মধ্যে যে সমতার কথা বলেছেন, তা-ও যথার্থ।
প্রয়াগের নিকটস্থ হাজার হাজার সাধু-সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসার জন্য তাঁদের তাঁবুতে উপচে পড়া মানুষের ভিড় এই বিশ্বাস বহন করে যে, এই মহাপ্রাণরা সঠিক দিশা দেখাতে পারবেন। আর আমাদের বইমেলায় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশকদের গড়ে তোলা অজস্র অস্থায়ী স্টলের মধ্যে থাকে সাহিত্য সাধকদের সৃষ্ট অমূল্য সম্পদ, যার স্পর্শে পাঠককুল পরিতৃপ্তি লাভ করেন। তবে প্রয়াগের কুম্ভমেলায় কোটি কোটি মানুষের স্নানে কার কতটা পুণ্য লাভ হয়েছে, তা নিশ্চিত ভাবে জানা না গেলেও কলকাতার বইমেলায় লক্ষ পাঠক যখন ‘বইস্নাত’ হচ্ছেন, তখন তাঁদের জ্ঞানের ভান্ডারে যে অনেক পুঁজিই জমা হবে, সেটা নিশ্চিত ভাবে বলা যেতে পারে। বইয়ের সংস্পর্শে মানবজীবনের সামগ্রিকতায় অনিবার্য উন্নতি ঘটে। যার কারণে অগণিত বইপ্রেমীকে বইমেলার প্রাঙ্গণে নিয়মিত হাজির হতে দেখা যায়।
স্বরাজ সাহা, কলকাতা-১৫০
পড়ার অভাব
“লিটল ম্যাগাজ়িন পড়েন? ঘেঁটে দেখেছেন কোনও দিন?”— এই প্রশ্ন যদি জিজ্ঞাসা করা হয় মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালিকে, তাঁরা সবাই খুব আত্মবিশ্বাসী উত্তর দিতে পারবেন বলে মনে হয় না। অনেকে হয়তো সন্দীপ দত্তের নাম শোনেননি, লিটল ম্যাগাজ়িন ছিল যাঁর শয়নে স্বপনে জাগরণে। লিটল ম্যাগাজ়িনের প্রকৃত সংগ্রাহক, সংরক্ষক ছিলেন তিনি। ‘এখন বাংলা সাহিত্যে ভাল কিছুই লেখা হচ্ছে না’— এটা চলতি কথা। এ সব ছিল থাকবে। কিন্তু কে ভুলতে পারে আনন্দবাজার পত্রিকা-র প্রবাদপ্রতিম সাংবাদিক-সম্পাদক সন্তোষকুমার ঘোষকে! শুনেছি, সেই সময় প্রকাশিত প্রায় প্রতিটি লিটল ম্যাগাজ়িন তিনি খুঁটিয়ে পড়তেন, ভাল লেখা খুঁজে বার করতেন, তার লেখককে দিয়ে বড় পত্রিকায় লেখাতেন। এ যেন এখন স্বপ্ন। লিটল ম্যাগাজ়িনে কিন্তু আজও বহু ভাল কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, মন দিয়ে পড়েন ক’জন! সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, কোনও পত্রিকায় যে কবি বা লেখকের লেখা বেরোল, তিনি সেই পত্রিকাতেই প্রকাশিত অন্য লেখক বা কবির লেখা নিয়ম করে পড়েন না। নিজের লেখা প্রকাশিত হল কি না, সেটাই তাঁর কাছে যথেষ্ট।
লিটল ম্যাগাজ়িনের আয়ু কম। আগে তবু সরকারি ভাবে নির্দিষ্ট নীতিতে লিটল ম্যাগাজ়িনে বিজ্ঞাপন আসত। এখন সেই বন্দোবস্ত উঠে গেছে। যে যার নিজের প্রভাব খাটিয়ে বিজ্ঞাপন পেয়ে যায়। বিজ্ঞাপনের অভাবে পকেট থেকে টাকা খরচ করে পত্রিকা চালাতে হয়েছে— এমন তো কতই হয়েছে। বহু বিখ্যাত লিটল ম্যাগাজ়িন বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আবার নতুন লিটল ম্যাগাজ়িনের জন্মও হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার তথাকথিত ‘সেলেব্রিটি লেখক’দের লেখা প্রকাশ করে নিজেদের পত্রিকা বিক্রির হিসাবটা বাড়িয়ে নিতে চায়।
নানা পত্রিকার পাতায় এখনও চমকে দেয় খুব ভাল মানের প্রবন্ধ। বড় পত্রিকায় ফিচারের সংখ্যাই বেশি বটে, তবে ভাল প্রবন্ধ-নিবন্ধও লেখেন অনেকেই। তার পরেও মনে হয়, এক জন শিবনারায়ণ রায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, সন্তোষকুমার ঘোষের আর কি দেখা মিলবে? মধ্যবিত্ত বাঙালি এখন সিরিয়ালে দেখে বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ-এর কথা জানতে পারে। নতুন প্রজন্ম কেরিয়ারসর্বস্ব। তা হলে বাংলা সাহিত্য, লিটল ম্যাগাজ়িন, এ সব নিয়ে আলোচনা কি বাতুলতা? যাঁরা সত্যিকারের পড়াশোনা করেন, তাঁরা যেন কোন এক জাদুতে উধাও হয়ে গিয়েছেন। কালেভদ্রে কিছু প্রকৃত পড়ুয়ার দেখা মেলে, তা বাদে বেশির ভাগই সাহিত্যচর্চার নামে আমোদপ্রেমী। কারও ভাবার সময় নেই, ধৈর্য নেই।
সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে বাঙালির এত গর্ব, তার কোনও প্রতিফলন মেলে না ব্যক্তিগত জীবনচর্যায়। অধিকাংশ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি পরিবারের ছেলেমেয়েরা পড়ে ইংরেজি মাধ্যমে। তাদের কথ্যভাষা পাঁচমিশালি। কিছুটা হিন্দি, বেশির ভাগটাই ইংরেজি, অল্প বাংলা। নব্বইয়ের দশকের পরবর্তী সময়ে আমাদের সমাজের এই আমূল পরিবর্তন রীতিমতো গবেষণার বিষয়বস্তু। যাঁরা ষাট-সত্তর এমনকি আশির দশকের শুরুতেও জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা তবু কিছুটা নির্ভেজাল বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গ পেয়েছেন। তার পরে সবই যেন ভাসা-ভাসা, উপরচালাকিতে ভরা। বাংলা সিনেমাও আর বাংলা সাহিত্যনির্ভর নয়, তা যেন শুধু কলকাতার শহরের। তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের সিনেমা নয়। সেই সিনেমা ডায়মন্ড হারবার, ক্যানিং, পুরুলিয়াকে স্পর্শ করে না। যে গান তৈরি হয়, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তা সাধারণ মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে যায়।
হয়তো এই জীবনে এমনও শুনতে হবে— ‘বাংলা সাহিত্যের পাশে দাঁড়ান’। ভাল প্রবন্ধ, ভাল কবিতা, ভাল ছোটগল্পের জন্য আমরা অনেকেই কিন্তু চাতকপাখির মতো অপেক্ষায় আছি। টেলিভিশনের মোহ ছেড়ে আজকের বাঙালি কি পাড়ার জীর্ণ অবসন্ন লাইব্রেরিগুলোতে ভাল বইয়ের সন্ধানে ঢুকবে আর? একুশ শতকে তা যেন স্বপ্নসম, দুরাশা। শুধু আছে বইমেলা, বাঙালির বারো মাসের তেরো পার্বণের একটি হয়ে। সদ্যসমাপ্ত কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলায় ২৭ লক্ষ মানুষ ২৫ কোটি টাকার বই কিনলেন, অথচ এই কলকাতাতেই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালির বাংলায় কথা বলতে অনীহা। দোকানের সাইনবোর্ডও ইংরেজিতে। এক জন মানুষ এই নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন, তাঁর কথা এই সময় বড় মনে পড়ে— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।
দেবাশিস চক্রবর্তী, কলকাতা-৮৪
অজানা আজও
কলকাতার পুস্তক মেলার অনেক আগে এ রাজ্যের প্রথম বইমেলা অনুষ্ঠিত হয় মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরের রঘুনাথগঞ্জ শহরে, ১৯৬৩ সাল নাগাদ, যা ‘জঙ্গিপুর গ্রন্থমেলা’ নামে পরিচিত। এই গ্রন্থমেলা আজও সরকারি স্বীকৃতি পায়নি। অথচ, কে না জড়িয়ে ছিলেন এই মেলায়? তার প্রাণপুরুষ ছিলেন প্রখ্যাত নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়, যিনি ওই সময় জঙ্গিপুর কলেজে অধ্যাপনা করতেন, ছিলেন মেলা কমিটির সম্পাদক। সভাপতি ছিলেন মহকুমা শাসক অমলকৃষ্ণ গুপ্ত। এই মেলায় এসেছেন সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক রেজাউল করিম, নারায়ণ চৌধুরী, কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় এবং বিপ্লবী সাহিত্যিক নলিনীকান্ত সরকার-সহ বহু বিশিষ্টজন। সেই সময় জঙ্গিপুর গ্রন্থমেলা স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এর পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কুণাল কান্তি দে-র সম্পাদনায় ভারতের প্রথম বইমেলার ইতিবৃত্ত: স্মরণ ও মননে জঙ্গিপুর গ্রন্থমেলা-১৯৬৩ নামে গ্রন্থটি ২০২৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, যা এখনও অনেকেরই অজানা রয়ে গিয়েছে।
শান্তনু সিংহ রায়, মিঠিপুর, মুর্শিদাবাদ
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)