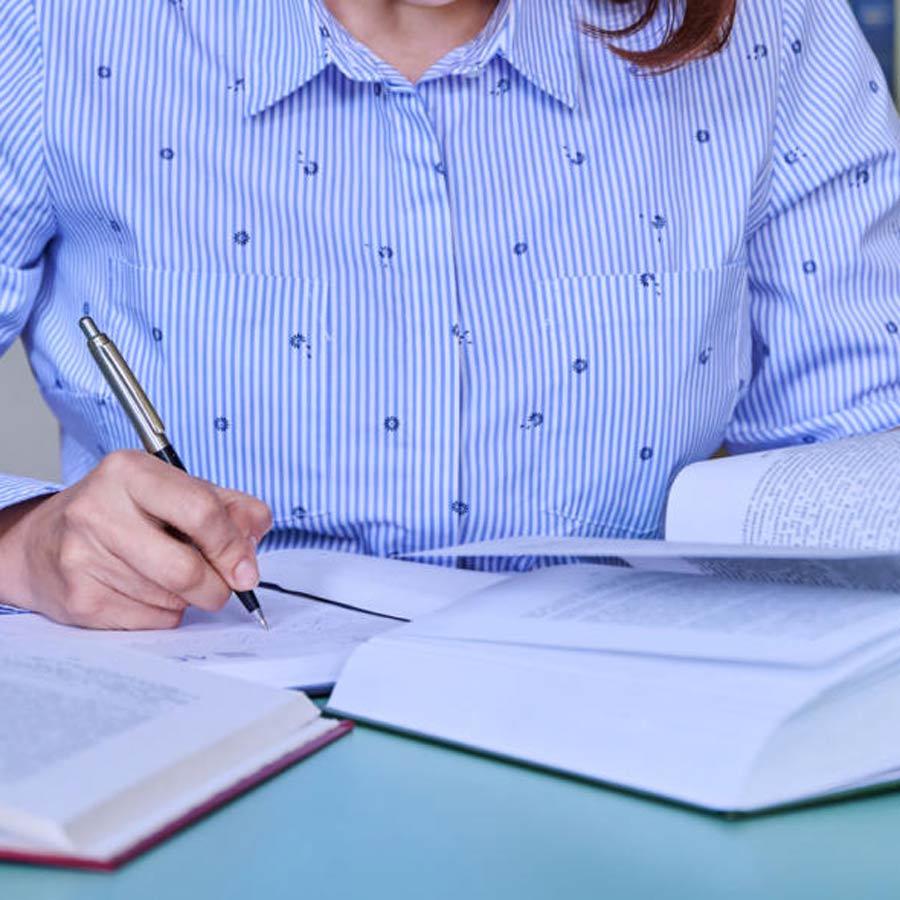অনুষ্টুপ বিশ্বাসের ‘সব হারিয়ে জিতে নেওয়া জয়’ (৮-১০) শীর্ষক প্রবন্ধ প্রসঙ্গে কিছু সংযোজন। সময়ের সঙ্গে পাল্টেছে পরীক্ষা পদ্ধতি। পরিবর্তন হয়েছে মূল্যায়নের রীতিও। ত্রিশ বছর আগে সরকারি স্কুলে বর্ণনাধর্মী প্রশ্ন আর খুঁতখুঁতে শিক্ষকদের কড়া মূল্যায়নের ফাঁদে পড়ে কেঁদে কুল পেত না ছাত্রছাত্রীরা। নিয়মিত পড়া ধরা, না পারলে কঞ্চি-শাসন, বাড়াবাড়িতে অভিভাবকদের ডাকা এবং বাড়িতে শেষ পর্যন্ত মার খেয়ে, নাজেহাল হয়ে স্কুলে যাওয়ার পথটাই ভুলে যেত তারা।
সেই ড্রপ আউট থামাতেই এল সর্বশিক্ষা মিশন। চোদ্দো বছর পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষা হল বাধ্যতামূলক। এল বিনা পয়সার বই, খাতা, ব্যাগ, জুতো, মিড-ডে মিল। উঠে গেল পাশ-ফেল। বাদ পড়ল কঞ্চি-শাসন। পিঠ বাঁচা আর পেট ভরার আহ্লাদে সংখ্যাগুরু শিক্ষার্থী ভুলেই গেল বিদ্যালয়ে আসার আসল উদ্দেশ্যটি। ফলে তারা শিখল না কিছুই। প্রকৃত শিক্ষা না হওয়ায় নবম-দশম স্তরে তারা হাবুডুবু খেল। অদ্ভুত ব্যাপার, তাতেও মাধ্যমিকে পাশের হার বাড়ল লাফিয়ে লাফিয়ে। ঢালাও নম্বর দেওয়ার অনুপ্রেরণা পাওয়ায় স্কুলের টেস্টে নাস্তানাবুদ শিক্ষার্থীও মাধ্যমিক বোর্ডের পরীক্ষায় পাশ করে গেল খুব সহজেই। পৌঁছে গেল একাদশ-দ্বাদশ পর্যায়ে। সেখানে আরও মজা। চালু হয়েছে সিমেস্টার পদ্ধতি। প্রথম আর তৃতীয় স্তরে এমসিকিউ উপায়ে মূল্যায়ন হচ্ছে। গোলাকার শূন্যস্থান ভরাট করলেই নম্বর। এক লাইনও লিখতে হবে না। উত্তর জানার দরকার কী! হল ম্যানেজ তো আছেই। তাই মূল্যায়নে দেখা যাচ্ছে মুড়ি-মিছরির এক দর।
কিন্তু এত সহজ, সুবিধাজনক, চাপমুক্ত ব্যবস্থাতেও লাভের খাতা পূর্ণ হচ্ছে কি? প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায়, যার মাধ্যমে পেশাপ্রবেশের সুযোগ থাকে, সেখানে কোনও ফাঁকিবাজি চলে না। ক্রমশ কঠিনতর প্রশ্নের পরীক্ষায় সময় থাকে মাপা ও অতিসংক্ষিপ্ত। কঠোর ও নিরন্তর অনুশীলন করে, তবেই এক জন মেধাবী পড়ুয়া সাফল্য করায়ত্ত করতে পারে ( দুর্নীতি না হলে)। তাই তখন গতানুগতিক, সহজে পাশ করে বড় হওয়া ছাত্রছাত্রীরা চোখে অন্ধকার দেখে।
বর্তমানে দুনিয়ার জ্ঞানভান্ডার চলে এসেছে হাতের মুঠোয়। তাই জ্ঞানমূলক প্রশ্নের যুগ শেষ। এখন বোধমূলক প্রশ্নের যুগ। সে জন্য অনেক জায়গাতেই চালু হয়েছে খোলা-বই পরীক্ষা পদ্ধতি। এতে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার সময় পাঠ্যবই নিয়েই বসতে পারছে। এতে মুখস্থ করার চাপ কমছে; বাড়ছে বোধের চর্চা। এআই নিয়ন্ত্রিত সময়ে যার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।
পার্থ পাল, মৌবেশিয়া, হুগলি
জয়ের আলো
অনুষ্টুপ বিশ্বাস ‘সব হারিয়ে জিতে নেওয়ার জয়’ শীর্ষক প্রবন্ধে সর্বক্ষেত্রে পরীক্ষা দিয়ে জীবনকে টিকিয়ে রাখার জন্য যোগ্যতার প্রমাণের কথা বলেছেন। বিদ্যালয়ের অন্দরে এখন কেবল পরীক্ষা আর পরীক্ষা। সব পরীক্ষায় ভাল ফল করতে হবে, কারণ বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফল তার উপর নির্ভর করে। পরীক্ষা শেষে হলের বাইরে মা-বাবা দাঁড়িয়ে। সন্তান বেরোলেই জিজ্ঞাসা করবেন। অর্থাৎ, পরীক্ষার বাইরেও পরীক্ষা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর সবেতেই যোগ্যতা চাই। এর পর তো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরীক্ষা। লাখ লাখ ছেলেমেয়ে ছুটছে যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য। সাফল্যের হার অতি নগণ্য। হতাশা, অবসাদ, অসুস্থতা ক্রমশ গ্রাস করে তাদের।
যে যে-ভাবেই জীবনধারণ করুক না কেন, পরীক্ষা তাদের চলতেই থাকে। সংসার সামলানোর, ছেলেমেয়েদের প্রতিষ্ঠিত করার, বাবা-মা’কে ভাল রাখার পরীক্ষা তো আছেই, পাশাপাশি বয়স বাড়ার সঙ্গে শারীরিক নানা পরীক্ষা চলতেই থাকে। আর আত্মীয়স্বজন, পাড়াপড়শির চোখে সকলে তো জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পরীক্ষার্থী। অথচ, জীবনবোধের বিকাশ ঘটানোর জন্য না লাগে পরীক্ষা, না লাগে পয়সা। লাগে মানবতা, মানসিকতা ও রুচিশীলতা। যে ছেলেটি চায়ের দোকানে কাপ প্লেট ধোয়, সে প্রতি দিন তার দুপুরের খাবার থেকে বাসস্ট্যান্ডে বসে থাকা এক মানসিক ভারসাম্যহীনকে খেতে দেয়। এরা পরীক্ষার পর পরীক্ষায় পাশ না করলেও বা জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটাতে না পারলেও অনিবার্য জয়ের পথ দেখায়।
স্বরাজ সাহা, কলকাতা-১৫০
শব্দযুদ্ধ
‘হিমের রাতে ওই গগনের দীপগুলিরে’ দেখতে পাওয়া যায় না। কারণ, হেমন্তিকার আগেই দখল করে নেয় ধোঁয়া। যা আলোর উৎসব হওয়ার কথা ছিল, তাকে রীতিমতো বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রতি বছরের মতো এ বারও দেখা গেল— ঘড়িতে রাত বাড়তে থাকার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ দানবের তাণ্ডব। কোথায় সবুজবাজি? কোথায় পরিবেশ বান্ধব? আদালত নির্দেশ দেয়, পুলিশ সতর্কবার্তা দেয়, পরিবেশবিদেরা আবেদন জানান। আমরা কী করি? কৌতুকমিশ্রিত গর্বভরে বলি, “এই ক’টা দিন তো।”
মনোবিদরা হয়তো বলবেন— এ এক ধরনের ‘কমপেনসেটরি আচরণ’। বাস্তব জীবনে যাদের প্রভাব কম, তারা আওয়াজে নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চায়। যত জোরে শব্দ, তত বড় আত্ম অহঙ্কার, একই সঙ্গে তত দুর্বল আত্মবিশ্বাস। ফ্রয়েড থাকলে হয়তো লিখতেন— ‘শব্দ ও মূর্খতা’। কিন্তু এই শ্লেষের আড়ালেও থেকে যায় মূল প্রশ্নটি— এই নিষিদ্ধ বোমাগুলো বিক্রি হচ্ছে কোথা থেকে? রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ প্রতি বছর বলে শুধুই ‘সবুজ’ বা পরিবেশবান্ধব আতশবাজি বিক্রি হবে। তবু বাজারে খোলামেলা ভাবে বিক্রি হচ্ছে সেই একই ‘চকলেট বোমা’, ‘লাল বোমা’, ‘রকেট বোমা’।
মনে হয় নিষেধাজ্ঞার কাগজটাই এখন বোমা মুড়িয়ে দেওয়ার কাজে লাগে। ব্যবসায়ীদের যুক্তি সব সময়ের মতোই সরল— ‘মানুষ যা চায়, তাই বিক্রি করি’। অর্থাৎ, নীতির অভাবকে বাজারের চাহিদা ঢেকে দেয়। আর প্রশাসন প্রতি বছর কিছু প্রেস মিটিং করে, কয়েকটি প্রতীকী অভিযান চালায়, দু’চার জন বিক্রেতাকে ধরে ছবি তোলে— সংবাদ শিরোনাম তৈরি হয়, কিন্তু নীরবতা ফেরে না। মজার ব্যাপার হল, এই একই সমাজ শান্তির কবিতা লেখে, রবীন্দ্রনাথের গান গায়, মা কালীকে পূজা করে ‘বিশ্বসংহার ও সমবিবর্তনের প্রতীক’ হিসেবে, অথচ এক রাতেই নিজেদের গলিগুলোকে বানিয়ে ফেলে মিনি যুদ্ধক্ষেত্র।
মনস্তত্ত্বের দিক থেকে দেখলে এটি আসলে এক সামষ্টিক বিকার— এক শব্দমুখী আত্মপ্রকাশ। অথচ, এর পিছনে লুকিয়ে আছে অস্থিরতা, দমন করা ক্রোধ, এবং এক অদ্ভুত সামাজিক রোগ— ‘শান্তি’কে সহ্য করতে না পারা। তাই এই সমস্যার সমাধান কেবল প্রশাসনিক নয়, মনস্তাত্ত্বিকও বটে। দরকার ‘সমষ্টিগত থেরাপি’। হয়তো দরকার ‘সাউন্ড ডিটক্স ক্যাম্প’। তত দিন পর্যন্ত প্রতি কালীপুজো আর দীপাবলির রাতে পশ্চিমবঙ্গের আকাশে চলবে এক মিনি যুদ্ধ। পাখিরা পালাবে, কুকুরেরা অসহায় হয়ে ছুটে বেড়াবে, বাচ্চারা কাঁদবে— আর আমরা, সভ্যতার দাবিদার নাগরিকেরা, গর্বভরে বলব— “এই নাও, আর একটা জোরদার বোমা।”
ঋকসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা-৭৮
আদান-প্রদান
‘ঐক্য-শিক্ষা’ (১১-১০) সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, কলকাতার বেশ কিছু স্কুল সচেতন ভাবে শ্রেণিকক্ষগুলিতে এক মিলনক্ষেত্র প্রস্তুত করতে উদ্যোগী হয়েছে। আলাদা কী ব্যবস্থা করা হল, বোধগম্য হল না। স্কুলগুলিতে বিভিন্ন ধর্মের, সম্প্রদায়ের, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে ছাত্রছাত্রীরা আসে, পাঠ গ্রহণ করে। এই ব্যবস্থা চলে আসছে খুব স্বাভাবিক ভাবে। বিদ্যালয়-শিক্ষার অনেক সমস্যা আছে এবং কাঠামোটির ক্রমশ অবনতি হয়তো ঘটছে। কিন্তু পারস্পরিক আদান-প্রদানে তেমন কোনও ইতর বিশেষ এখনও চোখে পড়েনি।
সৌমেন রায়, মেউদিপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)