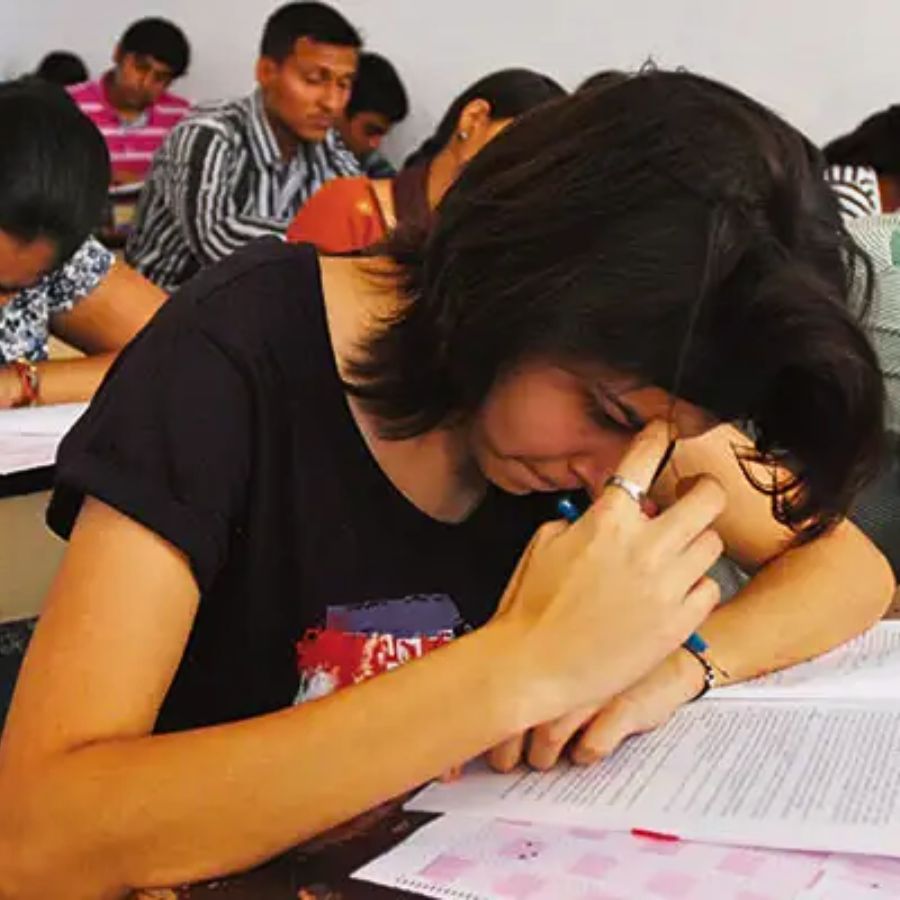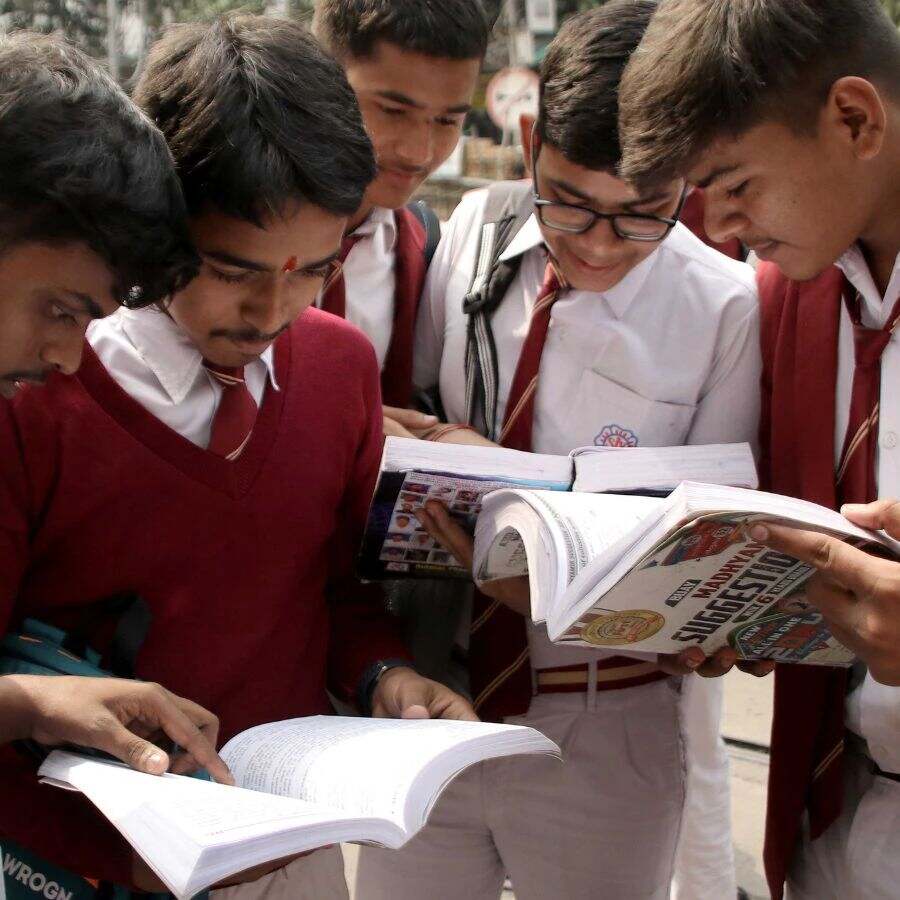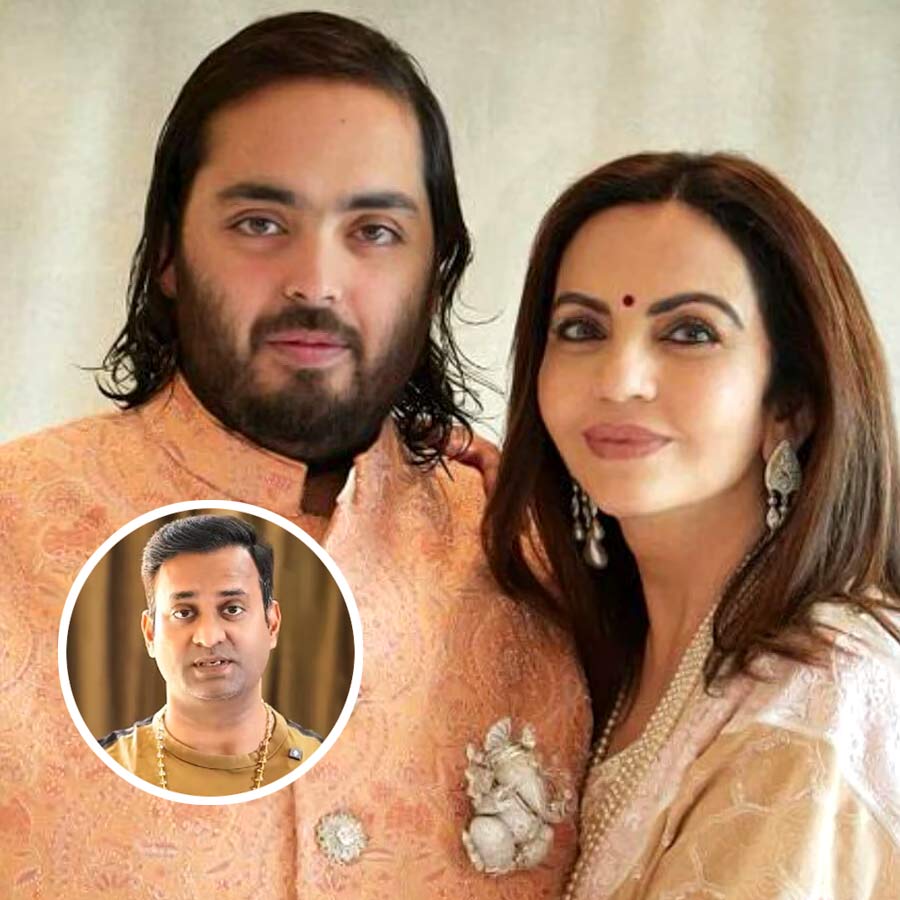রাজ্যের সর্বত্র ঘটে চলা অবৈধ কাজকর্মের প্রতি প্রশাসকদের সমর্থন রাজ্যটিকে কতটা বিপন্ন অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তার এক অতি সত্যনিষ্ঠ বর্ণনা দিচ্ছে ‘বৈধ’ (২১-১) শিরোনামে সম্পাদকীয়টি। কিন্তু শাসকের এতে কোনও হেলদোল হবে বলে মনে হয় না। আক্ষরিক অর্থেই পশ্চিমবঙ্গ আজ এক নৈরাজ্যের রাজত্ব। এখানে সাধারণ নাগরিক উৎকণ্ঠায় দিনযাপন করেন। প্রশাসন, আইনকানুন সাধারণের উপকারে লাগে না। শাসক দল ক্ষমতা ধরে রাখতে ন্যায়-অন্যায় বোধকে শিকেয় তুলে রাখাকেই যুক্তিযুক্ত মনে করে। যদি শাসক কোনও বেআইনি কার্যকলাপে বহু মানুষকে জড়িত থাকতে দেখেন, তবে কিছু কুযুক্তির অবতারণা করে সেই সমস্ত অবৈধ ক্রিয়াকলাপকে বৈধতা দান করেন। এতে এক দিকে আয়ের রাস্তা সুগম হয়, অপর দিকে যারা এই বেআইনি কাজ করেও ছাড় পেয়ে গেল, তাদের স্থায়ী আনুগত্য নিশ্চিত হয়। এই ভাবেই অবৈধ নির্মাণ, অবৈধ টোটোর রমরমা চলে রাজ্য জুড়ে। পশ্চিমবঙ্গের পরিবহণ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বর্তমানে টোটো এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। রাজ্যের প্রতি জেলায় ও শহরতলিতে স্বল্প দূরত্বে যাতায়াতের প্রয়োজনে টোটো এখন অপরিহার্য। তীব্র বেকারত্বে জর্জরিত রাজ্যে নিরুপায় বহু যুবকের রোজগারের পথ এখন টোটো চালানো। শহরতলিতে অটো-টোটোর দাপটে বহু রুটে বাসের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। প্রয়োজনের অধিক টোটো রাস্তায় নামার ফলে একাধিক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে, যা আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ। সংবাদপত্রের পাতায় প্রায়শই টোটো-সংক্রান্ত নানাবিধ অশান্তি-সংঘর্ষের খবর চোখে পড়ে। প্রত্যেক টোটো রুটে শাসক দলের ট্রেড ইউনিয়ন থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝেই বিভিন্ন রুটের টোটোচালকদের মধ্যে ব্যবসা স্বার্থ নিয়ে ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট মারামারি পথ অবরোধ ঘটে।
প্রসঙ্গত, পুরসভা বা পঞ্চায়েতের কোনও এলাকায় নির্দিষ্ট রুটে ক’টা টোটো চালানো যাবে, তার কোনও নিয়ন্ত্রণ প্রশাসনের হাতে নেই। ফলে, এই সুযোগে রাজনৈতিক দাদাদের মদতে যার যেমন খুশি রোজগারের জন্য টোটো নিয়ে নেমে পড়ছে। বহু ক্ষেত্রে অপরিসর রাস্তায় বেপরোয়া টোটোচালকদের জন্য সাধারণ মানুষকে দুর্ঘটনায় পড়তে হচ্ছে। কিছু বলতে গেলে মিলছে অভদ্র ব্যবহার। এর উপর কখনও কখনও এলাকার কর্তৃত্ব নিয়ে দু’দলের টোটোচালকদের বিবাদে সাধারণ যাত্রীদের হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে। মানুষের দুর্ভোগ বা যন্ত্রণায় এদের কিছু যায় আসে না। টোটোর আগ্রাসন বন্ধ করতে অবিলম্বে পরিবহণ দফতর, প্রশাসন যদি কঠোর আইন প্রণয়ন না করে, তবে অদূর ভবিষ্যতে আরও অনেক সামাজিক সমস্যায় প্রশাসনের মাথাব্যথা বাড়বে।
দেবকী রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া, হুগলি
শুধুই মহিমা
সুজিষ্ণু মাহাতোর লেখা ‘মনমোহন, শাহরুখ: এক যোগে’ (১৬-১) প্রবন্ধ সম্পর্কে কিছু কথা। ১৯৯১ সালের ২৪ জুলাই, যখন মনমোহন সিংহ নরসিংহ রাও সরকারের নতুন অর্থমন্ত্রী হিসাবে সেই বহুচর্চিত কথা— ‘সারা বিশ্ব উচ্চকিত এবং স্পষ্ট ভাবে শুনুক...’ বলছেন, তত দিনে ফৌজি এবং সার্কাস-এর কল্যাণে শাহরুখ খান ভারতীয় টেলিভিশন দর্শকদের কাছে একটি অত্যন্ত পরিচিত নাম। তবে জনমানসে আলোড়ন তোলে ডর এবং বাজিগর। তার পরেই আসে ইয়েস বস-এর (১৯৯৭) সেই লাইন ‘ডোন্ট ওয়রি, গেট রিচ’, যেটা দিয়ে প্রবন্ধকার মেলাতে চেয়েছেন শাহরুখ ও মনমোহনের উদারনীতির ধনতন্ত্রবাদী দর্শনকে।
একটু গোড়ার কথায় আসি। ১৯৯১ সালের অর্থনীতির যে উদারীকরণ তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংহ করেছিলেন, তার কৃতিত্ব ও প্রশংসা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও-এর গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রাপ্য, এটি সর্বজনবিদিত। কিন্তু বাদ সাধে সুজিষ্ণুবাবুর প্রবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রথম পঙ্ক্তি ‘কার্যত দেউলিয়া হতে চলা অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী’। প্রশ্ন জাগে, তা হলে তার আগের বছরগুলি (মানে সত্তর, আশির দশক) ধরে সেই অর্থনীতিকে দেউলিয়া করল কে? কারা ছিলেন সেই সময়ের রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর-সহ অন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক, যাঁদের ভুল সিদ্ধান্তে দেশের অর্থনীতি প্রায় দেউলিয়া হতে বসেছিল? নথি বলে, ১৯৮২-৮৫ সালে রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর ছিলেন মনমোহন সিংহ-ই। তারও আগে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের ‘চিফ ইকনমিক অ্যাডভাইজ়র’ ছিলেন তিনিই। ১৯৭৬ থেকে ৮০ সাল অর্থ মন্ত্রকের সচিব ও ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৭ সালে প্ল্যানিং কমিশন-এর ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন মনমোহন সিংহ।
১৯৯১-৯৭ সালে মনমোহন সিংহের সাফল্য যদি শাহরুখ খানের সঙ্গে ভাগ করে দেওয়ার অবকাশ থাকে, তা হলে ১৯৭২ থেকে ১৯৯১ এই বিশ বছরে তাঁর ব্যর্থতার দায়ভার, প্রবন্ধকার কোন নায়কের সঙ্গে ভাগ করবেন? গত কয়েক বছরে ভারতে রাষ্ট্র কী ভাবে বলিউডের মাধ্যমে গণরুচি নির্মাণ করছে তা দেখতে পান প্রবন্ধকার। তিনি কি জানেন না, নেহরু প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে শুধু লেখার জন্য মাজরুহ সুলতানপুরির মতো কিংবদন্তি সংখ্যালঘু লেখককে জেলে যেতে হয়? আঁধী, কিসসা কুরসি কা-র মতো রাষ্ট্রের অপছন্দের সিনেমা বন্ধ করে দেওয়া হয় এক নির্দেশেই। শাহরুখ খান থেকে জন আব্রাহাম সারা জীবন আপন ধর্মীয় পরিচয়ে সিনেমা করলেও পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরের দশকে প্রবাদপ্রতিম মহম্মদ ইউসুফ খানকে দিলীপ কুমার নাম নিয়ে সিনেমা করতে হত।
সত্যিই, ভারতের মানুষকে প্রভাবিত করার সব থেকে বড় মাধ্যম আজও সিনেমা। স্বাধীনতার পর থেকে একটা দীর্ঘ সময় সেটা দিয়ে সমাজকে ‘স্লো পয়জ়নিং’ করা হয়েছে। সেই যুগ থেকেই সিনেমার নায়ককে দাগী অপরাধী, চোর-ডাকাত, স্মাগলার, সমাজবিরোধী, এমনকি মহান সন্ত্রাসবাদী হিসাবেই বেশির ভাগ সময় মহিমান্বিত করা হয়েছে। পরিশ্রম করে সামান্য থেকে অসামান্য হওয়া, সফল হওয়া, শিক্ষিত হওয়া নায়ক-নায়িকাকে কেন্দ্র করে সিনেমার কাহিনি সে যুগের ক’টা আছে, যা আজ টুয়েলভথ ফেল, দঙ্গল, মেরি কম-এ দেখা যায়। তবে বাম জমানার ৩৪ বছরে বাংলা সিনেমাকে এ রাজ্যের সরকার কী ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিল, সেই অধ্যায় এ যাত্রা তুলে রাখাই রইল।
সৌমাভ ভট্ট, কৃষ্ণনগর, নদিয়া
নেতাজির স্মৃতি
নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর কারাবাসের সূচনা হয়েছিল সেই ১৯২১ সাল থেকে। পরের বছর মুক্তিলাভ করে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি-র সম্পাদক হন। এর পর দেশ স্বাধীনের লড়াই আর কারাবাস যেন সুভাষচন্দ্রের জীবনে নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার নোয়াপাড়া থানা সে রকমই একটি ঐতিহাসিক স্মৃতির সাক্ষী হয়ে আছে ১৯৩১ সাল থেকে। ওই দিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ নেতাজি যাচ্ছিলেন অবিভক্ত চব্বিশ পরগনা জেলার জগদ্দলের গোলঘর এলাকায় বঙ্গীয় পাটকল শ্রমিক সভায় ভাষণ দিতে। পথে তাঁকে শ্যামনগর চৌরঙ্গী কালীবাড়ির কাছে ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যায় নিকটেই নোয়াপাড়া থানায়। সেখানে তাঁকে একটি কক্ষে আটক করে রাখা হয়েছিল কিছু সময়। শোনা যায়, ওই সময়ে তিনি কিছু খেতে অস্বীকার করায় সুশীলকুমার সুর নামে এক বালক তাঁকে একটি কাপে চা পরিবেশন করেন। তিনি তা সাদরে গ্রহণ করেন। আজ সেই ছোট্ট কক্ষে নেতাজির একটি ছবির সামনে দ্রষ্টব্য হিসেবে ওই কাপ ও ডিশটি রাখা আছে সযত্নে।
এই বছর থেকে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু নামাঙ্কিত একটি স্মৃতি গ্রন্থাগারের সূচনা করা হয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ নেতাজি এবং দেশপ্রেমের ইতিহাস সম্পর্কে আরও জানতে পারেন।
বাবুলাল দাস, মাঝেরপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)