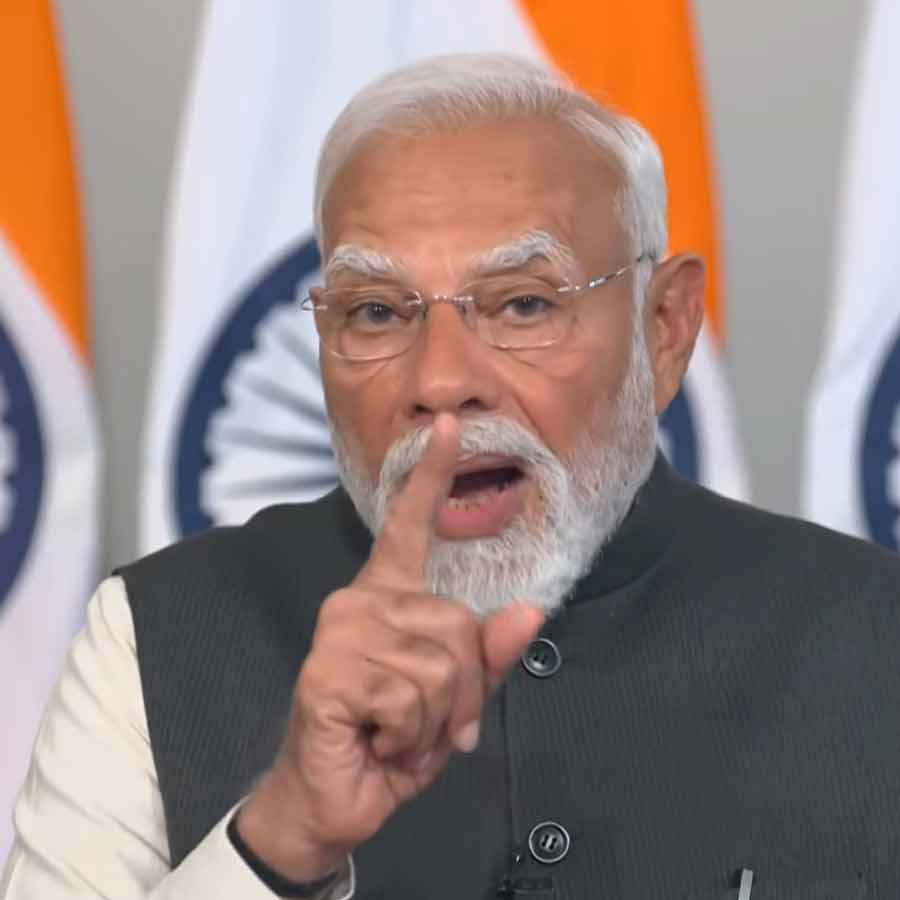বারান্দার ঘুলঘুলিগুলো সব শালিক পাখির বাসায় ভরে গেছে। বড় শালিক আর ছানা শালিকে খোপগুলো সব ভর্তি। মাঝে মাঝে পায়রা আর ঘুঘুদের আসতে দেখা যায়, তবে তারা কেউ থাকে না। এ দিক ও দিক খাবার খুঁজে ফিরে যায়। এ সব দেখতে ভালই লাগে গোপাল চৌধুরীর। ইস্কুলে ছেলেপুলেদের অভাব খানিকটা যেন ওরাই পূরণ করে দেয়। সারাক্ষণ ছটফটানি, উড়ে উড়ে যাওয়া আসা। ওদের চেঁচামেচি সমানে চলতেই থাকে। আর ওটুকুর মধ্যেই যেন প্রাণ পায় এত বড় স্কুলবাড়িটা। চোখ ভরে দেখেন গোপালবাবু। অবশ্য দেখা ছাড়া আর করার আছেটাই বা কী! মন দিয়ে চার পাশ দেখতে দেখতে অনেকটা সময় কেটে যায়।
স্কুল বসার সময়টা শুরু হয়ে গেলে রোজ ঘুরে ঘুরে একতলা-দোতলার সব ক’টা ঘরে এক বার করে পায়চারি করে আসেন গোপালবাবু। বহু দিনের অভ্যাস। অবশ্য এই নিয়ে কেদার আর মহীতোষ দু’জনেই হাসাহাসি করে খুব। বলে, “ওই গোপাল বেঞ্চি গুনতে চলল।”
এসব কথায় ভ্রুক্ষেপ করেন না গোপাল চৌধুরী। রোজ এক বার স্কুলবাড়ির সবটা টহল না দিলে মনের ভিতরে খচখচ করে সারাক্ষণ। মনে হয় যেন প্রতিটি অন্ধকার ঘর, মলিন ব্ল্যাকবোর্ড, প্লাস্টার খসে পড়া দেওয়াল নিঃশব্দে ডাকছে। ওরাও এত বছরের অভ্যেস কাটিয়ে উঠতে পারছে না। কীভাবে যেন এই বঁাধন কাটিয়ে উঠতে পারেন না গোপাল চৌধুরী। বাঁধন কাটাতে যে চান তাও অবশ্য নয়। স্কুলের সারি সারি ক্লাসঘরগুলোর সামনের টানা বারান্দা দিয়ে হেঁটে বেড়ানোর সময় মধ্যে তিনি অনুভব করেন স্কুলবাড়ির আনাচ-কানাচ জুড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে প্রাচীন এক হাওয়া। ছুঁয়ে যাচ্ছে তাঁর চোখ-মুখ-চুল। আশ্চর্য একটা ভাল লাগা চোরাস্রোতের মতো বইতে থাকে তাঁকে ঘিরে। চোখ বুজে বুক ভরে সেই বাতাস ভিতরে টেনে নেন তিনি।
ইস্কুলটা স্বাধীনতারও আগের। সেই ১৯৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই বিদ্যালয়। এলাকার কয়েক জন বিচক্ষণ আর দূরদর্শী মানুষ অনুভব করেছিলেন, স্থানীয় শিশুদের জন্য একটা বিদ্যালয় হওয়া দরকার। সম্ভ্রান্ত লোকজন অনেকেই এগিয়ে আসেন। গড়ে ওঠে ইস্কুল।
তারও বছর খানেক আগে এই এলাকারই এক স্বদেশি যুবক নগেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী খুন হন ব্রিটিশ পুলিশের গুলিতে। তাঁরই স্মৃতিতে গড়ে ওঠে এই নগেন্দ্রপ্রসাদ স্মৃতি বিদ্যামন্দির। স্কুলের অফিসঘরের সামনেই তাঁর আবক্ষ মূর্তি। মেন গেট দিয়ে ভিতরে পা রাখলে প্রথমেই নজরে আসে। প্রতিদিন ঢোকার সময় গোপালবাবুর দৃষ্টি গিয়ে পড়ে মূর্তির চোখে। নিমেষে হাতঘড়িতে সময়টা দেখে নেন। দেরি হয়ে গেল কি না। অবশ্য দেরি তাঁর হয় না কোনও দিনই। এত বছরের অভ্যাস। রিফ্লেক্সও বলা যেতে পারে।
সেই নব্বই দশকের শুরুতে এই ইস্কুলে বাংলার শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন তিনি। না, তখন টাকা দিয়ে চাকরি বিক্রি হওয়ার ঘটনা শোনা যায়নি। শিক্ষকদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা মাপার দাঁড়িপাল্লাও বসেনি কোথাও। তখন বামফ্রন্টের বিজয়পতাকা আকাশে উড়ছে পতপত করে। পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি তখনও ছিল, কিন্তু যেন আর একটু চোরাগোপ্তা, আর একটু লাজুক। নাকি তখন সংবাদ মাধ্যমের এমন বাড়-বাড়ন্ত ছিল না বলে এ রকম মনে হয়, কে জানে!
আজকাল কোনও কিছুই আর তলিয়ে ভাবতে ইচ্ছে করে না গোপালবাবুর। মনে হয়, হয়েই তো এল! আর এত চুলচেরা খতিয়ানে লাভ কী! সব সময়েরই একটা নিজস্ব ধর্ম থাকে। মানুষও বদলায়, সময়ও। যে ভাবে মানুষ পাল্টায়, সে ভাবেই সময়ও পাল্টে যায়। অভিযোগ করার কিছু নেই।
যা-ই হোক, গোপালবাবুর বড়দা বলরাম চৌধুরী ছিলেন এলাকার শাসকদলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা। গোপালবাবুকে তাই সহজেই চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন ম্যানেজিং কমিটিকে বলে। সেই থেকে আজও চলছে।
তবে ভাই গোপালকে এখানে গুঁজে দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও একটা কারণ অবশ্য ছিল। ছোটবেলা থেকেই গোপালবাবুর বাম পা আকারে কিঞ্চিৎ ছোট। ফলে সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটা প্রধান মাপকাঠি। এমন খোঁড়া ছোট ভাইটিকে যাতে বেশি হাঁটাহাঁটি না করতে হয়, সেই কারণেই বাড়ির কাছে এই নিশ্চিন্ত ব্যবস্থা। শারীরিক খুঁতের ব্যাপারটা একটু বড় করে দেখিয়ে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র আদায় করে কাজটা করতে বেশি বেগ পেতে হয়নি বলরাম চৌধুরীকে। আর সেই থেকেই নগেন্দ্রপ্রসাদ স্মৃতি বিদ্যামন্দিরে গ্রীষ্ম হোক বা বর্ষা, বারো মাসের ভরসা গোপাল স্যর। ছেলেরা জনান্তিকে যাঁকে ‘ল্যাংড়া স্যর’ বলেও ডাকে! অবশ্য ‘ডাকে’ না বলে ‘ডাকত’ বললেই যথাযথ হয়। কারণ সেই লকডাউনের আগে অবধি গুটিকয় ছাত্র টিকে থাকলেও লকডাউনের পরের দু’-তিন বছরে সব ঝকঝকে ফর্সা।
ইস্কুলের লেখাপড়ার চেয়ে ছেলেরা গ্যারাজে গাড়ি সারানো, বাজারের রাস্তায় মোবাইল সারানো কিংবা মিস্ত্রি-মজুরের কাজে বেশি আগ্রহ বোধ করেছে। এক সময় শিক্ষকরা বেরোতেন ছাত্রদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের ডেকে আনতে। লাভ হয়নি। অভিভাবকদেরও উৎসাহ ছিল না। অনেকে তো মুখের উপর বলেই দিয়েছে, “কী হবে মাস্টারমশাই, লেখাপড়া শিখে?” মাস্টারমশাইরা কখনও উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, কখনও তাও করেননি। হাল ছেড়ে দিয়েছেন। সত্যি! কী হল পড়াশোনা শিখে? তাঁরাও তো যথাসম্ভব মন দিয়েই পড়াশোনা করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পেয়েছিলেন। তাতে কী-ই বা হল! সে সব কথা মনে পড়লে বুক খালি করে দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে গোপালবাবুর।
দীর্ঘকাল ধরেই এই ইস্কুলে ছাত্রসংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। গোঁজামিল দিয়ে বাড়িয়ে-টাড়িয়ে দেখানো হত এক সময়। কিন্তু ইদানীং প্রযুক্তির ব্যবহারে আর সেই সুযোগ নেই। ফলে এখন স্রেফ ইস্কুল কবে পাকাপাকি ভাবে উঠে যায় তার জন্য অপেক্ষা। বাংলা স্কুল এখন সমাজের দুয়োরানি। তার পরিণতি নিয়ে সমাজের কারও মাথাব্যথা নেই।
প্রতিদিন সকালে এসে হাজিরা খাতায় সই করে পা গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই। অবশ্য ঠিক পৌনে এগারোটায় নিজেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঢংঢং করে ঘণ্টা বাজিয়ে দেন গোপাল চৌধুরী। এত বছরের অভ্যাস ওই ধাতব শব্দে দিন শুরু করার! হাতের মধ্যে পিতলের ভারী চাকতিটা কাঠের হাতুড়ির আঘাতে থরথর করে কাঁপতে থাকে ক্রমাগত। ঘণ্টার আওয়াজে আর পাখিরাও আলাদা করে চমকে ওঠে না, তাদেরও বোধহয় অভ্যেস হয়ে গেছে। গুটিকতক চেনা মানুষ ছাড়া আর যখন কেউ নেই, তারা জানে তাদেরও বিপদের ভয় নেই।
তার পর অকারণ অপেক্ষা। দিনভর। কখনও কদাচিৎ পুরনো ছাত্র কেউ হয়তো সার্টিফিকেট-টিকেট কিছু নিতে এল। তার সঙ্গে গল্পগাছা। একটু হয়তো চা-বিস্কুট। কুশল বিনিময়। তাদের ব্যস্ততা থাকলেও দু’দণ্ড গল্প করে সময় কাটানোর চেষ্টা। সে সব কী দিনই না গেছে এক সময়, সেই স্মৃতিচারণ।
গোপালবাবু ছাড়া আরও জনা চারেক মানুষ এখনও আছে এই ইস্কুলের সুতোয় আটকে। তাদের মধ্যে মহীতোষ শিক্ষকতার পাশাপাশি জীবনবিমার এজেন্ট। সারা দিনে কোনও এক সময় এসে খাতায় সই করে যায় দয়া করে। আর কেদারবাবুর চাকরি আছেই মোটে মাস ছয়েক। ফলে তাঁর আসা যাওয়ার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। ক্লার্ক সুবিমলও ইচ্ছেমতো যায় আসে। তার বাড়ি কাছাকাছি। সারাটি দিন পোড়া ইস্কুলবাড়িতে থাকেন শুধু গোপালবাবু এবং সুপ্রিয়া।
বছর পনেরো আগে সুপ্রিয়া এই স্কুলে জয়েন করে। গোপালবাবুর থেকে প্রায় আঠারো বছরের ছোট। তার পর চোখের সামনে সুপ্রিয়ার বিয়ে হল। তিন-চার বছর সংসারের পরে ডিভোর্সও হয়ে গেল। সন্তানাদি নেই। মহীতোষ-কেদাররা সেই দিকেই ইঙ্গিত করে সব সময়। গোপালবাবু অবিবাহিত, সুপ্রিয়াও ডিভোর্সি। সেখান থেকেই তৈরি হয় টিকা-টিপ্পনির রসদ।
গোপালবাবুকে বলে, “আমরা না থাকলেই তো তোর সবচেয়ে সুবিধে। ফাঁকা মাঠ। সারা দিন খেলা কর। লুডু খেল। ফুটবল খেল। যত খুশি গোল দে। তবু স্কোর বোর্ডে কিছু উঠবে না।” কথা শেষের চোখ টেপা আর খ্যা-খ্যা হাসিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না-বলা কথাগুলো। কিংবা কখনও তারা বলে, “সামনে খাবার থাকতে উপোস করে মরা কি ভাল দেখায় রে গোপাল! খাবারেরও তো তাতে অভিমান হতে পারে! তখন আবার তোকে মানভঞ্জন পালা অ্যাক্টো করতে হবে, কী বলিস... হা...হা...হা!”
মুখ বুজেই সব শোনেন গোপাল চৌধুরী। এই সব নিয়ে বাগ্বিতণ্ডায় জড়াতে আর মন চায় না। সুপ্রিয়ার কানেও নিশ্চয়ই যায় এ সব কথা। অস্বস্তি কাটাতে আলমারি হাতড়ে পুরনো ফাইল বার করেন গোপাল মাস্টার। ধুলো ঝেড়ে কবেকার পুরনো সব রেকর্ডে চোখ বোলান। বহু বছর আগের কত শিক্ষকের হাতের স্পর্শ। তাঁদের মলিন হয়ে আসা ঝর্না কলমের সই। অচেনা নাম।
সে সব দেখে বিস্মৃতির আবছায়া থেকে মানুষটির চেহারা কল্পনা করার চেষ্টা করেন গোপালবাবু। এও তাঁর এক রকম খেলা। যেমন একটা নাম যদি হয় বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়— চোখ বন্ধ করে যেন সেই ধুতি আর চাদরের আবছা অবয়ব দেখতে পান তিনি। এক জন গান্ধীবাদী মানুষের মুখ। চার পাশে তখন কথা বলে ওঠে এক দল অচেনা লোক। খাদ্য আন্দোলন, বুভুক্ষু মানুষের কথা উড়ে বেড়ায়। নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তোলার স্বপ্ন থইথই করে চার পাশে। বুঁদ হয়ে ভাবতে থাকেন গোপাল চৌধুরী। কোনও দিকে খেয়াল থাকে না। আচমকা সুপ্রিয়ার ডাকে হুঁশ ফেরে, “গোপালদা, চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।”
ভাবনাচিন্তা সরিয়ে রেখে কাপটা টেনে নেন গোপাল মাস্টার। ইদানীং সুপ্রিয়াই ব্যবস্থাটা করেছে। অবশ্য বিরাট কিছু নয়। একটা ইনডাকশন হিটার রাখা হয়েছে স্টাফ রুমে। তাতেই বার দুয়েক চা করে। আর মাঝে মধ্যে চালে ডালে কিংবা সেদ্ধ ভাত ফুটিয়ে নেয়। কাজ তো কিছু নেই। এ সব করে যতটা সময় কাটে আর কী। অবশ্য এতে ভারী সুবিধে হয় গোপালবাবুর। বিয়ে-থা করা হয়নি। ফলে এই বয়সে এসে রান্নাবান্না এক রকম ঝামেলাই মনে হয়। সাধারণত দুপুরে স্কুল থেকে এক বার বেরিয়ে কাঁঠালতলা মোড়ে প্রসাদের দোকানে মাছ-ভাত খেয়ে আসেন। আর এখন সুপ্রিয়ার কল্যাণে কোনও কোনও দিন সেই পরিশ্রমটুকুও বেঁচে যায়। দুপুরের খাওয়াটা স্কুলেই সারা হয়ে যায়।
বছর দুয়েক আগে হেডমাস্টার সমীরণবাবু রিটায়ার করার পরে আলমারির সব চাবি আপাতত গোপাল চৌধুরীর হেফাজতেই থাকে। রোজ সেই সব খুলে পুরনো কাগজপত্র ওলটপালট করে দেখেন তিনি। এক সময় কত কৃতী ছাত্র এই স্কুল থেকেই পাশ করে গেছে। বিখ্যাত সিনেমা পরিচালক অর্ধেন্দুবিকাশ মুস্তফী এখানকার ছাত্র ছিলেন। মনে আছে প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উৎসবে তিনি এসেছিলেন এক বার। কবি সুনীল সমাজপতিও এখানেই পড়াশোনা করেছেন ছোটবেলায়। ফুটবলার জোহেব আখতারও এই স্কুলেরই ছাত্র। জেলাস্তরে ফুটবল খেলেছেন, কলকাতার বড় ক্লাবেও চান্স পেয়েছিলেন। আরও কত মানুষ। একটা স্কুল উঠে যাওয়া মানে এত বছরের এত এত ছাত্র তাদের লালনক্ষেত্রটাই হারিয়ে ফেলবে চিরকালের মতো।
গোপালবাবুর মনে হয়, সরস্বতী পুজোর দিন, বা অন্য কোনও অনুষ্ঠানে অনেকেই তাদের স্কুলে ফিরে আসে, দেখতে আসে তাঁদের বেড়ে ওঠার চারণভূমি এখন কেমন আছে। অনেক সময় বন্ধুবান্ধবরা মিলেও আসে। ছোটবেলার কথা বলে, ঘুরে ঘুরে চার পাশ দেখে। কিছুক্ষণের জন্য বর্তমানের সমস্ত সমস্যা ভুলে ফিরে যায় ফেলে-আসা শৈশব কৈশোরে। কিন্তু এই স্কুলটা যখন আর থাকবে না, কোথায় ফিরবে তারা? কার কাছে ফিরবে? কেমন লাগবে তখন তাদের?
মাটি পাথর ফেলে বুজিয়ে দেওয়া একটা পুরনো কুয়োর ভিতরে যেমন অনেক জলের শব্দ, কলসির আওয়াজ, মহিলাদের কলহাস্য চাপা পড়ে যায়, ঠিক তেমনই কত কত ইতিহাস, কত ছেলেবেলা, কত মান-অভিমান চিরকালের জন্য আড়ালে চলে যাবে। আর নিপুণ শিকারির মতো তাকে গলা টিপে মেরে ফেলে দু’-চার বছরের মধ্যেই মাথা তুলবে হাইরাইজ়। ব্যালকনি থেকে উঁকি মারবে টবের বাহারি ফুলগাছ। বেশ কয়েক বছর বাদে অধিকাংশ মানুষই ভুলে যাবে যে এখানে এক দিন একটা ইস্কুল ছিল। কত শৈশব খেলে বেড়াত আচারের শালপাতা আর হজমিগুলির চার পাশে!
চোখের সামনে নীলা সিনেমাহলের পরিণতি তো দেখেছেন গোপাল চৌধুরী। আশির দশকে যেখানে ছিল ব্ল্যাকারদের রমরমা। বিকেল হতে না হতেই লোকজনের ভিড়। চিৎকার চেঁচামেচি। সেখানে এখন প্রকাণ্ড পাঁচতলা কমপ্লেক্স। পাশ দিয়ে যেতে অবাক লাগে নিজের। সেই সব পুরনো সিনেমার কাট-আউট যেন আজও স্পষ্ট ভেসে ওঠে চোখে। উঁচু ক্লাসে কিংবা কলেজে পড়ার সময় তাঁদের প্রজন্মের যে সিনেমা-অভিযান, তার সাক্ষী বলে যে আর কিছু রইল না। মনে বড় কষ্ট হয় গোপালবাবুর। বেশ বুঝতে পারেন যে, নিঃসঙ্গতার সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে তিনি সময়ের কিছু আগেই বুড়ো হয়ে যাবেন। আঁতিপাঁতি করে অতীত খোঁজা আর যা নেই তার জন্য মন খারাপ হওয়া যে বয়স হওয়ারই লক্ষণ!
আর শুধু কি তিনি! চোখের সামনে সুপ্রিয়া মেয়েটাও যেন দিন-দিন কেমন বুড়িয়ে যাচ্ছে দ্রুত। অথচ যখন প্রথম আসে, কত ছটফটে ছিল। একটা শ্রী ছিল চেহারায়। গায়ের রংটা সামান্য চাপা, কিন্তু মুখে একটা লাবণ্য ছিল বরাবর। বিয়ের পরে যেন কাচের শার্সির মতো ভেঙে গেল সব কিছু। ওর জন্য খারাপ লাগে গোপালবাবুর, কিন্তু কোনও দিন মুখ ফুটে সহানুভূতি প্রকাশ করেন না। কানে বেজে ওঠে ফুটবল, লুডু খেলার সেই সব কুৎসিত ইঙ্গিত। কী দরকার, এই তো শামুকের মতো সমস্ত আবেগ খোলসের মধ্যে গুটিয়ে তিনি তো বেশ আছেন! কেটে তো যাচ্ছে দিনগুলো!
আজ আলুসেদ্ধ দিয়ে ভাত চাপিয়েছে সুপ্রিয়া। এক শিশি ঘি এনে রাখা আছে আগেই। অর্থাৎ আজ আর হোটেলে যেতে হবে না গোপালবাবুকে। তাঁর বাড়িতে তিন ভাইয়ের এক হাঁড়ি ছিল বহু দিন। তখন তাই অবিবাহিত গোপাল চৌধুরীর খাওয়া নিয়ে এত সব সমস্যা ছিল না। দুই বৌদি খুঁতো দেওরকে খানিক বেশিই স্নেহ করত। আর যা-ই হোক, যত্ন-আত্তিতে ত্রুটি হত না। কিন্তু তার পর যা হয় সব বাড়িতে। বড়দা মারা গেল। দাদাদের ছেলেমেয়েরাও বড় হয়ে গেল চটপট। তাদের কয়েক জনের বিয়েও হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। বৌদিদের সেই ছড়ি ঘোরানোর দিন আর নেই। ফলে গোপালবাবুও পড়লেন আতান্তরে। এ জন্যই বেঁচে থাকতে মা বার বার বলত বিয়েটা করে নিতে। তখন কান দেননি। এখনও যে আফসোস হয় খুব তা নয়, তবু মাঝে মধ্যে বড্ড একলা মনে হয়। বিয়েটা করলে তাও তো সুখ দুঃখের দুটো কথা বলার কেউ থাকত।
সাড়ে চারটে বাজলে আবারও ঘণ্টা বাজান গোপালবাবু, তার পর তালা-চাবি দিয়ে স্কুল বন্ধ করে বেরিয়ে পড়েন। সাতের বি বাসে চেপে সুপ্রিয়া ফিরে যায় ওর বাপের বাড়ি। এর পর বিরাট একটা সময় কাটানো সিঁড়ি-ভাঙা অঙ্কের মতোই বেশ কঠিন হয়ে ওঠে আজকাল। অধিকাংশ দিন বিনোদিনী সান্ধ্য পাঠাগারে গিয়ে বসেন গোপাল চৌধুরী। সেখানেও প্রায় একই অবস্থা। লাইব্রেরিয়ান সিদ্ধেশ্বর বছর দুয়েক আগেই রিটায়ার করে গেছে। নতুন এক জন আপাতত সপ্তাহে দু’দিন আসে। তারও উপায় নেই। অন্য এক লাইব্রেরির দায়িত্বও তারই ঘাড়ে। বাকি চার দিন সিদ্ধেশ্বরই এসে দরজা খুলে বসে থাকে। কিন্তু সেখানেও পাঠকের সংখ্যা দিন-দিন কমতে কমতে তলানিতে ঠেকেছে। ওই দু’-একটা পুরনো মুখ ঘুরে ঘুরে আসে শুধু। প্রতি বছর শীতকাল এলেই সেই লিস্ট থেকেও একটা একটা করে নাম চিরতরে বাদ যেতে থাকে। বার্ধক্য আর শুকনো পাতার এই এক আশ্চর্য মিল, প্রতি শীতেই একে একে ঝরে যেতে হয়। আস্তে আস্তে শেষ হয়ে আসছে বই-পড়া মানুষের প্রজন্ম। এত গ্রন্থাগার আন্দোলন, জেলায় জেলায় বইমেলা, সব ঢক্কানিনাদ হয়েই রয়ে গেল। নতুন প্রজন্মকে আর লাইব্রেরিতে টেনে আনা গেল না কিছুতেই। তারা স্মার্টফোনেই খুঁজে নিয়েছে তাদের যাবতীয় বিনোদন। বাংলা সাহিত্যচর্চা এখন রুগ্ণ শিল্প। সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে এ নিয়ে কথা হয় বিস্তর। এও তো এক ব্যর্থতা। এ দায় আসলে কার! কেউ জানে না। বইয়ের পাতার সাদা-কালো হরফকে যদি লড়াই করতে হয় মোবাইলের চলমান রঙিন বিনোদনের সঙ্গে, কী করে জিতবে সে! এ তো এক অসম লড়াই! লড়াইয়ের আগেই এক পক্ষের করুণ পরাজয় নিশ্চিত হয়ে আছে।
একই শহরের ভিতরে যেন একাধিক শহর লুকিয়ে থাকে। যার মধ্যে একটা নবীন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের হাসি-মশকরার জগৎ। তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা চাহিদা সব আলাদা। সেখানে অনলাইন মার্কেটিং, ডেটিং, ক্যাব, ফেসবুক, এমন কত নতুন নতুন শব্দ। আর অন্য দিকে রেশন কার্ড, পাঠাগার, খাদ্য আন্দোলন, নকশালবাড়ি, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান-সহ নানা স্মৃতিমেদুরতা আঁকড়ে ধরে এক দল মানুষের আপ্রাণ বেঁচে থাকার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, আর একটি ম্রিয়মাণ হলুদ রঙের শহর। এই দুটোর মধ্যে কোনও সেতু নেই। কমন প্যাসেজ নেই। যেন হওয়া সম্ভবও নয় কখনও। সেই জন্যই এই দূরত্বকে বোধ হয় ভাল বাংলায় অসেতুসম্ভব বলে। বসে বসে এমনই নানা কথা ভাবতে ভাবতে আজকাল মাঝে মাঝে তন্দ্রা আসে গোপালবাবুর। ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমে ভেসে আসে টুকরো টুকরো স্বপ্ন। বেশির ভাগই অতীতের ছাত্রভর্তি স্কুলবাড়ির। তাঁর পড়ানো, ছেলেপুলের বদমাইশি, গমগমে পরিবেশ। ঘুমন্ত অবস্থায় চেয়ারে বসে বসেই তাঁর ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে এক চিলতে হাসি। হঠাৎ চটকা ভেঙে গেলে ফিরে আসেন বর্তমানে। চার দিক শুনশান। পাখপাখালির কিচিমিচি ছাড়া কোনও শব্দ নেই। নতুন করে মন খারাপ হয়। একটা গান মনে পড়ে যায়। কলেজ-আমলে শোনা গান— ‘স্বপন যদি মধুর এমন/ হোক সে মিছে কল্পনা/ জাগিও না আমায় জাগিও না...’ মান্না দে-র গান। খুব ভাল লাগত গোপালবাবুর।
আজ আচমকা বাসনের শব্দে সম্বিৎ ফিরল গোপাল চৌধুরীর। কাপড় দিয়ে সসপ্যান ধরে ভাত নামাচ্ছে সুপ্রিয়া। শ্যাওলা রঙের তাঁতের শাড়ি। সাদা ব্লাউজ় পরেছে ভিতরে। ব্লাউজ়ের নীচেই একটা লালচে জড়ুল। এত বছর পাশাপাশি কাজ করছেন গোপাল চৌধুরী, কিন্তু সুপ্রিয়ার নাভির উপরে যে এমন একটা জড়ুল আছে তা তো জানতেন না। দীর্ঘ বিবাহবিচ্ছিন্ন জীবন, সন্তান না হওয়া ইত্যাদি নানা কারণে সুপ্রিয়ার দেহের বাঁধুনি এখনও অটুট। স্বাভাবিক জৈবিক নিয়মেই কয়েক পলক বেশি তাকিয়ে ফেলেন গোপালবাবু। তার পরই নিজেকে শাসন করেন, চোখ নামিয়ে নেন।
ভাবতেই কী অদ্ভুত লাগে গোপাল মাস্টারের। একটা জীবনে কত কী যে এমনই অজানা থেকে যায়! নিজের মনের ভিতরেও যেন কত অন্ধকার গলিঘুঁজি, সবটার হদিশ যেন তাঁর নিজেরও জানা নেই। এ ভাবে কখনওই তাকান না গোপালবাবু সুপ্রিয়ার দিকে। আজ যেন কী একটা হয়ে যায়। ঘাড়ে হালকা ঘামের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একফালি অগোছালো চুল চোখে পড়ে। মেয়েটার মাথায় রুপোলি রেখা উঁকি দিচ্ছে থেকে থেকে।
সবার আঙুলের ফাঁক দিয়েই গড়িয়ে যায় সময়। অবাধ। নিয়ন্ত্রণহীন। সেই চোরাবালির ভিতরে একটা সিনেমাহল হারিয়ে যায়। লাইব্রেরি মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে রাস্তার ধারে। তরুণীর কয়েকটা অবাধ্য চুলে রুপোলি রঙ ধরে। চুপি চুপি একটা গোটা ইস্কুল দখল করে নেয় শালিক পাখির দল। চোখ আর মন দুটোই সরিয়ে নেন গোপালবাবু। কী হবে আর! এত দিন যখন হয়নি... থাক তখন। বিকেলের হলুদ শহরে আলো মরে এসেছে, সন্ধের অন্ধকার নামতে কতটুকুই বা দেরি!
আর সুপ্রিয়া দুটো স্টিলের থালায় বেড়ে দিতে থাকে ফেনা ভাত। তারই ফাঁকে ফাঁকে জেগে ওঠে কয়েকটা আধফালি করা সেদ্ধ আলু। সামান্য ঘিয়ের গন্ধ দিয়ে মেখে প্রথম গ্রাস তোলেন গোপাল চৌধুরী। বড় তৃপ্তি হয় তাঁর। একটু আগের উঁকি মারা অবাধ্য মনটা এখন আবার লুকিয়ে পড়েছে। খেতে খেতে গোপালবাবু খেয়াল করেন না অনেক কিছুই। খেয়াল করেন না যে, তখন একটা শ্যামলা রঙের মেয়ে আড়চোখে তাঁর মুখে অবিকল একটা হলুদ রঙের শহর খুঁজে ফিরছে আঁতিপাঁতি করে।
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)