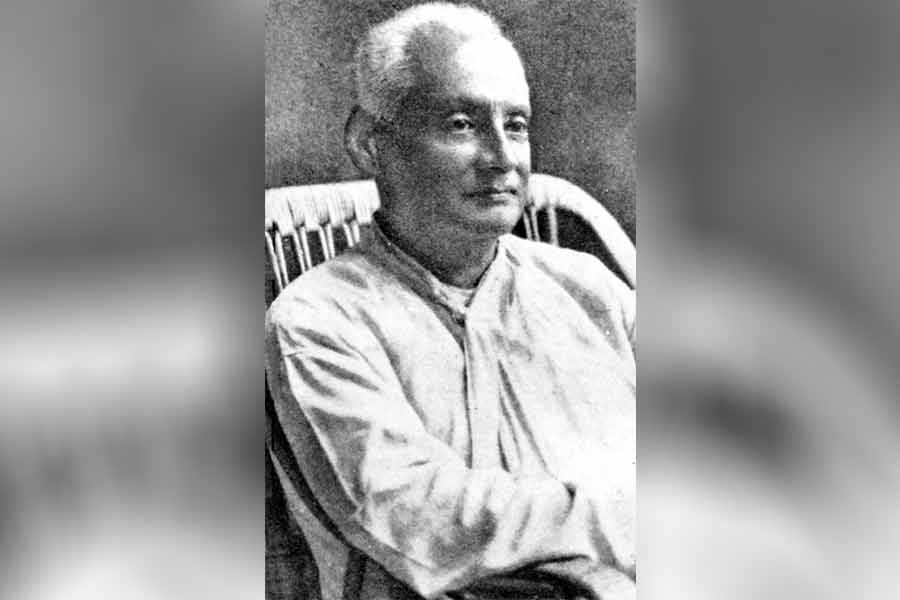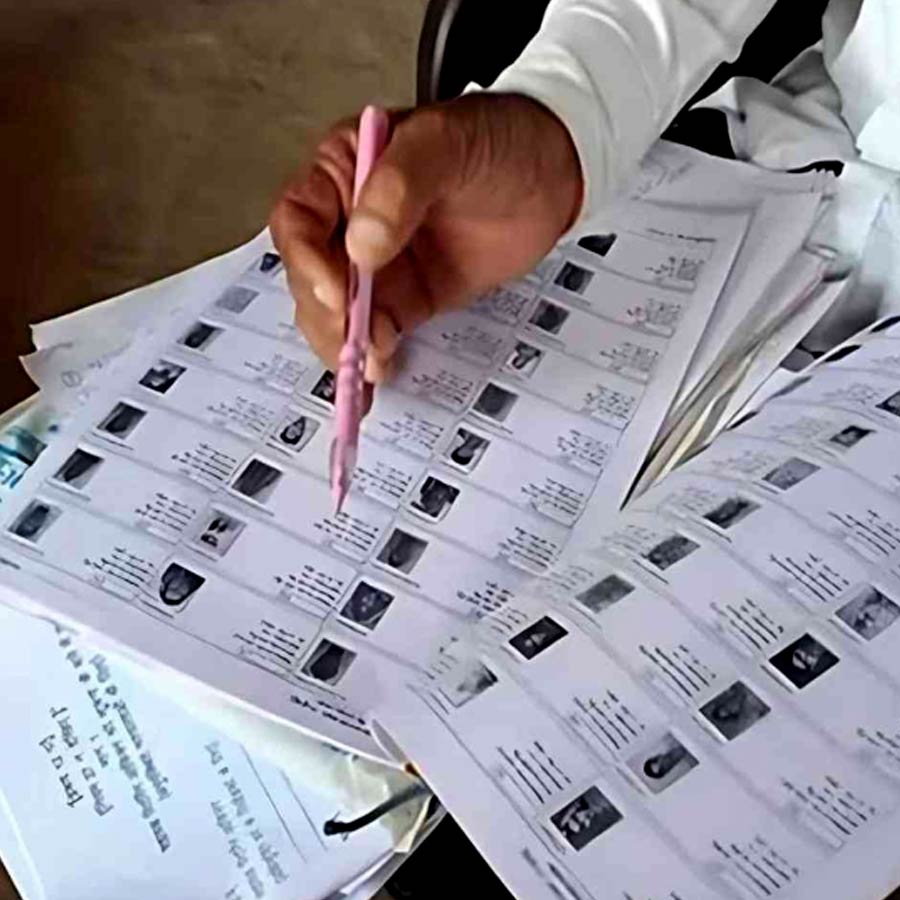গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী প্রমোদকুমারী দেবী গুরুতর অসুস্থ। স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ কেদার দাস দেখে নিদান দিলেন, ক্যান্সার হয়েছে এবং তখনই রাঁচি নিয়ে যেতে হবে। কারণ ‘এখানে সেরকম পাওয়ারফুল রেডিয়াম নেই।’ তাই তড়িঘড়ি রাঁচি গমন এবং সেখানে পরিচিত নয়নাভিরাম মোরাবাদি পাহাড়ের কোলে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি ‘সত্যধাম’ হয়ে উঠল গগনেন্দ্রনাথের পরিবারের সাময়িক নিবাস। সেই ১৯২৯ সালে চিকিৎসার প্রয়োজনে তিন মাস অন্তর অন্তর রাঁচি নিয়ে গিয়ে শক্তিশালী রেডিয়াম দেওয়ায় প্রমোদকুমারী ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন।
এই চিকিৎসার প্রয়োজনেই রাঁচিতে এক বার কলকাতা থেকে গাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং গাড়ি রাখার সুবিধার্থে ‘বলিহার লজ’ ভাড়া নেওয়া হয়। লজের গাড়িবারান্দার উপর আর্চসদৃশ কাচ দিয়ে ঘেরা ঘরটা গগনেন্দ্রনাথের বেশ মনে ধরল। কাচের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের ঢালে আলো-আঁধারের মিশেল, সূর্যাস্তের বিদায়ী বর্ণচ্ছটা, গাছগাছালি আর পাখপাখালির সংসার, প্রকৃতির হাতে বন্য জগতের নিজস্ব পরিচর্যা— এ সবই মন উদাস করে দিত। এখানে বসেই রং-তুলি নিয়ে তন্ময় হয়ে যেতেন। রূপ আর রঙের প্লাবনে ভেসে যেত ক্যানভাস। এক শীতের দুপুরে নরম রোদে পিঠ দিয়ে যখন এ রকমই কোনও রূপসাগরে ডুব দেওয়ার তোড়জোড় করছেন, তখনই এক গণৎকারের আবির্ভাব। গগনেন্দ্রনাথকে সামনে থেকে দেখে সহজসরল ভাবেই গণৎকার বলে বসলেন, ‘আপনি ভাগ্যবান মহাপুরুষ ছিলেন। কিন্তু আর আপনার বেশি দিন নেই।’
সেই শীতেই কলকাতায় ফিরে আসার পর এক ভোরবেলায় বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে গগনেন্দ্রনাথ পড়ে গেলেন। ডাক্তার এসে বললেন স্ট্রোক হয়েছে।
পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলেন। দীর্ঘ চিকিৎসার পর মাসছয়েক বাদে অল্প অল্প চলাফেরা শুরু হল। চেহারার পরিবর্তন হয়নি। গৌরকান্তি, সৌম্য, সুন্দর। বোধশক্তি অটুট। শুধু কে যেন বাক্শক্তি কেড়ে নিয়েছে। তার চেয়েও মর্মান্তিক, তাঁর সেই সাধের তুলি আর হাতে তুলতে পারলেন না। দৃষ্টি আগের মতোই অনুসন্ধিৎসু, সজাগ, সৃষ্টিশীল। মনের আঙিনা জুড়ে তখনও রঙের প্লাবন। শুধু রাঁচির সেই গণৎকারের কথা নির্মম ভাবে সত্যি হয়ে গেল।
প্রাকৃতিক নৈসর্গিক দৃশ্যচিত্র গগনেন্দ্রনাথের তুলিতে অপরূপ হয়ে ধরা পড়ত। পাহাড় বা নদীর নিজস্ব অব্যক্ত সৌন্দর্যের সঙ্গে সবাক জনজীবন মিলেমিশে পরস্পরের পরিপূরক রূপে লোকজীবন সংস্কৃতির সামগ্রিক শিল্পরূপ ভেসে উঠত ক্যানভাসে। দার্জিলিংয়ে হিমালয়ের শৃঙ্গগুলোর ধ্যানগম্ভীর দৃশ্যের পাশাপাশি পাহাড়ি তরুশ্রেণির মাঝে আঁকাবাঁকা পথ ধরে আদিবাসীদের ওঠানামা অনন্য পূর্ণতা দিয়েছে তাঁর শিল্পভাবনাকে। তাঁর তুলিতে নুলিয়াদের জলজ চাঞ্চল্য সমুদ্রের নিমগ্ন বেলাভূমিকে আরও বিস্তারিত ও প্রসারিত করেছে। রাঁচির পাথুরে টিলার গায়ে আপাতধূসর আকাশকে বর্ণময় করেছে শিশু-কাঁখে লাল পাড় সাদা শাড়ি পরিহিতা আদিবাসী রমণীদের ছন্দোময় চলন। গগনেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা সুজাতা দেবী তাই বলেছেন, ‘শিল্পীর চোখে তিনি যা দেখেছিলেন আমাদেরও তাই দেখতে শেখালেন। ... তিনি আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিলেন, তাই না হলে আগে শুধু বরফের পাহাড় বলেই দেখেছিলাম।’
রাঁচি থেকে কলকাতায় ফিরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হলেও স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের সেবা-শুশ্রূষায় বেঁচে রইলেন বেশ কয়েক বছর। মনের গভীর আর্দ্রতায় সিক্ত সেই তুলিতে তখনও অপেক্ষারত কত রঙের ঢেউ, কত ভাবনাকে রূপ দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা। মনে মনে হয়তো অতীতে আচ্ছন্ন হয়েছেন। রঙের খেলায় পুনরায় মেতে উঠতে চেয়েছেন। মনের চিত্রপটে ভেসে উঠেছে সেই চৈতন্যলীলার ভাবরস বা শ্মশানকালীর ভয়াল রূপ। কখনও বা ফিরে গেছেন প্রিয় প্রাকৃতিক দৃশ্যপটে। তিনি ব্যঙ্গচিত্রে যেমন রেখেছেন বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তার ছাপ, তেমনই তাঁর চিত্রকল্প নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফসল ‘কিউবিজ়ম’। আর শেষের দিকে এল সাদা-কালোর রহস্যময় চিত্রমালা। জাপানি এবং চিনা শিল্পরীতিতে আকৃষ্ট হয়ে প্রাচীন স্থাপত্যের আদলে সাদা-কালো আলো-আঁধারের মিশেলে অনবদ্য এক শৈলী ফুটিয়ে তুললেন। এই রহস্যময়তাকে প্রগাঢ় করল আপাদমস্তক কালোয় আচ্ছাদিতা অবগুণ্ঠিতা এক নারী। কখনও প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের দীপশিখাকে আড়াল করে সমস্ত অন্ধকারকে বরণ করে সে দাঁড়িয়ে আছে। কখনও ললাটের ঈষৎ আলোর বর্ণচ্ছটা সামগ্রিক অন্ধকারকে গরিমা প্রদান করেছে। শিল্পবিশারদ স্টেলা ক্রামরিশ এই চিত্রগুলোকে ‘মায়া’ সিরিজ় বলে চিহ্নিত করেছেন। আবার বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ছবিগুলির রহস্যময়তায় জোড়াসাঁকোর অন্দরমহলের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পেয়েছেন। এই সমস্ত ভাবনা মাথায় রেখেও ক্রমপ্রসারিত এক আঁধারের উদ্ধত আগ্রাসনকে মুছে ফেলা যায় না।
এই অনুষঙ্গেই গগনেন্দ্রনাথের ‘বৈতরণী’ সিরিজ়ের অবতারণা। কোনও এক অজানা উৎস থেকে উৎসারিত কালোর সর্বগ্রাসী ঢেউয়ে যেন ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছেন। সুদূরের কোনও অজ্ঞাত আহ্বানে মেতে উঠছেন। তার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত, ইশারা অনুধাবন করে বিমূর্তকে রং-রেখার ভাষায় অনুবাদ করে আশ্বস্ত হচ্ছেন। প্রথম ছবিতে কালো কাপড়ে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত এক কাপালিক বেশে যমরাজের আবির্ভাব। দ্বিতীয় ছবিতে আশ্চর্য ভয়াবহ যমপুরীর সামনে অপেক্ষারত বৈতরণী। তৃতীয় আর চতুর্থ চিত্রে পরলোকের আহ্বানে বৈতরণীতে ইহলোক থেকে পরলোকে পথ পরিক্রমার দৃশ্য। আর অন্তিম চিত্রে যেন উল্কারূপ মানবাত্মা মহাকাশের নিঃসীম অন্ধকারে ক্রমবিলীয়মান।
এক সন্ধ্যায় হঠাৎ কী মনে করে রাঁচির গাড়িবারান্দায় দুই কন্যা পূর্ণিমা আর সুজাতাকে ডেকে শার্সির সামনে বসিয়ে কাচে আলো-আঁধারের সংমিশ্রণে যে রহস্যময় প্রতিবিম্বকে শিল্পিত রূপ দেওয়ার চেষ্টায় মেতেছিলেন, সেই আগ্রহ যেন ‘বৈতরণী’তে পৌঁছে চূড়ান্ত রূপ পেল। মহাজগতের গভীরে যে অপার রহস্যের অফুরান হাতছানি, সেই আঁধারে বিলীন হয়ে গেল আত্মপ্রতিবিম্ব।
গগনেন্দ্রনাথের জীবনের শেষার্ধে এই সাদা-কালোর জগতে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ প্রসঙ্গে মেয়ে পূর্ণিমা দেবী বলেছেন— ‘এরপর শুরু হল কাল সাদার ছায়াছবি, মৃত্যুদূত এল ঘোড়ায় চড়ে। জীবনেও মৃত্যুদূতের ডাক এসে পৌঁছল। সে জানাল, “আর যাবার পথ নেই, সব অন্ধকার। এর পিছনে কি আছে তুমি আবিষ্কার করতে পারবে না। তোমার তুলি থামাও।”’ কোনও কৃষ্ণসাগরের অতল গহ্বরে হারিয়ে গেল তাঁর তুলি।
এক সময় এই মৃত্যুই গগনেন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিয়েছিল তুলি। বড় ছেলে গেহেন্দ্রনাথ বিয়ের এক বছরের মধ্যেই টাইফয়েড বা মেনিনজাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত (১৯০৫) হন। গগনেন্দ্রনাথ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লে বন্ধু দীনেশচন্দ্র সেন মনোকষ্ট লাঘব করতে কথকতা শোনার পরামর্শ দেন। ঠাকুরবাড়িতে আসেন কথকঠাকুর ক্ষেত্র চূড়ামণি। বসে কথকতার আসর। সমব্যথী রবীন্দ্রনাথ খুড়তুতো ভাইকে কীর্তন শুনতে বলেন। শিলাইদহ থেকে আসেন কীর্তনিয়া শিবু সাহা। বসে কীর্তনের আসরও। কিছুতেই কিছু হয় না। শেষমেষ আনমনে তুলি হাতে তুলে নিয়ে বিমর্ষ মনোজগৎকে কিছুটা আশ্বস্ত করেন গগনেন্দ্রনাথ।
যে পুত্রশোক গগনেন্দ্রনাথকে নিভৃতে তুলি হাতে তুলে নেওয়ার প্রথম অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল, সেই নিকষ কালোর প্রেমেই আত্মসমর্পণ করে অন্ধকারের সাম্রাজ্যে ফিরে গিয়েছিলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)