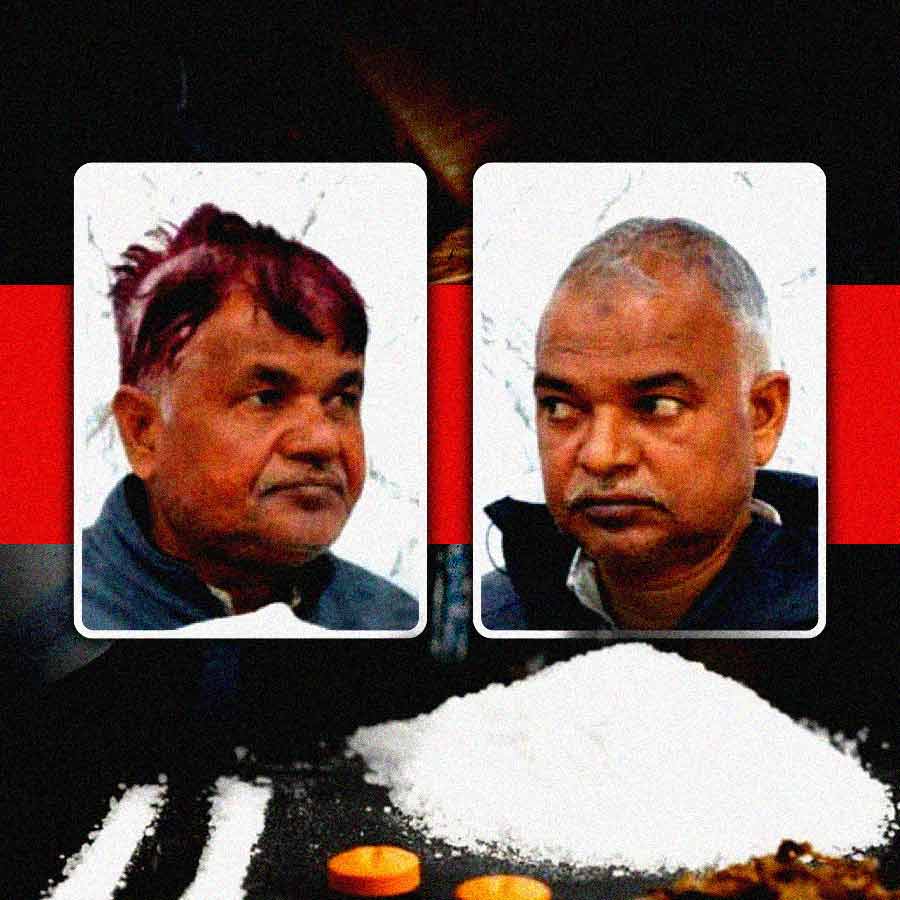কোপেনহাগেন সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে সক্কাল সক্কাল চড়ে বসলাম ডেনমার্কের তৃতীয় বৃহত্তম শহর ওডেন্স যাওয়ার ট্রেনে। ওডেন্সেই জন্মেছিলেন হান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসেন। ১৮০৫-এ। তিনি ডেনমার্কের দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার— কিংবা তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু।
ঠিক দেড়শো বছর আগে, জীবনের শেষ বছরে, ১৮৭৫ সালে, অ্যান্ডারসেন লিখলেন ‘ওডেন্স’ নামের কবিতাটি, যা তাঁর শৈশবের স্মৃতিচারণ। লিখলেন, ‘এখানে প্রতিদিন দৌড়োতাম আমি’। আজ ওডেন্স শহরে কবি এবং রূপকথাকার সেই অ্যান্ডারসেনের পদচিহ্ন হারিয়ে ফেলার জো নেই।
দিকচিহ্ন অনুসরণ করে গিয়ে পড়লাম পুরনো শহরে হ্যান্স জেনসেন স্ট্রেড এবং ব্যাংস বোডার-এর কোণে, ছোট্ট হলুদ বাড়িটায়, যেখানে জন্মেছিলেন অ্যান্ডারসেন। ১৯০৮ থেকে বাড়িটা একটা মিউজ়িয়ম— যেন অ্যান্ডারসেনের জীবনের ধারাবিবরণী। আবার ক্যাথিড্রালের কাছে যে বাড়িতে অ্যান্ডারসেন কাটিয়েছেন তাঁর দুই থেকে চোদ্দো বছর বয়স পর্যন্ত জীবনকাল, শিশুকালের সেই বাড়িটাকেও মিউজ়িয়ম করা হয়েছে ১৯৩০ থেকে। মিউজ়িয়মে সযত্নে রাখা বিভিন্ন ভাষায় অ্যান্ডারসেনের গল্পের অনুবাদ। তার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই আমার চোখ আটকায় একটি বাংলা বইতে— নাম ‘অ্যান্ডারসেনের অমর গল্প’। প্রচ্ছদে গোলাপের ছবি। বোঝাই যাচ্ছে, সেটা ‘দ্য রোজ় ইলফ’ গল্পটির অনুরণন; যা এই বইতে অনূদিত হয়েছে ‘গোলাপ পরী’ শিরোনামে।
ওডেন্স প্রবল ভাবে মনে রেখেছে তার শ্রেষ্ঠ সন্তানকে, বয়ে নিয়ে চলেছে তাঁর স্মরণিকা। শহর জুড়ে অজস্র স্ট্যাচু আর ভাস্কর্য— মূলত অ্যান্ডারসেনের গল্পের চরিত্রদের নিয়েই। ক্যাথিড্রালের পাশেই ফেয়ারি টেল পার্ক। সেখানে স্ট্যাচু হয়ে বসে রয়েছেন স্বয়ং অ্যান্ডারসেন, সেই ১৮৮৮ থেকে। ভাস্কর্যটির স্রষ্টা লুই হ্যাসেলরিস। এখানে অ্যান্ডারসেনের হাতে একটি বই, তিনি যেন গল্পের ঝাঁপি খুলে দর্শকদের গল্প বলতে প্রস্তুত।
অ্যান্ডারসেন লিখেছেন দেড়শোরও বেশি রূপকথার গল্প। সে সব অনূদিত হয়েছে ১২৫টিরও বেশি ভাষায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলিত চেতনায় গল্পগুলি যেন গাঁথা হয়ে গিয়েছে বিচিত্র বর্ণচ্ছটার সুতোয়। শিশুদের জন্য সে সব সহজলভ্য রূপকথা, আর পরিণত পাঠকদের জন্য সেগুলি প্রতিকূলতার সম্মুখে সদ্গুণ এবং স্থিতিস্থাপকতার যৌথ পাঠ। আজ দুনিয়া জুড়েই শৈশবের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে থাকে ‘দ্য আগলি ডাকলিং’, ‘দ্য নাইটিঙ্গল’, ‘দ্য স্নো কুইন’, ‘থাম্বেলিনা’র মতো মণিমুক্তো। রূপকথা কখনও পর্যবসিত হয় শ্লেষেও। ‘রাজা, তোর কাপড় কোথায়?’— দুনিয়ার নানা সংস্কৃতিতেই পরিণত হয়েছে প্রবাদে। এর বীজও পুঁতেছেন অ্যান্ডারসেন, তাঁর গল্প ‘দি এম্পারার’স নিউ ক্লোথস’-এর মধ্যে।
১৮৪৫ সালে প্রকাশিত ‘দ্য লিটল ম্যাচ গার্ল’ গল্পটি আমার ভারী পছন্দের। সেটি সম্ভবত অ্যান্ডারসেনের প্রতিভার এক অনন্য বিচ্ছুরণ। সে গল্পে এক জমে-যাওয়া ঠান্ডায় নববর্ষের প্রাক্কালে, একটি দরিদ্র মেয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে দেশলাই বিক্রির ব্যর্থ চেষ্টার পর বাবার মারের ভয়ে নিজেকে উষ্ণ করার জন্য একের পর এক দেশলাই জ্বালায়। ক্ষণিকের সেই আগুনগুলিতে তৈরি হয় পর পর স্বপ্নের সিরিজ়। উষ্ণ লোহার চুল্লি, ঝলসানো হাঁস, একটি ভালবাসাপূর্ণ পরিবার, দুর্দান্ত ক্রিসমাস ট্রি, তার প্রয়াত ঠাকুমা— একমাত্র যিনি তাকে ভালবাসতেন। দেশলাই জ্বলে ফুরিয়ে গেলে অদৃশ্য হয়ে যায় দৃশ্যগুলোও। সব দেশলাই শেষ হলে বরফে জমে মারা যায় মেয়েটি। পৌনে দু’শো বছর ধরে অজস্র মিউজ়িক্যাল, ব্যালে, অপেরা, অ্যানিমেশন আর সরাসরি অভিনয়ে ঋদ্ধ হয়েছে দেশলাই বিক্রি করা ছোট্ট মেয়েটির রূপকথায়ন।
তবু অ্যান্ডারসেনের সবচেয়ে বেশি পরিচিত এবং জনপ্রিয় গল্প হয়তো ওই ছোট্ট মৎস্যকন্যার আখ্যান। মহাসমুদ্রের ঝকঝকে, স্বচ্ছ, নীল জলের গভীরতম তলদেশে থাকে মৎস্যকন্যা— এ ভাবেই শুরু ১৮৮ বছর আগেকার সেই গল্পের। কনিষ্ঠা মৎস্যকন্যার দুঃখ-সুখের চিত্রমালায় সোনার কাঠির ছোঁয়া দিয়ে রূপকথা এঁকেছেন অ্যান্ডারসেন, যা প্রকাশিত হয় ১৮৩৭ সালে। গল্পটি মৎস্যকন্যা সম্পর্কিত কিংবদন্তি এবং জার্মান রোম্যান্টিক ঘরানার লেখক ফ্রেডরিক ডি লা মোটে ফক-এর ১৮১১ সালে লেখা রূপকথা-ভিত্তিক উপন্যাস ‘আনডাইন’-এর মিশেলে নির্মিত। সে গল্পে আনডাইন ছিল এক জলের আত্মা, যে মানুষের আত্মা লাভের জন্য বিয়ে করে হাল্ডব্র্যান্ড নামে এক নাইটকে।
আজও মৎস্যকন্যার বিষণ্ণতা, তার প্রেম-অপ্রেম প্রবহমান কোপেনহাগেনের সমুদ্রতট ছাপিয়ে— আকাশে, বাতাসে। অগণন মানুষ তাতে আপ্লুত হয়। শৈশব ছাপিয়ে গোটা জীবনকেই প্লাবিত করে অর্ধেক মানবীর সেই কোমল, ব্যথাদীর্ণ ভালবাসা।
কোন মন্ত্রে অ্যান্ডারসেন লিখতে পেরেছেন এমন আবেশ জাগানো গল্প? অ্যান্ডারসেনের ছিল সুবিস্তৃত কল্পনাশক্তি। লেখক নিজে অবশ্য একে মনে করেছেন যুগপৎ এক মস্ত উপহার ও অভিশাপ। পঞ্চাশ বছর বয়সে, বন্ধু এডওয়ার্ড কলিনকে লিখছেন, “আমি জলের মতো, তাই সব কিছুই আমাকে গতিশীল করে। সব কিছুই প্রতিবিম্বিত হয় আমার মধ্যে।” এ সবের মধ্যে অ্যান্ডারসেন পেয়েছেন আনন্দ, আশীর্বাদ, একই সঙ্গে যন্ত্রণাও।
১৮৫৫ সালে লেখা ‘দ্য ফেয়ারি টেল অব মাই লাইফ’-এ অ্যান্ডারসেন বলেছেন, ছেলেবেলায় তিনি ছিলেন ‘এক অনন্য স্বপ্নালু শিশু’। শৈশবের বর্ণনায় তিনি লিখছেন, বাবা তাঁর জন্য তৈরি করেছিলেন প্রচুর খেলনা। তাঁর কাছে ছিল এমন ছবি, যা পাল্টে দেওয়া যেত সুতো টেনে। ছিল একটি ট্রেডমিল খেলনা, যা চালু হলে নাচতে থাকত মিলার। শৈশবে তিনি ভালবাসতেন পুতুলের পোশাক সেলাই করতে কিংবা বাড়ির উঠোনে নির্জন গুজ়বেরি ঝোপের পাশে বসে ঝাঁটার হাতলের সাহায্যে মায়ের অ্যাপ্রনটিকে দেওয়াল থেকে টেনে ধরতে।
ছেলেবেলায় অ্যান্ডারসেনের জুতো প্রস্তুতকারক বাবা— যিনি নিজে পড়েছিলেন প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত— ছেলেকে পড়ে শোনাতেন সাহিত্য, পড়তেন আরব্য রজনীর গল্প। এ সবের মধ্য দিয়েই ছোট্ট হান্সের হৃদয়তন্ত্রীতে রূপকথার সুর গাঁথা হয়েছিল কি না, কে জানে! ১১ বছর বয়সে বাবাকে হারান হান্স। ১৪ বছর বয়সে ভাগ্যান্বেষণে আসেন কোপেনহাগেনে। অভিনয় করে পেট চালানোর অভিপ্রায়ে। সেখান থেকে ক্রমে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ রূপকথাকার হয়ে ওঠাটাও যেন একটা আশ্চর্য রূপকথার গল্প।
অ্যান্ডারসেনের গল্পগুলি অতিক্রম করেছে কালকে, সংস্কৃতিকে। সে সবের বৈচিত্র, নীতিবোধ এবং প্রায়শই মিঠে-তিতা বিষয়বস্তুর সংমিশ্রণ মুগ্ধ করেছে অগণন পাঠককে। অ্যান্ডারসেনের লেখনী প্রসারিত উপন্যাস, নাটক ও কবিতার মতো অন্যান্য ক্ষেত্রেও। শৈল্পিক এবং বৌদ্ধিক বিকাশ দ্বারা চিহ্নিত ড্যানিশ স্বর্ণযুগের লেখক তিনি। তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন প্রচলিত রোম্যান্টিক সাহিত্য আন্দোলনে, যা জোর দিয়েছিল আবেগ, কল্পনা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে। তাঁর কবিতাগুলি প্রায়শই রোম্যান্টিক সংবেদনশীলতায় ঋদ্ধ— প্রেম, আকাঙ্ক্ষা আর প্রকৃতির সৌন্দর্যে মাখামাখি।
কোনও এক ম্যাজিকেই হয়তো কোপেনহাগেনে পৌঁছে কোনও মতে হোটেলে ব্যাগপত্র রেখেই অসংখ্য ভ্রমণকারীর মতো আমিও ছুটি পোতাশ্রয়ের প্রবেশমুখে। সেখানে উপকূলরেখার ধারে এক ল্যাঞ্জেলেডে পাথরের উপর মন্দ্রিত বিষণ্ণতায় উপবিষ্ট ব্রোঞ্জের মৎস্যকন্যা, মানুষ রাজপুত্রের প্রতি তার প্রেম আর শতাব্দীলালিত এক দুঃখের প্রতিমূর্তি হয়ে। সন্ধ্যার মায়ামেদুর আলোয় মাখামাখি সে এক অনিন্দ্য রূপশ্রী। তাকে দেখতে নেমেছে টুরিস্টের ঢল। পরদিন সকালে আবার ছুটি সেই কন্যার এক ভিন্নরূপ দর্শনে, সূর্যের আলো তখন উল্টো দিকে। বোঝার চেষ্টা করি, কেন এটি বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ফোটো-তোলা মূর্তিগুলির অন্যতম। মানুষের অন্দরে অন্তরে জমে থাকা রূপকথা কি বাস্তব রূপ নিয়েছে এই পরিমণ্ডলে?
১.২৫ মিটার দীর্ঘ আর ১৭৫ কেজি ওজনের মৎস্যকন্যার মূর্তিটা ১১২ বছরের পুরনো। ভাস্কর এডওয়ার্ড এরিকসেনের নির্মাণ। এই মূর্তি অবশ্য ভাস্করের আসল সৃষ্টির এক প্রতিলিপি মাত্র। আসল মূর্তিটা সুরক্ষিত কোনও গোপন নিভৃত স্থানে। কিন্তু তা-ই বা বলি কী করে? আসল কি, আর নকলই বা কাকে বলে, তাই কি জানি? অগণিত দর্শকের এই বিস্ময় কি ‘আসল’ নয়?
এ বার ইতস্তত ঘোরা কোপেনহাগেনের অলিগলিতে। এ শহরে এলে যেতেই হবে নেহাউন এলাকায়, যা ছিল এক সময়ের ব্যস্ত বাণিজ্যিক বন্দর, সেকালের নাবিকদের আনাগোনার কেন্দ্রস্থল। আজ এটি শহরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় এলাকাগুলির মধ্যে একটি। রংচঙে বাড়ি, ক্যানাল, দুর্দান্ত খাবার এবং প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল।
নেহাউন-এর ২০ নম্বর বাড়িটার নাম বয়েল হাউস। এর তিনতলায় অ্যান্ডারসেন থেকেছেন ১৮৩৪ থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত। এখানে বসবাসকালেই লিখেছেন ‘দ্য টিন্ডার বক্স’ আর ‘লিটল ক্লজ় অ্যান্ড বিগ ক্লজ়’-এর মতো প্রথম দিকের রূপকথাগুলি। এক পাশে ক্যানাল আর অন্য ধারে সারি সারি বাড়ি। ক্যানাল জুড়ে টুরিস্টের বেড়ানোর নৌকোর ছড়াছড়ি। হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়াই একটা বাড়ির সামনে। নেহাউন-এর ৬৭ নম্বর বাড়ি সেটা। দরজার প্লাকে লেখা, ‘ডিগটারেন এইচ সি অ্যান্ডারসেন বোয়েডে হার’। ড্যানিশ ভাষায় যার অর্থ ‘কবি এইচ সি অ্যান্ডারসেন এখানে বাস করতেন’। ১৮৪৫ থেকে ১৮৬৪ পর্যন্ত দু’দশক কাল এই বাড়িটায় বসবাস করেছেন রূপকথার স্রষ্টা।
কোপেনহাগেনের সিটি হলের কাছে প্রধান রাস্তাটার নাম এইচ সি অ্যান্ডারসেন’স বুলেভার্ড। কোপেনহাগেনের সুন্দর পার্কগুলোর অন্যতম সপ্তদশ দশকে তৈরি কিংস গার্ডেন। এখানেও আছে অ্যান্ডারসেনের স্ট্যাচু, ১৮৮০-তে যা তৈরি করেছেন ভাস্কর অগস্ট সোবি। অ্যান্ডারসেনের কোলে বই। মূর্তির ভিত্তিতে পিতলের রিলিফে আঁকা তাঁর রূপকথার চিত্র— ‘দ্য স্টর্ক’, ‘দি আগলি ডাকলিং’।
বিদায়বেলায় আর এক বার আসতেই হয় মৎস্যকন্যার স্ট্যাচুর কাছে। স্ট্যাচুটা নিয়ে বিতর্ক অনেক। মৎস্যকন্যাকে তার প্রেম-বিরহে একাকী ছাড়তে নারাজ মানুষ। উল্টে তাকে সহ্য করতে হয় অনেক অত্যাচার। ১৯৬৪ আর ১৯৯৮ সালে চুরি হয়ে যায় তার মাথা। তার হাত কেটে নেওয়া হয় ১৯৮৪-তে। ২০০৩ সালে তাকে ছুড়ে ফেলা হয় সমুদ্রে। ২০০৪ সালে তুরস্ক ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে চাইলে প্রতিবাদে মৎস্যকন্যার মাথা ঢেকে দেওয়া হয় বোরখা দিয়ে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে প্রতিবাদে রাশিয়ান নারীবাদী রক মিউজ়িকের দল ‘পুসি রায়ট’-এর মতো করে মুখ ঢেকে দেওয়া হয় মৎস্যকন্যার। তার গায়ে স্প্রে করা হয়েছে বার বার। যেমন, ২০১৭ সালে উত্তর আটলান্টিকের স্বশাসিত ড্যানিশ অঞ্চল ফ্যারো দ্বীপপুঞ্জের পাইলট তিমি হত্যার প্রতিবাদে মৎস্যকন্যার গায়ে লাল রং লেপে দেয় কেউ। ২০২০ সালে মৎস্যকন্যার বসে থাকার ল্যাঞ্জেলেডে প্রস্তরখণ্ডের উপর হিজিবিজি ভাবে কেউ লিখে দেয়, ‘ফ্রি হংকং’। সে বছরই ‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার’ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে প্রস্তরখণ্ডটিতে গ্রাফিতিতে লেখা হয় ‘রেসিস্ট ফিশ’। মৎস্যকন্যার সঙ্গে জাতিবিদ্বেষের সম্পর্ক বুঝতে অনেকেইঅবশ্য হিমশিম।
কিংবা, এর একটা পটভূমি হয়তো তৈরি হয়েছে ইতিমধ্যে। ২০১৯ সালে ডিজ়নি ঘোষণা করে তাদের ‘দ্য লিট্ল মারমেড’ ছবির পুনঃরূপায়ণে ছোট্ট মৎস্যকন্যা এরিয়েল-এর ভূমিকায়— হ্যাঁ, ডিজ়নির ছবিতে এটাই কনিষ্ঠা মৎস্যকন্যার নাম— অভিনয় করবেন কৃষ্ণাঙ্গ হলিউড-অভিনেত্রী হ্যাল বেরি। কিন্তু সাদা-কালোর মৈত্রীবিহীন দ্বন্দ্ব যে আমেরিকার শোণিত-প্রবাহে। এরিয়েল-এর ভূমিকায় কৃষ্ণকলির কথা শুনেই ঝড় ওঠে। সেই ঝড় প্রবলতর হয় ২০২৩ সালে ছবিটি মুক্তি পেলে। কৃষ্ণাঙ্গী এরিয়েল সম্পর্কিত ক্রোধ যেন একটি প্রিয় কার্টুন-চরিত্রের অপ্রীতিকর পুনর্নির্মাণের চেয়েও হয়ে ওঠে অনেক বেশি কিছু। কিন্তু ডিজ়নির ছবিগুলো তো অনন্যরূপে আমেরিকান। তাই সেই জাতিবিদ্বেষের ঢেউ কী করে সুদূর চিন কিংবা দক্ষিণ কোরিয়াতেও পৌঁছয়, তার ব্যাখ্যা সহজ নয়। হয়তো অ্যান্ডারসেনের রূপকথার রাজকুমারীর যে ছবি মানুষের হৃদয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রোথিত, তার এমন উৎসরণকে গ্রহণ করতে কল্পনায় যতটা লাফ দিতে হত, সে বড় সহজ নয়।
মৎস্যকন্যার গায়ে সক্রিয় রাজনীতির ছোঁয়াও লেগেছে বার বার। ২০২৩ সালের মার্চে প্রস্তরখণ্ডে রাশিয়ার পতাকা এঁকে দেয় কেউ— ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়াকে সমর্থন করে। ছোট্ট মৎস্যকন্যার মতামত নিয়ে কেউই অবশ্যভাবিত নয়।
অ্যান্ডারসেন লিখেছেন, “মৎস্যকন্যার চোখে জল হয় না, কিন্তু তার কষ্ট আরও বেশি।” মানুষের আত্মা অর্জন করতে অ্যান্ডারসেনের মৎস্যকন্যা রাজি ছিল তার সামুদ্রিক জীবনধারা আর মৎস্যকন্যার পরিচয়ও ছাড়তে। সে মানুষ হতে চেয়েছিল বটে, কিন্তু দুনিয়ার বিচিত্র সমস্ত সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যায় প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িয়ে পড়তে চায়নি নিশ্চয়ই। তবু আশ্চর্য ভাবে কোপেনহাগেনের পোতাশ্রয়ের মুখে একখণ্ড পাথরে শতাব্দীকালের বেশি উপবিষ্ট থেকে সে যেন ক্রমেই সম্পৃক্ত হয় মানুষের দুনিয়ায়, বৈশ্বিক মানবিক সম্পর্কের টানাপড়েনের মাঝে।
কে জানে, ক্রমে এ ভাবেই হয়তো ‘মানুষ’ হয়ে ওঠে মৎস্যকন্যা, এমন মানুষ হওয়া তার কল্পনায় না থাকলেও। আর এ পথেই হয়তো তার স্রষ্টা— হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসেন— ক্রমেই হয়ে পড়েন এক রূপকথার চরিত্র।
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)