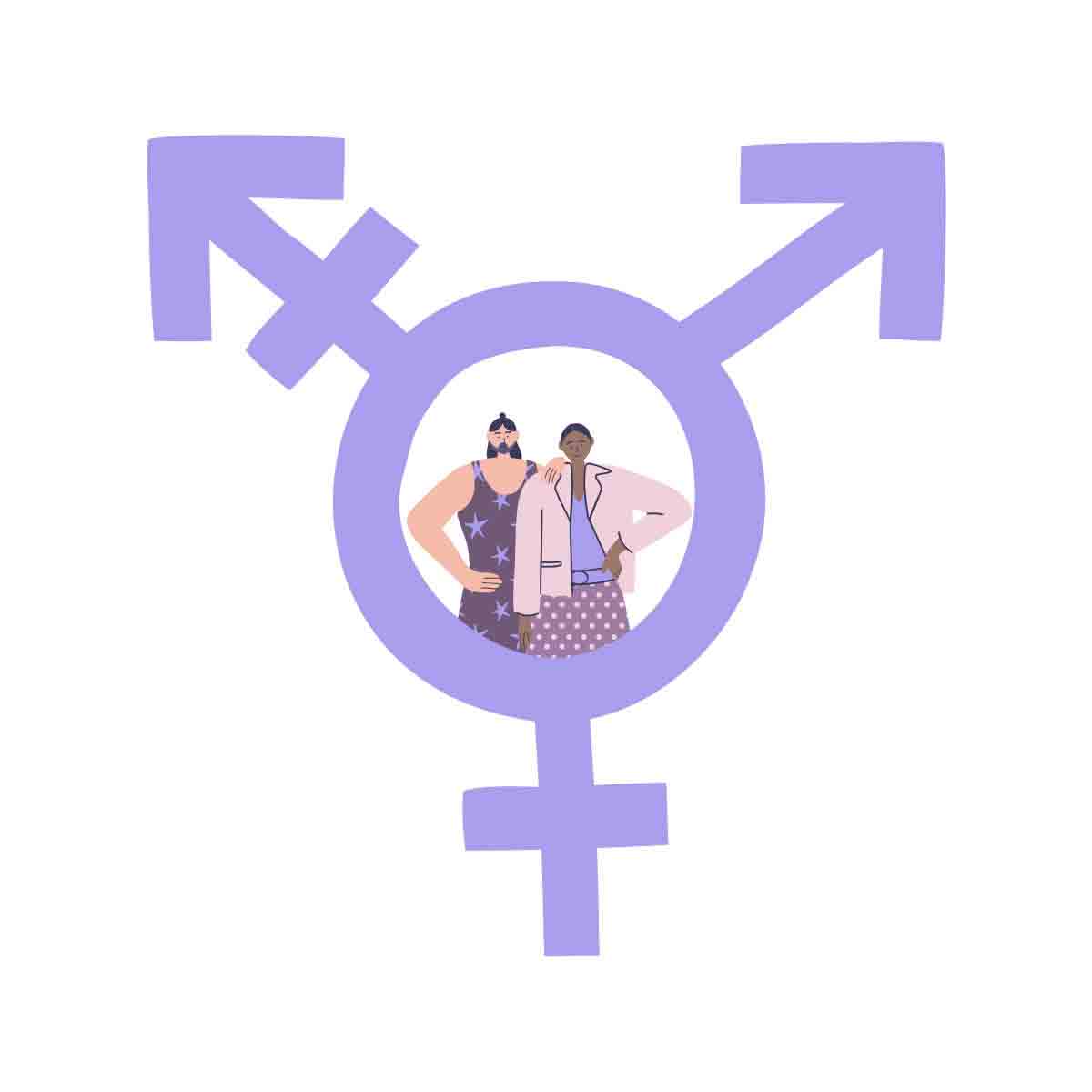বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কমলাকান্ত’ গ্রন্থের ‘চন্দ্রালোকে’ শীর্ষক রচনায় দেখেছি, চাঁদকে নিয়ে খুব ঝামেলায় পড়ে গেছেন কমলাকান্ত। চাঁদের লিঙ্গ কী হবে?— “আমাদিগের মতে চন্দ্র He- ইংরাজি মতে She, এখন উপায়? He কি She স্থির হইবে কী প্রকারে?” এর পর কমলাকান্ত ভাবছেন, অযোধ্যার যে নবাবটি হাঁসপাখি নিয়ে খেলা করেন, চোখে সুর্মা লাগান, সে He, নাকি She? আর জোয়ান অব আর্কের মতো যে নারী যুদ্ধবিদ্যায় পারঙ্গম, সে She না He? স্থির করতে না পেরে কমলাকান্ত আবার আফিম চড়ালেন।
এটা ১৮৭৪ সালের লেখা। একই সময়ে তিনি ‘বিজ্ঞান রহস্য’ লিখছেন। লিঙ্গপরিচয়ের সঙ্কট নিয়ে তিনি কিছু একটা ভেবেছিলেন ঠিকই। পুরুষ বা নারী কি শুধু বাহ্যিক লিঙ্গচিহ্নে নির্ধারিত করা যায়? এ রকম একটা চিন্তা তার মাথায় এসেছিল আবছা ভাবে, যদিও গভীরে যাননি এর বেশি। কিছু দিন পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চিত্রাঙ্গদা’ প্রকাশিত হয়। পুরুষের পরিচয় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল চিত্রাঙ্গদাকে। পুরুষের পোশাক পরানো হয়েছে, যুদ্ধবিদ্যা শেখানো হয়েছে। যৌবনে চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের প্রেমে পড়ল। রবীন্দ্রনাথ নানা ব্যঞ্জনাধর্মী বাক্যে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করে সাহিত্য সৃষ্টি করলেন। মনোবিশ্লেষণের দিকে যাননি, আত্মপরিচয়ের সঙ্কটকে তেমন করে তুলে ধরেননি। কারণ সাহিত্য এবং বিজ্ঞানকে দু’টি আলাদা ঘর ভাবা হত।
১৯২৭ সালে ‘সাহিত্যধর্ম’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “বিজ্ঞানের নির্বিচার কৌতূহল সাহিত্যের স্বভাবকে পরাস্ত করিতে উদ্যত।” তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, রসবোধ নিয়ে যে সাহিত্য ও কলা, সেখানে বিজ্ঞানের নাক গলানো ঠিক নয়। বলেছিলেন— সাহিত্য থেকে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতময় আলো-আঁধারির আব্রুটাকে সরিয়ে দিচ্ছে বিজ্ঞান। বলেছিলেন, এটা একটা অলজ্জ দুঃশাসন বৃত্তি এবং এই ভাবেই সাহিত্যের বস্ত্রহরণ হয়। অবশ্য সত্তর-উত্তীর্ণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ মত পরিবর্তন করে বলেছিলেন— “বিজ্ঞান মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ এবং রসচেতনার কোন ক্ষতি করেনি, বরংপ্রসারিত করেছে।” ‘বিশ্বপরিচয়’-এ তিনি এমন কথাই লিখলেন।
রবীন্দ্রনাথের ১৯২৭-২৮ সালের ধারণাটি আসলে ইউরোপীয় অর্জন। ডারউইনের তত্ত্ব সাত দিনে বিশ্বসৃষ্টির বাইবেলীয় তত্ত্বটিকে নস্যাৎ করে দিল। কিন্তু ১৮৬০ সালে তো ব্রুনো বা হাইপেশিয়ার মত হত্যা করে দেওয়া সম্ভব নয়, রেনেসাঁস হয়ে গেছে বহু দিন আগে। টিন্ডাল হাক্সলি কেপলাররা একটা সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ অবধি সংস্কৃতির দ্বিখণ্ডন হয়ে গেল। দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস এ সব নিয়ে হিউম্যানিটিজ়, অন্য ভাগে বিজ্ঞান। এই ভাগাভাগি বহু দিন ছিল। ক্রমশ বিভাজন কমে আসছে। কতগুলি বিষয় আছে, যার ভিতরে ঢুকতে গেলে, বুঝতে গেলে বেড়া ভেঙে দিতে হবে। জেন্ডার স্টাডি বা লিঙ্গ-সমীক্ষা তেমনই একটা বিষয়।
এক জন মানুষের পরিচয়ের জন্য তাঁর লিঙ্গ-পরিচয়টি অন্যতম প্রধান। এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে, শারীরিক চিহ্নে লিঙ্গ-পরিচয় ঠিকমতো নির্ধারণ করা যায় না বহু ক্ষেত্রেই। এক জন মানুষ শরীর এবং মনে আলাদা জেন্ডারের হতে পারেন। সিস(CIS)-জেন্ডার হলেন তাঁরাই, যাঁরা শরীর এবং মনে একই জেন্ডারে স্থিত বলে বিশ্বাস করেন। ল্যাটিন CIS শব্দটি থেকেই ‘সিমেট্রি’ শব্দটি এসেছে। যাঁরা মনে করেন মন এবং শরীরের জেন্ডার আলাদা, শরীর যে লিঙ্গচিহ্ন ধারণ করে আছে, সেটা ভুল। মন অন্য জেন্ডারে অবস্থান করছে, এ রকম যাঁরা ভাবেন, তাঁরা ট্রান্সজেন্ডার। বাংলায় বলা হচ্ছে রূপান্তরকামী। রূপান্তরকামীদের একটা অংশ নিজের লিঙ্গ অনুযায়ী সাজসজ্জা পছন্দ করে না। হয়তো কেউ লিঙ্গচিহ্নে পুরুষ, কিন্তু মেয়েদের মতো পোশাক পরতে ভালবাসে, প্রসাধন করতে চায়, গয়নাগাঁটি পরে। এঁদের ‘বিপরীত সাজসজ্জাকামী’ বা ট্রান্সভেস্টাইট বলা হচ্ছে। এটাই আরও তীব্র রূপে যদি কারও মধ্যে থাকে, সে তখন রূপান্তরকামী। ভাবে ভুল দেহে বন্দি হয়ে আছে। এই ভাবনা তীব্রতর হলে ওরা লিঙ্গচ্ছেদ পর্যন্ত যেতে পারে। এই যে বললাম ‘মেয়েদের মতো’, এটা কিন্তু খুব গোলমেলে শব্দ। মেয়েদের মতো সাজসজ্জা, মেয়েদের মতো কথা বলা, এটার কি কোনও নির্দিষ্ট মানদণ্ড আছে? মিটার বা প্যারামিটার আছে? গজ ফুট গ্রাম বা লিটারে কি মেয়েলিত্ব মাপা যায়? আবার মিজ়োরামের মেয়েলিপনা আর রাজস্থান বা গুজরাতের মেয়েলিপনা এক রকম নয়। মেয়েলি ভাষা বা মেয়েলি আচরণ যুগে যুগে পাল্টায়, এলাকাভেদে পাল্টায়। কাশীশ্বরী কলেজের মেয়েদের ভাষা আর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া মেয়েদের ভাষা এক রকম নয়। আর পোশাক-পরিচ্ছদ? সাজসজ্জা? গরমের দেশে দু’ফালি কাপড়ই ছিল পুরুষ-নারী সবার জন্যই। মেয়েদের জন্য অতিরিক্ত আরও এক ফালি দরকার হত। শীতের দেশে অন্য রকম পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি হয়ে গিয়েছিল।
ভিক্টোরিয়ান যুগেও পুরুষেরা ফ্রক পরেছে। আর গয়নাগাঁটি পরতে ভারতীয় রাজপুরুষরা খুবই ভালবাসত। শিখণ্ডীর মধ্যে একটু মেয়েলি ভাব ছিল বলে, উনি যে একটু বেশি ঝুলের কর্ণালঙ্কার বা কণ্ঠহার পরতেন, তা নয়। সব রাজপুরুষই অলঙ্কার পরতে ভালবাসতেন। রূপান্তরকামীদের মধ্যে যাঁরা লিঙ্গচিহ্নে পুরুষ, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, ওরা শৈশবেই মেয়েদের সঙ্গে খেলনাবাটি খেলা, পুতুলখেলা এ সব ভালবাসত, গোপনে গামছা জড়িয়ে ঘোমটা দিত, চুপিচুপি লিপস্টিক মেখেছে ঠোঁটে, চোখে কাজল পরেছে। বড়রা দেখতে পেয়ে বকাবকি করেছেন, হয়তো চড়-থাপ্পড়ও মেরেছেন, কিন্তু প্রবণতাটা যায়নি।
বিষয়টা শুরু হয়েছিল ‘চিত্রাঙ্গদা’ নিয়ে। চিত্রাঙ্গদা কিন্তু রূপান্তরকামী নন। গল্পটা হচ্ছে, মণিপুরের রাজা চিত্রবাহন শিবের কাছে বর পেয়েছিলেন যে, তাঁর বংশে কেবল পুত্রই জন্মাবে। তখন তো ‘শতপুত্রের জননী হও’ বলে একটা জনপ্রিয় আশীর্বচনই প্রচলিত ছিল সমাজে। শিব বচন দিয়েছিলেন ঠিকই, ‘কিন্তু কোথা হইতে কী হইয়া গেল’, রাজার কন্যাসন্তানই জন্মাল। রাজা কিন্তু কন্যাসন্তানকে কন্যা বলে মেনে নিলেন না। ছেলেদের পোশাক-পরিচ্ছদ পরালেন, বয়ঃসন্ধিতে নকল গোঁফদাড়ি জুড়ে দিয়েছিলেন কি না, কোথাও লেখা নেই। তবে যৌবনের অন্য চিহ্ন ঢিলে পোশাকে ঢাকা যায়।
প্রাচীন গল্পগাথায় পুরুষের ভূমিকায় নারী বা নারীর ভূমিকায় পুরুষ নানা ভাবেই এসেছে। শেক্সপিয়ারের কয়েকটি নাটকের কথা বলাই যায়। ‘মার্চেন্ট অব ভেনিস’-এ পোর্শিয়া উকিলের ছদ্মবেশে শাইলকের বিরুদ্ধে মামলায় লড়ে গেলেন। ‘অ্যাজ় ইউ লাইক ইট’-এর একটি নারীচরিত্র রোজ়ালিন্ড পুরুষ হয়ে গিয়ে গ্যানিমিড নাম নিয়ে নেন। ‘টুয়েল্ফথ নাইট’ নাটকে আবার ভায়োলা সিজ়ারিয়ো হয়ে যাচ্ছেন। ‘চিত্রাঙ্গদা’ এ রকমই একটি আখ্যান, যেখানে বাধ্য হয়ে চিত্রাঙ্গদাকে পুরুষের মতো হতে হয়েছিল। মহাভারতে অজ্ঞাতবাসের সময় অর্জুনকে বিরাটরাজার ঘরে ছদ্মবেশে থাকতে হয়েছিল। এখানে নারীর ছদ্মবেশ নিতে পারেননি অর্জুন, আধা-নারীর ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন। নারীর যা পোশাক ছিল সে সময়, সে রকমই পরিধান করেছিলেন। চালচলনে কিছুটা মেয়েলিপনা জাহির করার চেষ্টা করেছিলেন হয়তো। তাঁর চওড়া কাঁধ, গম্ভীর গলা, উচ্চতাজনিত কারণে মেয়েলিপনা করতে কিছু অসুবিধা হয়েছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু মহাভারত-রচয়িতা এ সব বিশদে যাননি। অর্জুন তাঁর নাম পাল্টে নিজেকে ‘বৃহন্নলা’ বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। ‘বৃহন্নলা’ আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। শব্দটার মানে হল দীর্ঘভুজা। এই শব্দটির অর্থপ্রসার ঘটেছে। এখন বৃহন্নলা বলতে নপুংসক বা কিম্পুরুষ বা ক্লীব ধরনের মানুষদের বোঝানো হয়। কোথাও দেখেছি ‘চিত্রাঙ্গদা’ শব্দটিও বিশেষ্য পদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চিত্রাঙ্গদা বা বৃহন্নলা ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন, তাঁদের ভিতর থেকে রূপান্তর গ্রহণের তাড়না আসেনি। ‘আমার এই দেহটি ভুল দেহ। এই দেহ আমি চাই না’— এ রকম একটা নাছোড় বোধ তাঁদের ছিল না।

আবার কিছু মানুষ আছেন, যাঁদের মধ্যে একটা প্রশ্ন কেবল মাছির ভনভনানির মতো ঘুরে বেড়ায়— আমি কি পুরুষ? নাকি নারী? এ রকম মানুষ সংখ্যায় কম, এঁদের ত্রুটি জন্মগত। প্রাচীন ভারতে এই ধরনের মানুষদের একত্রে বলা হত ‘তৃতীয়া প্রকৃতি’ আর এর ইংরেজি হল ‘থার্ড জেন্ডার’। অর্জুন অজ্ঞাতবাসের সময় বলেছিলেন যে, আমি তৃতীয়া প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখব।
প্রকৃতি হচ্ছে মূল জিনিসটা, যেমন মাটি। দার্শনিকরা বলবেন, ঘট-পট ইত্যাদি হচ্ছে মাটির বিকার। দুধ প্রকৃতি, ছানা সন্দেশ রসগোল্লা সব দুধের বিকার। মানুষ প্রকৃতি, নপুংসক ক্লীব কিম্পুরুষেরা কিন্তু প্রকৃতির বিকার নন, এঁরাও প্রকৃতি। স্বাভাবিক প্রকৃতিরই অংশ। এঁদের বলা হয়েছিল তৃতীয়া প্রকৃতি। এই উচ্চারণের মধ্যে এঁদের প্রতি সম্মান দেখানো আছে, যা নপুংসক ইত্যাদি শব্দের ভিতরে নেই। আমাদের ভাষায় পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ছাড়াও তৃতীয় লিঙ্গ রয়েছে, যাকে ক্লীবলিঙ্গ বলা হয়। শব্দভান্ডারে ক্লীবলিঙ্গ প্রচুর। স্বয়ং ব্রহ্ম ক্লীবলিঙ্গ। ‘বৃহন্নলা’ শব্দটিকে অন্য ভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়, ‘বৃহৎ নরা’ থেকে বৃহন্নলা ভাবতে অসুবিধা নেই, এর অর্থ হচ্ছে সম্মানিত মানুষ।
রাস্তাঘাটে অনেক মানুষকেই দেখা যায় যাঁরা মেয়েদের মতো সাজসজ্জা করেন, বেশ উগ্র ভাব থাকে সাজসজ্জার মধ্যে— চোখে কাজল, ঠোঁটে লিপস্টিক, শাড়ি বা কুর্তি, হাতে তালি। এদের আমরা হিজড়ে বলে থাকি। হিজড়েরা একটা পেশাদার সম্প্রদায়। নানা রকম জীবনসংগ্রামের মধ্যে এরা বেঁচে থাকেন। কোনও বাড়িতে নতুন শিশু জন্মালে এঁরা খবর পেয়ে যান। খবর সংগ্রহের নানা রকম ব্যবস্থাও থাকে এঁদের। ওই সব বাড়িতে যান, বাচ্চাকে কোলে নিয়ে নাচান, নিজেরাও একটু নাচেন, ঢোল বাজান। এই কাজটাকে বলে ‘ছল্লা’য় যাওয়া। আমি ছোটবেলায় দেখেছি, গৃহস্থরা এঁদের সঙ্গে ভালই ব্যবহার করত। হিজড়েরাও বিরাট পরিমাণ অর্থ দাবি করতেন না। আর হিজড়েদের অসম্মানও করত না কেউ। এমন একটা বিশ্বাস ছিল যে, এরা একই দেহে নারী ও পুরুষ, শিব ও শক্তির মিলিত রূপ। শিব যেমন অর্ধনারীশ্বর হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিলেন, তেমনই হিজড়েরাও অর্ধনারীশ্বরের অংশসম্ভূত অথবা শিবশক্তির অংশ, তাই এঁদের আশীর্বাদের বিশেষ গুরুত্ব আছে।
বর্তমানে সাধারণ মানুষের মধ্যে আর এই ধারণা তেমন নেই। কারণ হিজড়েদের চাহিদা বেড়ে গেছে, টাকা না পেলে দুর্ব্যবহার করার ঘটনাও ঘটে। এর নানা কারণও আছে। আর এখনকার দিনে জীবনযাত্রার ব্যস্ততা ও অন্যান্য নানা কারণে সন্তান-সন্ততি কম হয়। শহরের বড় বড় আবাসনের ভিতরকার ফ্ল্যাটবাড়িগুলোতে ঢোকাই মুশকিল। প্রবেশের ছাড়পত্র মেলে না মূল ফটকের নিরাপত্তারক্ষীদের কাছ থেকে। ফলে হিজড়ে-সম্প্রদায়ের মানুষজন অন্য নানা উপায়ে পয়সা রোজগারের চেষ্টা করেন। শহরের বড় রাস্তাগুলির সিগন্যালের সামনে দাঁড়িয়ে গাড়ির আরোহীদের কাছ সাহায্য প্রার্থনা করেন— এক রকম ভিক্ষাই বলা যেতে পারে। বাসে কিংবা রেলগাড়িতেও এঁদের দেখা যায়। হাতের বিশেষ কায়দায় এঁরা তালি দেন, এই তালির নাম ‘ঠিকরি’। দলবদ্ধ ভাবে এঁরা ওঠেন, মানুষ ভক্তিতে না হোক, ভয়েই দু’-দশ টাকা এঁদের দিয়ে দেন।
হিজড়েদের বাসস্থানগুলিকে ‘খোল’ বলে। এঁদের এলাকা ভাগ আছে। এক-একটি এলাকায় এক-এক জন করে ‘গুরু মা’ পরিচালনা করেন। এঁদের নিজস্ব নিয়মকানুন আছে, কেউ ইচ্ছে করলেই হিজড়ে সম্প্রদায়ে নাম লেখাতে পারেন না। যাঁদের লিঙ্গ-পরিচয়ে সমস্যা আছে, তাঁরাই হিজড়ে পরিবারের সদস্য হতে পারেন। গুরু মা-রা ঠিক বুঝতে পেরে যান।
হিজড়েদের মধ্যে অনেক রকম মানুষই আছেন। সবাই নানা কারণে তৃতীয়া প্রকৃতি হয়ে গেছেন। বেশির ভাগ মানুষই জন্মসূত্রে পুরুষ, মনে মনে নারী। আর আছেন জন্মগত ত্রুটির কারণে কিছু অসম্পূর্ণ মানুষ, যদিও এদের সংখ্যা বেশ কম। হিজড়েদের অনেকে উভলিঙ্গ বা হার্মাফ্রোডাইট ভাবেন, আসলে তেমন নয়। এই প্রসঙ্গে বলি, ‘হার্মাফ্রোডিটাস’ হচ্ছেন গ্রিক পুরাণের এক বিশেষ চরিত্র। এই চরিত্রটি দেবতা হার্মেস আর দেবী আফ্রোদিতির সন্তান। উনি ছিলেন উভলিঙ্গ। একই দেহে পুরুষ ও নারীচিহ্ন ধারণ করতেন। আমাদের অর্ধনারীশ্বর যেমন। চলমান হিজড়েদের মধ্যে এ রকম উভলিঙ্গ থাকে না।
জন্মের সময় মানুষের শুক্রাণু থেকে ২৩টি এবং ডিম্বাণু থেকে ২৩টি ক্রোমোজ়োম মিলে একটি ৪৬টি ক্রোমোজ়োমসম্পন্ন জ়াইগোট তৈরি হয়। এবং সেটার কোষ বৃদ্ধি হতে হতে মানব ভ্রূণ তৈরি হয়। এক জন মানুষের ক্রোমোজ়োম সজ্জাই হল তার ক্যারিওটিক টাইপ। ৪৬XY হল এক জন পুরুষ মানুষের স্বাভাবিক ক্যারিওটিক টাইপ, আর ৪৬XX হল একটি নারীর স্বাভাবিক ক্যারিওটিক টাইপ। নারীর কোষে Y-ক্রোমোজ়োম থাকে না। নিষিক্ত হওয়ার সময় ঠিক হয়ে যায় নতুন কোষটি ৪৬XX হবে, নাকি ৪৬XY হবে। মানে, ছেলে হবে, নাকি মেয়ে হবে। কিন্তু কদাচিৎ কখনও নিষিক্ত হওয়ার সময় গন্ডগোল হয়ে যায়। কখনও ৪৫X হয়ে যায়, মানে Y-টা থাকে না, ফলে মোট ক্রোমোজ়োম সংখ্যা ৪৬-এর বদলে ৪৫। এঁরা প্রায় মেয়েদের মতো লিঙ্গ নিয়ে জন্মান, কিন্তু অপুষ্ট। বুকে রোম গজাতে পারে বড় হলে। এই ধরনের মানুষদের ‘টার্নার সিনড্রোম’-এ আক্রান্ত বলা হয়। আবার কারও একটা ক্রোমোজ়োম বেশি হতে পারে। Y-তো বেশি হতে পারে না, X-ই বেশি হতে পারে, তখন ৪৭XXY ক্যারিওটাইপ হয়, মোট ক্রোমোজ়োম সংখ্যা ৪৬-এর বদলে ৪৭। একটা বেশি X-এর জন্য পুরোপুরি ব্যাটাছেলে হয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। এই মানুষরা ‘ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম’-এ আক্রান্ত বলা হয়। এ সব মানুষ নানা রকম রোগে ভোগেন। হিজড়ে সমাজে এইধরনের মানুষেরা সামান্য কিছু থাকেন, কিন্তু বেশি দিন নয়।
আর এক ধরনের জন্মগত ত্রুটি আছে, যেখানে যৌন-পরিচায়ক অঙ্গ পূর্ণ বিকশিত হয় না। মানব ভ্রূণের জননাঙ্গ বিকশিত হয় গর্ভসঞ্চারের বেশ কিছু দিন পরে। ভ্রূণ শরীরের একটা অংশকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাকে বলা হয় গোনাড অঞ্চল। এখান থেকেই পুরুষ বা স্ত্রী জননাঙ্গ বিকশিত হয়। কিছু কিছু টিস্যু শুক্রাশয় বা ডিম্বাশয়ে পরিণত হয়। যদি ৪৬XX হয়, তা হলে ডিম্বাশয় হবে, ৪৬XY হলে শুক্রাশয়। এ রকমই নিয়ম। গোনাড অঞ্চলে উলফিয়ান ডাক্ট এবং মুলেরিয়ান ডাক্ট থেকে নিঃসৃত হয় কিছু রাসায়নিক, যা প্রজননতন্ত্রের বিকাশ ঘটায়। যদি এখানে কোনও গন্ডগোল হয়ে যায়, তবে প্রজননতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ ঘটে না। দেখা গেল, পুরুষটির লিঙ্গ খুবই ছোট কিংবা শুক্র কিংবা শুক্রাশয় বা অণ্ডকোষটি দেখা যাচ্ছে না, পেটের ভিতর ঢুকে আছে। আবার হয়তো মেয়েদের ক্ষেত্রে ডিম্বাশয় বা জরায়ু তৈরি হল না। এই সব শারীরিক ত্রুটি যাঁদের আছে, তাঁদের বলা হয় ট্রান্স-সেক্স। এটা শারীরিক ত্রুটি, মানসিক ব্যাপার নয়। অপরিণত পুরুষরা নারী হতে চায় না, বা অপরিণত নারীরা পুরুষ। তবু সমীক্ষায় দেখা গেছে, দেড়শো জন হিজড়ের মধ্যে এক জন এ রকম শারীরিক ত্রুটিযুক্ত মানুষ থাকে। একশো জনে চার জন টার্নার বা ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোমে আক্রান্ত মানুষ থাকতে পারে। কিন্তু উভলিঙ্গ বলে কিছু হয় না। জীব জগতে কেঁচো জাতীয় কিছু প্রাণী আছে, যাদের মধ্যে দু’রকম বৈশিষ্ট্য আছে।
মানুষের মধ্যে কিছু ছদ্ম উভলিঙ্গও থাকতে পারে। যা মনে হচ্ছে, আসলে তা নয়। তাইল্যান্ডে কিছু ‘শি-ম্যান’ আছেন, যাদের স্তন এবংলিঙ্গ দুটোই আছে, তাঁরা আসলে পুরুষ। কৃত্রিম স্তন তৈরি করিয়েছেন কিছু কামুক মানুষের চাহিদা মেটাবার জন্য।
এই শি-ম্যানরা ব্যবসার কারণে কৃত্রিম। আর রূপান্তরকামী যাঁরা, মানে ট্রান্সজেন্ডার এবং শারীরিক ত্রুটিজনিত লিঙ্গচিহ্ন-যুক্ত মানুষেরা ট্রান্সসেক্স। এঁরা সবাই মিলেই তৃতীয়া প্রকৃতি। আমি একটি উপন্যাস লেখার জন্য এদের কয়েকটি ‘খোল’-এ গিয়েছি। এক-একটা খোলে ১২-১৪ জন এক সঙ্গে কমিউন করে রয়েছে। প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা ইতিহাস, ভূগোল এবং বিজ্ঞান। কিন্তু সবাই এক-এক জন গোটা মানুষ। এঁদেরপ্রেম-ভালবাসা থাকে, চাঁদের আলো, বৃষ্টির ফোঁটা, দক্ষিণা বাতাস ভাল লাগে, এক সঙ্গে ফুচকা খেতে ভাল লাগে।
পাণিনির মতে ‘মন’ শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ। এক রসিক কবি মজা করে লিখেছিলেন— মন শব্দটাকে ক্লীবলিঙ্গ জেনে প্রিয়ার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, এখন দেখছি মনটি প্রিয়ার সঙ্গেই রমণ করছে। ‘মনস্তু রম্যতে তত্র হতা পাণিনি বয়ম’। যাঁরা ছল্লা করেন, তাঁদের বাইরেও কিছু এই ধরনের মানুষ আছেন, যাঁরা নাচ-গান করেন। বিহারে এঁদের ‘লোন্ডা’ বলে। এঁরা পুরুষ, কিন্তু মেয়েদের মতো সাজগোজ করে, যৌন উত্তেজক অঙ্গভঙ্গি করে নাচ-গান করেন। সত্যিকারের মেয়েরা যা করেন, তার চেয়ে অনেক বেশি করেন। বিয়ে হোলি ইত্যাদি আনন্দ-অনুষ্ঠানে ওঁদের বায়না করা হয়। ওঁরা জানেন ওঁরা নারী নন, তাই নাচতে সঙ্কোচ হয় না, আবার আনন্দলেহনকারী পুরুষদেরও সঙ্কোচ বা অপরাধবোধ হয় না, কারণ ওরা জানে, মেয়েদের সঙ্গে তো আর ফষ্টিনষ্টি করছে না, ছেলেদের সঙ্গেই তো...
হিজড়ে এবং লোন্ডারা মোটামুটি প্রায় সবাই ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামী। ওদের মধ্যে অল্প কিছু জন লিঙ্গচ্ছেদ করিয়ে নেয় বা ওদের ভাষায় ‘ছিবড়ে’ নেয়। আরও ভাল কথায় নির্বাণ হয়ে যাওয়া। এই সব মানুষদের এ রকম আলাদা পেশা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো ছাড়া দুনিয়ায় আর কোথাও নেই। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে আর পাঁচটা মানুষের মতো রূপান্তরকামী মানুষরা সংসারেই থাকে, আমাদের দেশে মেয়েলি পুরুষরা নিজের সংসারে এবং সমাজে নিয়ত লাঞ্ছনা এবং দুর্ব্যবহারের শিকার হয়ে থাকেন। এখনকার ভাষায় বলা যায়, নিয়ত প্যাঁক খান। এই কারণেই মেয়েলি পুরুষেরা নিজেদের মতো করে নিজেদের সঙ্ঘ তৈরি করে নিয়েছে। আর যাঁরা জেনেটিক্যালি নারী, লিঙ্গচিহ্নেও নারী, কিন্তু নিজেকে ভাবে পুরুষ, ভাবে ‘ভুল দেহ নিয়ে জন্মেছি’, ওদের কিন্তু আলাদা কোনও সঙ্ঘ গড়তে হয় না। বাড়ির কোনও মেয়ের মধ্যে একটু ছেলে-ছেলে ভাব থাকলে, মেয়েটিকে বলা হয় স্মার্ট মেয়ে। তবে এই ভাব যদি প্রবল হয়, তখন একটু সমস্যা হয়। নিজের নাম পাল্টে ফেলে, কিন্তু অস্ত্রোপচার করে লিঙ্গ নির্মাণ করা সম্ভব হয় না। পুরুষকে নারীর মতো করে দেওয়া সম্ভব। কৃত্রিম স্তন যোনি ইত্যাদি তৈরি করা যায়, কিন্তু পুংলিঙ্গ তৈরি করা যায় না। কয়েক জন পুরুষ হতে চাওয়া মেয়েকে দেখেছি, হিস্টোরেকটমি বা জরায়ু অপসারণ করে নিয়েছে। সার্জারির মাধ্যমে নারী-শরীর পাওয়া পুরুষদের সমস্যা প্রচুর। হরমোন সাপ্লিমেন্ট নিয়ে যেতে হয়, কেউ বা জন্মসূত্রে টাক-প্রবণ, তাঁদের পরচুলার আশ্রয় নিতে হয়। চওড়া কাঁধ যাঁদের, তাঁদের প্রচুর সমস্যা। সব সময় সব সমস্যা মাথায় নিয়েও তাঁদের যুদ্ধ জারি রাখতে হয়।
কেন এমন হয়? কেন জেনেটিক পুরুষের মনে এই লিঙ্গ-পরিচয়ের অতৃপ্তি, বা জেনেটিক নারীর? এর কোনও উত্তর নেই। অনেক গবেষণা হয়েছে, অনেক রকম সম্ভাবনার কথাও উঠে এসেছে, কিন্তু স্পষ্ট উত্তর মেলেনি। যাঁরা পুরুষ-শরীরে নারী, তাঁরা পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শারীরিক সম্পর্কও তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে এটা সমপ্রেম, পুরুষের সঙ্গে পুরুষের প্রেম। আসলে কিন্তু এটা বিষমপ্রেম। যে বাহ্যিক পুরুষ, সে তো ভিতরে নারী। এখানে নারীর সঙ্গে পুরুষেরই সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে।
তা বলে কি সমপ্রেমীরা নেই? আছে তো। সমপ্রেমীরা কিন্তু লিঙ্গ পরিবর্তন করে নারী হতে চায় না। একটা সময় মনে করা হত, সমপ্রেম একটা ব্যাধি। এখন আর তা মনে করা হয় না। তবে অনেক দেশে সমপ্রেম বেআইনি। আমাদের দেশেও আগে বেআইনি ছিল। ২০০৯ থেকে এটা আর শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, জর্ডনে সোদোম এবং ঘমৌরা নামে দুটো শহরের কিছু মানুষ নানা কারণে সমপ্রেমী আচরণ করত বলে, ঈশ্বর শহর দু’টিকে ধ্বংস করে দেন। সোদোম শহরের নামেই সমপ্রেমের অন্য নাম হয়েছে সোদোমি। যেমন লেসবস দ্বীপের নারী কবি স্যাফো-র নারীশরীরের প্রতি মুগ্ধতা ছিল, তিনি তা নিয়ে কবিতাও লিখেছিলেন। নারীর প্রতি নারীর আসক্তিকে গ্রিসের লেসবস দ্বীপের কবি স্যাফো-র নামে না হয়ে কী ভাবে যেন দ্বীপটির নামেই হয়ে গিয়েছে।
বেশ কিছু দিন হল অন্য রকম যৌনতার মানুষদের একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এলজিবিটিকিউ— যার মানে লেসবিয়ান-গে-বাইসেক্সুয়াল-ট্রান্সজেন্ডার এবং ক্যুইয়ার। আমি ব্যক্তিগত ভাবে এই ব্র্যাকেটকে সমর্থন করি না। বাইসেক্সুয়াল বা উভকামীদের এর মধ্যে রাখতে চাই না, আর কিউ বা ক্যুইয়ার বলতে ঠিক কী বোঝায় আমি বুঝতে পারিনি। আমি অনুসন্ধানে দেখেছি, মনে মনে নারী এমন বহু পুরুষের দুর্দশার জন্য দায়ী বাইসেক্সুয়াল বা উভকামীরা। উভকামীরা নারী বা পুরুষ ভেদ না করেই যৌনসঙ্গী হয়ে যেতে পারে, এবং হয়ও। এঁরা অনেকেই রূপান্তরকামী পুরুষের দিকে কিছু দিন ঝুঁকে যায়, আবার পরে সরে যায়। উভকামীদের অনেকেরই স্ত্রী-সন্তান আছে, আবার পুরুষ সঙ্গীও আছে। যৌনতার স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে এদের মান্যতা দেওয়া যায় না, যেমন সমর্থন করা যায় না পিডোফাইল বা শিশুকামীদের।
আমার সংলগ্নতা রূপান্তরকামীদের প্রতি। কী আশ্চর্য এক বোধ কাজ করে মাথার ভিতরে। দু’দণ্ড শান্তি পেতে দেয় না। সমাজ উপেক্ষা করে। সমস্ত উপেক্ষা নিয়েও আজ অনেক রূপান্তরকামী মানুষ সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছেন পৃথিবী জুড়ে তো বটেই, এই দেশেও। বিচারক হয়েছেন, জনপ্রতিনিধি হয়েছেন, শিক্ষাবিদ হয়েছেন আইনজ্ঞ হয়েছেন, প্রশাসক হয়েছেন। মানুষের মনোভাব পাল্টেছে। অনেকে মূল স্রোতে স্থিত আছেন।
প্রাচীন ভারতে, গ্রিসে, রোমে এই ধরনের মানুষদের উপেক্ষা করা হত না। শিখণ্ডীর কাছে মাথা নুইয়েছিলেন মহাবীর ভীষ্ম। এখন তৃতীয় লিঙ্গ নামে কিছু একটা যে আছে, এটা প্রতিষ্ঠিত। অনেক ক্ষেত্রেই ফর্ম পূরণের সময় ফর্মের মধ্যে লিঙ্গ পরিচয়ের জন্য মেল, ফিমেল ছাড়াও ‘আদার’ লেখা একটা ঘর থাকে। এই ‘আদার’রা তৃতীয়া প্রকৃতি। উভকামীরা এঁদের মধ্যে পড়েন না।
উভকামীদের নিজেদের আত্মপরিচয়-সঙ্কট নেই। সঙ্কট তাঁদেরই, যাঁদের কাছে ‘কে তুমি?’ এই প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর নেই।
চিত্রাঙ্গদার কি নিজের কাছে প্রশ্ন ছিল, কে তুমি?
একটা উত্তরই একমাত্র ১০০ ভাগ ঠিক।
সেটা হল— আমি এক জন মানুষ।
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)