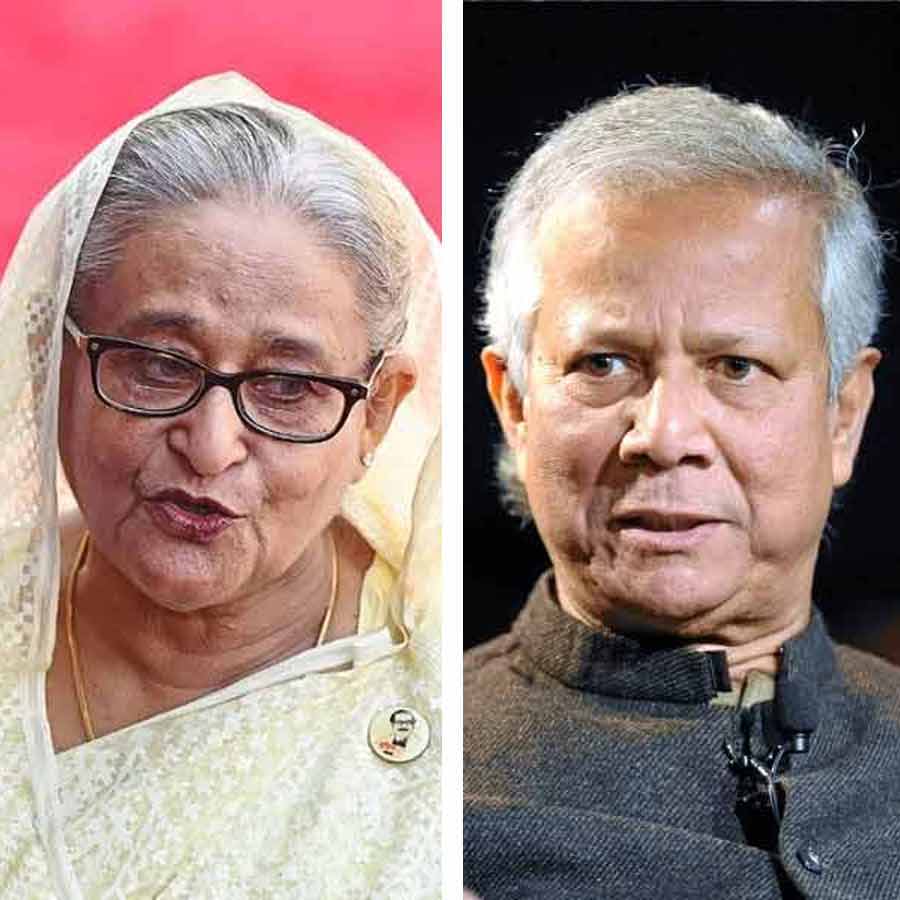মা শব্দের উচ্চতা, গভীরতা এবং ব্যাপ্তি এত বেশি যে, ধ্বনিটি সব কিছুকে এর কেন্দ্রে টেনে নেয়। এই মা, জগৎ ও জীবনের জন্য অপরিহার্য। মা ছাড়া জগৎ-সংসার অচল। তাই ১৯১৪ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন, প্রতি বছরের মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারকে আন্তর্জাতিক মাতৃদিবস হিসেবে ঘোষণা করেছেন।
বিশ্বের নানা ভাষার সাহিত্যে মায়ের কথা আমরা অনেক পড়েছি। ম্যাক্সিম গোর্কির ‘মা’, মহাশ্বেতা দেবীর ‘হাজার চুরাশির মা’। আবার ‘বিন্দুর ছেলে’র বিন্দুবাসিনী মা। পড়েছি জীবনানন্দ দাশের কলমে মা কুসুমকুমারী দেবীর কথা। নানা কাহিনিতে বিমাতার অত্যাচার এবং ভালবাসার কথা, ব্যক্তিগত জীবনে ছেলের প্রতি মায়ের পক্ষপাতিত্বের কথা। কিন্তু ভালবাসার এই পক্ষপাতিত্ব যে কতখানি ক্ষতিকারক হতে পারে, তা বিখ্যাত কয়েক জনের মায়ের সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা জানলে বোঝা যায়। এ ক্ষেত্রে অন্ধ মাতৃভক্তিও যে সমস্যাজনক হয়ে উঠতে পারে, তেমন উদাহরণও মেলে ভূরি ভূরি। মায়েদেরও, সব ক্ষেত্রে, উত্তরণের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। মেয়ে বা পুত্রবধূ হিসেবে তাঁরা যে বঞ্চনা পেয়েছেন, মায়ের আসনে এসে সেই বঞ্চনার হিসাব ফিরিয়ে দিয়েছেন পরবর্তী প্রজন্মের মেয়ে বা পুত্রবধূকে। কোথাও যে এই ক্রমাবর্তনশীল চক্র ভাঙতে হবে, তা বোঝার মতো শিক্ষিত হতে তাঁদের সময় লেগেছে বহু যুগ।
কল্যাণী দত্তের লেখা থেকে জানা যাচ্ছে, ‘ছন্দের জাদুকর’ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ‘ভারতী’ পত্রিকার চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের কাছে সত্যেন্দ্রনাথ কবুল করেছিলেন যে, মাতৃ-আজ্ঞায় বিবাহিত হয়েও তিনি ব্রহ্মচারী ছিলেন। প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটেছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ‘প্রবাসী’তে লেখেন, “একপুত্রা মাতার শোকের সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমাদের নাই।” সত্যেন্দ্রনাথ মাতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্য স্ত্রীকে চিরতরে দূরে রেখে সেই বেদনা-বিদ্যুৎ নিয়েই ছন্দে-সুরে ফুলঝুরি খেলে গেলেন। স্ত্রী কনকলতা দেবী বিমর্ষ এবং নিঃসঙ্গ জীবনযাপনে ক্রমে রুগ্ণ হয়ে পড়েন।
মাতৃত্ব জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং মেয়েটিকে তা বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়েছে, এমন ঘটনাও অজস্র। রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মাত্র তেরো বছর বয়সে মা হন। যখন তিনি নিজেই শৈশবাবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারেননি, একটি সন্তানের দায়িত্ব ও যত্ন নেবেন কী করে? সেই সময়ের নারীদের আঁতুড়ঘর আর রান্নাঘরেই জীবন কেটে যেত। আমার দিদিমার মা সতেরোটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন, যার মধ্যে ছ’টি সন্তান মারা যায়। ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়কে নিজের পাঁচটি ও আগের পক্ষের তিনটি, মোট আটটি সন্তানের দায়িত্ব নিতে হত। প্রসূতি রোগে, আ্যানিমিয়ায়, টিটেনাস হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হতেন অসংখ্য মা।
ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হল। স্থাপিত হল বেথুন স্কুল, ১৮৫০-এ। বিদ্যাসাগরও ১৮৫৭-৫৮ সালের মধ্যে বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলি ও নদিয়া জেলায় মোট ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যাসাগর মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন, এ দেশের মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে উঠুক। ১৮৮৩ সালে চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হলেন। চন্দ্রমুখী ১৮৮৪ সালে স্নাতকোত্তর ও কাদম্বিনী ১৮৮৬-সালে ডাক্তার হলেন। এ ছাড়া ছিলেন অবলা দাস, বিধুমুখী বসু প্রমুখ শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত নারীও। তখনও পরিবার পরিকল্পনা বা জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপায় বেরোয়নি, তাই শিক্ষা অথবা পেশাগত কারণে বাইরে বেরোতে হলে সন্তানদের দেখবে কে? শুরু হল মাতৃত্ব, পরিবারের প্রতি দায়িত্ব ও পেশার সংঘাত।
মাতৃত্ব একটি মেয়ের কাছে বোঝার পরিবর্তে আনন্দের অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে ১৯৬০ সালে গর্ভনিরোধক ওষুধ বেরনোর পর। নারীজীবনের মোড় ঘোরার সে এক সন্ধিক্ষণ। নারীরা সক্ষম হলেন তাঁদের মাতৃত্বের সময় এবং সন্তানসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে। কেউ কেউ স্বেচ্ছায় মাতৃত্ব না নেওয়ার সিদ্ধান্তও নিতে পারলেন।
এত দিন নারী এগোতে চাইলে পিছনে টেনে ধরত সন্তান ও পরিবারের প্রতি দায়িত্ব। এ ছাড়া পর্দানশিন নারীর বাড়ির বাইরে এসে নিজস্ব পেশা বেছে নেওয়ায় ছিল হাজারো বাধা। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ক্লদিয়া গোল্ডিন মাতৃত্ব, পরিবার ও পেশাকে এক সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াকে আমেরিকার নিরিখে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। সেটা কিছুটা আমাদের সমাজের পটভূমিতেও প্রযোজ্য।
প্রথম পর্যায় (১৮৭৮-১৮৯৭): হয় পরিবার, নয় পেশা— যে কোনও একটা দিক বেছে নিতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায় (১৮৯৮-১৯২৩): প্রথমে পেশা, তার পর পরিবার। এ সময় অনেক জনের মধ্যে ‘দ্য ফেমিনিন মিস্টিক’ বইয়ের লেখিকা বেটি ফ্রিডান, গায়িকা দিনা সোরে ও অন্যান্য যাঁরা পেশায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিবাহ ও সন্তানের মা হন। বেটি ফ্রিডান তাঁর বইয়ে দেখিয়েছেন, একটা সময় পর্যন্ত সমাজ স্পষ্ট ভাবেই দাবি করত, এক জন নারী সংসার, গৃহকর্ম, দাম্পত্য এবং সন্তানাদির মাধ্যমেই পরিপূর্ণতা পাবে। তার পেশা, শিক্ষাদীক্ষা কিংবা রাজনৈতিক মতামত নিতান্তই বাহুল্য।
তৃতীয় পর্যায়ে (১৯২৪-৪৩)— প্রথমে পরিবার, তার পরে পেশা বা চাকরি। সন্তান একটু বড় হলে পেশায় প্রবেশ। আমেরিকান সাংবাদিক ও সমাজকর্মী গ্লোরিয়া স্টাইনেম যেমন। ষাটের দশকের শেষে, সত্তরের দশকের শুরুতে ‘নিউ ইয়র্ক ম্যাগাজ়িন’ পত্রিকার এই বিখ্যাত কলাম-লেখক সে দেশে নারী স্বাধীনতার জোয়ার এনেছিলেন।
চতুর্থ পর্যায়ে (১৯৪৪-৫৭), আগে পেশা, পরে পরিবার। এই সময়কাল থেকে পেশাগত জীবনে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাধীন মহিলাদের আর দাম্পত্যের সমস্ত শৃঙ্খল পরা সম্ভব হয় না। ফলে বাড়তে থাকে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার।
পঞ্চম পর্যায়ে (১৯৫৮ ও তার পরবর্তী), নারীরা তাদের কেরিয়ার তথা পেশা এবং পরিবার এক সঙ্গে চালাবে। বর্তমানে আমাদের দেশেও এই পর্যায়ের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। বিভিন্ন রকমের ক্রেশ-কাম-স্কুলে বাচ্চা রাখার সুবিধে এসেছে, বা বাড়িতেই আয়ার ব্যবস্থা করা যায়। বাড়িতে বা ক্রেশে সর্বক্ষণের জন্য ব্যবস্থা আছে সিসি ক্যামেরার। ফলে বাচ্চার মা বা বাবা তাঁর কর্মস্থল থেকেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে নজরদারি করতে পারবেন। কিছু কিছু পরিবারে অবশ্য বাচ্চার দায়িত্ব ঠাকুমা-দিদিমারা নিয়ে থাকেন। অনেক বিধবা বা বিবাহবিচ্ছিন্না মায়েদের সন্তান পালনের জন্যে উপার্জন করতে বেরোতেই হয়। তাঁদের ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না বাচ্চাকে দেখাশোনা করা, এবং তা হয় না বাচ্চাটিকে ঠিক মতো মানুষ করে তোলার জন্যই।
নারীর মাতৃত্ব বহু সংগ্রাম, বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে। একক মাতৃত্ব বা ‘সিঙ্গল মাদারহুড’-এও সে পিছপা নয় আর। ঘর এবং বাহির এক সঙ্গে সামাল দিয়ে সে সফল ভাবে মানুষ করে তুলছে তার সন্তানকে। সর্বত্র নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার এই নমনীয়তাই যেন এক জন মায়ের সব সময় জিতে যাওয়ার রহস্য। মা এমনই এক নির্ভরতার নাম। সন্তানের সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়।
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)