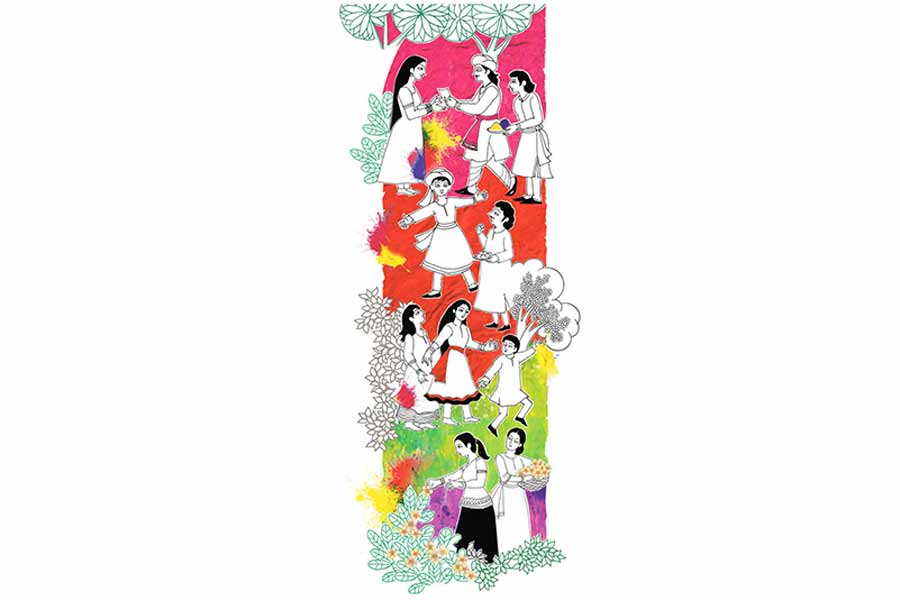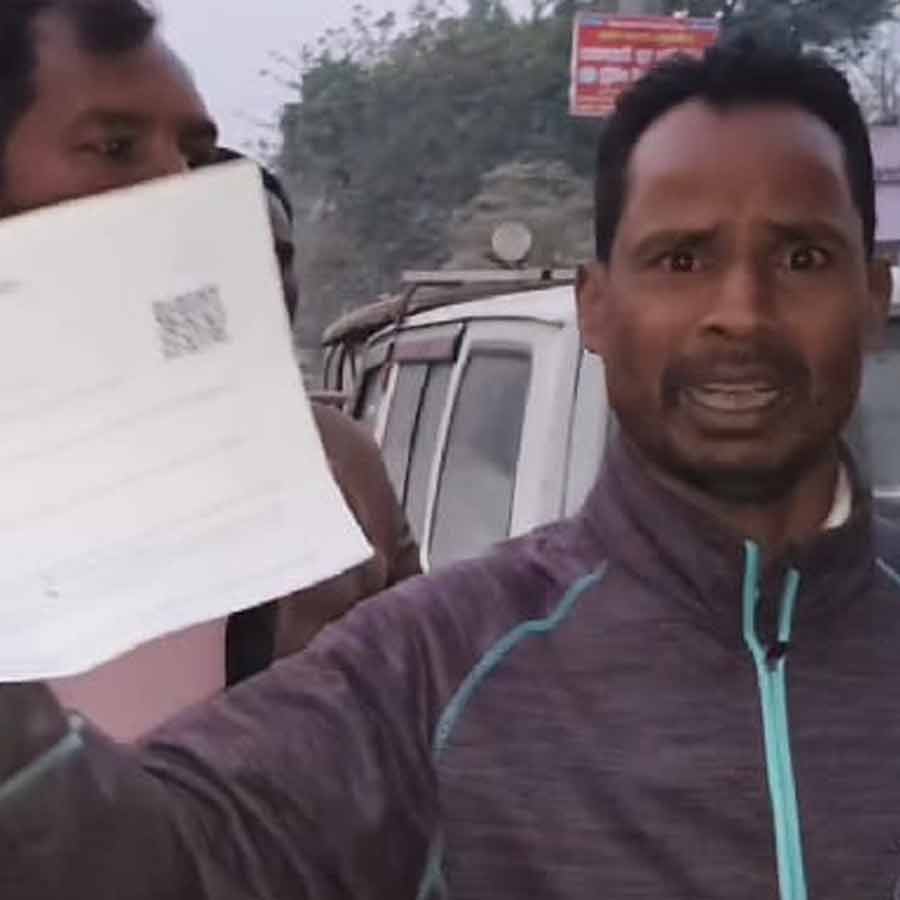কী রে, দোল খেলবি না?”
আজও ফাল্গুন এলে স্মৃতির অতল থেকে সেই স্বর ভেসে আসে। মনে হয়, কত দিন আগে শুনেছিলাম সেই স্বর? তখনকার আমি কি আর এই আমি-টা ছিলাম? সেই সাড়ে চার-পাঁচ বছর বয়সের আমিটাকে খুব মনে পড়ে এখন। মনে পড়ে সারা পৃথিবীর বিস্ময় নিয়ে সেই বেঁচে থাকার সময়টাকেও। ছোটবেলা সত্যি আমাদের এক আশ্চর্য সময়। সেই বয়সে আস্তে আস্তে যেন পাপড়ি মেলে পৃথিবী, কত কী এসে যোগ হয় জীবনে! কত ঘটনা, কত কৌতূহল, কত প্রশ্ন! মনে পড়ে, সেই ধু ধু ছোটবেলায় তেমনই একটা প্রশ্ন করেছিল সোমাদি, “কী রে, দোল খেলবি না?”
সোমাদি আমার নিজের দিদি নয়, কিন্তু আমার নিজের দিদির চেয়ে কমও কিছু নয়। ছোট্ট মফস্সলের যে বাড়িটায় আমরা ভাড়া থাকতাম, সেই বাড়ির বাড়িওয়ালা জেঠুর মেয়ে সোমাদি। আর সোমাদির দাদা ছিল আমাদের সবার শঙ্করদা। সেই আশির দশকের মফস্সল ছিল কিছুটা গ্রাম-ঘেঁষা। কৌতূহলী, আত্মীয়তাপ্রবণ মানুষে ভরা। তখন সবার বাড়িতে রেডিয়ো চলত। লোডশেডিংয়ের মধ্যে কালো-হলুদ আবছায়ায় কাটত জীবন। ছাদে-ছাদে ডানা মেলে দাঁড়িয়ে থাকত অ্যান্টেনা। সে ছিল এক বিচিত্র সময়! জীবন ছিল ছোট ছোট আনন্দের পুঁতি দিয়ে গাঁথা একটা মালা! আর এই আনন্দের একটা অংশ ছিল আমাদের ‘দোল’!
কে যেন হাওয়া থেকে রবার দিয়ে মুছে দিচ্ছে শীত। দিন বড় হচ্ছে ক্রমে। পাড়ার সজনে গাছে ঝেঁপে এসেছে খই-সাদা ফুল। বাড়ির পাশের পুকুরের উপর থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে কুয়াশার ওড়না। আর তার মধ্যে দিয়ে জেগে উঠছে ফাল্গুন। জেগে উঠছে দোল!
দোল না হোলি? দুটো কি এক? মনে আছে, পাড়ার দাদা আর কাকুরা মজা করে গব্বর সিংয়ের গলায় বলত, “হোলি কব হ্যায়? কব হ্যায় হোলি?” কেউ কেউ বলত, দোলের পরের দিন হোলি! তবে আমাদের কাছে দোল আর হোলি মিলেমিশে এক হয়ে যেত প্রতি বার।
আমাদের বাড়ির সামনেই বড় রাস্তা। তার উপরেই ছিল রামখিলাওনের কাঠগোলা। ওরা দেখতাম দু’দিনই রং খেলত। আমরাও যোগ দিতাম ওদের সঙ্গে। সারা পাড়াই যোগ দিত। তবে এই খেলার প্রস্তুতি কিন্তু শুরু হত আগেই।
বাড়ির পাশে, পুকুরের ও দিকে, ছিল যোগেন সর্দারদের জমি। দোলের কিছু দিন আগে থেকেই দেখতাম সেখানে এনে জড়ো করা হচ্ছে গাছের শুকনো পাতা, ডাল আর কাঠের টুকরো। তার পর দোলের আগের দিন বিকেলে সে সব সাজানো হত। বাঁধা হত। আমাদের উত্তেজনা বাড়ত ক্রমশ। হবে না? বুড়ির ঘর বানানো হচ্ছে যে! এ বার পোড়ানো হবে সেই ঘর।
একদম ছোটবেলায় ব্যাপারটা ভাল লাগত না আমার। খালি মনে হত, বুড়ির ঘর পুড়িয়ে দিলে বুড়িমা থাকবে কোথায়! তবে বুড়িমাটি ঠিক কে, সেটা নিয়েও নিশ্চিত ছিলাম না। সেজকাকা, মানে যাকে আমি ভাইপো বলে ডাকতাম, তাকে জিজ্ঞেস করতাম, “বুড়িটা কে গো?”
ভাইপো সহজ গলায় বলত, “চাঁদের বুড়ি!”
ও বাবা! সেই যে সুতো কাটে আর সারা পৃথিবীতে সুতো ছড়িয়ে দেয়! সেই বুড়ি! কী কাণ্ড! হাঁ করে দেখতাম, সন্ধেবেলা দাউদাউ করে জ্বলে উঠছে বুড়ির ঘর। আর জড়ো হওয়া সবাই চিৎকার করছে, “আজ আমাদের বুড়ির ঘর, কাল আমাদের দোল/ পূর্ণিমাতে চাঁদ উঠেছে বলো হরিবোল!”
কেউ কেউ আবার বলত এটা নেড়াপোড়া। ছড়াটাও বদলে দিত একটু। আর সেই ছড়ার সঙ্গে কাঁসর-ঘণ্টাও বাজত। অনেকেই বাড়ি থেকে আলু নিয়ে এসে সেই আগুনে দিত। কী? না, বিটনুন দিয়ে আলুপোড়া খাওয়া হবে। অন্য সময়ে যা খেতে চাইতাম না, ওই দিন সেই আলুপোড়া খাওয়ার জন্যই অস্থির হয়ে যেতাম সবাই! কালচে হয়ে যাওয়া আলুর খোসা ছাড়িয়ে লঙ্কা, তেল আর বিটনুন দিয়ে মাখত সোমাদি। সবাইকে ভাগ করে দিত যত্ন করে। আমার ছোট্ট হাতের পাতায় আলু মাখার গোল্লা দিয়ে জিজ্ঞেস করত, “কী রে, দোল খেলবি না?”
খেলা বলতে তখন জানতাম ফুটবল, ক্রিকেট বা আমাদের মতো করে ছোঁয়াছুয়ি, লুকোচুরি। সেখানে দোল আবার কেমন খেলা! এখানে কি দুটো দল থাকে? হারা-জেতা থাকে? জিতলে আনন্দ করে আর হারলে সবাই দুয়ো দেয়!
প্রথম দোল খেলার দিন বুঝেছিলাম, এ খেলায় হার নেই কোনও। এ খেলায় আসলে সবাই শুধু জিতেই যায়!
একান্নবর্তী পরিবার তখনও বেঁচে ছিল পৃথিবীতে। তাই দোল খেলা হত এক সঙ্গে। খুড়তুতো-পিসতুতো মিলিয়ে আমরা চার ভাই-বোন প্রায় এক সঙ্গেই থাকতাম। সঙ্গে দোতলা থেকে সোমাদি নেমে আসত। আগের দিন বাবা কিনে আনত প্লাস্টিকের পিচকারি। কিনে আনত আবির আর নানা গুঁড়ো রং। এক-এক করে সেই সব রং ন’কাকা গুলে দিত দু’-তিনটে প্লাস্টিকের বালতিতে।
সকালে উঠে আমরা ঠাকুরের পায়ে আবির দিতাম প্রথমে। বড়দের গালেও আবিরের দাগ দিতাম একটু করে। মা বলত, মানুষের পায়ে আবির দিতে নেই। বড়রাও আমাদের কপালে আবিরের টিপ পরিয়ে দিত। মিষ্টি খাইয়ে দিত। এর পর শুরু হত খেলা! ন’কাকার গুলে দেওয়া রং পিচকারিতে ভরে রাস্তা দিয়ে যাওয়া মানুষের গায়ে ‘পুচ’ করে ছড়িয়ে দেওয়াতে কী যে আনন্দ ছিল, সে বলে বোঝানো যাবে না! অধিকাংশ মানুষ এতে মজা পেলেও দু’-এক জন রেগেও যেত! এর মধ্যে শঙ্করদা ছাদ থেকে গেরিলা সৈন্যের মতো রংভরা বেলুন নিয়ে আক্রমণ করতে পথচারীদের! আমাদেরও লক্ষ করে মারত মাঝে মাঝে! আরে, শঙ্করদা তো আমাদের দলের! সে আমাদের বেলুন মারছে কেন? আমরা তাই রাগে চিৎকার করে উঠতাম ‘সেমসাইড সেমসাইড!’ শঙ্করদা সাইকেলের পাম্পারের মতো পিচকারি হাতে হাসত খুব!
সাদাকালো মানুষজন, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে রঙিন মানুষজনে পাল্টে যেত। আবিরের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ত হাওয়ায়। রঙে ভেজা জামায় এসে লাগত ফাল্গুনের শিরশিরে হাওয়া। ঠান্ডা লাগত আমার। আমি খেলা থামিয়ে, মাঝে মাঝে গিয়ে একটু জড়িয়ে ধরতাম রান্নাঘরে দাঁড়ানো মাকে। আমার থেকে একটু রং লেগে যেত মায়ের গায়ে! মা কোনও উৎসবে যোগ দিত না। রংও খেলত না। তাও ও-ই ছিল মায়ের রং-খেলা।
দিন আরও ঘন হলে বড়রাও বেরোত রাস্তায়। এক-এক জনকে ধরে সবাই মিলে রং মাখাত। কুখ্যাত ছিল বাঁদুরে রং। দোলে লাগালে নাকি রথের আগে উঠত না। আমরা খুব ভয় পেতাম সেই রং। আর ছিল সিলভার কালার। লাগালে মনে হত নিকেল করা মানুষ!
পাড়ার ক্লাবের বড়রা লুকিয়ে-চুরিয়ে মদ্যপানও করত, তবে গুরুজনদের সামনে আসত না সে সময়। মনে আছে, দোলের পর বেশ কিছু দিন হাতের পাতা লাল করে ঘুরে বেড়াত লোকজন। তার পর সেই রং ফিকে হতে থাকত ক্রমশ। যে ভাবে বসন্ত ক্রমে ফিকে হয়ে আসত দোলের পরে।
দোলের দিন সকালে বেরোত দোলের সং। পাড়ার ক্লাব থেকে শোভাযাত্রা করে আমরা ছোটরা-বড়রা সবাই বেরোতাম। তখন এমন বাড়িতে বাড়িতে গিটার থাকত না। থাকত হারমোনিয়াম। মনে আছে, উজ্জ্বলজেঠু মোটা কাপড় দিয়ে হারমোনিয়াম বেঁধে, কাঁধে ঝুলিয়ে বাজাতে বাজাতে গান গাইত— “সাত সুরো কি বাঁধ পায়েলিয়া/ শতরঙ্গি তন ওর চুনারিয়া/ হোলি আয়ি হোলি আয়ি রে!”
আবির মেখে, টুপি পরে বেশ ঘণ্টাদুয়েক ধরে নানা পাড়া ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেত আমাদের মিছিল। দরবেশ আর ফুটকড়াই দেওয়া হত সেই ভিড় থেকে। কত মানুষ এসে যোগ দিত আমাদের সঙ্গে! আর সেই মিছিলেই নবকাকার কাছে এসেছিল দীপ্তিদি।
নবকাকা, মানে যাকে আমরা নবকা বলতাম, তার ছিল কসমেটিক আর ঝুটো গয়নার একটা ছোট দোকান। দীপ্তিদির বাবা দীপ্তেশজেঠু ছিল আমাদের মফস্সলের বসন্ত চৌধুরী। বাটা কোম্পানির উঁচু পদের ম্যানেজার। দীপ্তিদি দারুণ গান গাইত। নাচত। উচ্চ মাধ্যমিকে আর্টস নিয়ে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিল। ইংরিজিতে এমএ করেছিল যাদবপুর থেকে। কলকাতার কোনও এক কলেজে পড়ানোর চাকরিও পেয়ে গিয়েছিল। মানে সব মিলিয়ে সোনার মেয়ে ছিল দীপ্তিদি। এ সবের সঙ্গে মেয়েটা কেমন যেন গম্ভীর আর রাগী ধরনেরও ছিল। মনে আছে পাড়ার কাকিমারা বলত, “এত্ত দেমাগ না!” বলত, “দেখ, একদম ‘দাদার কীর্তি’-র মহুয়া!”
দীপ্তিদি কাউকেই পাত্তা দিত না। শুনতাম, অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন থেকে সম্বন্ধ এসেছে বিয়ের! তখন এ সব খবর দাবানলের আগে ছড়িয়ে পড়ত পাড়ায়। আমরা শুনে ভাবতাম—মেলবোর্ন! মানে সেই যেখানে ইন্ডিয়া গত বছর পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে! রবি শাস্ত্রী কী যেন নামের একটা গাড়ি পেয়েছে! অত দূরে চলে যাবে দীপ্তিদি!
তার পর সে বার দোল এল। দোলের শোভাযাত্রা বেরোল। আর ভটচাজপাড়ায় দীপ্তিদিদের বাড়ির সামনে দিয়ে সেই রং আর গানবাজনার মিছিল যখন যাচ্ছে, হঠাৎ দীপ্তিদি বেরিয়ে এসে যোগ দিল মিছিলে! আমরা সবাই অবাক! যে মেয়ে পাথরের মতো মুখ করে থাকে, সে এমন মিছিলে এসে যোগ দিল কেন? আমি ছোট ছিলাম, তাই অতশত বুঝিনি কী হল! বুঝলাম দোলের বিকেলে।
রং-খেলে-ক্লান্ত মফস্সল দুপুরে ঘুমিয়ে একটু দেরি করে বিকেল শুরু করেছিল সে দিন। আমরা শুনলাম, দীপ্তিদিকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না! সে কী! পাওয়া যাচ্ছে না মানে! দীপ্তিদি কি নেল-কাটার নাকি ছোট্ট সোনালি সেফটিপিন!
কিন্তু সন্ধে হতে হতে ব্যাপারটা ঘোরালো হল। কাছের পুরনো মন্দিরে যখন দোলপূর্ণিমার পুজো হচ্ছে, তখন দীপ্তেশজেঠু তার চার ভাইকে নিয়ে সারা মফস্সল তন্নতন্ন করে খুঁজেও মেয়েকে না পেয়ে পুলিশে যাবে কি না ভাবতে শুরু করল। আমার ঠাকুরদার দোকানে এসে দীপ্তেশজেঠুর তো প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা! ঠিক সেই সময়ে মেমানপুর থেকে একটি ছেলে সাইকেল করে এসে খুঁজে খুঁজে দীপ্তেশজেঠুর হাতে একটা চিঠি দিয়ে গেল। কী হয়েছে, না, দীপ্তিদি নবকাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে কলকাতার এক অজানা ঠিকানায়! কাল ওরা নাকি বিয়ে করবে! রেজিস্ট্রি ম্যারেজ!
দীপ্তেশজেঠু আর কাউকে হাতের কাছে না পেয়ে সেই দূতকেই দুমাদ্দুম পিটিয়েছিল। প্রশ্ন, দীপ্তিদি ওকে চিঠি দিয়ে গেল কেন! তার পর নবকার বাড়িতে গিয়ে তার অসহায় বাবা মাকে যা নয় তা-ই বলেছিল! সে বার দোলের পরের কয়েকটা দিন ওটাই ছিল আমাদের ছোট্ট শহরের আসল আলোচনার বিষয়।
তবে ক্রমে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছিল সবার কাছে। ক’দিন পরে দীপ্তিদি নাকি দ্বিতীয় চিঠি পাঠিয়েছিল বাড়িতে। বলেছিল, নবকার কোনও হাত নেই এতে। সবটা দীপ্তিদির পরিকল্পনা। সেই স্কুল লাইফ থেকে নবকার দোকানে নাচের গয়না কিনতে যেত দীপ্তিদি। নবকা নাকি মুখ তুলেও তাকাত না! দীপ্তিদির সেই ভাল লাগার শুরু। পরে দীপ্তিদি নিজেই নবকাকে ভাল লাগার কথা জানিয়েছিল। নবকা রাজি হয়নি। বলেছিল, “আমি তোমার চেয়ে এগারো বছরের বড়। এটা সম্ভব নয়।”
কিন্তু দীপ্তিদি কি শোনার মেয়ে? নবকাকে রাজি করিয়েছিল ঠিক। কলেজে চাকরি পেয়ে বাড়ি ভাড়া করেছিল যাদবপুরে। জানত, দীপ্তেশজেঠু এই সম্পর্ক মানবে না। মেয়েকে অস্ট্রেলিয়ায় বিয়ে দেবে জোর করে। তাই দোলের আনন্দ-মিছিলের সুযোগ নিয়ে সকালের শোভাযাত্রায় এসে নবকাকে চিঠি দিয়েছিল দীপ্তিদি। দোল উৎসবের পর, ক্লান্ত নির্জন শেষদুপুরে নবকাকে রেডি হয়ে থাকতে বলেছিল। তার পর দু’জনে মিলে পালিয়ে গিয়েছিল গুরমিত সিংয়ের হলুদ কালো ট্যাক্সি করে!
দীপ্তেশজেঠু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। আর কোনও দিন মেয়ের মুখ দেখবে না ঠিক করেছিল। জনে-জনে বলে বেড়িয়েছিল যে, ওদের মেয়ে মারা গিয়েছে। নবকার দোকানটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার পর থেকে। আমাদের বসন্ত চৌধুরী ভেঙে-পড়া রাজপ্রাসাদের মতো হয়ে গিয়েছিল ক্রমশ। আর এ ভাবে কোথা দিয়ে কেটে গিয়েছিল ছ’টা বছর! মফস্সলের পাট চুকিয়ে তত দিনে আমরাও চলে এসেছি দক্ষিণ কলকাতায়! ধীরে ধীরে স্মৃতি থেকে ফিকে হয়ে গিয়েছিল দীপ্তিদি আর নবকার ঘটনা।
তার পর ক্লাস টেন-এ পড়ার সময়,
সে বার ওই মফস্সল শহরেই পিসির
বাড়ি গিয়েছিলাম দোলের আগের দিন। ওখানে দোল ও তার পরের দুটো দিন কাটাব ভেবেছিলাম।
বিকেলে ঠাকুরদার সঙ্গে বেরিয়েছি। দেখি দীপ্তেশজেঠু! ঝলমলে হাসিখুশি মুখ!
কী ব্যাপার? না, মল্লিকবাজার থেকে রং কিনছে দীপ্তেশজেঠু। আর তার আকাশি রঙের স্কুটারের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে হলুদ ফ্রক পরা কোঁকড়া চুলের বাচ্চা একটা মেয়ে। বছর চারেক মতো বয়স তার।
আমার ঠাকুরদা জিজ্ঞেস করেছিল, “কেমন আছ দীপ্তেশ! কত দিন পর দেখা হল! আর সঙ্গের এই মামণিটি কে?”
দীপ্তেশজেঠু এক গাল হেসে, ঝুঁকে পড়ে বাচ্চা মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, “ও টুপু। আমার দীপ্তির মেয়ে। কাল এসেছে ওরা। ছ’বছর পর! নাতনিকে নিয়ে রং কিনতে বেরিয়েছি। কাল দোল না! জানেন কাকু, দোল এক দিন ছিনিয়ে নিয়েছিল আমার দিপুকে! আর দেখুন আর একটা দোল সুদ সমেত ফিরিয়ে দিল সব কিছু!”
দেখেছিলাম, বসন্তের রঙে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আমাদের বসন্ত চৌধুরী! বড়-হয়ে-ওঠা আমি, মনে মনে শুধু বলেছিলাম, ‘বুরা না মানো, হোলি হ্যায়!’
দোল বলো বা হোলি, ফাগ বলো বা ফাল্গুন— এর মানেই যেন রঙের মেলা। মনোকষ্টের ধূসরতা থেকে পাল্টে যাওয়া প্রকৃতির লালিমার খেলা। এই সময় শীতের রুক্ষতা মুছে পৃথিবী যেন রং-তুলি হাতে বেরিয়ে পড়ে সব নতুন করে রাঙাবে বলে! তাই তো নতুন পাতার রঙে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ডালপালা। শিমুল-পলাশের আবির লাগে হাওয়ায়। বাড়ির বাগানে ঝাঁপিয়ে আসে আরও কত ফুল! দরবেশ প্রকৃতি যেন তার নানা রঙের তাপ্পি দেওয়া আলখাল্লা পরে বেরিয়ে পড়ে পথে! বেরিয়ে পড়ে গাছে গাছে। তার আগুন লাগায় নির্জনতার ডালে ডালে। বাগান জুড়ে ফুটে ওঠে ফুলের গুলাল! তাদের কারও নাম ‘মাদাগাস্কার পেরিউইঙ্কল’, কারও নাম ‘ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান জেসমিন’ আবার কারও নাম ‘নিরো’স ক্রাউন’! এ সব কিন্তু আসলে নয়নতারা, রঙ্গন আর জংলি টগর। কিন্তু বিধানদা এ ভাবেই ফুলের নামগুলো বলত! আর আমরা
ভোঁ হয়ে তাকিয়ে থাকতাম! ভাবতাম, সত্যি, বিধানদা কত জানে!
বিধানদার শখ ছিল ফুলগাছের। বলত, “গাছেদের সারা বছরই দোল!”
বিধানদাদের বাড়ির সামনের অনেকটা জায়গা জুড়ে ছিল ফুলের গাছ। ডালিয়া, জিনিয়া, চন্দ্রমল্লিকা ছাড়াও সেখানে দেখতাম ‘সালফার কসমস’, ‘পেরিক্যালিস’, ‘ব্লিডিং হার্ট’, ‘ফিউশা’, ‘ক্রিপিং বাটারকাপ’, আরও কত্ত অচেনা ফুলের মেলা!
এই ঘটনার কথা যখন বলছি, তখন আমরা বেশ কিছুটা বড় হয়েছি। বসন্ত তার অন্য রং নিয়েও ক্রমে উজ্জ্বল হচ্ছে আমাদের সামনে। উত্তম-সুচিত্রা বা সৌমিত্র-অপর্ণার চিরকালীন প্রেম ছাড়িয়ে জীবনে এসে আছড়ে পড়ছে অনিল-মাধুরীর ছায়া। তবু কখনও-সখনও আর একটু পুরনো শচীন-সারিকার সিনেমার গানও মাঝে মাঝে এসে কড়া নাড়ছে মনে। নির্জন ফাল্গুনের দুপুরে, ছমছমে হাওয়ায় বি-পিসিদের বাড়ির রেডিয়ো থেকে ভেসে আসছে, “শাম তেরি বন্সি পুকারে রাধা নাম…”! মনের মধ্যে কিসের যেন উচাটন তৈরি হচ্ছে! মনে হচ্ছে, এ জীবন যেন কার জন্য সমর্পিত! কার জন্য যেন অপেক্ষা করছে একলা প্রজাপতি! কে যেন আসবে বলেও এখনও ঠিক এসে পৌঁছচ্ছে না আমাদের কাছে! আর ঠিক এমনই এক অপেক্ষার সময়ে পাড়ায় এসেছিল তপুকাকুরা।
দক্ষিণ কলকাতায় আমাদের পাড়াটা একটু পুরনো ধাঁচের। তখনও এখানে আর্চের জানলাওয়ালা বাড়ি ছিল অনেক। পুরনো প্রশস্ত ঝুলবারান্দায় বৃদ্ধ মাসিমা বসে থাকতেন একা একা। জানলার খড়খড়ি তুলে দেখা যেত রাস্তা দিয়ে অদ্ভুত সুরে ডাকতে ডাকতে চলেছে বাবরি চুলের জরিওয়ালা! এমনই একটা পুরনো বাড়ি ভাড়া নিয়ে আমাদের পাড়ায় এসেছিল তপুকাকুরা। তপুকাকুর দুই মেয়ে। বড় জন পড়ত প্রেসিডেন্সিতে। আর ছোট জন, যে প্রায় আমাদের বয়সি, সে পড়ত কলকাতার আর একটা নামী স্কুলের ক্লাস ইলেভেনে!
বাপ রে, কী দুষ্টু ছিল এই মেয়েটা! ভাল নামটা আর বলছি না। ওর ডাকনাম ছিল গুন্ডালি। মানে সত্যিকারের গুন্ডাই ছিল ও! হাফপ্যান্ট আর টি-শার্ট পরে, একটা সোজা হ্যান্ডেলের সাইকেল নিয়ে গুন্ডালি শাসন করত আমাদের পাড়া এবং সামান্য বেপাড়াও। আর এই শাসনকার্যের মধ্যেই গুন্ডালির চোখ পড়েছিল বিধানদার ফুলের বাগানে। কলকাতায় অমন বাগানঘেরা বাড়ি তখন কমে আসছিল দ্রুত। তাও বিধানদারা কোনও এক জাদুবলে আমাদের পাড়ার মধ্যে তেমন একটা বাড়ি বাঁচিয়ে রেখেছিল ঠিক।
ফার্স্ট ইয়ারে পড়া বিধানদা তখন সুমনের গান শোনো। পাড়ার অনুষ্ঠানে জয় গোস্বামীর কবিতা বলে। গুরু পাঞ্জাবি আর জিন্স ছাড়া কিছু পরে না। আমার বিচ্ছু বন্ধুরা তাকে জিজ্ঞেস করত, “আচ্ছা বিধানদা, কামু বা কাফকা দোল নিয়ে কিছু বলেনি?”
এমন অবস্থায় বিধানদার জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়ল গুন্ডালি! মানে ঠিক বিধানদার জীবনে নয়, বাগানে। সরস্বতীপুজোর রাতে বিধানদার বাগান সাফ করে দিল মেয়েটা। যে যে ফুলে পুজো হয় না, সেই ফুলও ভেঙে নিয়ে চলে গেল। আর শুধু গেল না, ইটের টুকরো দিয়ে বাগানের কংক্রিটের পথে লিখে গেল, “আমি আবার আসব!”
এ কি রঘু ডাকাত না বিশে ডাকাত? এখনকার দিনে কে ভাই এ ভাবে আবার ডাকাতি করতে আসবে বলে বার্তা লিখে রেখে যায়! বিধানদা রেগে গিয়েছিল খুব। ফুলের উপর এমন অত্যাচারের মানে কী? কিন্তু কে যে এমন করল, তা ধরতে পারেনি।
ডাকাত ধরা পড়ল, বা বলা যায় নিজেই ধরা দিল দোলের আগের দিন। দোলপূর্ণিমার দিন তপুকাকুর বাড়িতে বিরাট পুজো হবে। আমাদের সবার নেমন্তন্ন ছিল। ঠিক তার আগের রাতে আবার বিধানদার বাগানে হামলা হল! বাগান সাফ করে দিয়ে লিখে রাখা হল, “আমি আবার আসব। ইতি, গুন্ডালি।”
বিধানদা তো রেগেমেগে বাড়িতে খুব চিৎকার চেঁচামেচি করল। দোলও খেলল না এক ফোঁটা। আমরা কেউ ওর সামনেই যেতে পারলাম না ভয়ে। বিধানদা ঘোষণা করল, গুন্ডালিকে মজা দেখাবে।
দোলের বিকেলে আমরা তপুকাকুর বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, বিধানদার সাধের ফুল দিয়ে গোটা বাড়ি সাজিয়ে রেখেছে গুন্ডালি। বিধানদাও গিয়েছিল আমাদের সঙ্গে। আমরা তো ভাবছি এ বার জোর ক্যাচাল লাগবে! জয়েস, মিলার, ফুকো, সার্ত্র থেকে বিধানদা বাছা বাছা কোটেশন দেবে! সব বাউন্সার যাবে সবার! আর গুন্ডালিও নিশ্চয় ভয় পেয়ে সামনেই আসবে না!
কিন্তু আমাদের সবাইকে অবাক করে গুন্ডালি এগিয়ে এসে বিধানদার হাত চেপে ধরে সারা বাড়ি ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল সে দিন। দেখিয়েছিল, কী ভাবে বিধানদার বাগানের ফুলে সেজে উঠেছে গুন্ডালিদের সামান্য ভাড়ার বাড়িটা!
সন্ধেবেলা আমরা যখন ওদের বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি, শুনলাম বিধানদা রবিঠাকুরের কথা বলছে। নরম গলায় বলছে, “শুধু এবারের মতো/ বসন্তের
ফুল যত/ যাব মোরা দুজন কুড়াতে।/ তোমার কাননতলে ফাল্গুন আসিবে বারম্বার,/ তাহারি একটি শুধু মাগি আমি দুয়ারে তোমার।”
বিধানদার সঙ্গে গুন্ডালির প্রেম শুরু হয়েছিল সেই দোলের দিন থেকেই। আকাশে বিশাল সোনার থালার মতো চাঁদ উঠেছিল সে দিন। রাস্তার উপর লেগে ছিল রঙের আঁচড়, আবিরের দাগ। আমাদের সামান্য পাড়ায় ঘুরছিল ফাল্গুনের নরম হাওয়া। অনেক, অনেক ফুল ফুটেছিল সে দিন! তবে সে ফুল বাগানের নয়। সে ফুল চোখে দেখা যায় না।
চার বছর গুন্ডালিরা ছিল আমাদের পাড়ায়। তার পর এক দিন উঠে চলে যায়। সেও ছিল এক দোলের আগের সন্ধে। পাড়ার মোড়ে বুড়ির ঘর পোড়ানো হচ্ছিল তখন। আগুনের ফুলকি, জোনাকির মতো উড়ছিল হাওয়ায়। খই ফোটার মতো চিটপিট শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আর তখনই প্রায় নিঃশব্দে পাড়া ছেড়ে দূরে চলে গিয়েছিল তপুকাকারা!
শুনেছিলাম, গুন্ডালি ব্রেক-আপ করে নিয়েছে বিধানদার সঙ্গে। ওরা আর কথা বলে না। ঠিক কী হয়েছিল আমরা জানি না। শুধু জানি, এক বাগান ফুলের মধ্যে একাকী দাঁড়িয়েছিল বিধানদা! ফুলেরা লুণ্ঠিত হওয়ার অপেক্ষা করতে করতে ঝরে গিয়েছিল নিঃশব্দে।
বিধানদা বড় চাকরি করে এখন। দুই ছেলেই বিদেশে থাকে। দু’জনেই ডাক্তার। বিধানদাদের বাড়িটা এখনও আছে। শুধু বাগানটা আর নেই। কেবল একটা নীল বনলতার ঝোপ লোহার গেটের ওপর লতিয়ে আঁকড়ে থাকে পুরনো সময়কে। দোলের দিনে তার ঝরে পড়া ফুল নিয়ে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখে বিধানদা।
এক বার দোলের বিকেলে জিজ্ঞেস করেছিলাম, “তুমি আর বাগান করো না কেন বিধানদা?”
বিধানদা চওড়া করে হেসেছিল। তার পর বলেছিল, “‘হঠাৎ তোমার চোখে/ দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে/ আমার সময় আর নাই।/ তাই আমি একে একে গনিতেছি কৃপণের সম/ ব্যাকুল সংকোচভরে বসন্তের শেষ দিন মম।’ আমার বাগানের দিন বহু আগে শেষ হয়ে গেছে রে রাজা!”
আবার সেই দোল এল। জানি আবারও নতুন রঙে ভরে উঠবে পৃথিবী। তবু কেন জানি না, ফেলে আসা দোলের দিনগুলো মনে করে আজকাল কেমন যেন একা লাগে। বাবা মা সময়ের ভাঁজে হারিয়ে গিয়েছে। ভাই-বোনদের সঙ্গে রং খেলার সেই আনন্দ এখন শুধুই স্মৃতি! শুধু মনে হয়, কেউ কি এখনও দোলের সকালে হারমোনিয়াম বাজিয়ে পাড়ায় পাড়ায় গান গেয়ে বেড়ায়! আর কোনও নবকার সঙ্গে দেখা হয় দীপ্তিদির? শূন্য একটা বাগান বুকের মধ্যে লুকিয়ে আর কোনও বিধানদা বেঁচে থাকে এই কলকাতা শহরের কোনও পুরনো পাড়ায়! আর ফুটকড়াই! এখনকার ছেলে মেয়েরা কি জানে, ফুটকড়াই কী? বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে খেলে এর স্বাদ কেমন হয়!
আমি শুধু আশা রাখি, বুড়ির ঘর পোড়ানোর পরে সেই আলু মাখার স্বাদ আজও নিশ্চয়ই অমলিন! আজও আবিরের গন্ধে বাতাসে শিমুল ফোটে! পলাশ রাঙিয়ে ওঠে! প্রকৃতি তার দরবেশের রংচঙে আলখাল্লা পরে পথের ধুলোয় নামে। কোথাও কোনও ছোট্ট ছেলে রং মেখে জড়িয়ে ধরে তার মাকে! আশা রাখি আজও, দোলের মিছিল থেকে হাওয়ায় ওড়ে আবির-বাষ্প! শোনা যায় সমবেত আনন্দস্বর— “হোলি হ্যায়!” আজও দোলের দিনে সেই একটি মেয়েকে এক বার গালে রং দেবে বলে অপেক্ষায় থাকে কোনও একাকী যুবক। আশা রাখি আজও সবার ভালবাসার স্পর্শে রাঙিয়ে ওঠে দোল!
আর আজও কোনও সোমাদি ছোট্ট কোনও রাজাকে জিজ্ঞেস করে, “কী রে, দোল খেলবি না?”
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)