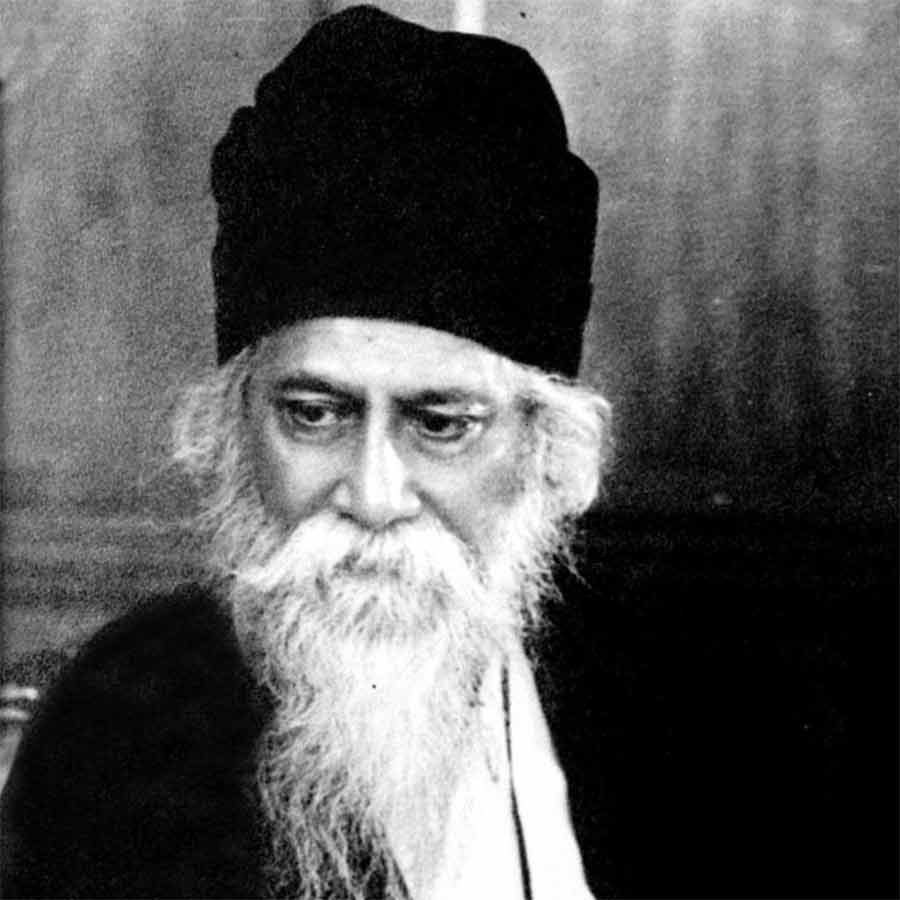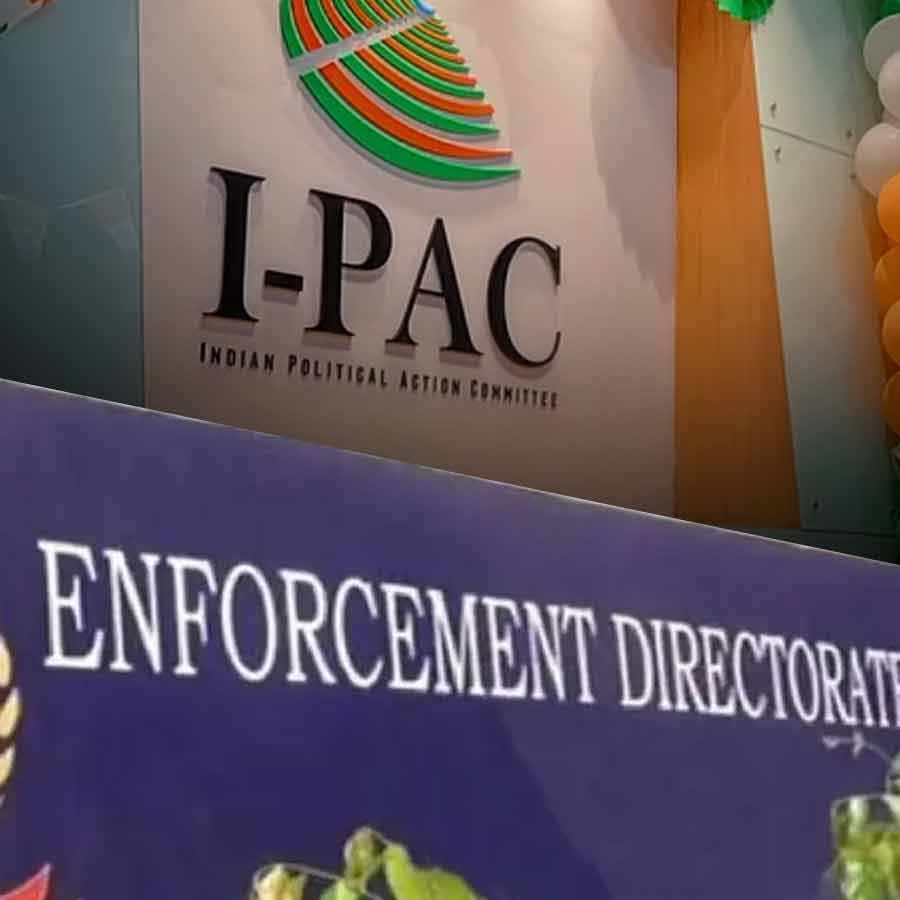কোথায় পাবো তারে..
সেই আশির দশকে শান্তিনিকেতনে পড়তে আসা একটি মেয়ে সারা জীবন ধরে রবীন্দ্রনাথকে খুঁজতে খুঁজতে বুঝেছে, তাঁকে এক সংজ্ঞায় ধরা সহজ নয়। বহমান ধারার মতো অদৃশ্য তিনি ছেয়ে আছেন সর্বত্র, স্পর্শ করতে চাইলেই কি পারা যায়? সুখে-দুঃখে আনন্দে-পরিতাপে বঙ্গহৃদয়ে তাঁর স্মরণ যেন চিরন্তন। এত দিনে লাখখানেক গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে এক তিল পরিমাণ অনাবিষ্কৃত নেই তিনি। হর্ষময় না রহস্যপ্রিয়, সরকারি না আটপৌরে, আবেগঘন সংলগ্নতা না শান্ত বিচ্ছিন্নতা, মিলের জাদুকর না মিলহীনতা, দেশের প্রতি ভালবাসা না দেশপ্রেমের বাড়াবাড়ি ও জাতীয়তাবাদ নিয়ে উপহাসের চাবুক, কোন দিক দিয়ে সে ধরবে তাঁকে?
যখন কচিকাঁচারা রং-তুলিতে স্যান্টা ক্লজ়ের মতো চিরকেলে দাদুকে কিছু না বুঝেই পেন্নাম ঠুকছে, যখন ল্যাম্পপোস্ট থেকে এভারেস্ট অবধি জাতীয় সঙ্গীত গমগম করছে, কেউ কেউ লিখতে চাইছেন রবীন্দ্রসঙ্গীত, কেউ বা তাঁর জোব্বা পোশাক দেখে তির্যক ভঙ্গিতে বলছেন তিনি যথেষ্ট স্বদেশি নন, তখন তাঁকে কী ভাবে ফিরে দেখবে কালের নিয়মে কিশোরী থেকে প্রৌঢ়া হয়ে যাওয়া সেই মেয়ে?
ঘরে-বাইরে ফ্রেমের ভিতরে যাঁর ছবিতে নিত্য পুষ্পমালা দোলে, আসলে তিনি চৌখুপি ফ্রেমের বাইরের মানুষ। বহুমুখী ও অবিরাম রচনাপ্রবাহের ধারায় তিনি বিশ্ববাসী বাঙালি তো বটেই, আরও বহু ভারতবাসীর আশ্রয়। এই নিরীশ্বর বাঙালির ঈশ্বর, রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে বুদ্ধদেব বসু কি সাধে লিখেছেন, “বাংলা ভাষায় যতদিন পর্যন্ত কবিতা লেখা হবে তিনিই ভাষার আদি উৎস বলে স্বীকৃত হবেন”!
বাঙালির মনের ভিতর রবীন্দ্রনাথ এমন ভাবে রক্তমজ্জায় মিশে গিয়েছেন, ঘনিষ্ঠ পরিজন ছাড়াও অল্প সময়ে দেখা হওয়া কত সাধারণ, নামহীন মানুষকে তিনি লতার মতো বেষ্টন করে রয়েছেন, তা দেখে এখনও বিস্মিত হয় মেয়েটি।
আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ, জানে তাকে এ কালিম্পং
রেভারেন্ড ডক্টর জন অ্যান্ডারসন গ্রাহাম নামটা কালিম্পঙের একটি নির্দিষ্ট এলাকাতেই পরিচিত। ইংল্যান্ড থেকে মিশনারির কাজ নিয়ে আসা গ্রাহাম সাহেবের চোখে পড়ে পার্বত্য এলাকায় নানা কাজে আসা ইউরোপীয় সাহেবদের সঙ্গে স্থানীয় মহিলাদের বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের কিছু করুণ পরিণতি। তাঁদের তথাকথিত জারজ সন্তান এই ইউরেশীয়রা, বেশির ভাগ পিতৃস্নেহবঞ্চিত। মূলত এই দেশ ও পরিচয়হীন, সমাজে ব্রাত্য হয়ে থাকা শিশুদের জন্য কালিম্পঙের ডেলো পাহাড়ে ১৯০০ সালে তৈরি করলেন আশ্রমসদৃশ এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যা পরবর্তী কালে ‘ডক্টর গ্রাহাম’স হোম’ নামে খ্যাতিলাভ করে। ধীরে ধীরে সেখানে কাগজ তৈরি থেকে বিভিন্ন রকম হাতের কাজ শেখানো শুরু হয়। ছাত্রদের নিজেদের কাজ নিজে করতে হত। দৈনন্দিন সাংসারিক কাজ শিখে নেওয়ার মধ্যে যে হীনতা নেই, বরং তা আত্মবিশ্বাস বাড়ায়, তা যেন রবীন্দ্রনাথের আশ্রম বিদ্যালয়ের আদর্শের মতো হুবহু এক।
খবরের পাতা ওল্টালে দেখতে পাই, স্বাস্থ্যোদ্ধার এবং প্রকৃতিসান্নিধ্যে সময় কাটাতে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৮ সালের এপ্রিলে প্রথম বার কালিম্পঙে যান। তখন থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে তিনি কালিম্পঙে অন্তত চার বার এসেছিলেন। এখানে বসেই ‘জন্মদিন’ কবিতাটি লেখেন। কালিম্পং থেকে সম্প্রচার বড় সহজ ছিল না, তবুও তাঁর তৎকালীন আবাস গৌরীপুর ভবনেই টেলিফোন সংযোগের ব্যবস্থা করা হল। আকাশবাণী-তে কবিতাটি পাঠ করলেন রবীন্দ্রনাথ। ঘটনাচক্রে ঠিক একই বছরে জন্মানো রবীন্দ্রনাথ ও গ্রাহাম সাহেবের যোগাযোগ হয় ওই আটত্রিশ সালেই। রবীন্দ্রপ্রয়াণের পর তাঁর প্রতিষ্ঠানে কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথের জন্য বিশেষ শোক জ্ঞাপন করছেন অতি অল্প সময় সান্নিধ্য পাওয়া প্রত্যন্ত পাহাড় এলাকার মিশনারি গ্রাহাম সাহেব।
বনদেবীর দ্বারে দ্বারে গভীর শঙ্খধ্বনি
এক বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বনভূমিতে যখন বুলডোজ়ারের হুমকি, আগুনের হলকায় ভীত ময়ূরের তীক্ষ্ণ কেকাধ্বনি ও পলায়নোদ্যত হরিণদলের ছবি আপনাকে অসাড় করে দিচ্ছে, যখন পাহাড় টিলা বন পুকুর সব গুঁড়িয়ে বুজিয়ে উন্নয়নের জঙ্গল তৈরি হচ্ছে, তখন একদা রসালবৃক্ষহীন, শুধু তালগাছ বা গ্রীষ্মে রুদ্র বাতাস যেখানে স্বয়ং মাটিতে হেঁটে বেড়ায়, এমন এক জায়গার কথা আপনার মনে পড়তে পারে। রুক্ষ ঊষর ভূমিতে এক আশ্রমসদৃশ বিদ্যালয় তৈরি করলেন রবীন্দ্রনাথ, যা কালে কালে দেশ-বিদেশের গাছে ভরে গেল। কত কাল পরেও ছাত্রছাত্রীরা রীতিমতো সাধারণ জ্ঞানের প্রতিযোগিতায় মেতে থাকল, কে এসেছে কবির সঙ্গে বুয়েনোস আইরেস থেকে, কে বা জাভা বালি শ্রীলঙ্কা থেকে। আশ্রমের ভিতর হরিণ ময়ূর হয়তো এল না, কিন্তু প্রতিটি ঋতু স্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য হরেক বর্ণ গন্ধের ফুল, এমনকি সবুজ বনপুলক অবধি সাক্ষী দেওয়ার জন্য হাজির হয়ে গেল। যখন বন সংরক্ষণ, প্রকৃতি-বিষয়ক সচেতনতা গড়ে ওঠার কোনও কারণ ছিল না, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখায়, আশ্রম বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের মনের ভিতরে প্রকৃতিকে, তার গুরুত্বকে একেবারে মর্মে প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছেন।
যে মেয়েটি রবীন্দ্রনাথকে খুঁজতে বেরিয়েছে, সেও তো এমন বৃষ্টিদিনে বন্ধুদের সঙ্গে হইহই করে শ্যামবাটী পেরিয়ে কোপাইয়ের দিকে চলে যেত। প্রকৃতির সঙ্গে এই মেলামেশা প্রকৃতির উপকারের জন্য নয়। মানুষ যে আর একটি প্রাণীমাত্র, প্রকৃতির সন্তান, এটি মর্মে মর্মে বুঝিয়ে দেওয়াই ছিল রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য। না চাইলেও মেয়েটি ও তার বন্ধুদল প্রতিটি ঋতু নিখুঁত ভাবে টের পেয়ে যেত। ওই খর গ্রীষ্মে কুর্চির সুবাস, ঠাস করে ইতিউতি পড়া তাল কুড়োনো, ওই ফুঁসে ওঠা বর্ষায় ক্যানালের রুদ্ররূপ, ঝড়ে পড়ে যাওয়া উত্তরায়ণের আম-তেঁতুল, শ্যামবাটীর দিকে কেয়াঝোপ, শরতে কোপাই নদীর পাশে কাশফুল আর হেমন্তের ধান ওঠা খরখরে মাঠ, শীতের হাওয়ায় ঝিরঝিরে আমলকি বনের কেঁপে ওঠা— এ সব যে দেখে, তাকে আর কোনও দিন বই মুখস্থ করে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার প্রবন্ধ লিখতে হয় না। এমন আজব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কি দেখা গেছে, যেখানে শিক্ষকরা বৃষ্টিতে ভিজতে উৎসাহ দিচ্ছেন? প্রকৃতির সঙ্গে মিলে সহজে আনন্দ করার শক্তি ও অভ্যাস, কালবৈশাখীর ঝড়ে কোনও মতে নিজেকে সামলে রাখা, বর্ষার মুষলধারায় চুপচুপে ভিজে যাওয়ার মধ্যে যে অপরিসীম চরিতার্থতা আছে— রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কে শেখাতেন?
যে মেয়েটি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে খুঁজতে গেছিল, সে প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিল! শুনেছিল, একেবারে নিচু ক্লাস থেকে দশম শ্রেণি অবধি যাঁরা পড়ান, আরও উচ্চ শ্রেণির শিক্ষকদের সঙ্গে তাঁদের মান-মর্যাদায় কোথাও কোনও তফাত নেই। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এখানে কেউ হেলাফেলার লোক মনে করে না।
নিচু ক্লাসে প্রকৃতি পরিচয় শেখাতে গিয়ে শিক্ষক এক ছাত্রীকে বলছেন, বাড়ি যাতায়াতের পথে শালিক দেখে, তারা নিজেদের মধ্যে কী ভাবে কথা বলে সেটা শিখে আসতে। পরদিন তার বাড়ির কাজ।
দু’টি শালিকের নিজেদের মধ্যে কথা নকল করে শোনাল ছাত্রীটি! গুমোট গরমে ভোর ভোর জুতো-মোজা-টাই পরে পিঠে কচ্ছপের মতো শিক্ষার বোঝা চাপিয়ে যে ছোট ছেলেপুলেরা আলস্য ও বিরক্তি নিয়ে বাসে ওঠে, তাদের যদি এই শিক্ষা দেওয়া হত? কেন্দ্রীয় শিক্ষা সংস্কারে যখন শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশমূলক শিক্ষা, কারিগরি বা বৃত্তিমূলকে জোর, তথ্যমাত্র নয়— তার হাতে-কলমে প্রয়োগের দিকে নজর দিতে বলা হয়, তখন মনে হয়, হাতের কাছে পড়ে থাকা সোনাকে আমরা কাচের টুকরো বলেই অবহেলা করে এলাম। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতি এ ভাবেই একই সঙ্গে ‘মেনস্ট্রিম’ এবং ‘সাবঅল্টার্ন’।
দুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভরে
বড় রবীন্দ্রনাথকে খুঁজতে গিয়ে সংসারে থাকা মানুষটিকে যখন দেখি, দিনাতিদিনের ক্লেশ আর পাঁচটা আম আদমির চেয়ে বড় কম নয়। তৎকালীন আর পাঁচটি কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মতোই, বিশেষ করে যে কন্যা মাতৃহীন, একক পিতা হিসেবে তার দায় ছিল ঢের বেশি।
বন্ধু প্রিয়নাথ সেন রবীন্দ্রনাথের বড় মেয়ে মাধুরীলতার সঙ্গে বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র ওকালতি ব্যবসায়ী শরৎকুমারের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ আনেন। খানিক কথাবার্তা চলার পর বিশ হাজার টাকা পণের দাবিতে পরিণতি থমকে যায় প্রায়। প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ সরে আসতে পারতেন, কিন্তু ওই সেই কন্যাদায়! দেখি যে প্রিয়নাথের বাড়ি বার বার যাতায়াত করছেন, বিহারীলালের অন্য দুই কর্তাব্যক্তি ছেলের সঙ্গে কথা চলছে। অবশেষে রফার পর তা ঠেকল দশ হাজারে। গল্প এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু তা হল না। পাত্রপক্ষের দাবি বিয়ের তিন দিন আগেই ওই টাকা মিটিয়ে দিতে হবে। ঠাকুর কোম্পানির জন্য ঋণভারগ্রস্ত রবীন্দ্রনাথ টাকা দিতে পারছেন না বলে প্রিয়নাথ সম্ভবত অন্য কোনও জায়গা থেকে ধার নিয়ে টাকা মিটিয়ে দেওয়ার কথা বলেন, এবং মহর্ষির কানে যেন এই অপমানের খবর না যায় সেটাও জানান। পিতৃভক্ত রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সেটা সম্ভব হয়নি। যথারীতি মহর্ষি অপমানিত বোধ করেন, “কিন্তু বিবাহের পূর্বেই যৌতুক চাহিবার কি কারণ? আমার প্রতি কি বিশ্বাস নাই?” তিক্ত হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথকে লেখেন, “প্রথমে আমি সম্মতি দিয়েছিলাম তার কারণ আমি মূঢ়।” এই মূঢ়তার ভার তিনি চিরকাল বহন করার জন্য প্রস্তুত থাকবেন, কিন্তু পরিবারের উপর তুলে দিতে পারবেন না, এমনটাও জানাচ্ছেন।
অজস্র অপমানের ঘটনা তাঁর সাফল্যের পাশাপাশি হেঁটে চলেছিল। আজ আমরা যখন শুধু সুখের উদ্যাপনে ব্যস্ত, কঠিন সহ্য করতে গেলে নিজেকে বঞ্চিত মনে করি, তখন এই ঘটনাগুলি পাশে এসে দাঁড়ায়। আমরা পড়ি ঠিকই রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু উপলব্ধি করতে চাই না। কারণ সে পথে কোনও শর্টকাট পদ্ধতি নেই। যিনি সারা জীবন রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে রাখলেন সেই কবি শঙ্খ ঘোষের কথা ব্যবহার করে বলা যায়, এই শিক্ষার সহজ কথা ঠিক ততটা সহজ নয় মোটেই।শান্তিনিকেতনীদের প্রায়শই ঘোর ‘ক্ল্যানিশ’ আর ঈষৎ নম্র ন্যাকায় বিভূষিত করা হয়ে থাকে। আশ্চর্য ভাবে ওই অতকাল আগে তথাকথিত পৌরুষের চর্চাটিকে সযত্নে পরিহার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।
রবীন্দ্রশিক্ষায় পরিশীলিত ভদ্রতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, যাকে বাদবাকি বঙ্গসমাজ ন্যাকাপনা মনে করেছিল। এই ভদ্রতাবোধ এমন রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল যে, হস্টেলের সহায়িকা বা পাহারাদার কর্মী মহিলাদের কোনও ভাবেই অবহেলার দৃষ্টিতে দেখতে শেখেনি ছাত্রছাত্রীরা। ছুটিতে, পরবে তাদের বাড়িতে অনায়াস যাতায়াত ছিল। সেখানেও তারা বাবুদের বাড়ির ছেলেপুলে বলে বিরাট কিছু সম্ভ্রম দেখাত না। আমাদের অনেকের ঝুলিতেই, বাঁধনা পরবের পোড়া মাছের আর ঈষৎ গেঁজে ওঠা তালমদিরা মাতালের গল্প আছে। আর ‘ক্ল্যানিশ’-এর উত্তরে বলা যায়, পৃথিবীর জাত-ধর্ম নির্বিশেষে যে যেখানে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাকে আঁকড়ে রেখেছেন, তিনিই এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। আজ সমগ্র দেশ জুড়ে ধর্মের আচারকে কেন্দ্র করে তার উদগ্র বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। আমরা যারা এখনও স্তম্ভিত, ব্যথিত হয়ে থাকি, অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ তাদের হাতিয়ার। আজ সদর্থেই ‘ক্ল্যানিশ’ রাবীন্দ্রিকদের অতি প্রয়োজন।
‘সহজ পথে চলব ভেবে পড়ব না’
একঘেয়ে পরিশ্রমী রুটিনের বিরুদ্ধে বঙ্গ বুদ্ধিজীবীর এক ধরনের অবজ্ঞা আছে। রবীন্দ্রনাথ সেখানেও ব্যতিক্রমী। কবি-লেখকের হুল্লোড়ে শৃঙ্খল-বহির্ভূত জীবন যাপনে আমরা যারা শ্রদ্ধায় শিহরিত হই, তাঁদের জন্য একটি নিয়ম-সারণি দেখে নেওয়া যেতে পারে। সৈয়দ মুজতবা আলী, রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রিয় ছাত্র লিখছেন, “সকালে চারটার সময় দু ঘণ্টা উপাসনা করতেন। তারপর ছটার সময় স্কুলের ছেলেদের মত লেখাপড়া করতেন। সাতটা, আটটা, নটা, তারপর দশ মিনিটের ফাঁকে জলখাবার। আবার কাজ— দশটা, এগারোটা, বারোটা। তারপর খেয়ে দেয়ে আধঘণ্টা বিশ্রাম। আবার কাজ— লেখাপড়া; একটা, দুটো, তিনটে, চারটা, পাঁচটা— কাজ, কাজ, কাজ। পাঁচটা থেকে সাতটা ছেলেমেয়েদের গান শেখাতেন বা দিনুবাবুর আসরে বসে গান শুনতেন বা গল্প-স্বল্প করতেন। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে আবার লেখাপড়া, মাঝে মাঝে গুনগুন করে গান— আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত। কী অমানুষিক কাজ করার ক্ষমতা! আর কি অপরিসীম জ্ঞানতৃষ্ণা!” অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় পড়তে আসা অবাঙালি বা বিদেশি ছেলে মেয়েদের সঙ্গে এখানে পড়তে আসাদের তফাত আছে। এখানে যারা আছেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে আসেন আর সারা জীবন তাঁকে কোথাও যেন পাশে রেখে দেন। নব্বইয়ের শুরুতে হাতখরচের জন্য এক বিদেশি মহিলার গবেষণার সঙ্গী হতে হয়েছিল। তখন গুগল বিস্ফোরণের যুগ নয়, বাংলা না জানার কারণে অস্ট্রেলিয়ার মানুষ রুথের দোভাষী হতে হল। তাঁর গবেষণার বিষয়টিও অভিনব। তাঁর দেশে রবীন্দ্রনাথকে ‘প্রাচ্যের সন্ত কবি’ মনে করার যে প্রাচীন প্রবণতা আছে, সেটিকে খণ্ডন করতে চান তিনি। বিদেশিনিকে সাহায্য করতে গিয়ে রবীন্দ্র ভবন থেকে নানা পত্রিকা নামিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অশ্লীলতার অভিযোগ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছিল মেয়েটি।
কারও স্মৃতিকথায় পড়েছে, জওহরলাল নেহরু সপরিবার শান্তিনিকেতনে বেড়াতে আসছেন। একদা এখানকার ছাত্রী ইন্দিরা তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে সহজ ভাবে পৌষমেলায় ঘুরছেন।ইন্দিরা যে ছাত্রীনিবাসে থেকেছেন, সেখানেই থাকে এই মেয়েটি। সমাবর্তনের সময় এক চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটল সেখানে। ইন্দিরা-পুত্র প্রধানমন্ত্রী রাজীব তখন তাঁদের উপাচার্য। হস্টেলের নানা সমস্যা নিয়ে বেদম হইচই প্রতিবাদ শুরু হলে স্বয়ং তিনি চলে এলেন হস্টেলের কমনরুমে। রাত ন’টা বেজে গেছে, ফলে মেয়েরা রাতপোশাকেই। কমনরুমে রাজীব এসেছেন, ফলে সবাই দুদ্দাড়িয়ে দৌড়। প্রথমেই রাজীবের দেহরক্ষীদের বাইরে বার করে দেয় মেয়েরা। হলের মধ্যে আদ্যিকালের কাঠের বেঞ্চে পদ্মপলাশলোচন রাজীব গান্ধী বসে আছেন, চার পাশে ভিড় করে শ্রীসদন বা ভবনের মেয়েরা। স্মিত হেসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মায়ের হস্টেলের আবাসিকদের কাছে শুনছেন, কোন একটি ব্লকে ভাল ভাবে জল আসে না, কল কাজ করে না, কোথায় চৌবাচ্চা নোংরা, কোন একটি ঘর বিশেষ গরম, পিছনের পাঁচিল ঠিক ততটা সুরক্ষিত নয়! ওই রাত্তিরে মেয়েদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে পরের দিন উনি আবার হস্টেলের ভিতরে এসে দেখে-টেখে গেছিলেন। যদিও তাতে অবস্থার কোনও পরিবর্তন ঘটেনি! সুরসিক রবীন্দ্রনাথ এ সব দেখতে পেলে অবশ্যই মন্তব্য-সহ মুচকি হাসি উপহার দিতেন।
আর এক গল্প শোনা যেতে পারে। সদ্য শেষ হওয়া কলকাতা বইমেলায় এক গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত কবি-সাহিত্যিক জড়ো হয়েছেন। কলকাতার রাশিয়ান কনসুলেটের সদ্যনিযুক্ত কনসাল জেনারেল ম্যাক্সিম কজলভ উপস্থিত। শোনা গেছে তিনি নাকি বাংলা একটু-একটু বোঝেন, বলেনও। চলছে অনুষ্ঠান। চুপচাপ শুনছেন তিনি। কথা চলছে প্রকৃতি নিয়ে। বলতে বলা হল তাঁকে। বললেন, শিমুলতলার বাংলা বিভাগ থেকে হস্টেলের পাশ দিয়ে সোজা উত্তরায়ণের দিকে রাস্তা, ছাতিমতলার পিছন দিয়ে উদ্যান বিভাগের অত গাছ, গোয়ালপাড়া কোপাইয়ের দিকে বৃষ্টিতে ভেজা... এই সব আরও আরও জায়গা, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি তাঁর ছাত্রাবস্থায় রাশিয়ার বাইরে দেখা এক আশ্চর্য সৌন্দর্যময় পৃথিবী। প্রসঙ্গত বললেন, রবীন্দ্রনাথের জন্যেই আশির শেষ দশকে বাংলা বিভাগে পড়তে এসেছিলেন তিনি। কবিরা চুপচাপ। কেউ কেউ যে একটু আগে ভাবছিলেন ইউক্রেন নিয়ে কৌশলে কথা তুলবেন, শান্তিনিকেতনের অপরূপ বৃষ্টি আর কালবৈশাখীর ঝড় তাকে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।প্রায় পনেরো-ষোলো বছর আগের কথা। ভারতীয় লেখকদের একটি ছোট্ট দল কানাডার বিভিন্ন শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিতা গল্পপাঠ আলোচনায় অংশ নিচ্ছে। গুজরাতের কবি প্রবোধ পারিখ এর পরেই যাবেন স্পেন, বক্তৃতার বিষয় সেই রবীন্দ্রনাথ। এ বিষয়ে দলের সর্বকনিষ্ঠ কবি মেয়েটির শান্তিনিকেতনে পড়ে আসার কারণে গোপনে একটু গেরামভারি ভাব তো আছেই। অনুষ্ঠান চলছে ভ্যানকুভারের ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেমিনার হলের দোতলা-সমান কাচের দেয়ালের পর্দা কেউ একটা সরিয়ে দিল। আর অমনি মেয়েটির চোখ গেল পিছনে নানা বিদেশি বৃক্ষের অঙ্গনে এক আবক্ষ মূর্তির দিকে। রবীন্দ্রনাথ! এখানেও তিনি? তার পর আর কী, স্থান-কাল-পাত্র ভুলে ছাত্রী জীবনের মতো ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে ঠিক তাঁর পাশে গিয়ে একটা ছবি তুলে ফেলা!
কোথা হা হন্ত, চির বসন্ত! আমি বসন্তে মরি
রবীন্দ্রসঙ্গীত ও কবিতা যে কত ভাবে মানুষকে নাড়া দেয়, তা শান্তিনিকেতনের ছেলেপুলেরা হাড়ে হাড়ে জানে! যেমন এক বসন্ত উৎসব, থুড়ি দোলের আগের রাতে উপাসনা মন্দিরের সামনে রাস্তায় এক টুরিস্ট দলের আবেগ উপস্থিত হয়। গান তাঁরা জানেন না, তাই বলে কি রবীন্দ্রনাথ চাপা পড়ে থাকবেন? প্লাবিত জ্যোৎস্নারাতে উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি শুরু হয়, ‘আজি এ প্রভাতে রবির কর/ কেমনে পশিল প্রাণের পর...’ রবীন্দ্রনাথের আবাস উত্তরায়ণের একেবারে পিছনে মাটির বাড়ি শ্যামলীর ভিতরে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর একটি ছবি দেখে তাঁকে ইন্দিরা গান্ধী বলে অম্লানবদনে শনাক্ত করেছেন এক টুরিস্ট। রথীন্দ্রনাথের ছবি রবীন্দ্রনাথের বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞরা এ সবে ভ্রু কুঞ্চিত করতে পারেন, কিন্তু আমজনতার তাতে বয়েই গেল! তাঁরা আছেন বলেই ঘরে ঘরে গীতা, বাইবেল, কোরানের পাশে রবীন্দ্র-রচনাবলি সম্ভ্রমে সজ্জিত থাকে। বিশ্বভারতীর প্রকাশনা সংস্থা থেকে এখনও রবীন্দ্রনাথের বইয়ের বিপুল বিক্রির খবর পাওয়া যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেয়ে থাকে গীতবিতানপ্রেমীদের স্নানঘরের শখের গান। তার মধ্যে অল্পবয়সি-সহ মধ্যবয়সিরাও বিরাজমান। আর কিছু না থাকলেও যে গান থেকে যাবে বলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রত্যয় ছিল, যে গানের সুরের ভরকেন্দ্র কথা, তা কত জনকে স্পর্শ করেছে, জানে সব্বাই। রবীন্দ্রনাথকে খুঁজতে বসা মেয়েটি আশ্রমের শিক্ষায় শিক্ষিত নবীন প্রজন্মের গায়িকাদের প্রশ্ন করেছিল, কেন এখনও তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাছেই ফিরতে চান। এ প্রশ্নের উত্তরে সাহানা বাজপেয়ী বলেন, “শান্তিনিকেতনে বড় হয়ে ওঠার যে ক’টি আশীর্বাদ পাওয়া যায়, তার মধ্যে অন্যতম এক আশীর্বাদ রবীন্দ্রনাথের গান। দৈনন্দিনতার জগাখিচুড়ি সমাজমাধ্যমের উত্তেজক অথচ ক্ষণস্থায়ী ডোপামিন বোঝাই অস্থিরতার বাইরে যে জগৎটি রয়ে গেছে, আমার মনে হয় তাকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা ও গাওয়া ধরে রাখতে পারে। এই জন্যই, আমি বার বার রবীন্দ্রনাথের গানেই ফিরে যাই।”
অপরাজিতা চক্রবর্তীর মুখে শুনি, আজকের প্রজন্মকে যে পরিমাণে দৈনন্দিন প্রতিযোগিতায় মানসিক অবসাদের সম্মুখীন হতে হয়, রবীন্দ্রনাথ সেখান বিরাট আশ্রয়। আর এক নবীনা প্রকৃতি মুখোপাধ্যায়ের কথায়, “তিনি চিরন্তন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে আনন্দে উদ্যাপন করতে শিখিয়েছেন।”ঢাকা শহরে রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পী সন্জীদা খাতুনকে তাঁর অনুরাগী ও শিক্ষার্থীরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের মাধ্যমেই শেষ বিদায় জানিয়েছেন। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রীর প্রয়াণ-পরবর্তী নিয়ম পালনে উদার সাংস্কৃতিক চর্চার এই প্রকাশ এক সময় স্বতঃসিদ্ধই মনে হত। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সংস্কৃতি ও ধর্মকে পৃথক করে দেখার দৃষ্টিটি যেন হারিয়ে গেছে। সন্জীদা খাতুন রবীন্দ্রনাথের গানকে তার যথার্থ ভাবনায় নিজের সমগ্র জীবনে বহন করলেন, শিক্ষার্থী-সহ বহু সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। এ-ই তো চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমরা যারা রবীন্দ্রনাথকে দেখলাম না, তারা এমন একক মানুষের শান্ত ও স্পর্ধিত নীরব প্রতিবাদ দেখলাম।ওই যে মেয়েটি নিজস্ব রবীন্দ্রনাথকে খুঁজতে বসে দেখতে পাচ্ছে, কাঁকর মেশানো শালবীথি দিয়ে হেঁটে আসছে যে ছায়াশরীর, তিনিই তো শিখিয়েছেন, এই সভ্যতার সঙ্কটে প্রতিরোধ ছাড়া পন্থা নেই, নিন্দা ছাড়া অস্ত্র নেই, স্বাধীন দেশ হলেও প্রকৃত স্বাধীনতা থাকে না কখনও কখনও।
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)