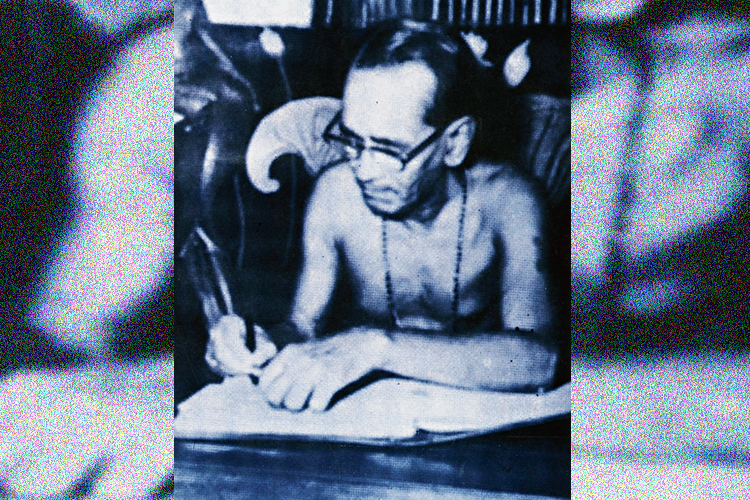রাশি রাশি সাদা গোলাপি পদ্মফুল আর সারা বেলা জুড়ে পদ্মগন্ধ। আমার দাদু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনের স্মৃতি। ছোটবেলায় নাতি-নাতনিদের কাছে দাদুর জন্মদিনটা বাৎসরিক মহোৎসব ছিল। তাঁর জীবদ্দশায় বছর বছর এই রকম জন্মদিন পালন করায় দাদুর নিজের কতটা লাভ হয়েছিল জানি না, কিন্তু আমাদের লাভ ছিল ষোলো আনা। সন্ধেবেলায় খাওয়াদাওয়া হত। লেখকদের মেলা বসে যেত। তাঁরা সবাই দাদুকে নিজেদের লেখা বই উপহার দিতেন। গান হত। এক বার পঙ্কজকুমার মল্লিক এসে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনিয়েছিলেন। সে ছিল এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
ওই দিন সারা সকালটা আমাদের চলে যেত রাশি রাশি পদ্মকুঁড়ির উপর আলতো চাপ দিয়ে ফুল ফোটানোর কাজে। এই পর্বে আমাদের নেত্রী ছিল ভাইবোন-গ্রুপের সকলের বড়দিদি শকুন্তলা। এ যখনকার কথা, তখন তাঁর বয়সও বছর বারোর বেশি নয়। আমাদের তো পাঁচ-ছয় থেকে শুরু। এর পর বড়রা হাত লাগিয়ে সোনার মতো ঝকঝকে পেতলের কলসে করে সেই সব ফোটা পদ্ম সারা বাড়ির নানা জায়গায় বসিয়ে দিতেন। আজও তাই দাদুর সঙ্গে ওতপ্রোত মিশে আছে পদ্মগন্ধ।
বাইরে থেকে দেখলে দাদু ছিলেন শ্যামবর্ণ, শীর্ণ, সাধারণ চেহারার এক মানুষ। আসলে ছিলেন শৌখিনও। স্নানের আগে গায়ে দিতেন সুগন্ধ তেল। মাথায় জবাকুসুম। স্নান শেষেও গায়ে দামি কোম্পানির ভারী মিষ্টি সুগন্ধি ক্রিমের প্রলেপ। তাই আমাদের কাছে দাদু মানেই সুগন্ধ। এমনকি তাঁর আঙুলের পান্নার আংটিটা থেকে পর্যন্ত সৌরভের আভাস পাওয়া যেত।
দাদুর থেকে সরাসরি আহ্লাদ যতটা না পেয়েছি, তার চাইতে অনেক বেশি পেয়েছি গভীর জীবনশিক্ষা। কাকভোরে অন্ধকার থাকতেই উঠতেন। নিজে বাগান থেকে ফুল তুলে সংক্ষিপ্ত পূজা করতেন। তার পর বিস্কুট সহযোগে গরম চায়ে চুমুক। এর পরেই বাড়ির সামনের পার্কটার ও পারে সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে হাঁক দিতেন, ‘‘শৈলজা, শৈলজা..।’’ ওপরের বারান্দা থেকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাতেন শৈলজানন্দ, ‘‘এসে গেছ তারাশঙ্কর—।’’ এই ছিল ওঁর সকালবেলার প্রাত্যহিকী। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কিন্তু বাড়ি এসে সোজা লিখতে বসে যেতেন। লিখতে লিখতে কোনও দিন বেলা একটা, কোনও দিন দেড়টা বেজে যেত। বাড়ির ভিতর থেকে স্নানে যাওয়ার ডাক পড়লেও লেখার অভীষ্ট জায়গায় না পৌঁছে কখনও আসন ছেড়ে উঠতেন না। এর পর স্নান করে দীর্ঘ সময় ধরে পুজো। পুজোর শেষে সংক্ষিপ্ত খাওয়াদাওয়া। ক্রনিক উদরাময়ের কারণে ডাক্তারের পরামর্শে মধ্যাহ্নভোজে প্রত্যেক দিনই ছোট্ট এক বাটি ভাত আর নুন-হলুদ দিয়ে সেদ্ধ করা অল্প একটু মাংসের স্ট্যু খেতেন। পাতে কখনও একটু উচ্ছেভাজা বা বড়িভাজা, সঙ্গে দু-তিন রকম ট্যাবলেটের ঝুরো। দাদু অম্লানবদনে বড়িভাজার মতো করেই সেই ট্যাবলেটের গুঁড়ো ভাতে মাখিয়ে খেয়ে নিতেন। খাওয়ার শেষে মাংসের বাটিতে তিন টুকরো মাংসের মধ্যে এক টুকরো মাংস আর একটুখানি ঝোল রেখে দেওয়া ছিল দাদুর প্রাত্যহিক নিয়ম। নির্দেশ ছিল ওই প্রসাদটুকু পালা করে এক-এক জন নাতি-নাতনি পাবে।
মায়ের কাছে শুনেছিলাম, দাদু মাঝে মাঝে আমার মাকে গানের সুরও সংশোধন করে দিতেন। তখন আমার মা গঙ্গা নিতান্ত বালিকা। গানের মাস্টারমশাই মাকে হারমোনিয়াম বাজিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাতেন। মাস্টারমশাইয়ের শেখানো সুরে ভুল থাকলে গান গেয়ে সে সুর সংশোধন করে দিতেন স্বয়ং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তারই মধ্যে একটি গান ছিল— ‘তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে তুমি ধন্য ধন্য হে।’

আমেদপুর-কাটোয়া ছোট লাইনের রেললাইন বসার সময় অনেক ইউরোপিয়ান সাহেব সাময়িক ভাবে লাভপুরের কাছাকাছি জায়গায় বসবাস শুরু করেছিলেন। কাজ শেষ হতে তাঁরা সংসার গুটিয়ে অন্যত্র চলে যান, সেই সঙ্গে নিজেদের ব্যবহৃত আসবাবপত্রগুলিও বিক্রি করে দিয়ে যান। ওই সব আসবাবের সঙ্গে একটি অর্গ্যানও ছিল। ছোট্ট ফোল্ডিং অর্গ্যান। মিষ্টি গম্ভীর আওয়াজ। দাদু সেটা কিনে নেন। শুনেছি, সেই অর্গ্যানটা দাদু নিজে বাজাতেন। আমি অবশ্য কখনও তাঁকে বাজাতে দেখিনি।
বাণীমা’কে (তারাশঙ্করের ছোট মেয়ে) অর্গ্যান বাজিয়ে গান করতে শুনেছি— ‘অলকে কুসুম না দিয়ো’। এ তো গেল আমার একেবারে শিশু বয়সের কথা। আরও বেশ ক’বছর পরের কথা— দাদু তখন সদ্য সদ্য ‘জ্ঞানপীঠ’ পেয়েছেন। ‘গণদেবতা’ উপন্যাস নিয়ে তখন খুব চর্চা চলছিল। এক বার চট করে পড়ে নেওয়ার জন্য অনেকেই তখন উৎসুক। এই সময়েই সঙ্গীতজ্ঞ জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের অ্যাকাডেমির তরফ থেকে ‘গণদেবতা’ উপন্যাসের গানগুলি রেকর্ডিং করে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য রেকর্ডার-সহ একটি দল কলকাতায় এসে দাদুর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বেশ কয়েকটি গান। এর মধ্যে ইংরেজ সরকারের জমি-জরিপ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চাষাভুষো গ্রামবাসীর গলায় একটি গানের কথা আমার খুব মনে পড়ে। সে সময় দাদুর পনেরোটি নাতি-নাতনিই হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে দশ জন অন্তত সেই গানে অংশ নিয়েছিল। এদের মধ্যে আমিই যেহেতু প্রকাশ্যে এখানে-ওখানে গান গাইতাম, তাই আমাকেই তিনি মূল গায়কের ভূমিকাটি দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, খুব যত্ন করে ধরে ধরে সে গানটি নিজে সুর করে আমাদের তুলিয়ে দিয়েছিলেন। গানটির প্রথম কয়েকটি পঙ্ক্তি ছিল এই রকম— ‘দেশে আসিল জরীপ—/ রাজা প্যাজা ছেলেবুড়োর বুক ঢিপ ঢিপ।/ হায় বাবা কি করি উপায়/ প্রাণ যায় তাকে পারি মান রাখা দায়।/ হায় বাবা...’’
দীর্ঘ গান। মাঝে দুটো করে পঙ্ক্তি মূল গান: তার পরে ধুয়োর মতো প্রত্যেক বারই ‘হায় বাবা কি করি উপায়’ পঙ্ক্তিগুলি ঘুরে ঘুরে আসে। এই অংশটা সবাই মিলে গাওয়া হয়েছিল। সুরের মধ্যে অদ্ভুত একটা একঘেয়েমি ছিল। এটিই ছিল এই গানের বৈশিষ্ট্য। ‘বেশি সুর লাগিও না’— দাদুর কড়া নির্দেশ। শেষে ‘হায় বাবা’ বলার সময় তাঁরই নির্দেশে সুরকে তো কুলোর বাতাস দিয়ে সম্পূর্ণ বিদেয় করে দিতে হয়েছিল। তবু বলব, শেষ পর্যন্ত সেটা একটা গান হয়েই উঠেছিল। উৎপীড়িত গ্রামীণ জীবন থেকে উঠে আসা জীবন্ত লোকগান।
দাদু অসাধারণ এক চিত্রকরও ছিলেন। ১৯৬২ সালে তাঁর বড় জামাই অকালে প্রয়াত হওয়ায় শোকস্তব্ধ হয়ে তিনি দীর্ঘ সময়কাল হাতে কলমই প্রায় ধরেননি। কিন্তু জাতশিল্পী কি প্রকাশ ছাড়া বাঁচতে পারেন? তাই বুঝি ওই সময় তিনি হাতে রংতুলি তুলে নিয়েছিলেন। ছবি এঁকেছিলেন নিরন্তর। এর মধ্যে বিখ্যাত ব্যক্তিদের অনেকগুলি প্রতিকৃতি ছিল। সঙ্গে ছিল একটি আত্মপ্রতিকৃতিও। ছিল তাঁর নিজের উপন্যাসের ক’টি চরিত্রের রূপায়ণ— কৃষ্ণেন্দু, রিনা ব্রাউন প্রভৃতি। এর মধ্যে সবচেয়ে ভাল হয়েছিল ‘আরোগ্য নিকেতন’ উপন্যাসের মৃত্যুরূপিণী অমৃতস্বরূপার দার্শনিক অভিব্যক্তিপূর্ণ ছবিটি। তাঁর সব ছবিই ছিল তেলরঙে আঁকা। জলরঙে তাঁকে কখনও আঁকতে দেখিনি।

তারাশঙ্করের শিল্পীসত্তার আর একটি প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর কাষ্ঠভাস্কর্যে। অনেকেই তাঁর এই শিল্পকৃতিকে ‘কাটুমকুটুম’ নামাঙ্কিত করতে চাইলেও আমি বলব, ভাস্কর্যের মতো বিরাট আকৃতির ওই সব সৃষ্টিগুলিকে কোনও মতেই কাটুমকুটুম বলা সঙ্গত হবে না। আমার নিজের চোখে দেখা, বীরভূমের এক কাঠফাটা গ্রীষ্মের দুপুরে, দাদু শালপুকুরের পাড়ের বিরাট একটা ন্যাড়া গাছের দিকে তীক্ষ্ণ একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। যেমন প্রখর রোদ, তেমনই প্রখর রূপসন্ধানী দৃষ্টি তাঁর। ন্যাড়া ডালের ভিতরে কোথায় একটুখানি রূপের আভাস পাওয়া যায়, তা-ই তখন খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। সে দিনই বিকেলবেলা লোক ডেকে সেই সব খটখটে ডাল কাটিয়ে নিলেন। আবার ছেনি-হাতুড়ি নিয়ে শুরু হয়ে গেল শিল্পসৃষ্টি। মৎস্যকন্যা, দুটি বৃহাদাকার পাখির লড়াই ইত্যাদি বেশ কিছু অনবদ্য নির্মাণ লাভপুরের সংগ্রহশালায় রয়েছে। এই সময়টা (১৯৬২-’৬৪) দাদু লেখালেখির থেকে কারুশিল্পে মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন বেশি। টালাপার্কের বাড়ির একতলায় সামনের যে ঘরটাকে আমরা বরাবর ‘ড্রয়িংরুম’ বলে এসেছি, সেটাই ছিল দাদুর রংতুলির যজ্ঞশালা। দাদু আঁকতেন বেশির ভাগই পাতলা কাঠের ক্যানভাসে। বড় বড় অয়েল পেন্টিংকে একটু একটু করে তুলির প্রলেপে চোখের সামনে সম্পূর্ণ হতে দেখেছি। অনেক রকমের ছবি দাদু এঁকেছিলেন, কিন্তু তাঁর হাতে সবচেয়ে সফল হয়ে ফুটেছে ল্যান্ডস্কেপগুলি। হলুদ, সবুজ আর চারকোল কালো রং ব্যবহারে দেখেছি তাঁর অসাধারণ দক্ষতা। চোখের সামনে ভাসছে সবুজ ধানখেতের ওপর হলুদ রঙের রোদ্দুরের আঁচল পড়ে থাকার দৃশ্য। আর ঘন গাছের জঙ্গলে অন্ধকারের স্তর— গাঢ় থেকে আবছা, কত রকমের কালো রঙের ব্যবহার! অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এ শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ১৯৬৪ সালের অগস্ট মাসে দাদুর ছবির প্রথম প্রদর্শনী হয়। সংবাদমাধ্যমে তা যথেষ্ট প্রশংসিত, আবার নিন্দিতও হয়েছিল। এক জন তো রসিয়ে লিখলেন, ‘তারাশঙ্কর এখন তার বড় ছেলে সনৎকুমারকে নাকি ‘রথী রথী’ বলে ডাকছেন।’ দাদুকে অবশ্য নিন্দুকের এই অপচেষ্টায় কখনও বিচলিত হতে দেখিনি।
১৯৬৩ সালে এক বার দাদুর সঙ্গে লাভপুর গিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিলেন ‘দিদি’ অর্থাৎ আমার দিদিমা আর মা। দাদু তখন তাঁদের সাবেক বৈঠকখানা বাড়িটিকে সাজিয়েগুছিয়ে বাসযোগ্য করিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর জন্মভিটেয় বসবাস করছিলেন তাঁর ভাইদের পরিবার। বৈঠকখানা বাড়ির লাগোয়া বিস্তীর্ণ জায়গায় ছিল নানা রকমের গাছ আর তাঁর নিজের তদারকিতে লাগানো হরেক রকমের ফুলের কেয়ারি। ফুলের রঙে আর সৌরভে এক কথায় জায়গাটা নন্দনকাননই হয়ে উঠেছিল। এখন সেখানে তারাশঙ্কর সংগ্রহশালা আর অতিথিনিবাস হয়েছে। দাদু নিজের হাতে সে সব ফুলের যত্ন করতেন। ফুল ফোটানোর কারিগরিতে তাঁর হাতে জাদু ছিল। টালার বাড়িতেও তিনি কেয়ারি করা ফুলের বাগান করেছিলেন। দিশি ফুল ছাড়াও কত রকমের বিদেশি ফুলের নাম— শুনেই কানে ভারী মিষ্টি লাগত।
সে সময় যে ক’দিন আমরা লাভপুরে ছিলাম, কত গরিব-দুঃখী মানুষ যে তাঁদের ‘বড়বাবু’র সঙ্গে দেখা করতে আসত কী বলব! প্রত্যেক দিন বস্তা বস্তা চাল আর কাপড় আসত দোকান থেকে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চলত সে সব বিতরণের পালা। দাদুর এই দানের মধ্যে প্রাক্তন জমিদারসুলভ কোনও সস্তা অহমিকার প্রকাশ কখনও দেখতে পাইনি। আসলে সব সাঁওতাল, বাউরি, কাহার মানুষদের সঙ্গে দাদুর একটা খাঁটি ভালবাসার যোগ ছিল। তাদের প্রত্যেককে তিনি নামে চিনতেন। ‘হ্যাঁ রে, তোর ছেলেটা কত বড় হল?’ বা ‘তোর বাপের হাঁপের টানটা এখন একটু কমেছে?’— এই ভাবে প্রত্যেকের সঙ্গে খুব আপনজনের মতোই কুশল প্রশ্ন বিনিময় করতেন।
টালা পার্কের বাড়ির একতলায় অনেকগুলো ঘরের মধ্যে একটার নাম ছিল ‘ড্রয়িংরুম’, আর একটিকে আমরা ‘লাইব্রেরি ঘর’ বলতাম। সেই ঘরের চারটে দেওয়ালই বইয়ে ঠাসা। জন্মদিনে লেখকেরা তাঁকে অজস্র বই উপহার দিতেন, মূলত সেই প্রীতির দানেই লাইব্রেরি ভরে উঠেছিল। এরই নানান বই পড়ে ছোট্টবেলা থেকে আমার পড়াশোনার ভান্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। জীবনে লাইব্রেরির গুরুত্ব যে কী, জেনেছি ওই ঘরটি থেকেই। এই ঘরটিতে মেঝেতে ডেস্ক রেখে, গদি দেওয়া আসনে বসে লিখতেন দাদু। কাকে বলে ‘সাহিত্যসাধনা’ আর ‘আসনসিদ্ধি’, তা নিজের চোখে দেখেছি!