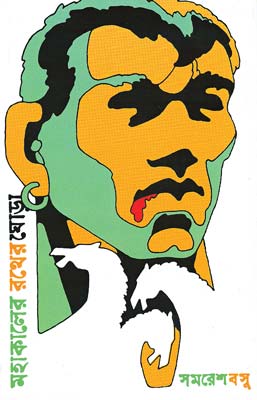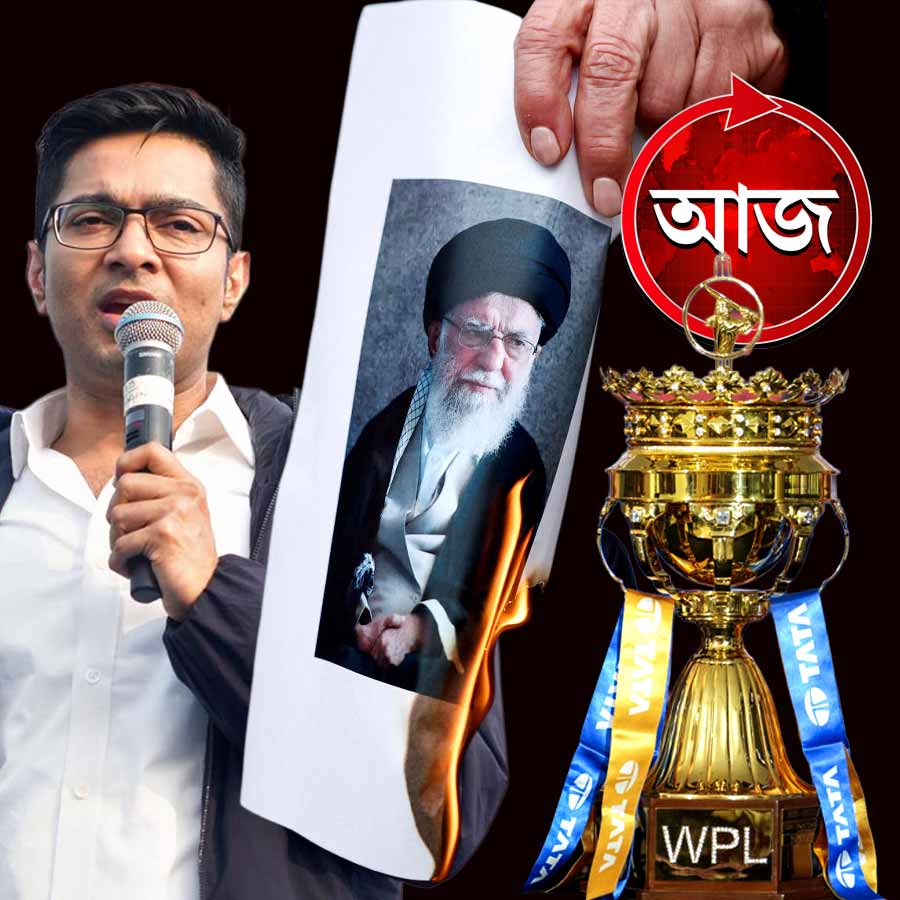ঘটনা, মেচি নদীর তরাই এলাকাতেই ওই তিন গ্রাম। নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া। সেখানেই কৃষকদের তিরে নিহত হন পুলিশ ইন্সপেক্টর ওয়াংদি। জঙ্গল সাঁওতাল ও কানু সান্যাল সেখানে তখন কৃষকদের নেতৃত্বে। রুহিতন কুরমিকে নায়ক করে সমরেশ বসুর উপন্যাস ‘মহাকালের রথের ঘোড়া’ সেই ঘোর বাস্তবকেই তুলে এনেছিল বাঙালি পাঠকের কাছে।
৫০ বছর আগে নকশাল আন্দোলনের চমৎকৃতি এখানেই। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা যাক বা না-যাক, কলরোল উঠেছিল বাংলা সাহিত্যেও। তার আগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প লিখেছেন তেভাগা নিয়ে, দেশভাগের পর উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রণা নিয়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্র থেকে প্রতিভা বসু কেউ বাকি ছিলেন না। কিন্তু নকশাল আন্দোলনের প্রভাব ছড়িয়ে গেল প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। ঝুম্পা লাহিড়ী বা নীল মুখোপাধ্যায়ের মতো কমবয়সি যে বাঙালিরা শুধুই বড়দের থেকে সেই সময়ের স্মৃতিকথা শুনেছেন, তাঁরাও আজ ইংরেজিতে ‘দ্য লোল্যান্ড’ বা ‘লাইভ্স অব আদার্স’-এর মতো উপন্যাস লেখার সময় তুলে আনছেন নকশাল-পটভূমি। ’৭০ বাংলা সাহিত্যেও মুক্তির সময়।
সমরেশ বসুর উপন্যাস ‘মহাকালের রথের ঘোড়া’ বই হয়ে বেরিয়েছিল বাম সরকার ক্ষমতায় আসার ১৯৭৭-এ। তার তিন বছর আগেই বেরিয়ে গিয়েছে মহাশ্বেতা দেবীর ‘হাজার চুরাশির মা’। পুলিশের গুলিতে নিহত ব্রতী, তার মা সুজাতা শেষ অবধি অ্যাপেন্ডিসাইটিস বার্স্ট করে মারা যান। তারও আগে ১৯৭১-এ ‘দেশ’ পত্রিকায় বেরিয়েছে অসীম রায়ের গল্প ‘অনি’। গোলদিঘিতে বিদ্যাসাগরের মাথা যারা কেটেছে, কলেজ-পড়ুয়া অনি সেই দলের শরিক। গল্পের শুরুতেই বাবাকে শোনায় সে, ‘তোমরাই না বলতে বাবা, বাংলাদেশের রেনেসাঁটা বোগাস?’ অনিকে এক দিন বাড়ির মধ্যেই ঘিরে ফেলে বিরোধী ছেলেরা। কাঁটাপুকুর মর্গে লাশ আনতে গিয়ে বাবা শোনেন জমাদারের ডাক, ‘চোর অনি। বাড়ির লোক কে আছেন?’ প্রশ্নমুখর তারুণ্যকে দলে-পিষে-থেঁতলে যে চোর গুন্ডা আখ্যা দিতেও ছাড়ে না রাষ্ট্রযন্ত্র, বাংলা গল্প তুলে ধরেছিল সেই কাহিনিও!


মেয়েদের দিকেও নজর দিয়েছিল নকশাল আন্দোলন। সমরেশ মজুমদার তাঁর উপন্যাাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী মাধবীলতার কথা লেখেন। আর সমরেশ বসু ‘শহিদের মা’ গল্পে তুলে ধরেন মফস্সলের এক বাড়ির কথা। বাদলের বাবা পুরনো কংগ্রেসি, দুই দাদা সরকারি বামপন্থী পার্টি করে। বাদল নকশাল। বাবা বাড়িতে এসে মাকে বলেন, ‘তোমার ছোট ছেলে আগুন নিয়ে খেলছে।’ দুই দাদাও ভাইকে একই হুমকি দেয়। শেষ অবধি বাদল খুন হয়, পাড়ার ছেলেরা তার নামে শহিদ বেদি তৈরি করে। তার এক বছর পরে বাদলের মৃত্যুদিনে স্ত্রীকে দুপুরের খাবার বাড়তে বলেন স্বামী, বড় ছেলে ও মেজ ছেলে মা’কে বারংবার খেতে দিতে বলে। কিন্তু ‘শহিদের মা’ সে দিন রান্নাই বসান না। পুরুষতান্ত্রিক পার্টিজান রাজনীতির প্রতি মধ্যবয়সিনী এক মায়ের নীরব প্রতিবাদটাই গল্পে তুলে ধরলেন সমরেশ।
পিছিয়ে নেই কবিরাও। লিখছেন শঙ্খ ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জানান, ‘মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চিৎকার করে।’ সরোজ দত্ত জানাচ্ছেন রাজার লালসায় গর্ভিণী আশ্রমবালিকার কথা, ‘রাজার প্রসাদভোজী কবি রচে শকুন্তলা।’ সমর সেন এই সময় কবিতার পৃথিবী থেকে বহু দূরে, কিন্তু ‘ফ্রন্টিয়ার’ বা ‘নাউ’ পত্রিকায় আগুন ছড়াচ্ছে তাঁর কলম।
বাঙালির তাত্ত্বিক দুনিয়াতেও কি প্রভাব ফেলেনি এই আন্দোলন? গোলদিঘিতে বিদ্যাসাগরের কাটা মুণ্ড গড়াগড়ি যাওয়ার কয়েক বছর পরে কলকাতাতেই তাঁর ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর: অ্যান ইলিউসিভ মাইলস্টোন’ লেখার খসড়া পড়ে শোনাচ্ছেন অশোক সেন। অনেক পরিকল্পনা সত্ত্বেও উপনিবেশের অর্থনীতি কী ভাবে বিদ্যাসাগরকে সফল হতে দেয়নি, তারই বিবরণ। সামনে বসে গৌতম ভদ্র, দীপেশ চক্রবর্তীর মতো আগুনখেকো ছাত্ররা।
সময় বদলে যায়! সমরেশ মজুমদার তাঁর নিবন্ধে শৈবাল মিত্রের কথা লিখেছেন। অগ্নিঝরা সেই সময় নিয়ে শৈবালের উপন্যাস ‘অজ্ঞাতবাস’। সেখানে, এক জায়গায় জোতদার খুনের কাহিনি জেনে নায়ক তপুর শরীর গুলিয়ে ওঠে। ‘ডজন ডজন জোতদার খতম করে কি গ্রামের অর্থনৈতিক কাঠামো বদলানো যায়?’ নেতাদের কাছে যে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি, সেই প্রশ্নই তুলে ধরা হল সাহিত্যে।
ভিন্ন প্রজন্মে মা, ছেলে একই আন্দোলন নিয়ে লিখছেন, বাংলা সাহিত্যে তারও উদাহরণ এখানেই। মহাশ্বেতা ‘হাজার চুরাশি...’ লেখার দুই দশক পরে তাঁর পুত্র নবারুণ ভট্টাচার্যের কলমে বেরিয়ে এল ‘হারবার্ট’। ন্যালাখ্যাপা হারবার্টের মৃতদেহ তোশকসুদ্ধু কেওড়াতলার ইলেকট্রিক চুল্লিতে ঢুকিয়ে দেওযা হয়। হারবার্টের মৃত নকশাল বন্ধু বিনু একদা ওই তোশকেই ঢুকিয়ে রেখেছিল ডিনামাইট স্টিক। সেটিই চুল্লির আগুনে ফেটে পড়ল, ‘কী ভাবে বিস্ফোরণ ঘটবে এবং তা কে ঘটাবে সে সম্বন্ধে জানতে রাষ্ট্রযন্ত্রের এখনও বাকি আছে।’