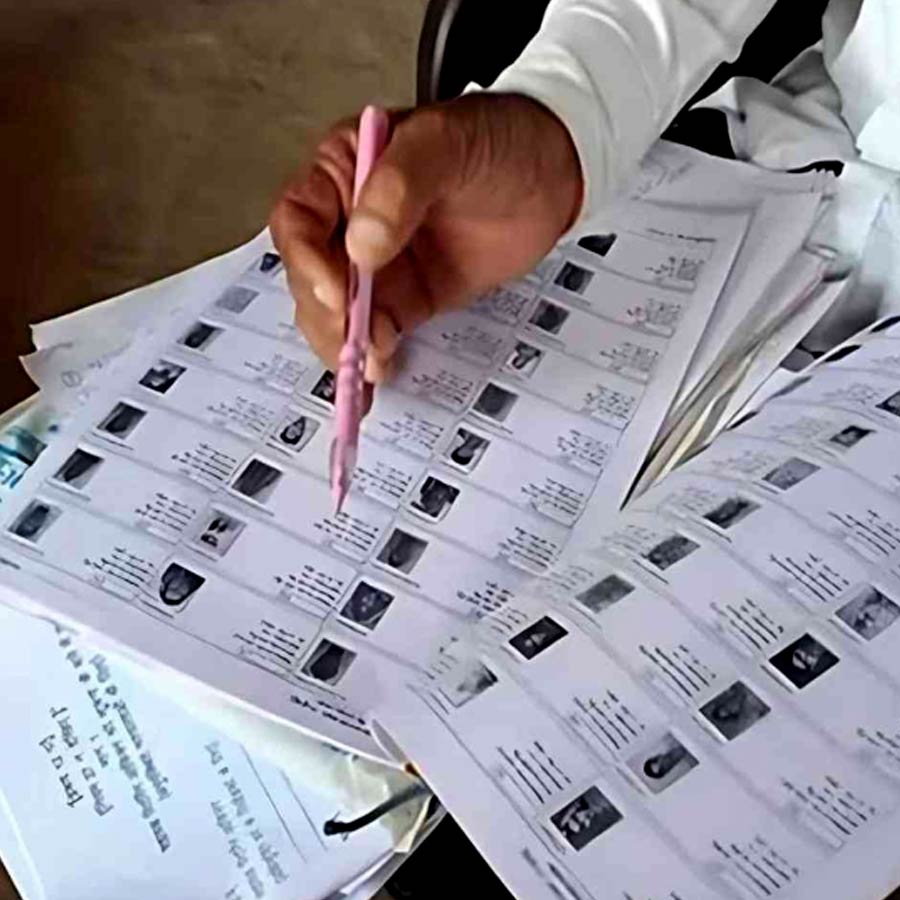দলিত বোধ গড়ে ওঠার সমস্ত উপাদান থাকা সত্ত্বেও বাংলায় ‘দলিত’ ধারণাটির আকার পেতে বহু সময় লেগে গেছে। দলিত আন্দোলনের সংগঠক, মরাঠি কবি অর্জুন ডাংলে দলিত বোধকে বলছেন বিদ্রোহী; তার আনুগত্য বিজ্ঞানের প্রতি, এবং শেষ পর্যন্ত তার চরিত্র হয়ে ওঠে বিপ্লবী। সম্ভবত, বাংলার সমাজে বিদ্রোহ, বিজ্ঞান এবং বিপ্লব সম্পর্কিত ধারণাগুলোকে মনে করা হয়েছিল স্বয়ম্ভু, এদের যেন কোনও সামাজিক উৎস থাকার ব্যাপার নেই। যে জাতিব্যবস্থা মানুষকে ঊনমানব করে তোলে, মানুষে মানুষে বিভেদ ও বিদ্বেষের প্রধানতম একটি উপাদান হিসেবে দেখা দেয়, এবং সমাজের বিরাট অংশের মানুষের শ্রমের ফল লুট করার জন্যই তাঁদের ‘দলিত’ করে রাখে, সেই ব্যবস্থার শিকড় এতটাই গভীরে যে, দলিতদের পক্ষে নিজেদের সংগঠিত করে তোলার পথেও সামাজিক, রাজনৈতিক এবং দার্শনিক বাধাও ছিল বিপুল।
সে বাধা যে একেবারে দূর হয়েছে তা বলা যাবে না, কিন্তু হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রজ্ঞায় প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ থেকে চলে আসা সামাজিক আন্দোলন এবং যোগেন মণ্ডলের নেতৃত্বে রাজনৈতিক সমাবেশ থেকে যে চেতনার উন্মেষ হয়েছিল, তা পরবর্তী কালে পশ্চিমবঙ্গে ‘দলিত’ ধারণাটির বিকাশের পথ খুলে দিয়েছে— শুরু হয়েছে দলিত সাহিত্য আন্দোলন। এ কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে, বোধি ও অনুশীলন— উভয় প্রকার সমৃদ্ধির পিছনেই নমশূদ্র জাতি সম্প্রদায়ের ভূমিকা বিরাট। মতুয়া আন্দোলনের মতো সামাজিক পুনর্নির্মাণ থেকে শুরু করে শিক্ষা ও চাকরিতে সংরক্ষণের পক্ষে রাস্তায় নামা পর্যন্ত বহুবিধ পথের দাবি বাংলায় বিভিন্ন নিম্নবর্ণ সম্প্রদায়কে নিজেদের মধ্যে, এবং পরস্পরের সঙ্গে, একত্র হয়ে দলিত চৈতন্য নির্মাণের উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। এই সব উপাদানের নির্মাণে নমশূদ্ররা অগ্রপথিক হিসেবে কাজ করেছেন।
বাংলার নমঃশূদ্র ১
সম্পা: কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর
৪০০.০০
কেএনটিএএ
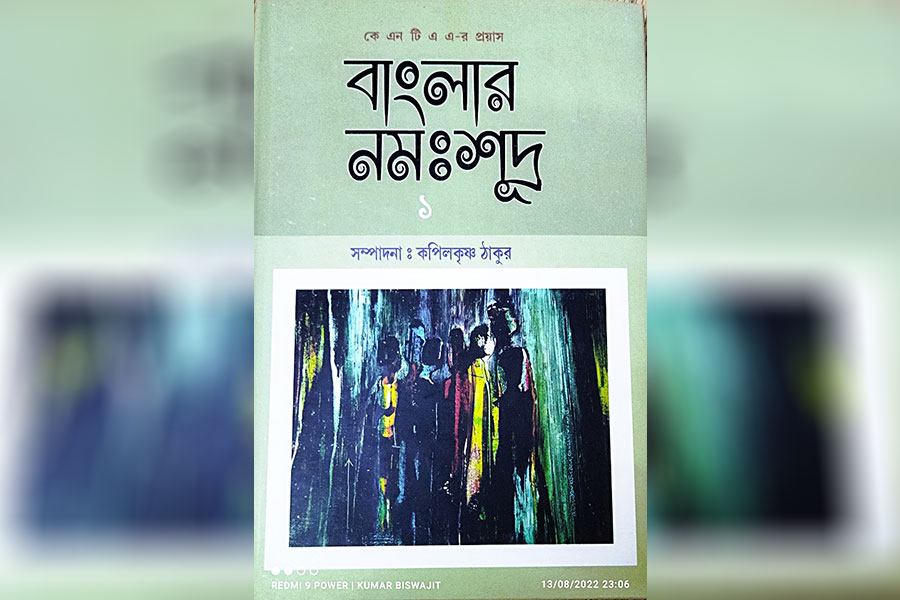

অথচ, কী ভাবে তাঁরা এই পথের নির্মাণে যোগ দিয়েছেন, কী তার সামাজিক ব্যাপ্তি ও বুদ্ধিগত গভীরতা, কেমন তার সংহতির প্রয়াস ও মননের অনুশীলন— এ সব নিয়ে সাধারণ পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার মতো প্রায় কিছুই ছিল না। কেবল নমশূদ্র নয়, কেবল দলিত জাতিসমূহই নয়, গোটা বাংলা ভূখণ্ড ও বাংলাভাষী মানুষের পক্ষেই অতি গুরুত্বপূর্ণ এই দিকটি নিয়ে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের বিশেষ কোনও প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। সৌভাগ্যের কথা, এই অভাব পূরণের একটা উদ্যোগ হিসেবে উঠে এসেছে নমশূদ্র ইতিহাস কংগ্রেস। ২০১৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এই কংগ্রেসে বলা হয়, “নমশূদ্র সমাজের তথ্যসমৃদ্ধ পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করতে হবে।”
সেই মোতাবেক সাহিত্যিক ও গবেষক কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে, বাংলার নমঃশূদ্র-র প্রথম খণ্ড। এই সঙ্কলনে আছে বারোটি প্রবন্ধ, একটি পরিশিষ্ট ও কিছু ছবি। নমশূদ্র ইতিহাস চর্চার সামাজিক সংযোগ, উৎস সন্ধান, ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় নমশূদ্র, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই জাতির অবদান, সংরক্ষণ আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকা, শিক্ষা বিস্তারে তাঁদের বিস্তৃত যোগদান, সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে নমশূদ্র, চিকিৎসা পেশায় তাঁদের ব্যুৎপত্তি, নমশূদ্র ইতিহাসের গবেষণায় সমীক্ষার বিবরণ-সহ বিভিন্ন বিষয়ে লেখা এই প্রবন্ধগুলি প্রচলিত ইতিহাস-বিশ্বাসকে পুনর্বিবেচনায় প্রস্তুত করতে পারে। পাশাপাশি, বাঙালি জাতিগঠনে দলিতের ভূমিকা এবং দলিত অস্তিত্ব, চেতনা ও আন্দোলনের ইতিহাস-রচনার পথ খুলতেও এই উদ্যোগ বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে।
নজরে
একই খরচে তৈরি করা যাবে দশ গুণ শক্তিশালী কম্পিউটার কিংবা স্মার্টফোন। সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ কমে হয়ে যাবে পাঁচ ভাগের এক ভাগ। এক জন মানুষের জিনোম-শৃঙ্খল সম্পূর্ণ ‘লিখে’ ফেলার সামর্থ্য বাড়বে একশো গুণ। কল্পবিজ্ঞান নয়। প্রযুক্তি যে ভাবে এগিয়ে চলেছে, সেই অনুসারে আগামী দশ বছরের মধ্যে ঘটে যাবে এই সবই। জানাচ্ছেন ব্রিটেনের প্রযুক্তিবিশারদ আজ়িম আজ়হার। তাঁর বইয়ের নাম এক্সপোনেনশিয়াল। গণিতশাস্ত্রের অন্যতম মৌলিক এই ধারণাটিকে লেখক একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করেছেন: কোনও প্রযুক্তির উৎপাদনশীলতা যদি কয়েক দশক ধরে প্রতি বছর অন্তত ১০ শতাংশ হারে বেড়ে চলে, তা হলে তাকে তিনি এক্সপোনেনশিয়াল প্রযুক্তি বলবেন। কম্পিউটার প্রযুক্তি, সৌরবিদ্যুৎ, জিন-প্রযুক্তি, থ্রি-ডি প্রিন্টিং বা ত্রিমাত্রিক মুদ্রণের মতো অনেক ক্ষেত্রে ঠিক এটাই ঘটছে। আমরা তার অভিঘাত টের পাচ্ছি পদে পদে, ‘প্রযুক্তির বিস্ফোরণ’ গোছের কথা বলছিও আকছার, কিন্তু সামর্থ্যের এই অ-পূর্ব অতিবৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর হাল কী দাঁড়াবে, সেটা কি ভাবতে পারছি?
এক্সপোনেনশিয়াল: অর্ডার অ্যান্ড কেয়স ইন অ্যান এজ অব অ্যাক্সেলারেটিং টেকনোলজি
আজ়িম আজ়হার
৫৯৯.০০
পেঙ্গুইন
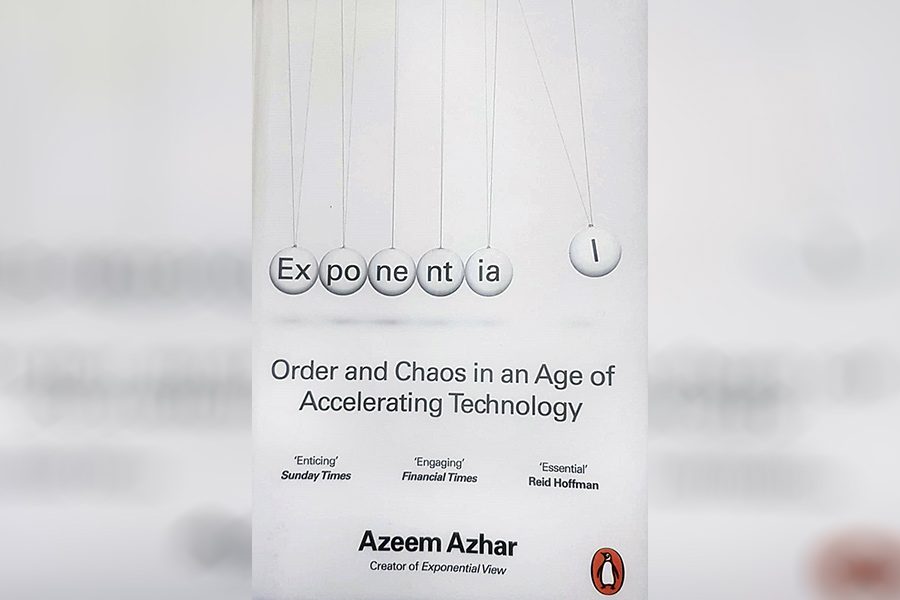

আজ়িম আজ়হারের বক্তব্য, বহুলাংশেই পারছি না। আর এই না-পারার ফলে ক্রমশই নিজেদের ঠেলে দিচ্ছি এক গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে। প্রযুক্তির বিস্ফোরণ যে অমিত প্রাচুর্যের সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে, তা হয়ে উঠছে বিপুল সঙ্কটের অনুঘটক। সঙ্কট বহুমাত্রিক। তবে তার প্রথম এবং প্রধান মাত্রাটি হল অসাম্য। সেই অসাম্যের এক দিকে আছে দুনিয়া জুড়ে বিভিন্ন শিল্পে ও পরিষেবায় অতিকায় পুঁজির অভাবনীয় অভিযান এবং তার দাপটে ছোট ও মাঝারি উদ্যোগের সর্বনাশ, অন্য দিকে সম্পদ এবং আয়ের বণ্টনে শ্রমজীবী মানুষের অংশ অতি দ্রুত কমে আসা। আসলে এ হল একই প্রক্রিয়ার দু’টি দিক।
অসাম্য বৃদ্ধির এই গল্প এখন পরিচিত, চর্চিতও। কিন্তু এই গল্পে প্রযুক্তির ভূমিকা ঠিক কেমন, বিশেষত প্রযুক্তির অগ্রগতি কী ভাবে একই সঙ্গে সম্ভাবনা এবং সঙ্কটের উৎস হতে পারে, সেটা লেখক বহু বাস্তব দৃষ্টান্ত দিয়ে, তথ্য-পরিসংখ্যান সহযোগে দেখিয়েছেন। প্রযুক্তি একটি চাবি, যা দিয়ে স্বর্গের দরজা খোলা যায়, নরকেরও। কোন দরজা খুলব, সেটা আমাদেরই দায়।